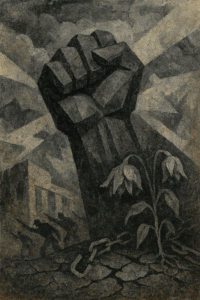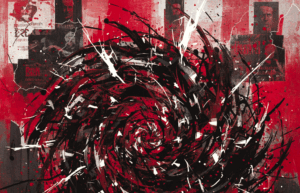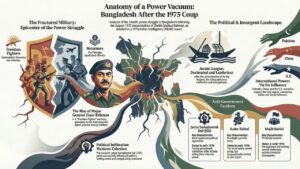This post has already been read 126 times!
মূল: স্তেফানি প্রেজিওসো
জ্যাকোবিন, ২১/১১/২০২৫
তিন দশকেরও বেশি সময় আগের কথা। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ টিম মেসন তখন একটি বড়সড় সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, গবেষণা আর লেখালেখির জগত থেকে ফ্যাসিবাদের গভীর তত্ত্ব বা সুস্পষ্ট ধারণাগুলো যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জার্মান নাৎসিবাদের তুলনা করতে গিয়ে তিনি পণ্ডিতদের একটি বিশেষ পরামর্শ দেন। তিনি বলেছিলেন, এই দুই শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় অমিল—সেটা সুনির্দিষ্টভাবে খুঁজে বের করতে হবে। একই সঙ্গে, এদের কোনো একটি অন্যদের চেয়ে ‘একেবারেই আলাদা’ বা ‘অনন্য’—এমন ধারণা আঁকড়ে না থেকে বরং একটি নিরপেক্ষ ও সংশয়বাদী দৃষ্টি বজায় রাখা উচিত। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, যখন ফ্যাসিবাদের আলোচনা সর্বত্র শোনা যাচ্ছে, তখন মেসনের সেই পুরনো বিতর্ক বা তর্কগুলোকে হয়তো অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাঁর তোলা প্রশ্নগুলো আজও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।
লাতিন আমেরিকা থেকে ভারত, কিংবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাশিয়া হয়ে পুরো ইউরোপ—সবখানেই উগ্র ডানপন্থীদের দাপট বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের উত্থানকে কেবল ওপর-ওপর না দেখে গভীর ঐতিহাসিক জ্ঞান আর বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা এখন সময়ের দাবি। এই শক্তিগুলোর উত্থান দেখে শুরুতে ধাক্কা লাগাটা স্বাভাবিক, কিন্তু তার পরপরই জরুরি প্রশ্নটি সামনে আসে: এর মোকাবিলা করব কীভাবে? এদের এজেন্ডা রুখে দিতে হলে সমাজের মানুষকে কীভাবে সতর্ক ও সংগঠিত করা যাবে? ফ্যাসিবাদের এই আপাত ‘প্রত্যাবর্তন’-এর শিকড় খুঁজে বের করা মোটেও সহজ কাজ নয়। আর আদৌ কি একে ‘ফ্যাসিবাদ’ বলা ঠিক? আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোঝাতে ‘ফ্যাসিবাদ’ শব্দটি ব্যবহার করা নিয়েও তুমুল বিতর্ক রয়েছে। কারো কারো মতে, এই শব্দটি ব্যবহার করা জরুরি, কারণ এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে সামনে কী ভয়ংকর দিন আসতে পারে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের বর্তমানকে বোঝার আলো দিতে পারে ঠিকই, তবে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে না।
‘ফ্যাসিবাদ’ শব্দটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েই চলেছে, আর তা জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন বিতর্কের। লেট ফ্যাসিজম, প্রিভেন্টিভ ফ্যাসিজম, এন্ড-টাইম ফ্যাসিজম, ফসিলাইজড বা জীবাশ্মভূত ফ্যাসিজম, ট্রাম্পিস্ট ফ্যাসিজম—এর সাথে আবার যোগ হয়েছে ‘নব্য-’, ‘উত্তর-’, ‘প্যারা-’, ‘সেমি-’, ‘মাইক্রো-’, এমনকি ‘টেকনো-ফ্যাসিবাদ’। অবিরাম ধেয়ে আসা এই শত্রুকে বোঝাতে বিশেষণের কোনো অভাব নেই। কিন্তু নতুন নতুন পরিভাষার এই পাহাড় মূলত একটি গভীর সংকটকেই আড়াল করে রাখছে। সংকটটা হলো—আমরা এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি, যা বিংশ শতাব্দীর অন্ধকারতম দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিলেও, অনেক দিক থেকেই তা আসলে সম্পূর্ণ নতুন।
ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম একবার বলেছিলেন, মানুষ যখন এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় যার কোনো অভিজ্ঞতা তাদের অতীতে ছিল না, তখন সেই অজানা বিপদকে চেনার জন্য তারা হাতড়ে বেড়ায় পরিচিত কোনো নাম বা শব্দ—যদিও সেই জিনিসটিকে তারা পুরোপুরি সংজ্ঞায়িত করতে পারে না বা বুঝতেই পারে না। এই অবস্থায় উপমা বা সাদৃশ্য খোঁজাটাই হয়তো একমাত্র পথ বলে মনে হয়। অচেনা কোনো কিছুকে বোঝার জন্য এটি একটি চেনা ভিত্তি তৈরি করে দেয় এবং দ্রুত প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো একটা কাঠামোও জোগায়।
কিন্তু সমস্যা বাধে তখনই, যখন শত্রুকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে যাওয়া হয়। লড়াই তো করতেই হবে—কিন্তু কার বা কিসের বিরুদ্ধে? চোখের সামনে বিপদ দেখে মনে হয়, একে সরাসরি মোকাবিলা করতে হলে একে ‘ফ্যাসিবাদ’ নামেই ডাকতে হবে। অথচ এই পুরনো শব্দটি আঁকড়ে ধরার বিপদও আছে। এতে আমরা অতীতের ব্যাখ্যার মধ্যেই আটকে থাকতে পারি, যা আজকের বাস্তবতাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে এবং কার্যকর জবাব তৈরি করতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইতিহাসবিদ ড্যানিয়েল বেসনার যেমনটি বলেছেন, “পরিস্থিতি ভয়ের হতে পারে—এবং পরিস্থিতি সত্যিই ভয়ের—কিন্তু তার মানেই এই নয় যে সেটা ফ্যাসিবাদ। সত্যি বলতে, বর্তমান পরিস্থিতি হয়তো ফ্যাসিবাদের চেয়েও বেশি ভয়ংকর হতে পারে।”
তাই মেসনের সেই পরামর্শ—আবেগমুক্ত তুলনা এবং মিল ও অমিল উভয় দিক বিচার করে দেখার পদ্ধতিটিই—আজকের দিনে আমাদের পথ দেখাতে পারে। আজকের উগ্র ডানপন্থীদের বুঝতে হলে পুরনো সংজ্ঞার প্রতি মোহ বা ভয়ের বশে দেওয়া কোনো উপমা কাজ করবে না; বরং প্রয়োজন ধৈর্যশীল ও গভীর বিশ্লেষণ। এটা না থাকলে আমাদের প্রতিরোধ অন্ধ, বিক্ষিপ্ত কিংবা বড্ড দেরিতে শুরু হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। ১৯২০ ও ৩০-এর দশকে, যারা ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা দিচ্ছিলেন, তাঁদের বড় অংশই তখন এর অভিনব দিকটি ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আজ আমাদের ঠিক সেই একই ভুল বা ফাঁদটি এড়িয়ে চলতে হবে।
ফ্যাসিবাদ কী?
রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদের অস্তিত্ব বা এর পুনরুত্থান নিয়ে প্রশ্নটি নিয়মিত বিরতিতেই ফিরে আসে। গত ত্রিশ বছরে ইতালিতে বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। আর ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে, বিশেষ করে তিনি যখন নিজের বিশেষ ক্ষমতাগুলোর পরিধি বাড়িয়েছেন এবং সংবিধানের মূল ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। ‘নতুন’ ফ্যাসিবাদী বিপদের সতর্কবার্তা দেওয়া বইতে লাইব্রেরির তাকগুলো ভরে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে—এবং মানুষের মনোজগতে—ফ্যাসিবাদের যে কেন্দ্রীয় অবস্থান, সেটাই সম্ভবত এর আজও টিকে থাকা বা গুরুত্ব পাওয়ার অন্যতম কারণ।
সমসাময়িক উগ্র ডানপন্থীদের এই উত্থানকে একটি বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ফেলে বিচার করার প্রচেষ্টাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বিশ্বনেতা বা আন্দোলনকে ‘ফ্যাসিবাদী’ তকমা দেওয়া যাবে কি না, তা যাচাই করতে প্রায়ই ইতিহাসবিদদের ‘বিশেষজ্ঞ’ হিসেবে ডাক পড়ে। কিন্তু তাঁরা দ্রুতই এক জটিল সমস্যায় পড়েন। ইতিহাসবিদ এমিলিও জেনটাইল যেমনটা লিখেছিলেন, এটি একটি ‘রহস্যময় বস্তু’। রাজনৈতিক শব্দভান্ডারে সম্ভবত ‘ফ্যাসিবাদ’ শব্দটিই সবচেয়ে অস্পষ্ট। তবে প্রায়ই দেখা যায়, এই অস্পষ্টতার দোহাই দিয়েই নতুন আরেকটি সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন এই নতুন ঘটনাটির—অর্থাৎ গণসমাজ ও কর্তৃত্ববাদের এই অদ্ভুত মিশ্রণের—আবির্ভাব ঘটে, তখন থেকেই এটি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। প্রতিটি ব্যাখ্যায় হয়তো কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা নৈতিক দিককে প্রধান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এর প্রায় সব সংজ্ঞাতেই কিছুটা সত্য থাকে, যদিও পরিস্থিতি অনুযায়ী যেগুলো খাপ খায় না, সেগুলোকে আড়ালে সরিয়ে রাখা হয়।
যদি খুব সহজে বা ‘পকেট ফর্মুলা’ হিসেবে বলতে হয়, তবে ফ্যাসিবাদকে বর্ণনা করা যায় একটি চরম ডানপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে, যা ১৯২০, ৩০ ও ৪০-এর দশকে ইতালি ও জার্মানিতে পূর্ণ রূপে বিকশিত হয়েছিল। এটি ছিল উগ্রভাবে মার্কসবাদ-বিরোধী, বর্ণবাদী, ইহুদিবিদ্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী। গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা ধ্বংস করা, সমতাকে অস্বীকার করা, দুর্বল ও অসহায়দের হেয় প্রতিপন্ন করা এবং নারীদের অবদমন করার ওপর ভিত্তি করেই এটি গড়ে উঠেছিল।
বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ফ্যাসিবাদ কেবল তখনই ছড়াতে পেরেছিল, যখন শ্রমিক আন্দোলন আর শাসকদের জন্য তাৎক্ষণিক হুমকি হিসেবে ছিল না। ১৯২০ ও ৩০-এর দশকে ইউরোপীয় সমাজে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে ফ্যাসিবাদের উত্থান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন—”এমন একটি দল যা নিজস্ব লক্ষ্য হাসিলের জন্য সংগঠিত এবং কেবল নিজেদের স্বার্থেই ক্ষমতা দখলে মরিয়া।” ফ্যাসিবাদের মধ্যে জন্মগতভাবেই একটি নাশকতামূলক বা বিধ্বংসী ঝোঁক ছিল: এটি একই সাথে ছিল বিপ্লবী আবার পুরনো ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতি; গণতন্ত্র এবং এনলাইটেনমেন্ট বা যুক্তিবাদের যুগের প্রত্যাখ্যানের এক আধুনিক প্রকাশ।
ফ্যাসিবাদের বিজয়ের নেপথ্যে ছিল আধা-সামরিক বাহিনীর সহিংসতা ও রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের যৌথ ভূমিকা, আর সেই সঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছিল সত্যিকারের এক গণআন্দোলন। রক্ষণশীলতা আর আধুনিকতা—এই দুই আপাত-বিপরীত ও ভিন্নমুখী উপাদানের এক অভূতপূর্ব মিলন ছাড়া ফ্যাসিবাদের পক্ষে মানুষের মন জয় করা অসম্ভব ছিল। জোসেফ গোয়েবলস একেই যথার্থ নাম দিয়েছিলেন—”ইস্পাত-কঠিন রোমান্টিকতা”। মানুষের মাঝে নতুন এক উঁচু-নিচু ভেদাভেদ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ফ্যাসিবাদ যেমন সহিংসতা ও সন্ত্রাসের ওপর নির্ভর করত, তেমনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত মগজধোলাই বা মতাদর্শিক দীক্ষাকে।
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী ডানপন্থার সঙ্গে ঐতিহাসিক ফ্যাসিবাদের যেমন স্পষ্ট যোগসূত্র ছিল, ঠিক তেমনি আজকের উগ্র ডানপন্থীদের সঙ্গেও সেই পুরনো ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ছাপ স্পষ্ট। একইভাবে, আজকের আমলের উগ্র ডানপন্থী আন্দোলনগুলোও জাতীয়তাবাদী, বর্ণবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, সমকামবিদ্বেষী, উগ্র পৌরুষবাদী, কর্তৃত্বপরায়ণ এবং মার্কসবাদবিরোধী। জাতীয় ও জন-ঐক্যের দোহাই দিয়ে তারা শ্রেণিসংগ্রামের ধারণাকে পুরোপুরি নাকচ করে দেয়। যেসব সামাজিক আন্দোলন তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সেগুলো এবং মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা গুঁড়িয়ে দেওয়াই এদের লক্ষ্য।
তারা নারীর অধিকারের ওপর আক্রমণ চালায় এবং ইহুদি, মুসলিম বা অন্যান্য গোষ্ঠীকে ‘বলির পাঁঠা’ হিসেবে চিহ্নিত করে। সংখ্যালঘু হোক বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ—যেই তাদের কল্পিত জাতীয়তাবাদের ছাঁচে খাপ না খায়, তাকেই সামাজিকভাবে কলঙ্কিত ও অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং নির্বাচনের মাঠ গরম করতে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারকে কাজে লাগানো হয়।
বর্তমানে অভিবাসী ও মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর মধ্যে এই প্রবণতা খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়, যার মূলে কাজ করে ‘গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট’ বা জাতি-প্রতিস্থাপনের মতো আজগুবি তত্ত্বের ভয়। এই ‘অপর’কে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতিসত্তা বা পরিচয় নিয়ে এক বর্জনমূলক বয়ান। এর উদ্দেশ্য হলো—জাতি ‘হুমকির মুখে’ বা ‘বিপদগ্রস্ত’, এই ধুয়া তুলে কর্তৃত্বপরায়ণ নীতিগুলোকে বৈধতা দেওয়া। এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে—ডোনাল্ড ট্রাম্প, জর্জিয়া মেলোনি, ভিক্টর অরবান এবং হাভিয়ের মিলের মতো নেতাদের নির্বাচনী কৌশল ও কথাবার্তার সঙ্গে বেনিতো মুসোলিনি ও অ্যাডলফ হিটলারের কৌশলের এক বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
ঐতিহাসিক ফ্যাসিবাদ আর আজকের উগ্র ডানপন্থী আন্দোলন—উভয়েরই উত্থানের পটভূমিতে কিছু মিল রয়েছে। যেমন—দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট; প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর মানুষের আস্থা কমে যাওয়া এবং প্রতিনিধিত্বের সংকট; সমাজে এক ধরনের দিশেহারা ভাব; এবং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয়—যেখানে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকেও সন্দেহের চোখে দেখা হয়। তবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক বিচার করলে দেখা যায়, প্রেক্ষাপট আসলে অনেকটাই ভিন্ন এবং বর্তমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটগুলোর ধরনও এক নয়।
ঐতিহাসিক ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক পরে, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন কোটি কোটি শ্রমিকের কাছে এক নতুন আশার দিগন্ত হয়ে উঠেছিল। আজকের দিনে তেমন কোনো বিকল্প বা আশার অস্তিত্ব নেই। ঐতিহাসিক ফ্যাসিবাদ একটি সর্বাত্মকবাদী ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল, যাকে দার্শনিক হান্না আরেন্ডট বর্ণনা করেছিলেন ‘মগজধোলাই আর সন্ত্রাসের এক নজিরবিহীন মিশ্রণ’ হিসেবে।
এর বিপরীতে, আজকের উগ্র ডানপন্থীরা অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কট্টর মুক্তবাজার-পন্থী, যদিও তারা রাষ্ট্রের দমন-পীড়নমূলক ক্ষমতা ব্যাপক হারে বাড়াতে চায়। হাভিয়ের মিলে বা ইলন মাস্কের মতো ব্যক্তিরা ‘আমলাতন্ত্র’ ধ্বংস করার প্রতীক হিসেবে করাত উঁচিয়ে ধরেন। কিন্তু বাস্তবে, ‘আমলাতন্ত্র’র দোহাই দিয়ে তাঁরা যা ধ্বংস করতে চান তা হলো সামাজিক নিরাপত্তা ও জনসেবামূলক খাত—সেগুলো যতই নড়বড়ে হোক না কেন। তাঁরা মূলত বিগত দশকগুলোর সেই নিওলিবারেল বা নয়া-উদারবাদী নীতিগুলোকেই আরও চরম রূপ দিচ্ছেন, যেখানে রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে চিত্রিত করা হতো। এটি রোনাল্ড রিগ্যানের ১৯৮১ সালের সেই ঘোষণারই প্রতিধ্বনি: “সরকার কোনো সমাধান নয়, সরকারই মূল সমস্যা।”
ঐতিহাসিক ফ্যাসিবাদ টিকে ছিল একটি সুসংহত মতাদর্শ এবং আধা-সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত বিশাল গণআন্দোলনের ওপর। জার্মানির ‘এসএ’ বা ইতালির ‘ব্ল্যাকশার্ট’-এর মতো বাহিনীগুলোতে লাখ লাখ ইউনিফর্ম-পরা সদস্য ছিল। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল শ্রমিক ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া, যাদের লাখো সদস্য সমাজতান্ত্রিক এজেন্ডার পক্ষে ছিল। আজকের দিনে শ্রমিকদের তেমন বিশাল কোনো সংগঠন নেই, আর সমসাময়িক উগ্র ডানপন্থী আন্দোলনগুলোও আগের মতো এমন ব্যাপক জনসমাবেশের ওপর নির্ভরশীল নয়। বর্তমানে কিছু সক্রিয় এবং সহিংস ডানপন্থী গোষ্ঠী অবশ্যই আছে, কিন্তু দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তাছাড়া, তারা কোনো একক রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র শাখা হিসেবে কেন্দ্রীভূত নয়—অন্তত এখন পর্যন্ত তো নয়ই।
এই আন্দোলনগুলোর প্রভাব মূলত ভোট বা নির্বাচনের রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ। তবে একথা ঠিক যে, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ট্রাম্পের সমর্থকরা যখন ক্যাপিটল হিলে হামলা চালিয়েছিল, তখন অনেকের মনেই অভ্যুত্থান চেষ্টার ভয় জেগেছিল। এমনকি ওই ঘটনাকে ১৯২৩ সালে হিটলারের ব্যর্থ ‘বিয়ার হল পুটশ’ বা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। আজ কেউ কেউ এমনও সতর্ক করছেন যে, ট্রাম্পের হাতে ‘ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট’ বা আইসিই হয়তো একটি সংগঠিত সশস্ত্র বাহিনী হিসেবেই ব্যবহৃত হতে পারে। ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভরসা রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস-এর ওপর। এটি এমন একটি আধা-সামরিক সংগঠন, যাদের মাঠপর্যায়ের শক্তি আর মতাদর্শিক শেকড়—দুটোই বেশ গভীর। ইতালিতেও নব্য-ফ্যাসিবাদী দল ‘ফোরজা নুওভা’-র সদস্যদের সহিংস আক্রমণ—যেমন ২০২১ সালের অক্টোবরে সিজিআইএল ট্রেড ইউনিয়ন সদর দপ্তরে ভাঙচুর—ভবিষ্যতে এমন জমায়েত বা হামলার এক উদ্বেগজনক ইঙ্গিত দেয়।
তবুও, আজ যদি আমরা ফ্যাসিবাদের কথা বলি, তবে একে বলতে হবে এমন এক ফ্যাসিবাদ, যার সেই আগের মতো গণআন্দোলনের চরিত্র বা ব্যাপকতা নেই। তবে আলবার্তো তোসকানোর মতে, এর ভেতরে আজও সেই ‘জাতীয় পুনর্জাগরণের’ স্বপ্ন টিকে আছে; টিকে আছে সেই তথাকথিত ‘উৎপাদনবাদী’ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা, যা শ্রমিক এবং মালিক—উভয় পক্ষকেই এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন ফ্যাসিবাদের প্রসঙ্গ আসত, তখন তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক রাজনৈতিক ঘটনা। এর রূপরেখা কেমন হবে, সমাজকে আমূল বদলে দেওয়ার ক্ষমতা এর কতটা, কিংবা অন্য দেশের পরিস্থিতিতে এটি কীভাবে খাপ খাবে—সেসব তখনো পুরোপুরি স্পষ্ট ছিল না, সংজ্ঞায়িত হওয়ার পথেই ছিল। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি কী?
বীভৎস জানোয়ার
পরিস্থিতি আরও বেশি উদ্বেগজনক হয়ে ওঠার কারণ হলো, এই আন্দোলনগুলোর ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতেই এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কোনো রাখঢাক ছাড়াই নিজেদের ঐতিহাসিক নাৎসিজম আর ফ্যাসিবাদের উত্তরসূরি ভাবে। তাদের প্রতীক, অঙ্গভঙ্গি, পোশাক-আশাক কিংবা মুখের বুলি—সবকিছুতেই তার প্রমাণ মেলে। প্যারিস বা মিলানে সাম্প্রতিক নব্য-ফ্যাসিবাদী মিছিলগুলো আসলে হিমশৈলের চূড়া মাত্র। কয়েক বছর আগেও হয়তো এগুলোকে গুরুত্বহীন বা অতীত নিয়ে একধরনের ‘আদিখ্যেতা’ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু আজ এর গুরুত্ব সম্পূর্ণ আলাদা, আর এর গভীরতা আমাদের পুরোপুরি বুঝতে হবে। এই আয়োজকরা ব্যক্তি হিসেবে কেমন, তার চেয়েও বড় কথা হলো—আমাদের সমাজ আজ নিজের অতীতকে কীভাবে দেখছে, এই ঘটনাগুলো সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।
ত্রিশ বছর আগে উমবার্তো একো বলেছিলেন: “আমাদের জন্য ব্যাপারটা খুব স্বস্তির হতো যদি বিশ্বমঞ্চে কেউ এসে বলত: ‘আমি আবার আউশভিটজ চালু করতে চাই, আমি চাই ইতালির চত্বরে চত্বরে আবার ব্ল্যাকশার্ট বাহিনী কুচকাওয়াজ করুক।’ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, জীবন এতটা সহজ-সরল নয়।” রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নাদিয়া আরবিনাতি যাকে একসময় “ইউরোপের ফ্যাসিবাদী মুখোশ” বলেছিলেন, আজকের এই মিছিলগুলো আর কেবল সেই মুখোশের বীভৎস রূপ হয়েই আটকে নেই। বরং এগুলো গত তিন দশক ধরে চলা এক প্রক্রিয়ার ফল—যেখানে ইতিহাসকে মুছে ফেলা হয়েছে, অতীতের ভয়াল সব ঘটনাকে তুচ্ছ করা হয়েছে, আর দাঁড় করানো হয়েছে সব ভুল বা মিথ্যা তুলনা। একদিকে যারা গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য লড়েছিলেন (অনেকেই হয়তো স্তালিনপন্থী রাশিয়ার বাস্তবতা না জেনেই)—তাঁদের সঙ্গে এক পাল্লায় মাপা হচ্ছে তাঁদের, যারা দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক এর উল্টো মেরুতে বা বিপরীত মূল্যবোধ নিয়ে।
সেই অতীতের সাক্ষী দেওয়ার মতো আজ আর কেউ বেঁচে নেই; পিয়ের পাওলো পাসোলিনির রূপক ধার করে বলা যায়—‘জোনাকিরা সব হারিয়ে গেছে’। ঐতিহাসিক সত্যগুলোকে এখন এতটাই ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যে, ইতিহাস যেন এমন এক পাত্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে ‘সবকিছু এবং তার বিপরীতটাও’ একসঙ্গে জায়গা পায়। এর ফলে পশ্চিমে যারা মনে করেন ‘ফ্যাসিবাদ আসছে’—এই জুজু দেখিয়ে মানুষকে জাগানো যাবে, তাঁরা এখন দেখছেন মানুষ হয় উদাসীন, নয়তো আরও খারাপ—জনগণ ইতিমধ্যেই উগ্র ডানপন্থীদের বুলি ও চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ইউরোপীয় কমিশনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জঁ-ক্লদ জাঙ্কার একসময় ঠাট্টা করে ভিক্টর অরবানকে “হ্যালো, ডিক্টেটর” বলে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। সেখান থেকে শুরু করে জর্জিয়া মেলোনির রাজনৈতিক শেকড়কে (যা তিনি নিজেও গোপন করেন না) স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়া—সব মিলিয়ে ১৯৪৫ সালের পর পশ্চিমা সমাজ যে মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার বড়াই করত, তার এই উলটপুরাণ আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।
আজকের এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীটি সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ইতিহাস বিকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধিতা, অপপ্রচার এবং সেন্সরশিপকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাদের এই কার্যক্রমের পেছনে রয়েছে ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, পডকাস্ট, টিভি চ্যানেল, পত্রিকা এবং থিংক ট্যাংক নিয়ে গড়ে তোলা এক বিশাল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমেই তারা চালাচ্ছে এক ‘অবিরাম অ্যালগরিদমিক প্রচারযুদ্ধ’। এটি ক্ষমতার এমন এক নতুন ও সর্বব্যাপী রূপ, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে—বিশেষ করে এমন এক সমাজে, যেখানে মানুষ একে অপরের থেকে বড্ড বিচ্ছিন্ন।
ইতালীয় দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ এনজো ট্রাভারসো যুক্তি দেন যে, ফ্যাসিবাদের ধারণাটি বর্তমান সময়ে একই সঙ্গে অপরিহার্য এবং অপর্যাপ্ত। রেইনহার্ট কোসেলেক-এর সূত্র ধরে তিনি ঐতিহাসিক সত্য এবং তাকে ভাষায় প্রকাশ করার মধ্যবর্তী যে টানাপড়েন, সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ১৯৩০-এর দশক থেকেই ফ্যাসিবাদ শব্দটি সব ধরনের কুপমন্ডুক প্রতিক্রিয়াশীলতা, রক্ষণশীলতা এবং কর্তৃত্ববাদের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এমনকি যেখানে ঐতিহাসিক ফ্যাসিবাদের ‘সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য’গুলো অনুপস্থিত, সেখানেও।
কিছু পণ্ডিত আরও এক ধাপ এগিয়ে ঐতিহাসিক ফ্যাসিবাদের গণ্ডি পেরিয়ে এই শব্দটিকে প্রয়োগ করেন। তাঁদের মতে, ফ্যাসিবাদ হলো “সাংস্কৃতিক অভ্যাস, প্রবৃত্তি এবং অশুভ তাড়নার এক সাধারণ সমষ্টি, যা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে নিজেকে প্রকাশ করেছে—এবং আবারও করতে পারে—এমনকি কোনো ফ্যাসিবাদী আন্দোলন বা শাসনব্যবস্থা না থাকলেও।” এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ফ্যাসিবাদের ধারণাটি একটি বিমূর্ত তত্ত্বে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে, যা নির্দিষ্ট সময়ের মূর্ত বা বাস্তব ঘটনাগুলোকে ধরতে ব্যর্থ হয়—বিশেষ করে দ্রুত পরিবর্তনের সময়ে। ইতিহাসবিদ রবার্ট প্যাক্সটন সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই উদ্বেগের প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন, শব্দটি প্রায়ই “আলোর চেয়ে উত্তাপই ছড়ায় বেশি।” তাঁর মতে, “ফ্যাসিবাদ শব্দটি এখন নিছক একটি গালি বা তকমায় পরিণত হয়েছে, ফলে আমাদের সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো বিশ্লেষণের জন্য এটি আর খুব একটা কার্যকর হাতিয়ার থাকছে না।”
মানুষের চেতনার চেয়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেক দ্রুত পরিবর্তিত হয়। ফলে সমাজে এমন সব নৈতিক ও সামাজিক রীতি-নীতি টিকে থাকে, যার বস্তুগত ভিত্তি হয়তো অনেক আগেই ধসে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প, মিলে, অরবান, মেলোনি, ভ্লাদিমির পুতিন বা মারিন ল পেন ‘ফ্যাসিস্ট’ কি না—তা নিয়ে তর্কে মেতে থাকলে খুব একটা লাভ নেই। কারণ এই বিতর্ক সেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিগুলোর ওপর আলো ফেলতে পারে না, যা এদের বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে।
একবিংশ শতাব্দীর রাজনীতির সংজ্ঞাই নির্ধারিত হচ্ছে সরকার ও সংসদগুলোর এক অদ্ভুত অক্ষমতা দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রাষ্ট্রীয় নীতিগুলো বুঝি ‘বাজার’-এর ইশারায় চলছে, কিন্তু বাস্তবে সেগুলো বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলোর গুটিকয় অতিধনী বা অভিজাত গোষ্ঠীর স্বার্থই রক্ষা করে চলেছে। গ্লোবাল সাউথ বা দক্ষিণের দেশগুলোতে এই নীতিগুলোর ফলাফল হলো বিরামহীন সংঘাত, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ আর স্থায়ী দারিদ্র্য। অন্যদিকে গ্লোবাল নর্থ বা উত্তরের উন্নত দেশগুলোতে এগুলো ডেকে আনছে কঠোর ব্যয়-সংকোচন নীতি আর আকাশছোঁয়া বৈষম্য। একই সঙ্গে, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা-ও দ্রুত ভেঙে ফেলা হচ্ছে। আর এই পরিস্থিতিই কর্তৃত্ববাদের উত্থান, গণতান্ত্রিক অর্জনগুলোর ক্ষয় এবং সহিংসতার পরিবেশকে স্বাভাবিক করে তোলার এক উর্বর জমিন তৈরি করে দিয়েছে।
সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন ফর ইউরোপ (CLUE)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে ইতালির মেলোনি সরকারকে সেই তালিকায় ফেলা হয়েছে, যারা “পদ্ধতিগতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আইনের শাসনকে দুর্বল করছে।” বিচার বিভাগ, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে প্রতিবাদ ও ধর্মঘটের মতো মৌলিক অধিকারগুলো এখন তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। প্রতিবেদনে তাদের এই কর্মকাণ্ডকে “গুরুতর এবং পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন” হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি শাসন বিভাগের হাতে ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান কুক্ষিগতকরণের বিষয়টিতেও জোর দেওয়া হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালে আরেকটি উদাহরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম কয়েক মাসেই গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরার প্রক্রিয়া নিয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই: অভিবাসীদের গণহারে দেশ থেকে বিতাড়ন, সরকারি চাকরিতে ঢালাও ছাঁটাই, ভোটাধিকার আইন বা ‘ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট’-এর ওপর আক্রমণ, গবেষণার ওপর সেন্সরশিপ ও অর্থায়ন বন্ধ করা, মার্কিন শহরগুলোর সামরিকায়ন এবং ‘অ্যান্টিফা’কে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করে বামপন্থীদের ওপর দমন-পীড়ন চালানো।
প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃত্ববাদের এই বর্তমান জোয়ার কিন্তু আকাশ ফুঁড়ে আসেনি। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের পর নব্য-উদারবাদী বা নিওলিবারেল নীতি ও বয়ান যে উগ্র রূপ নিয়েছিল, সেটাই আজকের এই পরিস্থিতির জ্বালানি জুগিয়েছে। এর ফলেই তৈরি হয়েছে তীব্র বৈষম্য, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ধ্বংস এবং কোটি কোটি শ্রমিককে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এক অনিশ্চিত ও নড়বড়ে জীবিকার দিকে।
এর ফলে তৈরি হওয়া নিরাপত্তাহীনতা, ভয়, হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে এমন এক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে, যাকে ওয়েন্ডি ব্রাউন বর্ণনা করেছেন ‘শ্রেণিচেতনাহীন শ্রেণিক্ষোভ’ হিসেবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই বৈষম্যের ক্ষত আরও গভীর হয়েছে। ‘টেকারস, নট মেকারস’ শীর্ষক সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে শতকোটিপতিদের সম্পদ তিনগুণ দ্রুতগতিতে বেড়েছে। অন্যদিকে, ২০১৫ সাল থেকে শীর্ষ ১ শতাংশ ধনী সম্মিলিতভাবে ৩৩.৯ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করেছে। ঠিক বিপরীত মেরুতে তাকালে দেখা যায় এক ভয়াবহ চিত্র—বিশ্বের ৩৬০ কোটি মানুষ, অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির ৪৪ শতাংশই এখন বিশ্বব্যাংকের নির্ধারিত দারিদ্র্যসীমার নিচে ধুঁকছে।
সম্পদের এই আকাশচুম্বী ব্যবধান প্রাবন্ধিক রিচার্ড সিমুর বর্ণিত ‘ডিজাস্টার ন্যাশনালিজম’ বা ‘বিপর্যয়শ্রয়ী জাতীয়তাবাদ’-এর গতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। এটি এমন এক রাজনীতি, যা সংকটকে পুঁজি করে নিজের আখের গোছায় এবং সমাজকে সামাজিক ও জলবায়ু বিপর্যয়ের কিনারে ঠেলে দেয়। এই বিপদকে অস্বীকার করা মানে ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তোলা। নাওমি ক্লাইন এবং অ্যাস্ট্রা টেলরের মতে, “রোগবালাই, বিষাক্ত খাবার এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য যে সুরক্ষা-কাঠামোগুলো তৈরি হয়েছিল, সেগুলোর ওপর ট্রাম্পের ক্ষিপ্ত আক্রমণ মূলত ধনিকগোষ্ঠীর জন্য বেসরকারিকরণ ও মুনাফা লোটার হাজারটা নতুন সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। আর এই ধনিকগোষ্ঠীই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও তার আইনি সুরক্ষাকে ধ্বংস করার এই প্রক্রিয়ায় ইন্ধন জোগাচ্ছে।”
বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তোলপাড় বোঝার তাগিদ থেকেই পুঁজিবাদের চলমান রূপান্তর এবং রাজনীতি, সমাজ ও পরিবেশের ওপর এর প্রভাব নিয়ে একাধিক গভীর গবেষণা শুরু হয়েছে। ডিলান রাইলি এবং রবার্ট ব্রেনার একে আখ্যা দিয়েছেন নতুন এক ‘পলিটিক্যাল ক্যাপিটালিজম’ বা ‘রাজনৈতিক পুঁজিবাদ’ হিসেবে। এই ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, বড় বড় বেসরকারি গোষ্ঠীগুলো এখন রাষ্ট্রক্ষমতার অন্দরমহলে ঢুকে পড়ছে এবং সেখানে একধরনের কর্তৃত্ববাদী প্রভাব বিস্তার করছে। এর ফলে, বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধীরগতির এই সময়েও তারা বিপুল পরিমাণ ‘বাড়তি মুনাফা’ হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।
ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে মেটা, অ্যামাজন এবং গুগলের কর্তাদের উপস্থিতি—যাঁদের অর্থনীতিবিদ সেড্রিক ডুরান্ড ‘প্রযুক্তি-সামন্তপ্রভু’ বলে অভিহিত করেছেন—তা আসলে হিমশৈলের চূড়া মাত্র। কর্তৃত্ববাদ যদি আংশিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির ‘রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুতি’রও ইঙ্গিত দেয়, তবে আমাদের এই শ্রেণির ভেতরের ত্রুটি, দুর্বলতা এবং ফাটলগুলোও খতিয়ে দেখতে হবে—সম্প্রতি হেজ ফান্ড বিলিয়নেয়ার রে ডালিও-র ফিন্যান্সিয়াল টাইমস-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে যার স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে।
আসন্ন বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে, আমরা বর্তমানে যে সন্ধিক্ষণটি অতিক্রম করছি, তা নিয়ে গবেষণার একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র উন্মোচিত হচ্ছে। আমাদের অবশ্যই ‘ফ্যাসিবাদ’ বিষয়ক বিতর্কের সেই আচ্ছন্নতা (বা ঘোর) কাটিয়ে উঠতে হবে—যেই ‘ফ্যাসিবাদ’ এমন এক প্রতিপক্ষ, যার নিছক উল্লেখই যেন বিদ্যমান রাজনৈতিক দল ও ব্যবস্থাগুলোর নৈতিকতা ও বৈধতা নিশ্চিত করে দেয়। এর পরিবর্তে, আমাদের ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে যে, আমরা কীভাবে আজকের এই অবস্থায় এসে পৌঁছালাম। এটিই আমাদের সামনের চ্যালেঞ্জ। আমাদের সামনে এখন এক কঠিন কর্মযজ্ঞ অপেক্ষা করছে।
লেখক পরিচিতি: স্তেফানি প্রেজিওসো লুজান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক। ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ওপর তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।
অনুবাদ – কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে।
মূল ইংরেজি – https://jacobin.com/2025/11/fascism-analogies-far-right-history
This post has already been read 126 times!