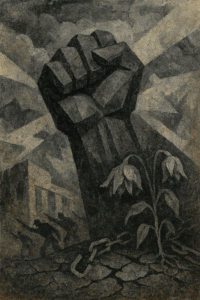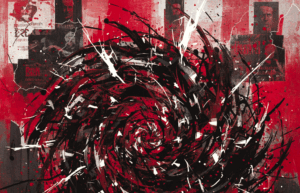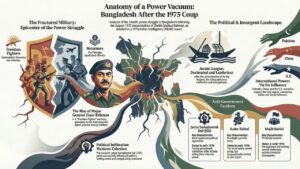source: http://goo.gl/OwqzaZ
This post has already been read 30 times!
শ্রীলঙ্কায় কি একটি রাজনৈতিক সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে? নাকি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে যে বাধা-বিপত্তিগুলো থাকে, সেগুলো এখন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে? নাকি যেকোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেসব অনিশ্চয়তা তৈরি করে, আমরা তা-ই প্রত্যক্ষ করছি? এসব প্রশ্নের কারণ এই নয় যে দেশের পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং আগামী ১৭ আগস্ট নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গত ২৬ জুন দেশের পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেননা, আগেই বলা হয়েছিল যে সংবিধানের কিছু সংশোধনী পাস করার পর পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন করা হবে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্লামেন্ট ২৩ এপ্রিল ভেঙে দিয়ে জুন মাসে নির্বাচন করা হবে বলা হয়েছিল; সেই বিচারে পার্লামেন্ট ভাঙা হয়েছে অনেক দেরিতে। ফলে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার কারণে নয়, প্রশ্ন উঠছে এ কারণে যে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা ঘটছে এবং নির্বাচনের ফলাফলের সম্ভাব্য যেসব চিত্র উঠে আসছে, তাতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা তৈরির এবং রাজনীতির পশ্চাদযাত্রার আশঙ্কা এখন অনেকের মনেই দানা বাঁধছে।
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে মাইথ্রিপালা সিরিসেনা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক কাঠামোতে তিনি বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটাবেন। সেই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখেই এ বছরের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মাহিন্দা রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ ভোটাররা সিরিসেনাকে বিজয়ী করেছিলেন। নির্বাচনের পরপর রাজনীতিতে যতটা আশাবাদ লক্ষ করা গিয়েছিল, গত কয়েক মাসে তাতে যে ভাটার টান লেগেছে, সেটা শ্রীলঙ্কার রাজনীতি বিষয়ে উৎসাহীরা নিঃসন্দেহে অবগত আছেন। এটা ঠিক যে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সিরিসেনা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাতে তিনি সফল। সংবিধানের ঊনবিংশ সংশোধনী প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের সাংবিধানিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য প্রণীত বিংশতিতম সংশোধনী পার্লামেন্ট পাস করেনি। তাঁর প্রতিশ্রুত ১০০ দিনের পরিকল্পনার এক বড় অংশও তিনি বাস্তবায়ন করতে পারেননি। উপরন্তু তাঁর বিরুদ্ধেও আত্মীয়স্বজনকে সরকারি উচ্চপদে আসীনের অভিযোগ উঠেছে, দুর্নীতির প্রশ্নও এসেছে। কিন্তু এসবের চেয়েও বড় সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে তাঁর সরকারের সাফল্য আশাব্যঞ্জক নয়। তামিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সময়, বিশেষ করে এই গৃহযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, যেসব যুদ্ধাপরাধের ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কোনো সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নিতে তিনি উৎসাহ দেখাননি।
কয়েকটি বিষয় এখানে স্মরণে রাখা দরকার, সিরিসেনা দলগতভাবে সাবেক প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষের দল শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির (এসএলএফপি) সদস্য, তবে তিনি যখন তাঁর দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন, তখন তাঁকে সমর্থন জুগিয়েছিল প্রধান বিরোধী দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউএনপি) এবং তামিল নাগরিক ও দলগুলো। সিরিসেনা যেমন দল ত্যাগ করেননি, তেমনি সাবেক প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষেও দলেই আছেন, যদিও রাজাপক্ষে দলের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। সিরিসেনা যখন নির্বাচনে বিজয়ী হন, তখন পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল এসএলএফপি বা ফ্রিডম পার্টি, কিন্তু তিনি বিরোধী দলকে সরকার গঠনের আহ্বান জানান এবং রানিল বিক্রমা সিংহে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। সংবিধান সংশোধনীর জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন নিশ্চিত করতে মার্চ মাসে ফ্রিডম পার্টির ২৬ জনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করে ‘জাতীয় সরকার’ গঠন করেন প্রেসিডেন্ট সিরিসেনা। যেহেতু সবাই জানতেন যে এই পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভা শিগগিরই ক্ষমতা থেকে সরে যাবে, সে কারণে এ নিয়ে কারোরই আপত্তি ছিল না। এই পটভূমিকায় ইউএনপির নেতারা আশা করেছিলেন যে তাড়াতাড়ি নির্বাচন হবে। তাঁদের আশা যে রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে তাঁরা পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভালো ফলাফল করতে পারবেন। ২২৫ সদস্যের পার্লামেন্টে তাঁদের আসন ছিল ৪০-এর মতো। আন্তর্জাতিক সমাজ, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলো, তাড়াতাড়ি নির্বাচনের জন্য সিরিসেনার ওপর চাপ বহাল রেখেছিল।
সিরিসেনার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার সময় থেকেই ফ্রিডম পার্টির ভেতরে দুটি পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠী জন্ম নেয়—একদিকে সিরিসেনা, অন্যদিকে রাজাপক্ষে। রাজাপক্ষে এখন এ রকম ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে তিনি দলের হয়ে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রার্থী হতে চান। তাঁর প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে ফ্রিডম পার্টির নেতৃত্বাধীন জোটের সদস্য কয়েকটি দক্ষিণপন্থী দল। তিনি আশা করেন যে সিরিসেনা তাঁকে সমর্থন করবেন। কেননা, দল বিভক্ত থাকলে ফ্রিডম পার্টির বিজয় হওয়ার আশা নেই বললেই চলে। যদি নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আশায় দলের নেতারা একজোট হন, তবে তাতে রাজাপক্ষের গোষ্ঠীই সবচেয়ে লাভবান হবে। যদি ফ্রিডম পার্টি বিজয়ী হয় এবং রাজাপক্ষে প্রধানমন্ত্রী হন, তবে দল ও সরকার কোনোটার ওপরই সিরিসেনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শুধু তা-ই নয়, তামিলদের সঙ্গে রিকনসিলিয়েশন বা বিরোধ মেটানোর বিষয়, যে ক্ষেত্রে গত কয়েক মাসে অগ্রগতি হয়েছে সামান্যই, তা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বলাই ভালো। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা দরকার যে তামিল টাইগাররা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হলেও বিশ্বজুড়ে তাদের যে নেটওয়ার্ক, সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। আর নৈতিক বিবেচনায় একটি গণতান্ত্রিক দেশ কোনো অবস্থাতেই তার অতীত অপকর্মের দায় এড়াতে এবং সংখ্যালঘুদের তাদের অধিকারবঞ্চিত করে শাসন অব্যাহত রাখতে পারে না। সবার অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচারভিত্তিক একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পথে শ্রীলঙ্কা গত তিন দশকে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। আশা করা যায় যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কার নাগরিকেরা সেই বার্তা দিতে চাইবেন না যে তাঁরা পেছনের দিকে হাঁটতে চান।
ইউএনপির নেতারা আশা করেন যে ফ্রিডম পার্টি তাদের তালিকায় রাজাপক্ষকে রাখবে এবং তা তাঁদের জন্য শাপে বর হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু সেই আশা কতটা বাস্তববাদী, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইউএনপির সমর্থনপুষ্ট সিরিসেনা যে ৫১ দশমিক ২৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন, তার সবটাই তাঁদের সমর্থকদের ভোট নয়, ফ্রিডম পার্টির একাংশও তাঁদের সঙ্গে ছিল। তা ছাড়া ধর্মভিত্তিক দক্ষিণপন্থী দল জাতিকা হেলা উরুমায়া (জেএইচইউ) সেই সময়ে তাঁদের সঙ্গে থাকলেও এখন দলটি ফ্রিডম পার্টির সঙ্গেই যাবে বলে ধারণা করা যায়। জনতা ভিমুক্তি পেরামুনা (জেভিপি) দুই দলের কারও সঙ্গে না গিয়ে নিজেদের প্রার্থী দেবে। দেশের উত্তর ও পূর্বে যে তামিলরা সিরিসেনাকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা তামিল দল টিএনএকেই ভোট দেবেন। ফলে ইউএনপির কমপক্ষে ১৫ শতাংশ ভোট কম পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, রাজাপক্ষে যে ৪৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন, তা তাঁর নিজস্ব এমন বলা যাবে না। যদি ফ্রিডম পার্টি একত্রও থাকে, তবু এর সবটাই তাঁর পক্ষে আসবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।
এই নির্বাচনের আরেকটি দিক হচ্ছে সময়ের প্রশ্ন। এই মুহূর্তে নির্বাচনের একটি অন্যতম কারণ হলো জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের আসন্ন রিপোর্ট। শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধের শেষ বছরগুলোয় সরকার ও তামিল যোদ্ধারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছিল কি না, যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে কাউন্সিলের রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা ছিল এপ্রিলে, কিন্তু শ্রীলঙ্কা সরকারের অনুরোধে তা ছয় মাস পেছানো হয়। এই রিপোর্টে সুনির্দিষ্টভাবে কারা যুক্ত ছিল, তা প্রকাশিত হতে পারে বলে বলা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারের ওপরে চাপ তৈরি হবে। এই রিপোর্ট পেছানোর একটি উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজনীতিতে, বিশেষ করে নির্বাচনের ওপরে, তার প্রভাব ঠেকানো। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে রাজনৈতিকভাবে রাজাপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে অনেকের ধারণা। আবার কেউ কেউ এই মতও দেন যে জাতিসংঘের এই রিপোর্টকে দেশের ওপরে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ এভাবে দেখিয়ে, সিনহালা জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা তৈরি করে রাজাপক্ষে আবারও ক্ষমতায় ফিরতে পারেন। এখন দুই সম্ভাবনা থেকেই নির্বাচনকে মুক্ত রাখা যাবে।
যেভাবেই বিবেচনা করা হোক না কেন, ১৭ আগস্টের নির্বাচন পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে উত্তেজনা থাকবে, থাকবে অনিশ্চয়তা। সেই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে নির্বাচন দেশকে কোন পথে নেবে, ভোটাররা শ্রীলঙ্কার জন্য কী ভবিষ্যৎ তৈরি করবেন?
প্রথম আলো’তে প্রকাশিত, ৩ জুলাই ২০১৫
থাম্বনেইলের ছবি সূত্র: লিঙ্ক
This post has already been read 30 times!