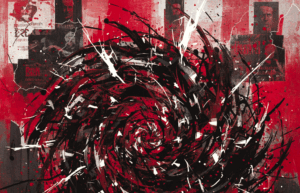This post has already been read 29 times!
কিসের জন্য দুঃখিত? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সামরিক অভিযান প্রসঙ্গে সঠিক প্রশ্ন উত্থাপন।
লেখক – আলি উসমান কাসমি
লাহোর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস, লাহোর, পাকিস্তান।
জার্নাল অফ দ্য রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, ভলিউম ৩৩, ইস্যু ৪, অক্টোবর ২০২৩
ক্লাসিক উর্দু মহাকাব্যে বলা হয়—রাজারা নিজের জীবনশক্তি এক পাখির দেহে স্থানান্তরিত করে সেটিকে নিরাপদ কোনো স্থানে বন্দি রাখতেন। রাজাকে হত্যা করতে চাইলে আগে সেই পাখিকে হত্যা করতে হতো। পূর্ব পাকিস্তানে ‘আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা’র জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত সামরিক অভিযানের (যার কোডনাম ছিল অপারেশন সার্চলাইট) মূল ক্রীড়ানক খাদিম হুসেন রাজারও ছিল এমন এক পাখি—একটি ময়না। তবে তাঁর গৃহের বাইরে আরেক ‘ময়না’ ছিল —শেখ মুজিবুর রহমান। পশ্চিম পাকিস্তানে পরিবারের সঙ্গে আলাপচারিতায় গোপনীয়তা রক্ষার জন্য রাজা শেখ মুজিবকে ‘ময়না’ ছদ্মনামে ডাকতেন। ১৯৭১ সালের ২৫–২৬ মার্চের সেই দূর্ভাগ্যজনক রাতে সেনারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে। রাজা আত্মজীবনীতে লিখছেন — “ময়নাটির হৃদয় বোধহয় দুর্বল ছিল; ট্যাঙ্কের গোলা ও রিকয়েললেস রাইফেলের বিকট গর্জন সইতে না পারে মারাই গেলো”। [1] পরে রাজার স্ত্রী যখন ময়নার মৃত্যুর সংবাদ ফোনে তাঁর মেয়েকে দিলেন, সে ভেবেছিল মা বুঝি শেখ মুজিবের কথাই বলছেন, মুজিব বুঝি সামরিক অভিযানে নিহত হয়েছেন।
এই ঘটনা যে কাউকেই ভাবাতে পারে যে, রাজার সেই ‘ময়না’ কি তবে পাকিস্তানেরই প্রাণ ও আত্মার প্রতীক ছিল? সেই রাতের সামরিক অভিযানের গর্জন যেমন সহ্য করতে পারেনি ময়না পাখিটি, তেমনি সহ্য করতে পারেনি পাকিস্তানও।
১৯৭১ সালের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা কোনো ইতিহাসবিদের জন্যই সহজ কাজ নয়। নুরুল কবিরের অনবদ্য নতুন বইটি ১৯৭১ সালের সহিংস ঘটনার উপস্থাপনে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী বয়ানের ভেতরকার নানা কিসিমের বিচ্যুতি ও উপেক্ষিত বিষয় সামনে নিয়ে এসেছে। এর অধিকাংশই জোরপূর্বক বিস্মৃতি বা অজ্ঞতার ভানের ফসল। পাকিস্তান রাষ্ট্র যেমন নিজেকে গণহত্যা ও ধর্ষণের অভিযোগ থেকে মুক্তি দিতে একটি সংশোধিত ‘ইতিহাস’ রচনার চেষ্টা করছে, তেমনি বাংলাদেশেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নানা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিকৃত করা হয়েছে। গত এক দশকে, শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উত্থান এবং তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে, বাংলাদেশ সরকার এমন এক ইতিহাসকথন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে যা এককভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে উপস্থাপন করে। এক জনসমক্ষে দেওয়া বক্তৃতায় হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মেজর জিয়াউর রহমানের অবদান খাটো করে অভিযোগ করেন যে, অপারেশন সার্চলাইটের রাতে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যোগসাজশ করে বাঙালিদের হত্যা করেছিলেন।[2] এটি বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে নেওয়া সেইসব প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ বিপরীত, যখন মেজর রহমানের সশস্ত্র সংগ্রামকে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলমান আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল—যে সময়ে শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন।।[3] কবির সিদ্ধান্ত টানেন : “এই পরিস্থিতিতে, শাসকগোষ্ঠী ও তাদের রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুগত ইতিহাসবিদদের হাত ধরেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখনও গড়ে উঠছে। তারা ‘জাতীয় ইতিহাস’-এর নামে ধনী সংখ্যালঘুর কাহিনি উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেন, আর দরিদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠের বয়ান উপেক্ষা করেন।”[4]
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সুসংহত ও দলিলসমৃদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করতে বাংলাদেশের বহু গবেষক যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় দিয়েছেন, তার গুরুত্ব অস্বীকার করার অবকাশ নেই। উদাহরণস্বরূপ, হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র কিংবা এ. এস. এম. শামসুল আরেফিনের একই ধরনের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য।[5] তবু নুরুল কবির মুক্তিযুদ্ধের সরকারি বয়ান থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া বিষয়গুলোর সমালোচনা করেছেন—বিশেষত সশস্ত্র সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা বামপন্থী সংগঠনের ভূমিকা। তাঁর মতে, শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে একমুখী বা আধিপত্যশীল বয়ানের নির্মাণ আসলে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক গরিবানার বহিঃপ্রকাশ। এটি বাঙালির জাতীয় চেতনার আন্দোলনকে বঞ্চিত করে এই জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস, নানা জনের রাজনৈতিক দর্শন এবং একাত্তরেরও বহু আগ হতে চলমান বামপন্থী সংগঠনগুলোর অবদানের স্বীকৃতি থেকে। এই বহুমাত্রিক ও জটিল ইতিহাসকে গ্রহণ করার বদলে শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ রূপে একপ্রকার নাগরিক ধর্মের মর্যাদায় বসানো হয়েছে—যেমনটি আরিল্ড রুড বর্ণনা করেছেন।[6] আজ জনসমক্ষে, সরকারি চিঠিপত্রে এবং পাঠ্যপুস্তকে শেখ মুজিবের নামের আগে সর্বদা ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি যুক্ত থাকে। কিছু ইউরোপীয় দেশে জারি থাকা হলোকাস্ট ডিনায়েল আইনের সাথে তুলনা করে ২০১৬ সালে শেখ হাসিনার সরকার ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যাটিকে প্রশ্ন করা আইনত দণ্ডনীয় করার প্রস্তাবও ভেবেছিল।[7] যদিও শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব বাস্তবায়ন হয়নি, তবুও অনুরূপ অভিযোগে সরকার এখনো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় নাগরিকদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।
পাকিস্তানে ১৯৭১ বিষয়ক প্রচলিত লেখালেখি ও জনপরিসরের আলাপ-আলোচনা মূলত ভারতের ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ এবং মুক্তিবাহিনীসহ বাঙালি সশস্ত্র গোষ্ঠীসমূহের সহিংসতা’র ওপর জোর দেয়। বাঙালিদের ওপর বছরের পর বছর যে অবিচার করা হয়েছে, তার একটি নামমাত্র স্বীকৃতি দেওয়া হলেও আদতে পুরো ১৯৭১-কে সাংবিধানিক ইতিহাসের একটি পাঠে সীমিত করে ফেলা হয়েছে। যদিও, এই পাঠও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকার এবং দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান জানানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবুও, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক দুর্দশা ও ট্রমা সম্পর্কিত আরও জরুরি প্রশ্নগুলোকে আড়াল করে ফেলে, যেগুলো এখনো কোটি কোটি পাকিস্তানি ও বাংলাদেশির জীবনে অমোচনীয় দাগ কেটে আছে। পাকিস্তানি একাডেমিকদের মধ্যে খুব কম লোকই এ বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। রিজওয়ান উল্লাহ কোকাবের সাম্প্রতিক বইটি ব্যতিক্রম, যেখানে পাকিস্তানের ভাঙনকে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে নেতৃত্বের ব্যর্থতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে।[8] আনাম জাকারিয়ার কাজটিও অনন্য, কেননা এতে রয়েছে বিদ্বৎসমৃদ্ধ ব্যাপকতা, বিশ্লেষণাত্মক কঠোরতা, এবং বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি—উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের জন-ইতিহাসকে বর্ণনা করার একটি আন্তরিক অঙ্গীকার।[9] অন্যদিকে, শর্মিলা বোসের ডেড রেকনিং[10]প্রকাশের পর থেকে যে কোনো অন্যায় অস্বীকার করা এবং বাঙালির বিরুদ্ধে বিহারি গণহত্যার অভিযোগ তুলে নিজেদের ‘ভুক্তভোগী’ হিসাবে উপস্থাপন করাটা পাকিস্তানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।[11] ১৯৭১ বিষয়ে পাকিস্তানি সাহিত্যের বড় অংশ গঠিত হয়েছে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের লেখা অসংখ্য আত্মজীবনী দিয়ে।[12] এই বইগুলোতে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দমন-অভিযান এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সামরিক বিবরণের পাশাপাশি ‘পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছেদের কারণসমূহ’ নিয়েও সাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ সৃষ্টির পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য গবেষণামূলক কাজ প্রকাশিত হয়েছে।[13] বিশেষত পাকিস্তানে মূল মনোযোগ ছিল ১৯৭১-কে কেন্দ্র করে টেলিফিল্ম, টেলিভিশন নাটক এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে।[14] ২০২১ সালে পাকিস্তানে মুক্তিপ্রাপ্ত এই সৃষ্টিশীল উপস্থাপনাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মূলত সেইসব দর্শকদের আশ্বস্ত করা, যারা আগে থেকেই পাকিস্তানি বয়ানকে সত্য বলে মানে। প্রযুক্তি-সচেতন এই নতুন ভিজ্যুয়াল বয়ানগুলো টার্গেট করেছে পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্মকে—বিশেষ করে লাহোর, করাচি ও ইসলামাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থীদের। উদাহরণস্বরূপ, খেল খেল মেঁ (২০২১) ছবিটি কিছু তরুণ পাকিস্তানি শিক্ষার্থীর গল্প বলে, যারা ১৯৭১ সালের যুদ্ধ নিয়ে একটি নাটক পরিবেশন করছে। তাদের প্রস্তুতি ও অভিনয়ের সময়—যার জন্য তারা ঢাকায় ভ্রমণ করে—তারা জানতে পারে যে, আসলে যা ঘটেছিল তা ছিল বাঙালিদের বিদ্রোহে উসকে দিতে ভারতের ষড়যন্ত্র। শত্রুপক্ষের সেই কৌশল এখনও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, এবারে বেলুচিস্তানে, প্রয়োগ করা হচ্ছে। অন্যান্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রও একইভাবে ১৯৭১ সালের ঘটনাগুলোকে কেবল পাকিস্তানের ‘ভুক্তভোগী’ অবস্থান এবং নিজের এক প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের জন্য সামরিক অভিযান চালানোর ‘অধিকার’-এর দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরে।
এই প্রোপাগান্ডামূলক ঢেউয়ের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি নিয়ে যেকোনো পাল্টা বয়ান নিষিদ্ধ ও দমন করেছে। এই লেখক, অন্য পাকিস্তানি শিক্ষাবিদদের সঙ্গে মিলে, ২০২১ সালের মার্চে লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন। এতে অংশ নেওয়ার কথা ছিল ১৯৭১ সালের সহিংস ইতিহাস নিয়ে কাজ করা শীর্ষ বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি গবেষকদের। কিন্তু কর্মসূচি ঘোষণার পরপরই সামরিক বাহিনীর চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপর্যায়ের প্রশাসন অনুষ্ঠানটি বাতিল করতে বাধ্য হয়।[15] সামাজিক মাধ্যমে কয়েকজন সামরিকপন্থী সাংবাদিক ও বিশ্লেষকের তীব্র প্রতিক্রিয়া থেকে ধারণা করা যায়, সম্মেলনের বিবরণীতে ব্যবহৃত ‘মুক্তি আন্দোলন’ এবং ‘গণহত্যাজনিত সহিংসতা’ শব্দবন্ধ সামরিক বাহিনীর উচ্চপর্যায়কে ক্ষুব্ধ করেছিল; পাকিস্তানি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবিদেরা এমন ভাষা ব্যবহার করবে, সেটি তাদের কাছে আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল।
১৯৭১ বিষয়ে আধিপত্যশীল বয়ান চাপিয়ে দিতে জোরপূর্বক সম্মেলন বাতিল এবং প্রোপাগান্ডা চলচ্চিত্র নির্মাণ—দুটোই রাজনৈতিক পরিণতি বিষয়ে ইতিহাসের ক্ষমতা নিয়ে সামরিক বাহিনীর উদ্বেগ এবং সেই কারণেই অতীত নিয়ন্ত্রণে তাদের আগ্রহ প্রমাণ করে। এই প্রেক্ষাপটেই আমি এই প্রবন্ধের কাজ শুরু করি। আমি ১৯৭১ সালের ইতিহাসবিদ নই; আমি আগ্রহী এমন একটি ধারণাগত কাঠামো তৈরি করতে, যা আমাদেরকে ওই ঘটনার একটি আরও ঘনিষ্ঠ ইতিহাস—তার পরিণতি, সম্মিলিত স্মৃতি, এবং ব্যক্তিগত ক্ষতি ও ট্রমা—লিখতে সাহায্য করবে।
সঠিক প্রশ্ন তোলা
১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক স্মৃতির তিনটি দিক এখনো তীব্রভাবে বিতর্কিত। প্রথমটি হলো ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রাক্কালে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি, একটি ব্যাপক সামরিক অভিযানের যৌক্তিকতা ও তার বৈধতা, এবং বাঙালি প্রতিরোধের অবৈধতা ও তাকে ‘জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ’ বলা থেকে সৃষ্ট অপরাধ। দ্বিতীয়টি হলো গণহত্যাজনিত সহিংসতা ও নারীকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ, তিন মিলিয়ন নিহত ও দুই লাখ নারী ধর্ষিত হওয়ার প্রচলিত সংখ্যার বিরোধিতা, এবং পাল্টা অভিযোগ হিসেবে বিহারিদের গণহত্যার প্রসঙ্গ। তৃতীয়টি হলো ভবিষ্যতের পথ—অতীত ভুলে গিয়ে, নাকি অতীতের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে এগোনো? এই প্রবন্ধ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৯৭১-সংক্রান্ত বিতর্কের এই তিনটি দিকের ওপর আলোকপাত করবে। আমি দেখাবো, কীভাবে এই প্রশ্নগুলো একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে এবং কীভাবে সেগুলো গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ ও আঞ্চলিক শান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে।
নিচে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব,আমার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা গণহত্যা কীভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল কিংবা শারীরিক ও যৌন সহিংসতার সঠিক ভুক্তভোগীর হিসাব সম্পর্কিত দলিলপ্রমাণ হাজির করা নয়। এর মানে এই নয় যে আমি এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাই, বা সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে বা চাপা দিয়ে রাখতে চাই। বরঞ্চ এই মনোভাবই পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের পছন্দসই ‘অগ্রসর হওয়ার’ সমাধান। খেল খেল মেঁ চলচ্চিত্রের ট্রেলারে দেখা যায়, মূর চরিত্র জারা ১৯৭১ সালের প্রকৃত ঘটনাচিত্র তুলে ধরতে গিয়েবলছেন : “একটি ভুল হয়েছিল… সেটা যে-ই করুক না কেন… চলো দু’পক্ষই ক্ষমা চেয়ে নেই।।”[16]
উক্তিটি আসল দায় নির্ধারণের প্রশ্নটি এড়িয়ে যায় এবং আভ্যন্তরীণভাবে দুই পক্ষকেই সহিংসতার জন্য দায়ী করে। আর্কাইভাল দলিলাদি দিয়ে উক্ত বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের বর্বর শক্তির অসম ব্যবহারকে দেখাতে গেলে ইতিহাসবিদ এক ধরনের ‘তথ্যের লড়াই’-এর ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়বেন, যেখানে নিহত ও ধর্ষিত মানুষের সংখ্যা নিয়ে প্রতিটি পরিসংখ্যানের বিপরীতে সেনাদের দায়মুক্তি দেওয়া পাল্টা তথ্য হাজির হবে। এর মানে এই নয় যে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম সহিংসতা নথিবদ্ধ করার জন্য আর্কাইভাল প্রমাণের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। বরং, প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমি দেখাব, আমার উদ্দেশ্য হলো আর্কাইভাল দলিলাদির বি-মানবিক ভাষা এবং ভুক্তভোগীর স্বরকে উপেক্ষা করে আক্রমণকারীর দাবিকে প্রাধান্য দেওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক করুণ দশার সমালোচনা করা। ‘প্রমাণ’ বা ‘আর্কাইভ’ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে তার ধারণাগত ভিত্তিকে যথেষ্ট ক্রিটিক না করে তথ্যের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে, আমার প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক কাঠামো শাহাব আহমেদ অনুপ্রাণিত এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দাঁড় করানো, যেখানে সঠিক উত্তরের পূর্বশর্ত হলো সঠিক প্রশ্ন তোলা—বরঞ্চ অনেক সময় একটি নিশ্চিত উত্তর পাওয়ার চেয়েও সঠিক প্রশ্ন করাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শাহাব আহমদ উর্দু ও পাঞ্জাবি ভাষার বিখ্যাত কবি মুনির নিয়াজির একটি কবিতা উদ্ধৃত করছেন —
কিসি কো আপনে আমল কা হিসাব কেয়া দেতে?
সওয়াল সারে গলত থে, জওয়াব কেয়া দেতে?
আমার কর্মের হিসাব আমিই-বা কাকে দিই?
সব প্রশ্নই ছিল ভুল—উত্তরই বা কীভাবে দিই?[17]
নিয়াজির এই পঙ্ক্তি এক অর্থে সক্রেটিসীয় প্রশ্নপদ্ধতির একটি কাব্য-সমালোচনা। কলিংউড সক্রেটিক পদ্ধতিকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে যে, বৃদ্ধ জ্ঞানী তার কনিষ্ঠ শিষ্যদের প্রশ্ন করে শেখান ‘কিভাবে তারা নিজেরা নিজের কাছে প্রশ্ন করতে পারে, এবং উদাহরণের মাধ্যমে দেখান যে, সবচেয়ে অস্পষ্ট বিষয়কেও কত বিস্ময়করভাবে আলোচিত করা যায়—শুধুমাত্র তাকিয়ে থাকার পরিবর্তে সেই বিষয়গুলো নিয়ে বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ প্রশ্ন করে’।[18] কলিংউড অধিবিদ্যার ঐতিহাসিক ভিত্তি সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত মতবাদে আরও বিশদভাবে বলেছেন, ‘যে কোনো বিবৃতি বা বক্তব্যই সবসময় কোনো না কোনো প্রশ্নের উত্তর হিসেবে করা হয়’। তিনি এটি আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেন: প্রশ্ন যৌক্তিকভাবেই তার উত্তরের আগে আসে, এবং প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে এক বা একাধিক প্রস্তাবনা।[19] তিনি লিখেছেন: ‘যে কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের সঙ্গে সরাসরি ও তাৎক্ষণিকভাবে জড়িয়ে থাকে একটিমাত্র পূর্বানুমান, অর্থাৎ, যা থেকে এটি সরাসরি ও তাৎক্ষণিক ‘হাজির’ হয়… তবে, এই তাৎক্ষণিক পূর্বানুমানেরও অন্যান্য পূর্বানুমান রয়েছে, যা গোঁড়ার প্রশ্নে পরোক্ষভাবে পূর্বানুমান হিসাবে হাজির থাকে’।[20] যে বিন্দুতে পূর্বধারণার ধারা শেষ হবে, সেই স্থানে আমরা চূড়ান্ত পূর্বধারণা খুঁজে পাব—যা কোনো পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দেয় না এবং তা সেই চিন্তকের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন, যে তাদের অনুমান করে; অতএব, এটি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, কীভাবে চিন্তকের ধারা তার নিজস্ব অনুমানের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।[21] যেখানে এই পূর্বানুমানের ধারা শেষ হবে, সেখানেই আমরা খুঁজে পাব “চূড়ান্ত পূর্বানুমান”—যা কোনো পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দেয় না, বরঞ্চ তা সেই চিন্তকেরই চিন্তাভাবনার প্রতিফলন, যিনি সেগুলো অনুমান করেছেছিলেন,; ফলে, এটি সেজন্যই বোঝা জরুরি যে, কীভাবে একজন চিন্তকের ভাবনা তাঁর নিজের পূর্বানুমান দ্বারা সীমিত হয়ে পড়ে।
কলিংউডের প্রশ্ন তোলার পদ্ধতি সেসব পূর্বানুমান উন্মোচনে আমাদের সাহায্য করে, যেগুলো প্রশ্ন এবং উত্তর হিসাবে এর ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলে। গাডামার এই পদ্ধতিকে নিজের হেরমেনিউটিক (ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি) কাঠামোর জন্য সম্প্রসারিত করে বলেছিলেন, ‘আমরা কেবল তখনই বুঝতে পারি যখন আমরা সেই প্রশ্নটি বুঝি যার উত্তরে কিছু বলা হয়েছে’। কিন্তু ইন্টারোগেটিভ বা প্রশ্নসূচক জিজ্ঞাসার বাগাড়ম্বর পুনরাবৃত্তি বা হেরমেনিউটিক বিশ্লেষণের বিপরীতে আমার পদ্ধতি হচ্ছে ইন্টারেপ্টিভ জিজ্ঞাসা বা কথার মাঝে প্রশ্ন করা, যেখানে কোনো সঠিক জবাব পাওয়াটা মূখ্য নয়; যার কাব্যিক রূপ ধরা পড়েছে নিয়াজির কবিতায়। এ দিক থেকে এই পদ্ধতির সিলসিলা সক্রেটীয় ধারার সাথে মিললেও এর লক্ষ্য আলাদা; কেননা, এটি স্তর ধরে ধরে উন্মোচন করে সত্যের দিকে ধাবিত হওয়ার বদলে প্রশ্নের জটিলতাকে এতদূর অনুসন্ধান করে যেখানে উত্তরের প্রয়োজনই ফিকে হয়ে যায়।
ধরা যাক, এই পদ্ধতি জারার বক্তব্যে প্রয়োগ করা হলো। তখন আমি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাদের পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ কিংবা ধর্ষণকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের দীর্ঘ তালিকা সাজাব না—কারণ বিপরীত পক্ষ তখনই তুলে ধরবে মুক্তিবাহিনীর হাতে বিহারিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতার উদাহরণ। এতে সংঘাতটি নিরপেক্ষ হয়ে যাবে, হিসাব ৫০:৫০; কোনো বিজয়ী বা পরাজিত নেই, নেই কোনো স্পষ্ট আক্রমণকারী বা ভুক্তভোগী। তবু যদি বলা হয়—ক্ষমা চাইতে হবে—যদিও আমার আলোচিত ক্ষমার রাজনীতির সাথে এর মিল নেই—তখন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে শুধু একটাই প্রশ্ন: “কিসের জন্য ক্ষমা?” সঠিক প্রশ্নের ইন্টারেপ্টিভ ক্ষমতা একটি ‘ফ্যাকচুয়াল বক্তব্যে’র সত্য-দাবির ভানকে শেষ করে দেয়, যা সহজ দ্বৈততায় ও গুছানো কাঠামোয় আলাপকে আগে থেকে ঠিক করা গন্তব্যে নিয়ে যেতে চায়। সঠিক প্রশ্ন সমাধানে বিলম্ব করা,, বিস্মৃতি, এবং ‘উভয়পক্ষই সমান’ধরনের ভ্রান্ত সমীকরণের সম্ভাবনাকে ন্যাস্যাৎ করে দেয়। এটি বাধ্য করে অতীতকে মোকাবিলা করার জন্য আত্ম-উপলধ্বি ও দায় স্বীকার করতে। সবচেয়ে বড় কথা, এই কৌশল আক্রমণকারীর প্রভাবশালী ক্ষমতাকে দুর্বল করে—হোক তা সেনাবাহিনী, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, রাষ্ট্র-সমর্থিত পাঠ্যপুস্তক, বা দালাল ইতিহাসবিদ—যিনি গল্পের বয়ানকে তার মতো করে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কারণ, যিনি প্রশ্ন তোলেন, তিনি-ই নির্ধারণ করে দেন উত্তরের সঠিক ধরন।[22] তাই আমাদের কাজ হচ্ছে এই ক্ষমতা ফিরিয়ে এনে সঠিক প্রশ্ন করা। আমরা হয়তো ডিসকোর্সের মূল ধারা গড়ে দিতে পারব না, কিন্তু যারা সেটি গড়ে দেয়, এবং নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হিসেবে হাজির করে,তাদের ক্ষমতা দুর্বল করতে পারব। একবার আমরা সঠিক ধরনের প্রশ্ন তুলতে পারলে, উত্তরের আধিপত্য/হেজেমনি হয়তোবা হ্রাস পাবে, এমনকি অপ্রাসঙ্গিকও হয়ে যেতে পারে। আমার এই প্রয়াস তাই সঠিক উত্তর খোঁজার জন্য নয়, কিংবা বিকল্প ইতিহাস লেখার জন্যও নয়—বরং ইন্টারেপ্টিভ ক্ষমতা দিয়ে আধিপত্যশীল ডিসকোর্সকে ব্যাহত করে আত্মসমালোচনার মুহূর্ত সৃষ্টি করা এবং অন্তরঙ্গ ঐতিহাসিক বয়ানের ভেতর দিয়ে প্রতিকারমূলক ন্যায়বিয়ারের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করা ।
তাই আমার উদ্দেশ্য ১৯৭১-এর বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনা নয়, কিংবা সরাসরি ইতিহাস রচনাও নয়; বরং একটি তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি—যা ১৯৭১-এর সহিংসতা সম্পর্কিত সঠিক ধরনের প্রশ্ন তুলতে সাহায্য করবে এবং ব্যক্তি, সমাজ, সম্মিলিত স্মৃতি ও আঞ্চলিক শান্তির ওপর এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বুঝতে দেবে। আমি প্রধানত পাকিস্তানি সাহিত্যে থেকে উপাদান নিয়েছি, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশি বিশ্লেষণ ও ভাষ্য এবং কয়েকটি তাত্ত্বিক-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমার আলাপ মূলত পদ্ধতিগত, ফলে, এটাকে একাত্তরের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে সহিংসতার ইতিহাস বিষয়ক যে কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উপর্যুক্ত ১৯৭১-সংক্রান্ত তিনটি বিতর্কের প্রসঙ্গে আলাপ শুরু করা যেতে পারে। কোনো সংঘাতকে ‘গৃহযুদ্ধ’, ‘বিদ্রোহ’ বা ‘মুক্তিযুদ্ধ’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত বা (অ)বৈধতা দেওয়ার জন্য যে গরিবি আইনিভাষা ব্যবহৃত হয় তার সমালোচনা দিয়ে শুরু করব। দ্বিতীয়ত, আমি আর্কাইভের ধারণার সীমাবদ্ধতা এবং প্রামাণিকতার যে পজিটিভিস্ট ধারণার উপর এটি নির্ভর করে তার বস্তুগত দিক বিশ্লেষণ করবো, পাশাপাশি সহিংসতা ও ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করতে এর অন্তর্নিহিত বি-মানবিক ভাষাকেও বিবেচনা নেওয়া হবে। আর ভাষার গুরুত্ব বজায় রেখেই, প্রবন্ধটি শেষ করব ক্ষমা প্রার্থনার অর্থগত দিক এবং দক্ষিণ এশিয়ায় টেকসই শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য তার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে।
সঠিক ধরনের প্রশ্ন তুলে ১৯৭১-এর ইতিহাসে অগ্রসর হওয়ার তাত্ত্বিক ভিত্তি পাল্টে দিয়ে, আমি প্রস্তাব করছি—১৯৭১ সালের মর্মন্তুদ ঘটনাবলির এক আরও ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বিবরণ রচনা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি , ভুক্তভোগীর আত্ম-প্রতিনিধিত্বের/উপস্থাপনের অধিকারকে তাদের এজেন্সিসমেত রাজনৈতিক ভাষায় স্বীকৃতি দেয় এমন এক মুক্তিকামী আখ্যান গড়ে তোলে; ভুক্তভোগীর ট্রমা ধারণ করতে সক্ষম এমন এক ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণের বিকল্প ব্যবস্থা দেয়; এবং আমূল পরিবর্তিত গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য ক্ষমার রাজনীতির ওপর জোরারোপ করে। বিবাদমান ইতিহাসকে ক্ষমাশীল অতীতে পরিণত করার তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে এই শক্তি সঞ্চারিত হবে। যেহেতু আমার যুক্তি মোতাবেক ইতিহাসের ভাষাকে আরও ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ করে তুলতে চাই , সেহেতু প্রবন্ধটি প্রায়শই ‘গবেষণা প্রবন্ধ’-এর শুষ্ক একাডেমিক সংযম থেকে সরে গিয়ে গীতিময়-আলঙ্কারিক ভঙ্গি গ্রহণ করে ঐতিহাসিক ভাষার ‘নিরপেক্ষতার’ সমালোচনা করেছে।
সহিংসতার বৈধতা—অথবা তার অভাব
এই আলোচনা আমি সরাসরি যুদ্ধ, বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার বিবরণ বা এমনকি ১৯৪৭-এর পাকিস্তানের জন্মের প্রসঙ্গ দিয়েও সূচনা করবো না। । আমি ফিরে যাব আরও মৌলিক এক সন্ধিক্ষণে—যা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য সমান তাৎপর্যপূর্ণ—১৯৪০ সালের ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাবে। মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে উত্থাপিত ওই প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছিল স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠার। কয়েক বছরের মধ্যে লীগ প্রস্তাবটি সংশোধন করে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একক রাষ্ট্রের দাবি তোলে। পঞ্চাশের দশক জুড়ে, প্রথমে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং পরে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি নেতৃত্ব লাহোর প্রস্তাবে ঘোষিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য একটি ফেডারেল গণতান্ত্রিক সংবিধানের আহ্বান জানায়। শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফার প্রেরণাও নেন এই প্রস্তাব থেকেই। এমনকি ১৯৬৬ সালে, তিনি লাহোর শহরেই এই দফাগুলো ঘোষণা করেন—স্থান ও তারিখের প্রতীকী মিল রেখে। আওয়ামী লীগ ও ইয়াহিয়া খানের আইনজীবী দলের আলোচনাতেও লাহোর প্রস্তাব বারবার গুরুত্ব পেয়েছিল। আর পাকিস্তানের ভাঙনের পরও, পঞ্চাশের দশকের প্রবীণ রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ একে একমাত্র কার্যকর নথি বলেছিলেন—যা দুই ভূখণ্ডকে একসাথে রাখতে পারত। তিনি লিখেন,
প্রথম দেখায় স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবকে এক ধরনের বিচ্ছেদমূলক কাজ বলে মনে হতে পারে। স্পষ্টতই এটি পাকিস্তানকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করেছে। যে কোনো স্বাভাবিক ঐক্যকে ভেঙে দেওয়া—যে কারণেই হোক না কেন, উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন যাই থাকুক না কেন, একটি অনভিপ্রেত ঘটনা। … সৌভাগ্যবশত, এটি কেবল উপরিতলের দৃষ্টিভঙ্গি।… বাংলাদেশের সাম্প্রতিক করুণ ঘটনাবলি প্রমাণ করেছে যে, আমাদের রাজনৈতিক পূর্বসূরিদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি, বরঞ্চ সেই পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুতিই ব্যর্থ হয়েছে। অতএব আমাদের পূর্বসূরিদের নিয়ে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই, বরং গর্বিত হওয়া উচিত। সেই পরিকল্পনা এতই সুপরিকল্পিত ও দূরদর্শী ছিল যে, সেখান থেকে যেকোনো বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবীভাবে মারাত্মক প্রমাণিত হতো। সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব হয়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবী। এটি মূলত এক বিশ্বাসঘাতকতার যৌক্তিক সমাপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়। …[23]
ফলে, পাকিস্তানে যদিও ২৩ মার্চকে ‘পাকিস্তান দিবস’ হিসেবে যথেষ্ট আবেগপূর্ণভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তবু এর প্রকৃত তাৎপর্য কী, কীভাবে বাঙালিরা লাহোর প্রস্তাবকে একটি কার্যকর ফেডারেল সমাধান, এবং একটি গণতান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে দুই অংশের মধ্যে আরও দৃঢ় বন্ধনের পথ হিসেবে দেখেছিল—সেই বিষয়ে তেমন উপলব্ধি নেই।
১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারে বাঙালিদের উচ্ছ্বাস এবং শেখ মুজিবের বিপুল জয়ের পর যে উদ্দীপনার ঢেউ উঠেছিল, তা আমাকে মনে করিয়ে দেয় জিজেকের ‘শেষ বিচারের দিনের’[24] একটি সেকুলার ধারণাকে। জিজেক লিখেছেন,বামপন্থী রেটরিকে প্রায়ই এমন এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত থাকে, যখন ‘সমস্ত সঞ্চিত দেনা পুরোপুরি পরিশোধিত হবে’, যেখানে ইশ্বরের স্থলে মানুষই হবে বিচারক ১৯৭০–৭১ সালে পূর্ব বাংলায় যা ঘটছিল, তা যেন ছিল সেই মুহূর্ত। যখন দীর্ঘ বছরের অবিচার, দমন ও শোষণের পর বাঙালি নেতারা জনগণের মধ্যে সঞ্চিত ‘ক্রোধের পুঁজি’কে লভ্যাংশের মতো ফিরিয়ে দিলেন এক ক্ষোভের বিপ্লবী উচ্ছ্বাসে। সেই মুহূর্ত আওয়ামী লীগের কর্মীদের আসন্ন ক্ষমতার ন্যায্য হিস্যার প্রত্যাশায় মাতিয়ে তুলেছিল; যে হিস্যা থেকে পাকিস্তানি রাষ্ট্র নানা শোষণমূলক কৌশলে, অমর জানের ভাষায় ‘ভয়ের শাসন’ দিয়ে, তাদেরকে বঞ্চিত করেছিল।[25]
আওয়ামী লীগ ১৯৪৭ থেকে শুরু হওয়া অসংখ্য অবিচারের প্রতীকী প্রতিকার দাবি করেছিল; যেমন : বাংলা ভাষার সমঅধিকারের অস্বীকৃতি, ভাষা আন্দোলনে ছাত্র হত্যাকাণ্ড, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিকে পাশ কাটিয়ে দুই অংশে সমতার নামে নানা প্রস্তাব (যেমন পশ্চিম পাকিস্তানকে ‘ওয়ান ইউনিট’ করা), জাতীয় রেডিওতে রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ, গণপরিষদে প্রকৃত দাবি ও অভিযোগে বাঙালি প্রতিনিধিদের উপেক্ষা, ফাতিমা জিন্নাহর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত কারচুপি করে আইয়ুব খানের জয় নিশ্চিত করা, এবং উন্নয়ন তহবিলে ন্যায্য ভাগ থেকে বঞ্চনা। এমনকি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রাজধানী হয়েও ঢাকা কখনো প্রধান ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। এসবের পরিণতি ছিল তীব্র হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চয়। তবু বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা স্বীকার করতে চাননি যে অনুন্নয়নের ঐতিহাসিক শিকড় ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত, কিংবা এই সময়ে আমলাতন্ত্রে বাঙালিদের উপস্থিতি এবং প্রাদেশিক উন্নয়ন তহবিল কিছুটা বেড়েছিল, অর্থাৎ ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছিল
ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর আওয়ামী লীগ সেটি প্রকাশ করেছে নানা স্তরে—কখনো ধর্মঘটের ডাক দিয়ে, কখনো প্রদেশের অ-বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতি ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। ইয়াহিয়া খানের আলোচনাকারী দলের সঙ্গে বৈঠকে শেখ মুজিবের প্রতিনিধিরা তাঁদের গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে পৌঁছান। আলোচনায় তাঁরা কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দেন। ইয়াহিয়া ও সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কাছে শুধু এই ঘটনাই—যে তাঁদের ইসলামাবাদে না ডেকে ঢাকায় এসে মুজিবের অনুমোদন চাইতে হচ্ছে—ছিল চরম অপমানের প্রতীক। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বাঙালি রাজনৈতিক দলগুলোর এক জোট যুক্তফ্রন্ট—একইভাবে মুসলিম লীগকে পরাজিত করেছিল। তখন পাকিস্তানি রাষ্ট্র দ্রুত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বিরোধী ঐক্যকে ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭০-এর প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল। তরুণ বাঙালি রাজনৈতিকর্মীদের এক নতুন প্রজন্ম মুজিবের ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের চারপাশে সমবেত হয়েছিল।
তবু, বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি সেনাদের বছরের পর বছরের জাতিগত অহংকারের প্রতিদান স্বরূপ জনসমক্ষে মানসিক মুক্তির অভিনয় চললেও, , সমঝোতার আলোচনা তখনো ভেঙে পড়েনি। আসল ঘটনা হলো—সেনাবাহিনীর ধৈর্য শেষ হয়ে আসছিল, কারণ তারা এই ধরনের প্রতীকী প্রতিদানমূলক কৌশলের সাথে অভ্যস্ত ছিল না। ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনার সময় ইয়াহিয়া খান বলেন—বিশ্ব তাকে নিয়ে হাসছে। এভাবে উপহাসিত হওয়ার অনুভূতি এবং হারানো পৌরুষ ফেরানোর উপায় হিসেবে সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। অমর জান ব্যাখ্যা করেছেন—জেনারেল ডায়ারের সংকট ছিল, তিনি মনে করতেন ভারতীয়রা প্রকাশ্যে ঔপনিবেশিক আইন অমান্য করে ব্রিটিশদের নিয়ে উপহাস করছে। তাই, তিনি মনে করেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে জড়ো হওয়া ভারতীয়দের নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে হবে, তাদের শিক্ষা দিতে। কিন্তু জানের মতে, সেই ‘শিক্ষা’র আসল শ্রোতা জালিয়ানওয়ালাবগে উপস্থিত মানুষেরা ছিলেন না, বরঞ্চ শ্রোতা ছিলেন গোটা ভারতবর্ষ, এমনকি সম্ভবত অন্য সব উপনিবেশও।[26] ইয়াহিয়াও একই কৌশল নেন। আলোচনার টেবিল চলতে থাকলেও, তার কমান্ডাররা সমান্তরালভাবে কয়েকদিন ধরে সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করছিল।
‘আইন-সংরক্ষণমূলক সহিংসতা’র যুক্তির ধারায় চলতে থাকে ২৫ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডসমূহ; যুক্তি দাঁড়ায় এই ধারণায়। এহেন পরিস্থিতিতে পুলিশ বা সামরিক পদক্ষেপ, ভাল্টার বেঞ্জামিনের ভাষায়, আইন প্রণয়নমূলক ও আইন সংরক্ষণমূলক সহিংসতার ভেদরেখা মুছে দেয়। তাঁর মতে, “এটি আইন প্রণয়নমূলক, কারণ এর মূল কাজ আইন জারি করা নয়, বরং যেকোনো ফরমানের জন্য আইনি দাবি প্রতিষ্ঠা করা; এবং এটি আইন-সংরক্ষণমূলক কারণ সেই লক্ষ্যপূরণের হাতিয়ার হিসেবে এটি কাজ করে।”[27]
এখানে রাষ্ট্রের সহিংসতার মৌল দাবির পুনরাবৃত্তি এবং অস্পষ্ট আইনি পরিস্থিতিতে আইনপ্রণেতা হিসেবে তার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ—দুটো একসাথে মিলিত হয়। জ্যাক দেরিদার ভাষায়, এই পুনরাবৃত্তি “আদি সত্তাকে [অরিজিন] মূল রূপে নিজেকে পুনরাবৃত্তি করতে, নিজেকে পরিবর্তিত করতে বাধ্য করে, যাতে এটি আদির মূল্য ধারণ করতে পারে, বা সংরক্ষণ করতে পারে”।[28] এই ধরনের সূত্রায়ন সামরিক অভিযানের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও বিবরণের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। মেজর জেনারেল এ. ও. মিট্টা জানাচ্ছেন,সেনাদের বড় বড় ব্রিগেড দুর্গে কেন্দ্রীভূত না রেখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মোতায়েন ছিল ছিল। তিনি এই কৌশলের বিরোধিতা করে উল্টে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে সফল হননি।[29] অথচ, এই তাৎক্ষণিকতা ও কমান্ড কাঠামোর ভাঙনই হয়ে দাঁড়ায় কার্যত সেই অভিযান-পদ্ধতির মূল কার্যনির্বাহী যুক্তি,যেখানে ময়দানের সৈন্যরা চার-পাঁচ জনের ছোট দলে স্বাধীনভাবে কাজ করে। আইন রক্ষার দায়িত্ব পালনের সময়, জেনারেল এ. কে. নিয়াজি সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন এলাকার সম্পদ ব্যবহার করে চলে,[30] এবং তাদের উপর হামলা করতে আসা বা মুক্তিবাহিনীর সাথে সহযোগিতার সন্দেহে থাকা ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত বিচার ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কালে তারা যেন নিজেরাই আইন তৈরি ও প্রয়োগ করে।
সাবেক সেনা কর্মকর্তারা এই কর্মকাণ্ডগুলোকে গর্বের সঙ্গে নিজেদের সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করেন। সম্প্রতি এক টিভি সাক্ষাৎকারে মেজর আরিফ হামিদ স্বীকার করেন যে, যে সকল অঞ্চলে রেললাইনকে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল সেখানে ‘সামষ্টিক শাস্তি’ বা কালেক্টিভ পানিশমেন্ট দেওয়ার নির্দেশ জেনারেল টিক্কা খান দিয়েছিলেন।[31] একইভাবে ব্রিগেডিয়ার কররার আলী আগা উল্লেখ করেন ১৭ জন বাঙালি অফিসার ও ১,৩২৫ জন প্রাক্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সদস্যের হত্যাকাণ্ডের কথা। তিনি ওই অভিযানের একটি ভয়াবহ বিবরণ দেন,
লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াকুব নিজ উদ্যোগে ‘অভ্যন্তরীণ শত্রু’ সমস্যার সমাধান করার সিদ্ধান্ত নেন। পরে জানতে পারি, আটক সব বাঙালি অফিসার ও সৈন্যকে ব্রিগেড সদর দফতরের কাছে একটি মাঠে আনা হয়। কর্নেল ইয়াকুব কাছাকাছি একটি স্কোয়াশ কোর্টের দর্শক গ্যালারিতে একটি ভারী ফায়ারিং স্কোয়াড বসান। অসহায় বন্দিদের কয়েকজন করে স্কোয়াশ কোর্টের নিচের অংশে আনা হতো, আর ওপর থেকে ফায়ারিং স্কোয়াড গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করত। পরবর্তী দফার বন্দিদের বাধ্য করা হতো আগের দফায় নিহতদের লাশ তুলে পাশের একটি গণকবরে ফেলে দিতে—যেটি ইঞ্জিনিয়ার্স কোম্পানির একটি বুলডোজার দিয়ে তড়িঘড়ি খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। সবশেষে অফিসারদের ‘বাংলাদেশে পাঠানো হয়’—ফিরে এসে কর্নেল ইয়াকুব এভাবেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন। ওই দিন, উন্মত্ত ওই কর্নেলের হাতে ঠান্ডা মাথায় খুন হন মোট ১৭ জন অফিসার ও ১,৩২৫ জন সৈন্য। সবচেয়ে সিনিয়র যিনি নিহত হন, তিনি ছিলেন ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্স ইউনিটের লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহাঙ্গীর। গুলি করার ঠিক আগে তিনি মাটিতে নিজের ইউনিফর্মের টুপি ছুড়ে ফেলে পা দিয়ে লাথি মারেন এবং অবজ্ঞাভরে চিৎকার করে বলেন—“জয় বাংলা।” এটাই ছিল তাঁর শেষ উচ্চারণ।[32]
সেনা অভিযানের আগের সময়ে—বিশেষ করে ১ মার্চ ১৯৭১-এ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা থেকে শুরু করে ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস কালো দিবস হিসেবে পালনের ডাক পর্যন্ত—আওয়ামী লীগ কর্মীরা কার্যত প্রদেশে এক সমান্তরাল সরকার গড়ে তোলে। ওই সময়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং অ-বাঙালি জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। সেনারা কার্যত ব্যারাকে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, বাজারের ব্যবসায়ীরা তাদের রসদ দিতে অস্বীকার করে। এমনকি ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের কর্মীরাও আলোচনার জন্য আসা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের—বিশেষত ভুট্টোকে—খাবার পরিবেশন করতে অস্বীকৃতি জানায়।[33] বিমানবন্দরে ফ্লাইট চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে পাকিস্তান বিমানবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ নিতে হয়েছিল।
আইনের বৈধতার একটি সমান্তরাল দাবি প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ কার্যকরভাবে সহিংসতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত আইনের স্বাভাবিক ভিত্তিটিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। বৈধতার নামে রাষ্ট্র যে সহিংসতা ও ভয় প্রদর্শন করে, আওয়ামীলীগের সহিংসতা ও ভয়-প্রদর্শন যেন ছিল তারই প্রতিফলন। ফলে, আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড কেবল সাধারণ আইনভঙ্গ বা অপরাধে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল আইনের সহিংস ভিত্তিকে প্রকাশ্যে উন্মোচন করা এবং সহিংসতার মাধ্যমেই আইনের একটি সমান্তরাল রূপ তুলে ধরার সম্ভাবনা তৈরি করা।[34] যেমন নাসের হুসেন আমাদের মনে করিয়ে দেন, বেঞ্জামিনের অপরাধ সম্পর্কিত দুটি ধারণার পার্থক্য টেনে: একটি হলো ‘আইনের বিরুদ্ধে এমন এক সীমালঙ্ঘন যা আইন দ্বারা দমন করা যেতে পারে… [এবং] আরেকটি হলো এক সাধারণ অস্থিরতা যা আইন লঙ্ঘন না করে বরং তার বিপরীতে একটি বিকল্প যুক্তি ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার হুমকি দেয়’।[35] সুতরাং, সামরিক অভিযানটি ছিল অন্য যে কোনো কিছুর চাইতে বেশি: মূলত রাষ্ট্রের সহিংসতাকে তার মৌল ভিত্তি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা।
বাঙালিদের মনে ভয় সঞ্চারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই অভিযান কার্যত যে-কোনো রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনা শেষ করে দেয়। সহিংসতার আশ্রয় নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে—যারা শেখ মুজিবের সর্বাধিক রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ও দ্বি-অর্থনীতির পরিকল্পনার পক্ষে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছিল। এতটাই ব্যাপক ছিল এই সমর্থন—যা সেনা অভিযানের পর প্রায় সর্বসম্মত রূপ নেয়—যে বাঙালি সেনা সদস্যরাও বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। মাঠপর্যায়ের অনেকে এই বিদ্রোহ অনুমান করলেও, দূরে বসা সামরিক পরিকল্পনাকারীদের জন্য এটি ছিল বিস্ময়কর। আসলে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ডিসেম্বর ১৯৭০-এর নির্ধারিত নির্বাচনের আগেই অপারেশন ব্লিটজ নামে একটি অভিযান পরিকল্পনা করেছিল। এর সফলতা নির্ভর করত সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের সহযোগিতার ওপর।[36] কিন্তু বাস্তবে, প্রাক্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও অন্যান্য বাঙালি-প্রধান সেনা ইউনিটের বড় অংশ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। ফলে, অপারেশন সার্চলাইট-এর একটি বড় অংশ ব্যয় করতে হয় এই বাঙালি ইউনিটগুলোকে নিরস্ত্র করার জন্য।
কাজেই, সংঘাতটিকে জাতিগত রূপ দেওয়ার কাজটি করেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, যেখানে প্রত্যেক বাঙালি, এমনকি সেনাবাহিনীতে কর্মরত সদস্যরাও, সন্দেহভাজন হয়ে ওঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী প্রায় পাঁচ লাখ বেসামরিক বাঙালিদেরও একইভাবে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। অন্তত ৮০,০০০ মানুষকে বিভিন্ন আটকশিবির ও অস্থায়ী কারাগারে পাঠানো হয়, তারা যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক পর পর্যন্ত আটক ছিলেন।[37] এই মনোভঙ্গির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, বাঙালিরা তখনও পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন। রাষ্ট্রহীন হয়ে যায়নি; হয়ে গিয়েছিল অধিকারহীন নাগরিক। সম্ভবত এই কারণেই সহিংসতার মাত্রা এত ব্যাপক হয়েছিল।এটি কোনো একক গোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, বরঞ্চ পুরো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চালানো হয়েছিল, যাদের বি-জাতিকরণ সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ এখানে শত্রু ছিল নাগরিকরেই; সবাই। তারা ছিল আড়ালে, অদৃশ্য, তবুও সর্বত্র উপস্থিত। আর যখন রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তখন সেই শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার যেকোনো অভিযান অবশ্যম্ভাবীভাবে গণহত্যায় রূপ নেয়।সেনাবাহিনী ও তার কমান্ড কাঠামোর ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারী হিসেবে পাকিস্তানি সামরিক নেতৃত্ব ভুলে গিয়েছিল,পুলিশি অভিযানের প্রথম নিয়ম হলো এমন সেনা মোতায়েন করা যাদের স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কোনো আবেগগত সম্পর্ক নেই। এই কারণেই, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অনেক পরিকল্পিত অভিযানে ব্রিটিশরা নির্ভর করত গুর্খা বা মিশ্র জাতিগত গঠনের ইউনিটগুলোর ওপর—যাতে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা অবাধ্যতার ঝুঁকি কম থাকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এখানে সেনাবাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল মূলত অ-বাঙালিদের রক্ষার নামে—যাদের সঙ্গে তাদের রক্ত, জাতিগত বা ভাষাগত যোগসূত্র ছিল। সেনা অভিযানের ‘কিছু মাত্রাতিরিক্ততা’র এক বহুল ব্যবহৃত ব্যাখ্যা হাজির করা হতো পূর্ব বাংলায় বসবাসরত পশ্চিম পাকিস্তানিদের ওপর বাঙালিদের ভয়াবহ সহিংসতার চাক্ষুস বর্ণনার ক্ষেত্রে। ব্রিগেডিয়ার কররার আলী আগা বিহারি ও অন্যান্য অ-বাঙালিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার ‘প্রতিক্রিয়া’ হিসেবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিশোধমূলক হত্যাযজ্ঞ ও ধর্ষণের ভয়ঙ্কর বিবরণ দিয়েছেন। বিশেষ করে অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে সংঘটিত শারীরিক ও যৌন সহিংসতার ব্যাপ্তি বোঝাতে আমি তার বক্তব্যের দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি লিখেন,
এ ধরনের নৃশংস ও অমানবিক ঘটনার সাক্ষী হওয়ার পর কিছু সৈন্যও উন্মত্ত হয়ে ওঠে, আর তখন অফিসারদের পক্ষে সেনাবাহিনীর প্রচলিত শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে এমনকি অফিসাররাও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারান। সংক্ষেপে বলা যায়—অনেক সৈন্যের মতো কিছু অফিসারের ক্ষেত্রেও প্রতিশোধস্পৃহা, এবং তা কার্যকর করার সুযোগ, এতটাই প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সেনাবাহিনীর প্রচলিত শৃঙ্খলার কড়াকড়িও সেটি দমিয়ে রাখতে পারেনি। প্ররোচনা, সুযোগ, পূর্ণ ক্ষমতা—এবং বহু ক্ষেত্রে বিজয়ী সৈন্যদের ব্যক্তিগত দুর্নীতি—পরাজিতদের জন্য এক ধ্বংসাত্মক ‘পারফেক্ট স্টর্ম’ সৃষ্টি করেছিল। কয়েকজন অফিসার নিয়মিত রাতের বেলা ব্যক্তিগত বাড়িতে হানা দিতেন, আর যে মেয়েদের আকর্ষণীয় মনে হতো, তাদের টেনে নিয়ে যেতেন রাত কাটানোর জন্য।
আমার মনে পড়ে আরেকটি ঘটনা। একবার আমরা খবর পাই—ইপিআরের কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য এমন এক এলাকায় প্রবেশ করেছে যেখানে কয়েকটি বাঙালি পরিবার বসবাস করত, এবং তারা কিছু মহিলাকে সোডোমাইজ করেছে। এই প্রতিবেদন যথাযথভাবে জানানো হয় কর্নেল ফজল হামিদকে, যিনি তখন ইপিআরের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। তার একমাত্র ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ছিল—যৌন সহিংসতা (rape) পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ‘বোধ্যগম্য’ হতে পারে, কিন্তু একজন মহিলাকে সোডোমাইজ করা বরং ‘লজ্জার বিষয়’![38]
প্রতিশোধের উদ্দেশ্য ছাড়াও, বাঙালিদের মতে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী একটি দখলদার বাহিনী হিসেবে কাজ করেছিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল, কারণ তারা বাঙালিদের অসম্মানিত বা শ্রদ্ধার অযোগ্য মনে করত। এই দাবির সমর্থনে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। হাফসা খাজা তার গবেষণামূলক প্রবন্ধে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর শীর্ষ জেনারেলদের প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক বিবরণে বাঙালিদের প্রতি তাদের অবজ্ঞার ইতিহাস খুঁজে বের করেছেন।[39] হামুদুর রহমান কমিশনও পূর্ব পাকিস্তানে দায়িত্বপ্রাপ্ত শীর্ষ সামরিক নেতৃত্বের বক্তব্য ও বাঙালিদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে কিছু হত্যাযজ্ঞ ও যৌন সহিংসতা অবশ্যই ঘটেছিল এবং বর্ণবাদী মানসিকতা এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করেছিল।
পাকিস্তানে ১৯৭১ বিষয়ক আত্মপক্ষসমর্থনমূলক অধিকাংশ লেখায় সামরিক অভিযানের যৌক্তিকতা খোঁজা হয় বিদ্রোহ দমন করার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম অধিকারের মধ্যে। ফয়সাল দেবজি সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন,পূর্ব পাকিস্তানের সহিংসতাকে বর্ণনা করতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিদ্রোহ, সশস্ত্র অভ্যুত্থান বা অভ্যন্তরীণ অশান্তি ইত্যাদি ব্যবহার না করে ‘গৃহযুদ্ধ’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। নয়। দেবজির মতে, এই শব্দের ব্যবহারই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ,কারণ গৃহযুদ্ধ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত করে।[40] শব্দচয়নের গুরুত্ব এখানে স্পষ্ট, কারণ আমরা কীভাবে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াইকারীদের দেখি তার ওপর তা প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশিদের জন্য এটি ছিল এক বৈধ মুক্তিযুদ্ধ—যার চূড়ান্ত সাফল্য ছিল একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র অর্জন। ‘মুক্তিযুদ্ধ’ শব্দটি ব্যবহার করে বাংলাদেশিরা এ সংগ্রামকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানায়—যে সংগ্রাম তাদের জনগণকে প্রচণ্ড বেদনা ও ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করেছে। এই শব্দের আবেগময় বাড়তি তাৎপর্য নিছক রাজনৈতিক অলঙ্কার নয়,এটি বাঙালিদের অসহ্য যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির স্বীকৃতির আহ্বান; , এটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে দখলদার বাহিনী হিসেবে অভিযুক্ত করে, এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেও বিজয়ী হওয়া জনগণের অদম্য মনোবলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। অন্যদিকে, পাকিস্তানি রাষ্ট্র এই সংঘাতকে নিরপেক্ষ আঁকারে হাজির করতে বা তার সহিংস অতীতকে খাটো করে দেখাতে ‘বিচ্ছিন্নতা’, ‘পতন’ ও ‘বিপর্যয়’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে একে তোয়াক্কা করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং পাকিস্তানি রাষ্ট্র ও তার বিদ্বৎসমাজের দায়িত্ব হলো এটা মেনে নেওয়া যে, বাঙালিরা এমন এক সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছিল, যা সংঘাত চলাকালীন অবস্থাতেই বিশ্বের বহু স্থানে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে বৈধ স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিল।
সে সময় আন্তর্জাতিক সমর্থন ও স্বীকৃতি পাওয়ার পেছনে একাধিক কারণ ছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন নির্মম সামরিক অভিযান চালায়—যেখানে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও লক্ষ্যবস্তু হন—তখন তারা কার্যত অস্বীকার করে বসেছিল যে আওয়ামী লীগ জনসমর্থনের বিপুল গণভোট-সমান ম্যান্ডেট পেয়েছিল। এর ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে এবং আওয়ামী লীগ ও তাদের নেতত্বে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার যৌক্তিকতা পায়। গ্রেপ্তারের ঠিক আগে, ২৫–২৬ মার্চ ১৯৭১-এর মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার একটি ঘোষণা দেন বলে জানা যায়,যদিও এর সত্যতা নিয়ে বিতর্ক আছে। তারপরও, নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অধিকাংশ ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ মুজিবনগরে সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।[41] তারা শপথ নেন যে এক দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চালাবেন। পরবর্তীতে কলকাতায় একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, যা নিয়মিতভাবে বেসামরিক প্রশাসনকে নির্দেশ জারি করত এবং এমনকি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানও তদারকি করত। বাংলাদেশের ইতিহাসবিদরা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যক্রমের ওপর বিস্তৃত প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করেছেন, যাতে প্রমাণিত হয়—১৯৭১-এর এপ্রিলে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ চালানোর বৈধতা রাখত।
এম. রফিকুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের পরিভাষা ও তার আইনি যৌক্তিকতা নিয়ে অগ্রগণ্য গবেষণা করেছেন। ১৯৬৭–১৯৭০ সালের নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ এবং একতরফা বায়াফ্রা প্রজাতন্ত্র ঘোষণার অভিজ্ঞতা ১৯৭১-এর ঘটনাপ্রবাহে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানেও, প্রভাব ফেলেছিল। আমেরিকান জনমত প্রভাবিত করতে ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফাউন্ডিং ফাদার’দের ঘোষণার উদ্ধৃতি টেনে বলেছিলেন—“যখনই কোনো সরকার মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ অন্বেষণের অবিচ্ছেদ্য অধিকারকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, তখন জনগণের তা পরিবর্তন বা বিলুপ্ত করার অধিকার আছে।”[42] রফিকুল ইসলামের মতে, একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনে কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই।[43] আসল বিষয় ছিল সেই ঘোষণা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ক্ষমতা, যা বাঙালিরা ভারতীয় সামরিক সহায়তা ও দেশের ভেতরে প্রবল জনসমর্থনের মাধ্যমে সফলভাবে প্রমাণ করেছিল। এই অর্থে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম আন্তর্জাতিক আইনে এক নতুন ধারা তৈরি করে—যেখানে উপনিবেশ-পরবর্তী রাষ্ট্র থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভের বৈধতা স্বীকৃত হয়। ফয়সাল দেবজির ভাষায়, বাংলাদেশ “এমন এক নতুন রাজনৈতিক যুক্তির প্রথম উদাহরণ, যেখানে রাষ্ট্র কেবল গৃহযুদ্ধ থেকেই জন্ম নেয়।”[44] এর আগে মুক্তিযুদ্ধ কেবল বিদেশি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বৈধ ধরা হতো। কিন্তু বাংলাদেশের সাফল্য পেছনে তাকিয়ে এক নতুন আইনি যুক্তি তৈরি করে, যা দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার দাবি ন্যায়সঙ্গত করে তোলে। এই নজির পরে কসোভো, বসনিয়া, পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের মতো স্থানে আন্তর্জাতিক মানবিক সহযোগিতার মডেল হয়ে দাঁড়ায়। তবু পাকিস্তানের বহু মানুষের জন্য বাংলাদেশকে মুক্তি আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া আজও এক গভীর মানসিক প্রতিবন্ধকতা। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায়, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এক নির্মম অভিযান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অস্বীকারের মাধ্যমে কার্যত দখলদার বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ছিল ন্যায়সঙ্গত।
এখানে একটি ঐতিহাসিক মিল খুঁজে পাওয়া যায় ১৮৫৭ সালের ঘটনাকে ‘ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ’ নামে অভিহিত করার বিষয়ে ব্রিটিশদের উদ্বেগের সঙ্গে। এমনকি ঘটনার শতবর্ষ উদ্যাপনকালেও (১৯৫৭ সালে) কমনওয়েলথ অফিস গভীরভাবে চিন্তিত ছিল ভারতীয় জনমনে বিদ্যমান উপনিবেশ-বিরোধী আবেগ এবং তা থেকে ব্রিটিশ স্বার্থের সম্ভাব্য ক্ষতি নিয়ে।[45] আরও ৫০ বছর পর হয়তো ‘মুক্তিযুদ্ধ’ শব্দটি বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে;পাকিস্তানি রাষ্ট্র এর বৈধতা স্বীকার করবে বলে নয়, বরঞ্চ ঘটনাটির স্মৃতি আরও ম্লান হয়ে যাবে বলে। তখন অবশিষ্ট যুদ্ধাপরাধীরাও আর বেঁচে থাকবে না। এ থেকেই বোঝা যায়—স্মৃতির শক্তি কতখানি, এবং কীভাবে রাষ্ট্র নিজস্ব পছন্দমতো ঐতিহাসিক আখ্যান দিয়ে ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের অর্থ স্থির করে রাখতে চায়। ভাল্টার বেঞ্জামিন ঐতিহাসিক মুহূর্তের তাৎক্ষণিকতা এবং একে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ ‘শত্রু বিজয়ী হলে মৃতরাও নিরাপদ থাকবে না। আর এই শত্রু কখনো বিজয়ী হওয়া থেকে বিরত থাকেনি।’[46] এই কারণেই বেঞ্জামিনের মতে, যদি কোনো ঐতিহাসিক নিজেকে দালাল হিসেবে গণ্য হতে না চান, তবে ইতিহাসকে অবশ্যই একটি বিপ্লবী অনুশীলন (revolutionary praxis) হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।[47] এই ধরনের র্যাডিকাল ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত, আগেই উল্লিখিত, একগুচ্ছ কুৎসিত প্রোপাগান্ডার প্রেক্ষিতে। যেগুলোর কিছু ইংরেজি ও বাংলায় অনূদিত/ডাব করা হলেও মূল শ্রোতা পাকিস্তানের জনগণ। সামরিক বাহিনী তাদের নাগরিকদের মধ্যে যে আদর্শিক ধোঁয়াশা ছড়িয়ে দিয়েছে, তাকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। এর জন্য তারা হয় ইতিহাসের একটি সরলীকৃত সংস্করণ ব্যবহার করবে অথবা পাকিস্তানকে ভাঙার ঘটনাকে একটি ভারতীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে তুলে ধরে ইতিহাসকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলবে। এই নতুন প্রচারণার আরও কিছু দিক রয়েছে, যার জন্য আলাদা বিশ্লেষণের প্রয়োজন।
বেঞ্জামিন যে ‘ দালালি ইতিহাস’ থেকে সাবধান করেছিলেন, তার সেরা উদাহরণ হলো শর্মিলা বোসের কাজ। তার Dead Reckoning বই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সব অপরাধ থেকে অব্যাহতি পেতে সাহায্য করেছে। বোসের একাডেমিক ডিগ্রি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, এবং তার ‘হিন্দু পরিচয়’—এসব মিলে তার বস্তুনিষ্ঠতার ধারণাকে পাকিস্তানে আরও শক্তিশালী করেছে। এই ধর্মীয় ‘যোগ্যতা’ আসলে হিন্দুদের সম্পর্কে বিদ্যমান এক ধরনের ধাঁচা (স্টেরিওটাইপ) জিইয়ে তোলে। ধারণাটি হলো—তিনি হিন্দু হয়েও সত্যবাদী, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ। পাকিস্তানে ‘ঢাকার পতন’ নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে বোসের বইকে বাংলাদেশের তথাকথিত ‘প্রপাগান্ডামূলক দাবির’ সবচেয়ে অথরিটেটিভ জবাব হিসেবে উল্লেখ করা খুবই সাধারণ ঘটনা। তাই তার কাজের বিভিন্ন ধোঁয়াশাপূর্ণ পদ্ধতিগত কৌশল বিশ্লেষণ করা এবং সঠিক প্রশ্ন তুলে সেগুলো উল্টে দেওয়া জরুরি।
বোস নিজেকে একজন স্ব-নিযুক্ত সত্য কমিশনার হিসেবে দেখেন, যিনি ১৯৭১ সালের ‘কথিত নৃশংসতা’ তদন্তের জন্য গঠিত এক-সদস্যের বিচার বিভাগীয় কমিশনের মতো কাজ করেন। তবে তার আচরণ একজন ঔপনিবেশিক কর্মকর্তার কথা মনে করিয়ে দেয়, যিনি প্রাচ্যবাদী ধারণার ভিত্তিতে কোনো বিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা অভ্যুত্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করছেন। সত্য দাবিগুলোর বিচারিক যাচাই এবং স্থানীয় সহিংসতা নিয়ে ঔপনিবেশিক বিবরণ—এই দুটি ভূমিকা তার মধ্যে মিলেমিশে গেছে। বিচারকের ভূমিকায় বোস বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেন, সাক্ষ্য যাচাই করেন, ফরেনসিক বিশ্লেষণ চালান—এবং শেষ পর্যন্ত দাবি করেন যে তিনি একটি নিরপেক্ষ রায় বা বস্তুনিষ্ঠ সত্যে পৌঁছেছেন। এই ভার যেন তাঁর উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি ‘১৯৭১ সালের সংঘাতের একটি অনন্য ইতিহাস রচনা করতে পারেন, যা পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।’[48] এর কারণ হলো, এমনকি কয়েক দশক পরেও বাংলাদেশিরা ‘সম্মিলিতভাবে ১৯৭১ সালের সুগবেষিত, নথিভুক্ত এবং চিন্তাশীল ইতিহাস তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে।’[49] অথচ তার গবেষণা মূলত সীমিত কয়েকটি কেস স্টাডির ওপর—যেখানে তিন ডজন পাকিস্তানি কর্মকর্তা ও সমানসংখ্যক বাঙালি জীবিত বা প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এত সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতেও তিনি পুরো যুদ্ধ ও এর মানবিক ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে চূড়ান্ত মন্তব্য করেন। তাঁর মতে ‘যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে’ মোট হতাহতের সংখ্যা ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ জনের মধ্যে ধরা যায়; যেখানে বাঙালি ও অ-বাঙালি, মুক্তিযোদ্ধা ও অযোদ্ধা, হিন্দু ও মুসলিম, পাকিস্তানি ও ভারতীয়—সবাই অন্তর্ভুক্ত।[50]
তার কাজ থেকে দুটি ‘বিশেষত্ব’ বোঝা যায়—একটি নাকি দ্বিদলীয় (bipartisan) দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের সক্ষমতা। বাংলাদেশিদের এ দুটিরই অভাব রয়েছে তিনি দাবি করেন। তিনি তাদের ‘পক্ষপাতিত্বের একাধিক স্তর এবং দুর্বল মান ও নথিপত্রের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব’ এর দোষে দুষ্ট বলে তিরস্কার করেন।[51] এমনকি মন্তব্য করেন—তিনি যেসব বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই তথ্য যাচাই বা স্বাধীন উৎস থেকে মিলিয়ে দেখার অভ্যাসে অভ্যস্ত নন।[52] ফলে ‘সম্ভাব্য কী ঘটেছিল’ সে বিষয়ে ‘যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে’ রায় দেওয়াটা নাকি তার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়[53]—এবং এই নিরপেক্ষতার জন্য নাকি পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারাও বিস্মিত হয়েছিলেন।
বোস নিরপেক্ষতার দাবি করলেও তার সম্পৃক্ততা নির্লিপ্ত নয়। তিনি শুরু করেছিলেন ১৯৭১-এর ইতিহাস আবেগমুক্তভাবে লেখার লক্ষ্যে। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে (পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কুখ্যাত কমান্ডার জেনারেল নিয়াজি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, “আবেগ ধরে রাখুন।”[54] পেছন ফিরে দেখলে বলা যায়, বোস এমন এক অবস্থান থেকে শুরু করেছিলেন, যেটি স্লাভয় জিজেক বর্ণনা করেছেন ‘সহিংসতাকে নির্লিপ্তভাবে বোঝার তাড়না’ হিসেবে, কারণ সহিংসতার অতিরিক্ত ভয়াবহতা ও ভুক্তভোগীদের প্রতি সহানুভূতি আমাদের চিন্তাকে ব্যাহত করতে পারে।[55] কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁছান ‘সহিংসতার এমন এক শীতল’ বিশ্লেষণে, যা ‘এর ভয়াবহতাকে পুনরুৎপাদন করে এবং তাতে অংশ নেয়’। পার্থক্য শুধু এই— তিনি গণহত্যামূলক সামরিক অভিযানের সাথে অভিযুক্ত পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের প্রচারিত বয়ান মেনে নেওয়ায় ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থেকেছেন, অন্যদিকে ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্যের মূল্যায়নে শীতল যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তার মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতায়ও এটি স্পষ্ট,যেখানে তিনি সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে মিশেছেন। এমনকি এমন একজনের সঙ্গে হালকা ঠাট্টা করেছেন, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি সন্দেহভাজন বাঙালিদের ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচায় ছুঁড়ে দিতেন—যা সে স্বীকার করেছে শুধু ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহার করেছে, বাস্তবে করেনি। একই কর্মকর্তা তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় নাচ ও গান নিষিদ্ধ করেছিলেন। এর জন্য বোস স্নেহভরে তাকে ‘ঠাকুরগাঁওয়ের আওরঙ্গজেব’ বলে ডাকেন।[56]
প্রমাণ সংগ্রহ এবং অংশীজন ও ঘটনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তৈরির পুরো প্রক্রিয়ায় বোস এমন এক ইতিহাসরচনার পদ্ধতি ও কাঠামো ব্যবহার করেছেন, যা ঔপনিবেশিক আমলের ‘দেশজ মানসিকতা’ সংক্রান্ত বয়ানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—যেখানে স্থানীয়দের বলা হয় খামখেয়ালি, অবিশ্বস্ত এবং বেখেয়ালি সহিংসতার প্রবণতাসম্পন্ন। বোসের এই পদ্ধতিগত পক্ষপাত নিয়ে নাঈম মোহাইমেন সূক্ষ্মভাবে ভাষিক প্রবণতাকে চিহ্নিত করেছেন। বাঙ্গালিদের বয়ানকে তিনি বলেন ‘claims’ বা দাবি, অথচ পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের বক্তব্য তিনি সরাসরি সত্য বলে ধরে নেন। মোহাইমেন যেমন উল্লেখ করেছেন, পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে তাঁর চিত্রায়ন হলো ‘ভালো মানুষ, সাধ্যমতো চেষ্টা করছে’; কিন্তু বাঙালিদের তিনি তুচ্ছ করেছেন এই বলে যে তাদের মধ্যে রয়েছে ‘তথ্যের যথার্থতা বা বিশ্লেষণী পরিশীলনের অভাব’, ‘অন্ধ ঘৃণা ও প্রতিহিংসা’, ‘নাটকীয় ভাষা ও মন্তব্য’, ‘অতিরঞ্জিত শৈলী’, এবং ‘বাস্তবতার উদ্দেশ্যহীন বিকৃতি’।[57] এর কারণ হলো, তিনি ‘বাঙালির মনস্তত্ত্ব’ সম্পর্কে তার ধারণা এমন কিছু লেখকের স্ব-প্রাচ্যবাদী (self-Orientalising) বিবরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন, যেমন জেনারেল ইয়াহিয়ার মন্ত্রিসভার মন্ত্রী জি. ডব্লিউ. চৌধুরী এবং নীরদ সি চৌধুরী। এই লেখকরা বাঙালিদের ‘কঠোর পরিশ্রম ও গঠনমূলক কর্মসূচির পরিবর্তে একটি নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবের’ জন্য নিন্দা করেছেন, যারা ‘অন্যদের উপর দোষ চাপানোর এক দারুণ প্রবণতা’ রাখে।[58] অন্য একটি ক্ষেত্রে, তিনি বাঙালিদের ‘চমৎকার গল্পবাজ’ বলে উল্লেখ করেছেন।[59] তবে তিনি এটি ব্যাখ্যা করেননি যে, বাঙালি হওয়ার এই ধরনের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলো একজন গবেষক হিসেবে তার নিজের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য নয়।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো,অবিশ্বস্থ উৎস হিসেবে বাদ দেওয়া তালিকায় হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট-এর নাম থাকা। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অনুসন্ধান আদালত (court of enquiry) হিসেবে গঠিত এই কমিশন শতাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নিয়ে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি নিয়ে বিস্তৃত তদন্ত চালায়। আজ পর্যন্ত এটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১৯৭১ সালের কর্মকাণ্ড ও তার পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ নথি—যদিও এর কিছু অংশ এখনো গোপন রাখা হয়েছে। এমনকি পাকিস্তানের সামরিক ইতিহাসবিদ ও সেনাপন্থী লেখকরাও এর মূল বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে বড় কোনো আপত্তি তোলেননি। তবে রিপোর্টটি গণহত্যা স্বীকারে কুণ্ঠা দেখিয়েছে,এতে নিহতের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৬,০০০ বলা হয়েছে, এবং কমিশনের দাবি অনুযায়ী তাদের বেশিরভাগই ছিল যোদ্ধা। যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গও রিপোর্টে কার্যত অনুপস্থিত। তবুও সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড—বিশেষত পেশাদারিত্বের অভাব ও শৃঙ্খলাভঙ্গ—নিয়ে রিপোর্টটি ছিল যথেষ্ট সমালোচনামূলক। বোসের অবস্থান এখানে বিস্ময়কর। তিনি পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় বয়ানকে সমর্থনকারী একাডেমিক উইলিয়াম রাশব্রুকের বইকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে গ্রহণ করলেও, এই কমিশন রিপোর্টকে আখ্যা দিয়েছেন “গভীরভাবে সমস্যাজনক” বলে। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পরিচালিত তদন্তকে তিনি অভিযুক্ত করেছেন “প্রমাণ ও বিশ্লেষণের নিম্নমান”-এর জন্য। তার ভাষায়—“যা কিছু এখানে ‘প্রমাণ’ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার অনেকটাই আসলে অভিযোগ; যেখানে অভিযুক্তদের জবাব বা অভিযোক্তা ও সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ ছিল না।”[60] কিন্তু বোস উপেক্ষা করেছেন যে, এই কমিশন কোনো অপরাধমূলক ট্রাইব্যুনাল ছিল না—বরং একটি তদন্তমূলক অনুসন্ধান আদালত, যার লক্ষ্য ছিল ঘটনার প্রকৃত বিবরণ ও প্রেক্ষাপট উদঘাটন, অপরাধীর বিরুদ্ধে সরাসরি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া নয়।
আদালত পূর্বাঞ্চলে দায়িত্ব পালনকারী সেনা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে এবং প্রভাবশালী সামরিক কর্মকর্তাদের নিজেদের আচরণ ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়। সব যুদ্ধবন্দী পাকিস্তানে ফিরে আসার পর কমিশন পুনরায় বসে, যাতে জেনারেল নিয়াজি ও রাও ফরমান আলির মতো ব্যক্তিরা তাদের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দিতে এবং তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জবাব দিতে পারেন। বোস এই রিপোর্টকে – যা কিনা তার কঠোরতা ও প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতার জন্য প্রায় সর্বসম্মতভাবে প্রশংসিত – অবজ্ঞা করার প্রধান কারণ——হলো যে এর বহু বিবরণ তার পছন্দের সেই ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এক নিখুঁত শৃঙ্খলাপূর্ণ পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালিদের ‘নারীসুলভ ও দুর্বল যোদ্ধা’ হিসেবে বর্ণগত শ্রেণিবিন্যাসের যুক্তি অনুসরণ করে, বোস মুক্তিযুদ্ধে তাদের সামরিক অবদানকে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি একটি পূর্ণ অধ্যায় উৎসর্গ করেছেন এই দাবি করতে যে লুঙ্গি-পরা হাতে অস্ত্রধারী মুক্তিকামী বাঙালির চিত্র আসলে এক ধরনের ছদ্মবেশ, আর প্রকৃত যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল পূর্ববাংলার ভেতরে অনুপ্রবেশ করা ভারতীয় কমান্ডোদের দ্বারা। তরুণ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচেষ্টা তিনি খাটো করে দেখিয়েছেন, একে কেবল কিশোরসুলভ উচ্ছ্বাস হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা তার মতে কোনো কার্যকর ফল বয়ে আনেনি। এই মনোভাব সবচেয়ে তীব্রভাবে প্রকাশ পায় মুক্তিযুদ্ধের এক প্রিয় চরিত্র—রুমি—সম্পর্কে তার শীতল ও নির্দয় বিবরণে। ২০ বছর বয়সী রুমি ঢাকায় পুলিশকে লক্ষ্যবস্তু করার অভিযানে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়েন এবং এরপর আর কখনো দেখা যায়নি। সোরেলের ভাষা ধার করে বলা যায়, বোস এমন একজন ঘটনার ইতিহাসলেখক, যিনি ‘মুক্তিকে হয় একটি স্বপ্ন অথবা একটি ত্রুটি হিসেবে বিবেচনা করার প্রলোভনে পড়েছেন’[61] এবং যিনি রুমির ‘কর্ম’ এবং তিনি ও তার সহযোদ্ধারা কিসের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে অক্ষম।
এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে, যেখানে বোস পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে দেশ রক্ষার এক মহৎ মিশনের অংশ হিসেবে মহিমান্বিত করেন। এমন কাঠামো সম্ভব হয় মূলত এই কারণে যে, বোস পাকিস্তানি রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূখণ্ডে সহিংসতা প্রয়োগের বৈধতায় বিশ্বাসী। তিনি সামরিক অভিযানের একপ্রকার আনুষ্ঠানিক নিন্দা জানান বটে, তবে তার আগে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বিচার সহিংসতা চালানো এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার অভিযোগপত্র সাজিয়ে নেন। আবার নিরপেক্ষতার স্বার্থে, তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত যে কিছু অতিরিক্ততা (excesses) ঘটে থাকতে পারে। এমন ঘটনাতেও তিনি কুখ্যাত কিছু হত্যাযজ্ঞের বিশদ বিবরণ দেন—কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে গ্রামবাসীদের উসকানিদাতা হিসেবে দায়ী করা, যাতে মনে হয় সেনারা বাধ্য হয়েই অভিযান চালিয়েছে। যেমন, থানাপাড়া হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে তিনি গ্রামবাসীদের ওপর দোষ চাপিয়ে বলেন, এর ফলে সেনারা ‘কম্বিং অপারেশন’ চালিয়ে গ্রামবাসীদের সারিবদ্ধ করে, পুরুষদের কিশোরদের থেকে আলাদা করে এবং তাদের অধিকাংশকে হত্যা করে। তবে তার দাবি—নিহতের সংখ্যা কোনোভাবেই কয়েক শত ছিল না। এ ধরনের ব্যাখ্যামূলক কৌশল প্রয়োগ করে বোসের উপসংহার—সহিংসতার সময়ও সেনারা পেশাদারিত্বের সঙ্গে, এমনকি মানবিকভাবে, ‘দুরূহ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের নিয়ম মেনে’ কাজ করেছে এবং ভেঙে পড়েনি।[62] তার কাছে আসল বিষয় হলো সংখ্যাগত হিসাব; মানুষের সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে কার জীবন থাকবে আর কার থাকবে না, সেই সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অভিজ্ঞতার মূল্য নেই।
কিন্তু বিহারী গণহত্যার প্রকাশিত ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে বোস একজন সুরতহালকারীর (coroner) মতো কাজ করেন না। তিনি কেবল হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর যে অতিরঞ্জিত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা-ই লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৭২ সালের ১০ মার্চ বিহারিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতায় তিনি অনায়াসে মেনে নেন যে ‘কয়েক হাজার বিহারি পুরুষ, নারী ও শিশু’ নিহত হয়েছিল।[63] একইভাবে, পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের আগস্টে প্রকাশিত White Paper on the Crisis in East Pakistan-এ মার্চ ১৯৭১-এ অভিযানের আগে ১ লক্ষ বিহারি হত্যার দাবি করে—এ ব্যাপারে বোস বলেন, সংখ্যাটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে, তবে এটিও তার কাছে যৌক্তিক মনে হয় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের হাতে বিহারি নিহতের সংখ্যা অগনিত।[64] আমি এখানে এই তথ্যগুলির সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না; শুধু দেখাচ্ছি, পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বাঙালি বেসামরিক হত্যার ক্ষেত্রে যে ‘পদ্ধতিগত কঠোরতা’ তিনি প্রয়োগ করেন, বিহারি হত্যার বেলায় তা প্রযোজ্য করেন না। জুডিথ বাটলারের ভাষায় বলা যেতে পারে, তিনি এমন কোনো অহিংসার সাধক নন, যিনি শোক-যোগ্যতার (grievability) মৌলিক সমতার ধারণায় বিশ্বাসী।[65] বরং তিনি সামরিক বাহিনীর অর্জনকে মহিমান্বিত করেন—হোক তা দেশ রক্ষার নামে, কিংবা আত্মরক্ষার যুক্তিতে। কেন বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে মার্চ ১৯৭১-এর পর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী দখলদার বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল, এই প্রশ্ন তার পক্ষে বোঝা বা তোলা সম্ভব হয় না। তার কাছে প্রশ্নটি অন্যভাবে দাঁড়ায়—কীভাবে ১৯৪৭ সালে ‘দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের জন্য স্বদেশ’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেশে কোনো বৈধ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন থাকতে পারে।[66]
রাষ্ট্রীয় সহিংসতাকে বৈধ হিসেবে দেখার মনোভাব বোসকে অন্ধ করে দেয় সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রতি, যা বাঙালিদের পক্ষ থেকেও সহিংসতার একটি সমান্তরাল আইনি যুক্তি তৈরি করেছিল। নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকার বাঙালি বেসামরিক নাগরিক ও বিদ্রোহী সেনাদের নির্দেশ দিয়েছিল পাকিস্তানি সেনা বা তাদের সহযোগীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে। এই অর্থে, বাংলাদেশের নির্বাসিত সরকারও কার্যত সেই সব বিদ্রোহীদের নিশানা করছিল, যারা রাষ্ট্রের অখণ্ডতার বিরোধিতা করেছিল। এ কারণেই রাষ্ট্রের সহিংসতার একচ্ছত্র অধিকারের পক্ষে বোসের সরলীকৃত যুক্তি ভয়াবহভাবে এসে দাঁড়ায় মুক্তিবাহিনীর বিহারিদের টার্গেট করার কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার ঝুঁকিতে। এই আত্মধার্মিক রাষ্ট্রীয় সহিংসতার যুক্তি মেনে নিলে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মনোভাবের কারণে একজন বিহারি হয়ে ওঠে ‘বৈধ লক্ষ্য’—একটি ‘বধযোগ্য দেহ’।
বোস অবশ্য নির্বাসিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আইনি ভিত্তি অতিরঞ্জিত বলে মানতে রাজি নন। তবে এর মানে এই নয় যে তিনি রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহিংসতার বৈধতাকেই পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তার কাছে মুজিবের নেতৃত্বাধীন আন্দোলন এমনকি অহিংস জনআন্দোলনের মানদণ্ডেও খর্ব ছিল। কেবল মুজিব জনসমাবেশ ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই তিনি গান্ধি হয়ে যান না—এমন মন্তব্য করেছেন বোস। তার মতে, মুজিবের রাজনৈতিক প্রতিরোধ গাঁধীয় ধাঁচের অহিংস আন্দোলনের মানদণ্ড পূরণ করেনি। নির্বাচনকালীন এবং সামরিক অভিযানের পূর্ববর্তী সময়জুড়ে বিচ্ছিন্ন কিছু সহিংস ঘটনা ঘটেছিল। একই সঙ্গে, বোস রাজনৈতিক আন্দোলনে সব ধরনের সহিংসতাকে অবৈধ বলে উড়িয়ে দেন না। কারণ এমন করলে তার পক্ষে সুভাস চন্দ্র বোস কিংবা ঔপনিবেশিক আমলের বাংলার ‘বিপ্লবী সন্ত্রাসী’দের ঐতিহ্য গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। তাই তিনি ‘সংগঠিত সহিংসতা’র নিমিত্তে একটি যথাযথ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য মুজিবের সমালোচনা করেছেন। শর্মিলা বোস লিখেছেন—“বাংলার আরেক বিখ্যাত সন্তান সভাষ চন্দ্র বসুর মতো মুজিব কখনো জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেননি, যে সুভাষ চন্দ্র বোস ভারতীয় জাতীয় সেনা গড়ে তুলেছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।”[67] কিন্তু ঠিক পরের বাক্যেই তিনি বলেন—“বিদ্রোহ দমন করতে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার প্রথম রাতেই মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়।”[68] অতএব, স্পষ্ট যে, মুজিব কোনো বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে পারেননি, কারণ সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো তার পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়নি; বরঞ্চ তাকে গৃহবন্দি নয়, সরাসরি গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো সংঘাতকাল তিনি কারাগারে কাটিয়েছিলেন এবং পূর্ব বাংলায় কী ঘটছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছিল।[69]
শুধুমাত্র সুভাষ চন্দ্র বসু পালাতে পেরেছিলেন বলেই তিনি প্রথমে নাৎসি জার্মানি ও পরে জাপানি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা স্থাপন করে একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন। বিপরীতে, মুজিব অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর সহযোদ্ধারা সফলভাবে একটি আধা-সংগঠিত মিলিশিয়া গড়ে তোলেন—যার মূল অংশ ছিল বিদ্রোহী পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সদস্য ও অন্যান্য বাঙালি ইউনিট। তারা ভারতের ভূখণ্ডে ঘাঁটি স্থাপন করে, যেখান থেকে কর্নেল ওসমানী পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করতেন। পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের প্রক্রিয়া এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, অনেক সময় যোদ্ধারা ওসমানীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করত—কারণ তিনি জরুরি অভিযানগত বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে দীর্ঘ নির্দেশিকা ও যোগাযোগপত্র রচনায় ব্যস্ত থাকতেন, আর তরুণ যোদ্ধারা যুদ্ধকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যেতে উদগ্রীব ছিল। তবে এ-ও সত্য, একাধিক সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে অসংখ্য উপদল ছিল, যারা কখনও কখনও রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করত।[70]
বোসের পদ্ধতি, প্রমাণ ও বর্ণনা নিয়ে আলোচনার অংশ শেষ করার আগে মনে রাখা জরুরি যে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তার মাঠপর্যায়ের গবেষণায় পূর্ণ সহায়তা দিয়েছিল। ২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকে, যখন দেশটি জেনারেল পারভেজ মুশাররফের সামরিক শাসনের অধীনে ছিল, সেনাবাহিনী শর্মিলা বোস ও ইয়াসমিন সাইকিয়াকে পাকিস্তানে এসে এমন সংবেদনশীল বিষয়ে গবেষণার অনুমতি দেয়। তারা উভয়ের জন্যই ১৯৭১ সালের পূর্বাঞ্চল ফ্রন্টে দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। সাইকিয়া তাদের কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন—কীভাবে প্রায়ই নারীবিদ্বেষী মানসিকতার ঐ কর্মকর্তারা তাকে তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলে একই পুরোনো বয়ান বারবার পুনরাবৃত্তি করতেন, নিজেদের কর্মকাণ্ড ও তার যুক্তি তুলে ধরতে। এই সাজানো সাক্ষাৎকারপরিসর এড়িয়ে যেতে সাইকিয়া লাহোর ও ইসলামাবাদের অবসরপ্রাপ্ত মেজর-ব্রিগেডিয়ারদের সংকীর্ণ পরিসর থেকে বেরিয়ে চকওয়াল জেলার গ্রামাঞ্চলে যান—অফিসার নন এমন সৈন্যদের সঙ্গেও, এমনকি তাদের স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে—যাতে আক্রমণকারীদের নিজেরাই যে মানসিক আঘাত বহন করছিল, তারও ধারণা পাওয়া যায়। অন্যদিকে, বোসকে সেনাবাহিনী এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন তাদের গোপন করার কিছুই নেই। বাস্তবে, সেনারা এমনভাবে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল যাতে বোস কখনো এমন কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা না পান যারা এমন সহিংসতায় জড়িত ছিলেন, যা তার নিজস্ব পদ্ধতিতে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তিনি এমন কারও সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেননি যাকে সেনাবাহিনী নিজেরাই যুদ্ধাপরাধের দায়ে কোর্ট মার্শাল করেছিল। ১৯৭১ সালের ২০ মে চুকনগরে হিন্দু হত্যাযজ্ঞের ক্ষেত্রে, বোস যশোর-খুলনা এলাকায় দায়িত্বপালনকারী বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তারা সবাই বিষয়টি নিয়ে অজ্ঞতার ভান করেন।[71] এই অদ্ভুত নীরবতা স্পষ্টভাবে ভিন্ন সেই পরিস্থিতিগুলোর তুলনায়, যেখানে সেনারা মনে করত তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ আছে। অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের কারণে বোস এই হত্যাযজ্ঞ অস্বীকার করতে পারেননি। তবে তিনি একে ‘এককালীন ঘটনা’[72] বলে আখ্যা দেন—দুই-একজন জীবিত বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির বয়ানের ভিত্তিতে, যারা অন্যত্র ঘটিত অনুরূপ ঘটনার কথা জানার সুযোগ পাননি। তিনি সেনাবাহিনীর নাম পরিষ্কার করতে তদন্তের আহ্বান জানান এবং এরপর আর গুরুত্ব দেননি। অন্য ঘটনার ক্ষেত্রে, যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হত্যাকাণ্ড, বোস সরাসরি সেই কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন যারা অভিযানে জড়িত ছিলেন—কারণ এতে সেনাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ ছিল। সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, তাদের লক্ষ্য ছিল ‘নিরপরাধ’ ছাত্র নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অবস্থানকারী সশস্ত্র বিদ্রোহী।
বোসের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর কার্যকর সম্পৃক্ততা থেকে যে বিবরণ বেরিয়ে আসে, তা এক ধরনের পুনর্মূল্যায়িত বয়ান—যা যুদ্ধ চলাকালীন বা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তারা বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে পারেনি, কিন্তু এখন তা সম্ভব হয়েছে। এমনকি জেনারেল ইয়াহিয়া খানও বোসের কাছ থেকে ইতিবাচক মূল্যায়ন পেয়েছেন; বোস তাকে বলেছেন, ‘পাকিস্তানের একমাত্র সামরিক শাসক, যিনি ক্ষমতা নেওয়ার এক বছরের মাথায় দেশকে গণতন্ত্রে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্যিই রেখেছিলেন।’[73] কিন্তু ইতিহাসকে এভাবে দেখা—বা ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করা—হলো গুরুতর ভুল; কারণ ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি, সামরিক অভিযান এবং তার পরবর্তী রক্তপাতই ছিল সেই সময়ের প্রকৃত পরিণতি। তবুও, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে বোসের অসংখ্য পদ্ধতিগত ত্রুটি—বা সরাসরি বিশ্লেষণে অক্ষমতা—থাকা সত্ত্বেও, ১৯৭১ সালের সহিংসতা নিয়ে তার কাজ পাকিস্তানে এখনো এক ধরনের নিরপেক্ষ ইতিহাসের উৎস হিসেবে কিংবদন্তি মর্যাদা ভোগ করছে।
সংখ্যার ভয়
পাকিস্তানের বিদ্রোহ দমন ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার সার্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হলেও, তা কোনোভাবেই বেসামরিক মানুষের ওপর সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডকে দায়মুক্তি দেয় না—বিশেষত হিন্দুদের, যাদের ধর্মীয় পরিচয় ও ভারতপন্থী মনোভাবের অভিযোগে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল, এবং বাঙালি নারীদের, যাদের ওপর চালানো হয়েছিল পরিকল্পিত যৌন সহিংসতা। এই যৌন সহিংসতা যে পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড ছিল তা একাধিক পাকিস্তানি অফিসারের সাক্ষ্যে প্রমাণিত—এর মধ্যে আছেন মেজর জেনারেল খাদিম হুসেইন রাজা, যিনি লিখেছেন, জেনারেল নিয়াজি হুমকি দিয়েছিলেন ‘তার সৈন্যদের [বাঙালি] নারীদের ওপর ছেড়ে দেওয়ার’।[74] সামরিক অভিযান অসামঞ্জস্যভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে নিশানা করেছিল—যারা সংঘাতের তুঙ্গ মুহূর্তে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেওয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থীর সিংহভাগ ছিলেন—এবং ধর্ষণকে ব্যবহার করা হয়েছিল বাঙালিদের আতঙ্কিত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার অস্ত্র হিসেবে। হত্যাযজ্ঞ ও যৌন সহিংসতার এসব অভিযোগ—এবং সেগুলো আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গণহত্যার পর্যায়ে পড়ে কি না—এ নিয়ে বিতর্ক সবচেয়ে সংবেদনশীল। স্বাধীন পর্যবেক্ষকরা বাংলাদেশের সরকারি দাবি—তিরিশ লাখ নিহত এবং দুই লাখ নারী যৌন সহিংসতার শিকার—প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তবুও, বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটি বিশাল মাত্রার হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন সংঘটিত হয়েছিল—এটি জীবনের অবিচ্ছেদ্য সত্য। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, আবার অনেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, শারীরিক ও মানসিক আঘাত পেয়েছেন, বা রোগ, অনাহার ও দারিদ্র্যের শিকার হয়েছেন—যা সরাসরি সামরিক অভিযানের ফল। এমনকি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই ব্যাখ্যাও যদি মেনে নেওয়া যায়,যে তারা জাতিগত পরিচয়ের বদলে শুধুমাত্র যুদ্ধ-সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল,তবুও অস্বীকার করার উপায় নেই যে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অসামঞ্জস্যভাবে বেশি ছিলেন হিন্দুরা, যাদের কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই চিহ্নিত করা হয়েছিল, এবং যে সেনাবাহিনী প্রকৃতপক্ষে ধর্ষণকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এই বাস্তবতাই পুরো অভিযানের চরিত্রকে জেনোসাইডাল করে তোলে। একই সাথে, এটিও জরুরি যে বাংলাদেশের রাষ্ট্র কর্তৃক ঐতিহাসিক গবেষণায় এক ধরনের গোঁড়ামি চাপিয়ে দেওয়ার এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, বিশেষত যখন বিরোধী দলকে লক্ষ্যবস্তু করতে বা বছরব্যাপী সহিংসতার সময় অবাঙালিদের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে স্মৃতিভ্রষ্টতা তৈরির জন্য ইতিহাসকে ব্যবহার করা হয়, তখন তার সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের ‘যুদ্ধাহত বীরঙ্গনা’ হিসেবে স্বীকৃতি এক ভিন্ন ধরনের বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। বিনা ডি’কস্টা যৌন সহিংসতা, জোরপূর্বক গর্ভপাত এবং যুদ্ধকালীন জন্ম নেওয়া শিশুদের দত্তক দেওয়ার আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার ঘটনা বিস্তৃতভাবে নথিভুক্ত করেছেন।[75] ইয়াসমিন সাইকিয়া ও নয়নিকা মুখার্জি সেগুলোকে শুধুমাত্র ত্যাগ ও সাহসের জাতীয়তাবাদী বয়ানের ভেতরে আটকে না রেখে এসব নারীর কাহিনী সংগ্রহ করেছেন।[76] তাঁদের কাছে এটি কোনো গবেষণাগত সীমাবদ্ধতা নয় যে উপকরণ নেই; বরং এটি ছিল এক সচেতন বর্ণনাকৌশল—যেখানে আঘাতের ভাষা প্রকাশ পায় নীরবতা ও অসংলগ্নতায়। সংখ্যা, আর্কাইভ, রাষ্ট্রীয় পুনর্বাসন কর্মসূচি, জোরপূর্বক গর্ভপাত ও দত্তকের নথিভুক্ত প্রমাণ—সবকিছু থাকার পরও, এই নীরবতা আসে ইতিহাসলেখার শাস্ত্রীয় সীমাবদ্ধতা থেকে। এটি ঐতিহাসিক বর্ণনার শৃঙ্খলাগত সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা বেঞ্জামিনের মতে, ভুক্তভোগীদের তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলার ভাষা থেকে বঞ্চিত করে। হলোকাস্টভিত্তিক মহাকাব্যিক প্রামাণ্যচিত্র Shoah-এ শোশানা ফেলমান দেখিয়েছেন, অস্বীকার ও বাকরুদ্ধতা একই সঙ্গে মজলুমিয়াতের শর্ত ও কারণ। তাঁর মতে, নীরব হয়ে যাওয়া কোনো স্থায়ী অবস্থা নয়, বরং একটি ঘটনার মতো। ভাষাহীন হলে ভুক্তভোগী কেবল নির্যাতকের ভাষায় কথা বলতে বাধ্য হন, যেখানে ‘নির্যাতিত যদি নিজেকে নির্যাতিত বলে, তবে তা তার নিজের কাছেও উন্মাদ শোনাবে’।[77] এই সাক্ষ্য যখন আইনি কাঠামোয় অনূদিত হয়, তা প্রায়ই হয়ে ওঠে অবাস্তব, বিকৃত, অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য। স্লাভয় জিজেক মনে করিয়ে দেন—অসংলগ্ন শব্দ, চিন্তার খণ্ডাংশ, এমনকি নিঃশব্দতাও ভুক্তভোগীর সত্যতার স্বপক্ষে প্রমাণ।[78] তাঁরা বাকরুদ্ধ হয়েছেন—এমন এক প্রতিক্রিয়া দেওয়ার অক্ষমতায়—যা আইনভাষার শৃঙ্খলিত কাঠামোর সাথে খাপ খায়। ফলে আঘাতপ্রাপ্তের মানসিক ভেঙে পড়া, অসংলগ্নতা ও নীরবতা আইনের সংকীর্ণ ন্যায়বিচার ধারণা ও ইতিহাসরচনার বুদ্ধিবৃত্তিক গরিবিয়ানার বিরুদ্ধে এক নীরব অভিযোগ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই ফেলম্যানের মতে, বেঞ্জামিন ‘ট্রমা হিসেবে ইতিহাসের একটি তত্ত্ব—এবং ট্রমাকে অন্তর্দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করার একটি সম্পর্কযুক্ত তত্ত্ব’ প্রস্তাব করেন, যেখানে ইতিহাস একটি ‘যৌক্তিক কার্যকারণ শৃঙ্খলের পরিবর্তে ট্রমাজনিত হস্তক্ষেপের একটি শৃঙ্খল’ হয়ে ওঠে।[79] এখানে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা—অর্থাৎ ইতিহাসের কর্তা—বাকহীন থেকে যায়, কারণ তাদের মজলুমিয়াত সম্পর্কে কথা বলার জন্য যে ভাষার প্রয়োজন, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ফেলম্যান বলেন, বাকহীনতা এমন কিছু যা রেকর্ডের বাইরে থেকে যায়, এবং ইতিহাস ও আঘাতের মধ্যেকার এই সুনির্দিষ্ট সংযোগটিই বেঞ্জামিনের ইতিহাস সম্পর্কিত ক্রিটিকের মূল বিষয়। ফলে যা আইনি কাঠামোয় বলা যায় না, আর্কাইভে সংরক্ষিত তথ্য দিয়ে কিংবা কেবল সংখ্যা গুণে ‘গণহত্যা’ প্রমাণ করা যায় না, প্রকাশ করা যায় কেবল কবিতা, শিল্প ও সাহিত্যের ভেতরে।
নথিভিত্তিক প্রমাণ সংগ্রহের যে প্রামাণ্যচিত্রধর্মী বা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি—যা যুদ্ধযন্ত্রকে শত্রু ধ্বংসের ক্ষেত্রে দক্ষতা এনে দেয়—তার সুবিধা আছে বটে। কিন্তু ফেলমানের মতে, শেষ পর্যন্ত আইখম্যান বিচার চলাকালে ভুক্তভোগীদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যই এমন এক ভাষার জন্ম দিয়েছিল, যা ইহুদি ভুক্তভোগীদের মানবিক মর্যাদা ফিরিয়ে এনে ইতিহাসকে ‘অভিজ্ঞতা হিসেবে’ পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল।[80] কিন্তু শর্মিলা বোসের মতো সংশোধনবাদীদের কাছে আর্কাইভের বর্ণনার অসংলগ্নতা ও জ্ঞানের ঘাটতি হয়ে দাঁড়ায় তার সীমাবদ্ধতার প্রমাণ, যা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ফরেনসিক নির্ভুলতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ। এই অবস্থান তাঁকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যেখানে অভিযোগকারী প্রত্যক্ষদর্শীর বিশ্বাসযোগ্যতা পর্যন্ত তিনি প্রত্যাখ্যান করে বসেন। বোস যখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণধর্ষণের মতো অপরাধ ঘটাতে পারে না, তখন তাঁর যুক্তির ভিত ছিল সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা,যা এমন ‘লজ্জাজনক কাজ’কে অনুমতি দেবে না। অথচ বাস্তবে, সেনা কর্মকর্তারাই জানিয়েছেন যে দৈনন্দিন যুদ্ধের বিশেষ প্রকৃতির কারণে শৃঙ্খলা ভয়াবহভাবে ভেঙে পড়েছিল। ইয়াসমিন সাইকিয়া সংগ্রহ করেছেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নন-কমিশন্ড সৈন্যদের সাক্ষ্য, যারা জানতেন যে বহু বাঙালি নারী যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে এক সৈন্যের বিবরণ:
“আমি কোনো নারীকে মারিনি বা আঘাত করিনি। কিন্তু কাউকে বাঁচানোর চেষ্টাও করিনি। আমার সহযোদ্ধারা অনেক নারীকে ধর্ষণ করেছে। কেউ কেউ তাদের ক্যাম্পে এনে বিয়ে করে থেকেছে। কেউ আটকায়নি। আপনি যখন জিজ্ঞাসা করেছেন, সত্যিটা বলি—আমার জ্যেষ্ঠ অফিসাররাও নারীদের ধর্ষণ করেছেন। কখনো আমাকে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হয়েছে। আমি জানতাম কেন তারা ভেতরে গেছে—তারা ধর্ষণ করতেই গেছে। কিন্তু আমি থামাতে পারিনি। আমি ছিলাম সিপাহী; অফিসারের আদেশ অমান্য করার অধিকার আমার ছিল না। আমার দায়িত্ব ছিল পাহারা দেওয়া—এবং সেটাই করেছি।”[81]
লিখিত ও নথিভুক্ত প্রমাণ অস্বীকার করা কেবল পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত গণহত্যার প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন—আউশভিৎসের প্রতিটি গ্যাস চেম্বারের বিবরণের বিপরীতে পাওয়া যায় একেকটি লিউখটার রিপোর্ট; পরিকল্পিত হলোকাস্টের প্রতিটি দাবির বিপরীতে থাকে একেকজন ডেভিড আরভিং। তাই এমনকি ‘নিরপেক্ষ’ ভান করা, সত্য বলার দাবি করা উৎস থেকেও লেখা পাওয়া ইতিহাসচর্চার স্বাভাবিক অংশ—এবং ইতিহাসবিদদের জন্য ক্রমাগত লড়াইয়ের ক্ষেত্র—যেখানে এই ধরণের অস্বীকৃতিকে ভেঙে ফেলা জরুরি। অতএব, এমন একক, নির্ভুল ঐতিহাসিক বয়ান চাওয়া, যা বিপরীত প্রমাণকে পুরোপুরি বাদ দেবে—এটি বাস্তবে এক ধরনের অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যাগুলোর—বিশেষ করে ‘চূড়ান্ত সমাধান’ (Final Solution)-এর মতো একটি বিপর্যয়কর ঘটনার—স্বাতন্ত্র্য কেবল এর পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত নয়, বরং দেরিদার ভাষায়, এটি ‘যা কিছুকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে ও ধ্বংস করতে চেয়েছিল, যা একই সঙ্গে ভেতর ও বাইরে থেকে একে তাড়া করে ফিরছিল’, তার মধ্যেও এর স্বাতন্ত্র্য নিহিত। রাষ্ট্রীয় ‘মিথিক সহিংসতা’ কেবল লক্ষ লক্ষ জীবনকেই নির্মূল করে না, বরং ন্যায়বিচার ও নামের দাবিকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং ‘নাম দেওয়া, খোদাই করা, ডাকা ও স্মরণ করার সমস্ত সম্ভাবনা’ নষ্ট করে দেয়। কিন্তু, একই সাথে, ডেরিডা বলেন, এটি ‘তার ধ্বংসের সংরক্ষণাগারকে অক্ষত রাখে, ভয়াবহ আইনি, আমলাতান্ত্রিক, রাষ্ট্রীয় বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য নকল যুক্তি তৈরি করে,’ যা সাক্ষ্যকে মুছে ফেলতে সাহায্য করে এবং এর ফলে অস্বীকার বা যৌক্তিকতা প্রদানের মাধ্যমে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়।[82]
এই কারণেই কেবল মৃতদেহ গোনা দিয়ে সত্য প্রমাণের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়—প্রমাণের অভাবে নয় (উপরের আলোচনায় তা দেখানো হয়েছে)—বরঞ্চ কারণ এটি প্রায়ই আলোচনা থেকে মানবিকতা সরিয়ে ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতার প্রতি আন্তরিকতা ব্যতিরেক কেবল পরিসংখ্যানের খেলায় নামিয়ে আনে। তাই সঠিক প্রশ্ন হওয়া উচিত সংখ্যার দিকে নয়, বরং—আর্কাইভ ও প্রমাণের প্রকৃতি আসলে কোন সত্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে, সেই ধারণাটিকে প্রশ্ন করা, এবং ভুক্তভোগীদের গল্প ও অভিজ্ঞতা লেখার জন্য এক নতুন সমালোচনামূলক ভাষা ও ঘনিষ্ঠ বর্ণনাভঙ্গি গড়ে তোলা।
এই পাঠ শুধু বাঙালিদের নয়, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে সংঘটিত বিহারিদের হত্যাযজ্ঞের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রণোদিত বয়ানের মূল কৌশল ছিল—বিহারি ভুক্তভোগীকে বাঙালি সহিংসতার পাল্টা প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো। উদ্দেশ্য ছিল না নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ ও গণধর্ষণের শিকার হওয়া বিহারিদের দুঃখ-যন্ত্রণার ভাষা দেওয়া , বরঞ্চ লাশের সংখ্যা পাশাপাশি সাজিয়ে তুলনামূলক হিসাব দাঁড় করানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। বাস্তবে, পাকিস্তান বিহারিদের দুর্দশা লাঘবে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি; বরং দায় এড়িয়ে বাংলাদেশকে তাদের দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে দেয়। ‘সংরক্ষণের’ নামে বাংলাদেশ সরকার তাদের শরণার্থী শিবিরে নিক্ষেপ করে, যেখানে তারা বছরের পর বছর মানবেতর অবস্থায় বন্দি থেকেছেন।[83] ফলে, যাদের নামে পাকিস্তানি সেনারা নৃশংস অভিযান চালিয়েছিল, সেই বিহারিরাই প্রকৃত বিপদের সময় পাকিস্তানের আর কোনো আগ্রহ বা সহানুভূতি পায়নি। বাংলাদেশ তাদের ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকলেও, পাকিস্তানই শেষ পর্যন্ত তাদের গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল।
যেসব বিহারি নিরাপদে পাকিস্তানে পৌঁছেছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার কোনো গুরুতর চেষ্টা আজতক হয়নি। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের অভিজ্ঞতা, কিংবা আল-বদর ও আল-শামসের স্বেচ্ছাসেবকদের জীবন নিয়েও খুব সামান্য একাডেমিক কাজ হয়েছে। ব্যতিক্রম বলতে আছে কেবল সালিম মনসুর খালিদের প্রশংসাপূর্ণ রাজাকার বর্ণনা।[84] এর বাইরে, বিহারি ও রাজাকারদের ‘বাংগালি প্রতিশোধমূলক হত্যাযজ্ঞের’ শিকার হিসেবে উপস্থাপন প্রায়ই শুধুমাত্র বাঙালি সহিংসতার পাল্টা দাবি হিসেবে ব্যবহৃত একটি পরিসংখ্যান বৈবেশি কিছু নয়। আমরা খুব কম জানি যুদ্ধের সময় বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলিকে পুনর্মিলিত করার জন্য পরিচালিত বৃহৎ কর্মকাণ্ড, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে বাঙালিদের প্রত্যাবাসন, কিংবা বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে অ-বাঙালিদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ার কথা। আরও কম বলা হয় সেই সত্যটি—যে হাজার হাজার বাঙালিকে অস্থায়ী শিবির ও কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছিল—যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানি সৈন্যদের ভারত ও বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর জন্য দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে। এই ঘটনা কার্যত আমাদের সামষ্টিক স্মৃতি থেকে মুছে গেছে।
মাত্র তিন বছর বয়সে নাইম মোহাইমেনও এমন এক শিবিরে তাঁর পরিবারের সঙ্গে পাকিস্তানে সময় কাটিয়েছিলেন। বহু বছর পর, সেই ইতিহাস অনুসন্ধানে ফিরে গিয়ে তাঁর গবেষণা বহু বিহারির কাছে জমে থাকা স্মৃতির দরজা খুলে দেয়। তাঁদের ছিল বেদনার্ত কাহিনি—এবং তাঁরা স্বস্তি পান এই ভেবে যে অবশেষে কেউ এসেছে শুনতে; এমন কেউ, যাকে তাঁরা ভাবতেন সেই দেশের মানুষ, যে তাঁদের পরিবারের ওপর সহিংসতা চালিয়েছিল।[85] এই অভিজ্ঞতা দেখায় কেন বিহারি ও বাঙালি ভুক্তভোগীদের মধ্যে মিথ্যা সমান্তরাল টানা—‘দুই পক্ষই সমান’ ধরনের বয়ান তৈরি করা—অন্যায়। মোহাইমেনের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, বিহারি ও বাঙালি একে অপরের সঙ্গে বিরোধে নয়, বরং ট্রমার অভিজ্ঞতায় যুক্ত। ভিটগেনস্টাইনের কথায়, ‘এটি ভাবা সম্ভব যে একজন ব্যক্তির ব্যথা অন্য একজন ব্যক্তির শরীরে হতে পারে।’ অন্য ব্যক্তির শরীরে নিজের ব্যথা অনুভব করার প্রক্রিয়াটি তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেন: ‘…আমি চোখ বন্ধ করে আমার বাম হাতে একটি ব্যথা অনুভব করছি। কেউ আমাকে তার ডান হাত দিয়ে ব্যথার জায়গাটি স্পর্শ করতে বলে। আমি তা করি এবং চারদিকে তাকিয়ে দেখি যে আমি আমার প্রতিবেশীর হাত স্পর্শ করছি…। এটি হবে অন্যের শরীরে ব্যথা অনুভব করা।’[86]
বীনা দাস এটাকে ব্যাখ্যা করেনে এভাবে, ‘অংশীদারিত্বমূলক বেদনা উপস্থাপন কেবল কল্পনায় সম্ভব’। এখানে বিহারির বেদনা যেন বাঙালির দেহে বাস করছে, এবং তা ছুঁয়ে অনুভব করা সম্ভব—উল্টোটাও সত্য। কিন্তু দাস মনে করিয়ে দেন, এই যৌথ বেদনার অনুধাবনকে বাস্তবে কার্যকর কোনো রূপে রূপান্তর করা যায় না।[87] ফলে বেদনা হয়ে ওঠে এক অভিন্ন অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার বাসনায়, যার ভাষিক বহিঃপ্রকাশ দক্ষিণ এশিয়ার অসংখ্য ভাষাতে দেখা যায়; যেমন, দুঃখ ভাগ করে নেওয়া। আর আর এই কারণেই, মানবীয় ট্র্যাজেডিতে, ভিলাশিনি কুপান যেমন বলেন, ‘তাদের বংশগতির (lineages) চেয়ে তাদের সম্পর্কগুলোই(linkages) বেশি গুরুত্বপূর্ণ’।[88] তার মতে, মূল বিষয়টি অতীতের প্রতি ন্যায়বিচার করা নয়, বরং বর্তমান সময়ে ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। এটি তার কাছে সহাবস্থানের একটি রূপ হিসেবে সংহতি নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য একটি পূর্বশর্ত।
ক্ষমা প্রার্থনার প্রশ্ন
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হামলা চালায়, তখন ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা ছিলেন কিশোরী। তাঁর বাবা—জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক—নিজ বাড়ির সামনে নিহত হন। সেনারা তাঁকে নিশানা করেছিল, কারণ তিনি ছিলেন এক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী। ২০১৬ সালের নভেম্বরে নয়নিকা মুখার্জিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ড. গুহঠাকুরতা বলেন—“যেদিন পাকিস্তান লাহোর বা ইসলামাবাদের কোথাও একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করবে, যেখানে তারা স্বীকার করবে যে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনারা বাংলাদেশিদের হত্যা ও ধর্ষণ করেছিল—সেদিন আমি পাকিস্তানকে ক্ষমা করার কথা ভাবতে পারব।”[89]
১৯৭১ সালের যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ পাকিস্তানের সামরিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে নির্মাণের দাবি জানিয়ে ড. গুহঠাকুরতা অতীতের স্বীকৃতির মাধ্যমে এক নতুন রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার প্রয়াস করেছেন। তাঁর কাছে, এই চাওয়া নিছক মুছে যাওয়া স্মৃতিকে বস্তুতে রূপ দেওয়ার প্রয়াস নয়, কিংবা স্মৃতি ধরে রাখার জন্য কোনো বস্তুগত চিহ্ন আঁকড়ে ধরা নয়; বরং আক্রমণকারীর ভেতরে অবশিষ্ট থাকা যে কোনো মানবিক বোধকে জাগিয়ে তুলতে, এবং স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের সঙ্গে বসবাসের পথ তৈরি করতে আহ্বান।
তবে তিনি জানেন, এই কাজের ব্যাপ্তি বিরাট; এমন এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ মানে অতীতের নৃশংসতাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করা। এ কারণেই, তাঁর মতে, ঘটনার স্বীকৃতি হলো ক্ষমা প্রার্থনার পূর্বশর্ত—যার অর্থ পাকিস্তান সরকারকে, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীকে, সরাসরি জিজ্ঞাসা করা যে তারা কোন ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইছে। এই প্রশ্ন বদলে দেবে ক্ষমা প্রার্থনার প্রকৃতিকে; এটি আর আগের পাকিস্তানি শাসকদের দেওয়া স্রেফ অনুশোচনার প্রকাশ থাকবে না। আন্তর্জাতিক চাপের অনুপস্থিতি, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা বা বসনিয়ার মতো পাকিস্তানকে আর সহিংসতার শিকার জনগণের সঙ্গে বসবাস করতে না হওয়া—এসবই দায় স্বীকার, পুনর্মিলনের সম্ভাবনা বিবেচনা, কিংবা ভুক্তভোগীদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গড়ে না উঠা নিশ্চিত করেছে।
অতীতের অপরাধের স্বীকৃতি ও ক্ষমা প্রার্থনার পথে এগোতে হলে প্রথমেই অপরাধীদের চিহ্নিত করা জরুরি—অন্তত একটি প্রতীকী বিচার আয়োজন করা এবং ক্ষমা চাওয়া। যেহেতু অপরাধীদের অধিকাংশই ইতিমধ্যেই মৃত অথবা এতটাই প্রবীণ যে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হবে retributive বা শাস্তিমূলক বিচার ও যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণের নৈতিক ভিত্তি তৈরি করা। এ বিষয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী জার্মান অপরাধবোধ (German guilt) নিয়ে হওয়া বিতর্ক আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়।
জার্মানদের অপরাধবোধ নিয়ে হানা আরেন্ট ও কার্ল জ্যাসপার্সের বিতর্ক থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হলো, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া গণহত্যার জন্য পুরো পাকিস্তানি জনগোষ্ঠীকে দোষী সাব্যস্ত করা এই বিতর্কের উদ্দেশ্য নয়। এমন পদক্ষেপ ফলপ্রসূ নয়, আরেন্ট যাকে বলবেন ‘অপরিপক্ক (naive)’, কারণ “যেখানে সবাই দোষী, সেখানে কেউই দোষী নয়।”[90] যুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানিতে আরেন্ট লক্ষ্য করেছিলেন, ‘যারা ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তারা নিজেদের এবং সমগ্র বিশ্বকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে তারা কতটা অপরাধী অনুভব করছে, অথচ খুব কম সংখ্যক অপরাধীই সামান্যতম অনুশোচনা প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিল। এই ধরনের সম্মিলিত অপরাধবোধের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতির ফলে যারা সত্যিকার অর্থেই অপরাধ করেছিল, তাদের একটি কার্যকর, যদিও অনিচ্ছাকৃত, দায়মুক্তি ঘটেছিল।’[91] তাই ক্ষমা প্রার্থনা পাকিস্তানের কোনো নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে নয়, বরঞ্চ আসতে হবে সরাসরি সেনাবাহিনী থেকে, কারণ এই সহিংসতার জন্য একমাত্র তারাই দায়ী।
ইয়াস্পার্স ব্যক্তির দায় [responsibility] ও সামষ্টিক অপরাধবোধ [guilt] মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দায়ের চারটি ধরন চিহ্নিত করেন।[92] প্রথমটি ফৌজদারি অপরাধবোধ, যা আদালতে প্রমাণ-ভিত্তিক বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধে ব্যক্তির ভূমিকা ও অবদান অনুযায়ী নির্ধারিত হতে পারে। অপারেশন সার্চলাইট-এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জড়িত অধিকাংশ ব্যক্তি এখন মৃত। মুজিব একসময় অন্তত ১৯৪ জন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাকে বিচারের মুখোমুখি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ‘বড় শক্তি’ এবং ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (OIC) বাংলাদেশের মানবিক সহায়তাকে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির শর্তের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষে জর্জরিত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের কাছে এই দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে পাকিস্তানের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও হামুদুর রহমান কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও যুদ্ধাপরাধী অফিসার ও জওয়ানদের কোনো বড় ধরনের কোর্ট-মার্শাল হয়নি। হয়তো অল্প কিছুজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার বিস্তারিত কখনো প্রকাশিত হয়নি।
দ্বিতীয় ধরনটি রাজনৈতিক অপরাধবোধ, যা সব নাগরিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ তারা বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুবিধাভোগী এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সেই ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষমতায় আনে। ইয়াস্পার্সের মতে, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অরাজনৈতিক বা উদাসীন থাকার কোনো সম্ভাবনা প্রায় নেই।[93] তাই, রাজনৈতিক অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের জন্য কিছু দায়বদ্ধতা থাকে। এখানে মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান একটি সর্বগ্রাসী (totalitarian) রাষ্ট্র ছিল না; এটি ছিল একটি কর্তৃত্ববাদী (authoritarian) রাষ্ট্র। সামরিক আইন সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করলেও ১৯৭০ সালে প্রথমবার প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক সারাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানের বহু অঞ্চলে বামপন্থি দল সক্রিয় ছিল এবং উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেত। কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চে রাজনৈতিক অচলাবস্থার পর মূলধারার দলগুলো—বিশেষত জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপিপি—সেনাবাহিনীর সঙ্গে একযোগে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানকে সমর্থন করে। ফলে, পাকিস্তান একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র হওয়ায় এর নাগরিকদের কর্মকাণ্ডের জন্য সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের চেয়ে বেশি দায়ী বলে মনে করা যায়। কারণ একটি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের বাসিন্দারা অজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত পদক্ষেপ নেওয়ার মতো শক্তির অভাবের অজুহাত দেখাতে পারে বা সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য থেকে বিরত থাকতে পারে।
তৃতীয় ধরনের দায় হলো নৈতিক অপরাধবোধ, যেখানে কোনো আদেশ পালনকারীকে তার কাজের পরিণতি নিয়ে আত্ম-পর্যালোচনা করতে হয়। নুরেমবার্গ বিচার প্রচলিত এই ধারণাটিকে বাতিল করে দেয় যে, ‘আদেশ মানেই আদেশ’ অথবা ‘বৈধ কর্তৃপক্ষের দেওয়া আদেশ’ পালন করা আবশ্যক। ইয়াস্পার্স মনে করিয়ে দেন যে, এটি কোনো বিজয়ীর বিচার ছিল না, বরং নাৎসি শাসনের জঘন্য নৃশংসতা এই ধরনের জবাবদিহিতা বাধ্যতামূলক করেছিল। যদিও কোনো গণহত্যায় অংশগ্রহণের পেছনে ভয়-ভীতি বা জীবনের হুমকির মতো কিছু পরিস্থিতি থাকতে পারে, তবুও আরেন্ট আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, নৈতিক দর্শনে সক্রেটিসের ঐতিহ্য হলো নিজের সাথে শান্তিতে থাকা, অপরাধ করা নয়।[94] পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে, আমার জানা মতে কেবল কর্নেল নাদির আলী অসাধারণ নৈতিক অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি এই ‘নৃশংস যুদ্ধযন্ত্র’ আর চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান। তার নৈতিক বিবেকের ভারে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগে বহু বছর তাকে মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে হয়েছিল। পরে তিনি পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যের মাঝে শান্তি খুঁজে পান। যুদ্ধের বর্ণনায় যখন ‘পাঞ্জাবি সেনাবাহিনী’ কে সহিংসতা, ধর্ষণ এবং ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী করা হচ্ছিল, তখন নাদির আলীর কাছে পাঞ্জাবিয়াতের মানবিক ধারণাকে আলিঙ্গন করা ছিল একজন পাঞ্জাবি হিসেবে নিজের পরিচয়কে পুনরায় নিশ্চিত করার একটি উপায়, যার মধ্যে তিনি শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল, পাঞ্জাবিদের যুদ্ধাপরাধীতে পরিণত হওয়ার কারণ হলো পাঞ্জাবিয়াতের মানবিক মূল্যবোধকে ত্যাগ করা।
ইয়াস্পার্সের সংজ্ঞায় সর্বশেষ প্রকারটি হলো মেটাফিজিক্যাল গিল্ট, এটি মানুষের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে জন্ম নেয়, যার ফলে একজন মানুষ তার জ্ঞান বা অংশগ্রহণ ছাড়াই পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া যেকোনো অন্যায় বা অবিচারের জন্য নিজেকে সহ-দায়িত্বশীল মনে করে এবং তা প্রতিরোধ করতে না পারার জন্য অনুশোচনা করে। ইয়াস্পার্স লিখেছিলেন,‘এমন কিছু ঘটার পরও আমি যে বেঁচে আছি, তা আমার উপর এক অবিচ্ছেদ্য অপরাধবোধের বোঝা চাপিয়ে দেয়।’[95] তাঁর ভাষা ছিল ধর্মীয়,যেখানে তিনি জার্মানদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কামনা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন আত্ম-বিশ্লেষণ এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে মুক্তির পথে পৌঁছায়। তবে বহু সমালোচকের মতে, ইয়াস্পার্সের এই দৃষ্টিভঙ্গি গুরুতর রাজনৈতিক পদক্ষেপকে বিলম্বিত করেছিল। আরেন্টের কাছে, সামষ্টিকতার ওপর এমন জোর ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের নির্দিষ্ট দায়কে হ্রাস করে। তাছাড়া, ইয়াস্পার্সের প্রস্তাবিত আত্ম-পর্যালোচনা-মূলক প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতিটি রাজনীতির বাইরে চলে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে, কারণ এতে অপরাধী ব্যক্তিরা ‘তাদের নিজেদের একক অভিজ্ঞতার বিষয়ভিত্তিক জগতে বন্দী হয়ে থাকে।’[96] পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়,যদি অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারা দায় স্বীকার করেনও, তা প্রায়শই প্রকাশিত হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, তাবলিগ জামাতে যোগ দেওয়া, বা দাতব্য কাজে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। এই কারণেই আরেন্ট মনে করতেন, অপরাধবোধ অনেক সময় মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ করে রাখে এবং জনপরিসরে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়। যেমন করে অ্যান্ড্রু শাপ ব্যাখ্যা করেছেন, আরেন্ট জোর দিয়ে বলেছিলেন যে নৈতিক বিবেচনা অত্যন্ত জরুরি, কারণ তা নির্ধারণ করে একজন ব্যক্তি কেমন হতে চায়। কিন্তু রাজনৈতিক পরিসরে আমাদের আমাদের পার্থিব কর্মের প্রকৃতি আমরা যে পৃথিবী তৈরি করি তার উপর এবং বৃহত্তর জনগণের প্রতি আমাদের অবদানের উপর প্রভাব ফেলে। তাই, একজন মানুষ হিসেবে অপরাধবোধ উপলব্ধি করা এবং একজন নাগরিক হিসেবে কাজের জন্য জবাবদিহি করার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।
এই পার্থক্যের ভিত্তিতে আরেন্ট জোর দিয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই ডিসকোর্সের মূল শব্দ ‘দায় [রেসপন্সিবিলিটি]’, আনুগত্য [অভিডিয়েন্স] নয়। আনুগত্য ধর্মীয় বিষয়ে প্রযোজ্য, কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নয়। তাই, আইনি আলাপে আনুগত্য থেকে দায়/দায়িত্বের দিকে সরে আসাটা কেবল নিছক শব্দের খেলা নয়, বরঞ্চ এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে। আরেন্ট বলেন, যখন নাৎসি শাসনের পতন ঘটে, তখন শুধুমাত্র কিছু কঠোর ও অনুতপ্ত-হীন অনুসারী অবশিষ্ট ছিল। বাকিরা নাৎসি মতাদর্শে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তাদের আদর্শবাদিতার অনুভূতির দ্বারা প্রতারিত বোধ করেছিল। অন্যদের জন্য এটি ছিল ‘কম শয়তান’ বেছে নেওয়ার একটি বিষয়, যাতে শাসন ব্যবস্থা তার গণহত্যার এজেন্ডা পুরোপুরি বাস্তবায়ন না করে। আরেন্ট যেমন বিখ্যাতভাবে বলেছিলেন, যারা কম শয়তান বেছে নিয়েছিলেন, তারাও খুব তাড়াতাড়ি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তারা তবুও শয়তানই বেছে নিয়েছিলেন। আরেন্টের মতে, নাজিবাদের ক্ষেত্রে ‘কম শয়তান’ বেছে নেওয়ার দাবি হাস্যকর। ‘ভেতর থেকে পরিবর্তনের জন্য কাজ করা’ যুক্তিটি কেবল তখনই অর্থবহ হতে পারত, যদি তা শাসন পরিবর্তনে দিকে ধাবিত হতো। নাজি সরকারের জন্য কাজ করা বহু মানুষই নাজিবাদের মূল বিশ্বাসে আস্থা রাখত না। আইখম্যান নিজেও ইহুদিদের নির্যাতন করার ধারণায় বিরক্ত হতেন, কিন্তু তাদের মৃত্যুতে নয়। কার্যত আইখমান, অন্যান্যদের মতো ‘যন্ত্রের একটি অংশ’ (cog in the machine) যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন। আধুনিক আমলাতন্ত্র এমনভাবে চলে, যাতে একটি অংশ বদলালেও যন্ত্র সচল থাকে। এখানেই বিচারবোরহিত অবস্থা মানুষের কাজে এমন এক চিন্তাহীনতা নিয়ে আসে, যাকে আরেন্ট বিখ্যাতভাবে বলেছিলেন banality of evil বা অশুভের সাধারণত্ব। । তবে, আইখমানের বিচার নাটকের সমালোচনা করার সময় আরেন্ট আইনের দুর্বলতা দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যা এই যান্ত্রিক চিন্তাহীনতাকে এমন মানবিক কর্মকান্ডে অনুবাদ করতে ব্যর্থ হয়, যা বিচার ও দায়িত্বের আওতায় আনা সম্ভব।
আরেন্টের যুক্তির একটি সীমাবদ্ধতা হলো, তিনি নৈতিক অনুভূতির শক্তিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি। এই শক্তি রাজনীতিতে অপরাধবোধের বোঝা সরিয়ে ফেলে জনসাধারণের আলোচনায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই, জনসম্মুখে লজ্জা, অনুশোচনা এবং নিজেদের দোষ স্বীকারের মাধ্যমে প্রতিশোধমূলক ন্যায়বিচারের বিভিন্ন রূপকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এ কারণেই শাপ (Shaap) একটি নতুন ধারণা দিয়েছেন, যাকে তিনি depersonalized conflictual politics বা ‘অব্যক্তিক সংঘাতের রাজনীতি’ বলে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত না করেও অতীতের ভুলের জন্য রাজনৈতিক দায়ভার গ্রহণ করতে পারে। শাপের মতে, এই প্রক্রিয়া হয়তো পুনর্মিলনের পথে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটাতে পারে, তবে এটি নতুন ও সৃজনশীল ফলাফলের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধাপরাধ স্বীকারের প্রত্যাশিত ফল হতে পারে গণতন্ত্র ও ফেডারেল কাঠামোর শক্তিশালী হওয়া। এটি অর্জনের জন্য, ১৯৭১ সালের বিতর্ককে অবশ্যই ‘আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য বৈধ সহিংসতা’র যুক্তি থেকে ‘মুক্তিযুদ্ধকে নির্মমভাবে দমন করা’র সত্যের দিকে সরাতে হবে। একই সাথে, ‘আদেশ পালন’ থেকে সরে এসে কৃতকর্মের জন্য ‘দায়িত্বশীলতা’র দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এই ধরনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি সেইসব উগ্র দেশপ্রেমমূলক বক্তব্যকে বাতিল করে দেবে, যা অতি-বিকশিত সামরিক প্রতিষ্ঠানকে ভয়ের শাসনের মাধ্যমে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করতে সাহায্য করে।
নচেত পাকিস্তানি রাষ্ট্র একই যুক্তি, কৌশল ও প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে—‘সার্বভৌম জাতি’র নামে, শৃঙ্খলা রক্ষার নামে, ভৌগোলিক অখণ্ডতা নিশ্চিত করার নামে। পদ্ধতিগত সাদৃশ্যের একটি উদাহরণ হলো—পশ্চিম পাকিস্তান ও তার সেনাবাহিনীর প্রতি তীব্র ঘৃণার মাঝেও, ১৯৭১ সালে সামরিক আইন প্রশাসন ঢাকায় ‘স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেছে’ ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানপন্থী সমাবেশ করেছিল। আমরা একই ধরনের চর্চা দেখি সাবেক ফেডারেলি অ্যাডমিনিস্টার্ড ট্রাইবাল এরিয়াস (FATA) ও বেলুচিস্তানের মতো বিদ্রোহপ্রবণ অঞ্চলে—যেখানে কর্পস কমান্ডাররা পাকিস্তানি পতাকা হাতে জিপ মিছিল আয়োজন করে বার্তা দেন যে ‘সব ঠিক আছে’। এমন প্রপাগান্ডামূলক কৌশল কেবল শহুরে উচ্চ-মধ্যবিত্ত ডানপন্থী পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সমর্থকদের শান্ত করতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অধিকারবঞ্চিত বেলুচরা বা চল্লিশ বছরের অন্তহীন যুদ্ধে ক্লান্ত পশতুরা পাকিস্তানি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সফল প্রকল্পের ধারণা মেনে নেবে। কেবল দীর্ঘস্থায়ী র্যাডিকাল গণতান্ত্রিক আন্দোলনই এমন সহিংসতার যন্ত্র ভেঙে দিতে পারবে, যা জাতির নামে এ সহিংসতাকে সম্ভব করে তোলে।
উপসংহার
নুরুল কবির ১৯৭১ সালকে ঘিরে পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের বয়ান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জিজেকের diseventalising বা ঘটনা-বিমোচনের ধারণার সহায়তা নিয়েছেন।[97] কবির বলতে চাইছেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সংকীর্ণ, একপেশে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে দেখলে, আসল ঘটনাগুলো এমনভাবে বিকৃত হয় যে, আগের বিপ্লবী দশকগুলোর অবদান যেন ঘটেইনি বলে মনে হয়।’[98] কবিরের মতে, এই ‘diseventalising’ বা ঘটনাকে গুরুত্বহীন করার আখ্যানগুলোর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও পরিণতি রয়েছে। কবিরের মতে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক বয়ান সচেতনভাবে আড়াল করে শ্রমজীবী মানুষের বিপুল অংশ, মার্কসবাদী কর্মী এবং গ্রামীণ কৃষকের সক্রিয় অংশগ্রহণ—যাঁরা কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য নয়, বরং মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্যও সংগ্রাম করেছিলেন। জাতীয় ঐক্য এবং একমুখী জাতীয়তাবাদী ধারণা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এমনভাবে সাজানো হয় যাতে কেবল “শুদ্ধ” ও একরৈখিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগ্রামই স্বীকৃত হয়। কবিরের মতে, এই ধরনের diseventalising এর সুস্পষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে—এর ফলে দেশে ধনী-গরিবের বৈষম্য বেড়েছে এবং গড়ে উঠেছে কর্তৃত্ববাদী একদলীয় শাসনব্যবস্থা।[99]
কবিরের এই তত্ত্ব ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারতের যে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়, তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত আন্দোলনগুলোকে দমন করার ক্ষেত্রে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর নৃশংস ইতিহাস এবং কাশ্মীরে তাদের ঔপনিবেশিক দখলদারিত্বকে আড়াল করে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে, যেমন এই প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, ১৯৭১–এর ঘটনাবলিকে প্রোপাগান্ডা চলচ্চিত্র এবং সংশোধিত ইতিহাসের মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে অন্যায় ও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের কথা অস্বীকার করা যায়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় দমননীতিকে বৈধতা দেওয়া হয়, নাগরিকদের বৈধ অধিকার অস্বীকার করা হয়, এবং একটি দমনমূলক রাষ্ট্র কাঠামো টিকিয়ে রাখা হয়। এই ধরনের বিকৃত ঐতিহাসিক আখ্যানের বিপরীতে, আমি একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের জন্য জিজেকের কাছে ফিরে যাই।
জিজেকের মন্তব্যটি আডর্নোর (Adorno) একটি বিখ্যাত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে। আডর্নো বলেছিলেন, আউশভিৎসের (Auschwitz) মতো মানব বিপর্যয়ের পর আর কোনো কবিতা লেখা সম্ভব নয়। এর জবাবে জিজেক বলেন যে, হলোকাস্টের মতো বিপর্যয়ের পর শুধু কবিতাই লেখা সম্ভব। তিনি যুক্তি দেন, ‘বাস্তববাদী গদ্য যেখানে ব্যর্থ হয়, সেখানে একটি ক্যাম্পের অসহনীয় পরিবেশের কাব্যিক চিত্রায়ণ সফল হয়… কবিতা তার সংজ্ঞানুসারে সবসময় এমন কিছু নিয়ে লেখা হয় যা সরাসরি বলা যায় না, কেবল ইঙ্গিত দেওয়া যায়’।[100] পাকিস্তানে, রাষ্ট্রশক্তির শীতল ও নীরস যুক্তি ১৯৭১-এর বিতর্ককে কেবল একটি ভারতীয় ষড়যন্ত্র এবং ‘আসল’ মৃতের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। কেবল কবিতার মাধ্যমেই পাকিস্তানিরা ১৯৭১ সালের শোক, রক্তপাত, বাস্তুচ্যুতি এবং ট্রমা বোঝার চেষ্টা করেছে। ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের হাম কে ঠেরে আজ়নবি, নাসির কাজমির ও কশ্তিয়াঁ চালানে ওয়ালে কিয়া হোয়ায়, এবং নাসের তুরাবির ও হুমসফর থা—সবই হারানো সম্পর্ক ও আন্তরিকতার শোকগাথা। আমি এই কাব্যিক অন্তরঙ্গতাকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর উচ্চারিত রাষ্ট্রীয় যুক্তির ‘নিকটবর্তীতা’-এর সঙ্গে তুলনা না করে পারি না। প্রায়শই শোনা যায় যে বালুচিস্তান বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার কারণ হলো প্রদেশটি পাকিস্তানের ভৌগোলিকভাবে অবিচ্ছিন্ন অংশ। এর অন্তর্নিহিত যুক্তি হলো, সামরিক বাহিনী বাংলাকে রক্ষা করতে পারেনি কারণ এটি অনেক দূরে ছিল এবং বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য সৈন্য ও গোলাবারুদ সরবরাহের কোনো সরাসরি সংযোগ ছিল না।
তাই, পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের কল্পিত জাতিসত্তার কাব্যিক অন্তরঙ্গতা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র টিকে থাকার নিশ্চয়তা প্রদানকারী ভৌগোলিক নৈকট্যের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সঠিক প্রশ্ন হলো: তারা এই দুটি ঐক্যের পদ্ধতির মধ্যে কোনটি বেছে নিতে চান। একবার পাকিস্তানিরা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে পারলে, উত্তরটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে।
কৃতজ্ঞতা
এই কাজের জন্য গবেষণা সামগ্রী উদারভাবে সরবরাহ করার জন্য আমি মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমানের কাছে সত্যিই ঋণী। তাঁর সহায়তায় আমি এই প্রবন্ধটি লিখতে পেরেছি। শারিকা থিরানাগামা প্রবন্ধটির একটি পূর্ববর্তী খসড়া পড়েছিলেন এবং যুক্তিকে আরও শাণিত করতে বিস্তারিত মতামত দিয়েছিলেন। আমি JRAS-এর দুজন বেনামী পর্যালোচক এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের সাপ্তাহিক আলোচনা সভার অংশগ্রহণকারীদের সমালোচনামূলক মতামতের জন্য কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধটির একটি পূর্ববর্তী, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বিবিসি উর্দুতে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমি জিশান হায়দারের কাছে এবং বিশেষ করে উর্দু খসড়াটি প্রস্তুত করতে তার সাহায্যের জন্য আবিদ হুসাইনের কাছে কৃতজ্ঞ।
তথ্যসূত্র
[1] Khadim Husain Raja, A Stranger in My Own Country: East Pakistan, 1969–1971 (Karachi, 2012), p. 52.
[2] Nurul Kabir, Birth of Bangladesh: The Politics of History and the History of Politics (Dhaka, 2022), pp. 70–71.
[3] Ibid., p. 101.
[4] Ibid., p. 889.
[5] Hasan Hafizur Rahman (ed.), History of Bangladesh War of Independence Documents (Dhaka, 2009); A. S. M. Shamsul Arefin (ed.), Bangladesh Documents 1971 (Dhaka, 2009). [নোকতা : মূল প্রবন্ধে লেখক হাসান হাফিজুর রহমানের নামের স্থলে ভুলবশত গোলাম মোস্তফা লিখেছিলেন।]
[6] Arild Engelsen Ruud, ‘Bangabandhu as the eternal sovereign: on the construction of a civil religion’, Religion (July 2022).
[7] https://www.nytimes.com/2016/04/06/opinion/the-politics-of-bangladeshs-genocide-debate.html (accessed 16 May 2023).
[8] Rizwan Ullah Kokab, Separatism in East Pakistan: A Study of Failed Leadership (Karachi, 2018).
[9] Anam Zakaria, 1971: A People’s History from Bangladesh, Pakistan and India (Delhi, 2019). এই সাহিত্যের একটি সাম্প্রতিক সংযোজন হল তারিক রহমানের লেখা, যেখানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর যুদ্ধগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। দেখুন Tariq Rahman, Pakistan’s Wars: An Alternative History (New Delhi, 2022).
[10] Sarmila Bose, Dead Reckoning: Memories of the 1971 Bangladesh War (Karachi, 2011). আমি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স (GHQ) কর্তৃক তাদের সার্ভিসেস বুক ক্লাবের অংশ হিসেবে বিতরণ করা সংস্করণটি ব্যবহার করছি।
[11] Junaid Ahmad, Creation of Bangladesh: Myths Exploded (Sindh, 2017) বইটি বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্পর্কিত এই ধরনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি চমৎকার উদাহরণ। লেখক পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে যেকোনো ভুল কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সহিংসতা চালানোর জন্য ভারত ও বাঙালি বিদ্রোহীদের দায়ী করেছেন।
[12] এমন ডজনখানেক কাজ আছে। এখানে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি নির্বাচিত বই দেওয়া হলো: A. A. K. Niazi, The Betrayal of East Pakistan (Karachi, 1999); Rao Farman Ali Khan, How Pakistan Got Divided (Karachi, 2017); Habib Ahmed, The Battle of Hussainiwala and Qaiser-i-Hind: The 1971 War (Karachi, 2015); Hakeem Arshad Qureshi, The 1971 Indo-Pak War: A Soldier’s Narrative (Karachi, 2013); Khadim Hussain Raja, A Stranger in My Own Country: East Pakistan, 1969–1971 (Karachi, 2012); Siddiq Salik, Witness to Surrender (Karachi, 1998); A. R. Siddiqi, East Pakistan: The Endgame: An Onlooker’s Journal 1969–1971 (Karachi, 2004)
[13] সাম্প্রতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নতুন কাজের মধ্যে রয়েছে: Strategic Analysis 45.6 (2021)-এর একটি বিশেষ সংখ্যা; Scott Carney and Jason Milkian, The Vortex: A True Story of History’s Deadliest Storm, an Unspeakable War, and Liberation (New York 2022); Habibul Khondker, Olav Muurlink and Asif Bin Ali (eds), The Emergence of Bangladesh: Interdisciplinary Perspectives (Cham, 2022); Taj Hashmi, Fifty Years of Bangladesh, 1971–2021 (Cham, 2022); Azra Rashid, Gender, Nationalism, and Genocide in Bangladesh (Abingdon, 2019); Farhan Karim (ed.), ‘The memorial reproduction of 1971 in present-day Bangladesh’, special issue of South Asia Chronicle 10 (2020); ‘The Walking Museum: 1971 Genocide and the University of Dhaka’, Centre for Genocide Studies, University of Dhaka, 2021.
[14] Jo Bichar Gaye, একটি জিও টিভি প্রযোজনা যা কর্নেল জেড. আই. ফুররুখের আত্মজীবনীমূলক বিবরণের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। একইরকমভাবে, একটি হুম টিভি প্রযোজনা, Khawab Tut Jatay Hain, এটি পাকিস্তানপন্থী বাঙালি অধ্যাপক সাজ্জাদ হুসাইনের একটি বইয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। পাকিস্তানি সামরিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য পরিচিত জাভেদ জাব্বার, ‘Separation of East Pakistan: The Untold Story’ শিরোনামে একটি ‘নিরপেক্ষ’ তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন।
[15] https://globalvoices.org/2021/03/26/cancellation-of-conference-on-50th-anniversary-of-the-bangladeshwar-of-liberation-sparks-criticism/ (accessed 16 May 2023).
[16] https://www.youtube.com/watch?v=1t3dMZ4B9JM (accessed 7 July 2023).
[17] উদ্ধৃত : Shahab Ahmed, What is Islam: The Importance of Being Islamic (Princeton, 2016), p. 542.
[18] R. G. Collingwood, Idea of History (New York: Oxford University Press, 1956), p. 274
[19] R. G. Collingwood, An Essay on Metaphysics (Oxford: Clarendon Press, 1948), pp. 23–33.
[20] Ibid.
[21] Jaakko Hintikka, Socratic Epistemology: Explorations of Knowledge-Seeking by Questioning (Cambridge, 2007), p. 84.
[22] সমাজবিজ্ঞানীদের—বিশেষ করে শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানী ও মার্কেটিং বিশেষজ্ঞদের—বিপুল সাহিত্যকর্মের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি ড. তানিয়া সাঈদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই সাহিত্যকর্মটি সঠিক প্রশ্ন করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে। তবে, এই সাহিত্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাদানের উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি তৈরি করা বা মার্কেটিং জরিপ এবং জনমতের জন্য আরও কার্যকর প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করার সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, মানববিদ্যা বা মানবিক বিদ্যার গবেষকরা ঐতিহাসিক বর্ণনাকৌশল বা সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের বিকল্প ধারণার জন্য এই ধারণাগত কাঠামোটি খুব বেশি ব্যবহার করেননি। এর ব্যতিক্রম হলো এডওয়ার্ড শাপিরোর ‘America and the bombing of Auschwitz: the importance of asking the right questions’ (সোসাইটি ৫৬.৬ (২০১৯), পৃষ্ঠা ৬২৫-৬৩৩) শীর্ষক নিবন্ধটি। শাপিরোর নিবন্ধে এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে যেখানে ইতিহাসবিদরা একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—যেমন ‘কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র ছিল না’ বা ‘কেন কনফেডারেটরা গৃহযুদ্ধে হেরেছিল’—এবং সেই প্রশ্নের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের ফলাফল কেমন হয়েছিল, তা দেখানো হয়েছে।
[23] Abul Mansur Ahmad, End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution (Dacca, 1975), cited in Rachel Fell McDermott, Leonard A. Gordon, Ainslie T. Embree, Frances W. Pritchett and Dennis Dalton (eds), Sources of Indian Traditions: Modern India, Pakistan, and Bangladesh (New York, 2014), pp. 862–864.
[24] Slavoj Žižek, Violence: Six Sideways Reflections (New York, 2008), p. 187
[25] Ammar Ali Jan, Rule by Fear: Eight Theses on Authoritarianism in Pakistan (Lahore, 2021)
[26] জান এই যুক্তিটি ২০১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ স্মরণে LUMS-এ আয়োজিত একটি সেমিনারে পেশ করেছিলেন। এই সেমিনারের কার্যবিবরণী একটি ভিডিওতে পাওয়া যায়, যেখানে ঔপনিবেশিক সহিংসতা ও এর উত্তরাধিকার, ইতিহাসে পক্ষপাতিত্ব এবং ইতিহাসের সঙ্গে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানটির কার্যবিবরণী এখানে দেখা যাবে: https://www.youtube.com/watch?v=N6Mw_a55Y4c
[27] Walter Benjamin, ‘Critique of violence’, in Walter Benjamin: Selected Writings. Volume I: 1913–1926, (eds) Markus Bullock and Michael W. Jennings (Cambridge, MA, 1996), p. 243.
[28] Jacques Derrida, ‘Force of law: the “mystical foundations of authority”’, in Deconstruction and the Possibility of Justice, (eds) Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld and David Gray Carlson (New York, 1992), p. 43.
[29] A. O. Mitha, Unlikely Beginnings: A Soldier’s Life (Karachi, 2003), pp. 347–348.
[30] Hamoodur Rahman Commission of Inquiry into the 1971 India-Pakistan War: Supplementary Report (Rockville, MD, 2007), p. 14
[31] 1 Nuqta e Nazar with Mujeeb Ur Rehman Shami and Ajmal Jami, 16 December 2021, Dunya News, https:// www.youtube.com/watch?v=pjKXRI5G0BQ (accessed 16 May 2023).
[32] Brigadier (Retd) Karrar Ali Agha, Witness to Carnage 1971: Contemporary Account of the Bengali Insurgency and Pakistan Army Operation Searchlight (March to May 1971) (Lahore, 2011), p. 272. আঘা ছাড়াও, হামুদুর রহমান কমিশনও কুমিল্লা গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছিল। তবে, বোস তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ভয়াবহ যুদ্ধাপরাধগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে একে একটি ‘কথিত গণহত্যা’ (alleged massacre) বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াকুবের এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকারের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং এটি নিয়ে আর কোনো তদন্ত করার প্রয়োজন মনে করেননি। Bose, Dead Reckoning, p. 216, fn. 55.
[33] Richard Sisson and Leo E. Rose, War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh (Berkeley, 1990), p. 120.
[34] শারিকা থিরানাগামা-কে ধন্যবাদ, তিনি বেঞ্জামিনের সহিংসতার সমালোচনার এই বিশেষ দিকটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
[35] Nasser Hussain, The Jurisprudence of Emergency: Colonialism and the Rule of Law (Ann Arbor, 2003), p. 107.
[36] Shuja Nawaz, Crossed Swords: Pakistan, its Army, and the Wars Within (Karachi, 2008), pp. 264–266.
[37] ইলিয়াস চাত্থার আসন্ন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করা মনোগ্রাফটিতে এই বন্দিশিবিরগুলো এবং সেখান থেকে বাঙালিদের পালানোর চেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।
[38] Agha, Witness to Carnage 1971, p. 209.
[39] Hafsa Khawaja, ‘Vicious and Embodied Imaginations: Martial Masculinities, Pakistan Army and Sexual Violence in 1971’ (MA thesis, Columbia University, 2021).
[40] Faisal Devji, ‘End of the postcolonial state’, Economic and Political Weekly 56.44 (30 October 2021), p. 68.
[41] Ali Riaz, Bangladesh: A Political History since Independence (London, 2016), pp. 28–33.
[42] Cited in Gary J. Bass, The Blood Telegram: Nixon, Kissinger and a Forgotten Genocide (New York, 2013), p. 419.
[43] M. Rafiqul Islam, ‘Secessionist self-determination: some lessons from Katanga, Biafra and Bangladesh’, Journal of Peace Research 22.3 (September 1985), pp. 211–221; National Trials of International Crimes in Bangladesh: Transnational Justice as Reflected in Judgments (Leiden, 2019).
[44] Devji, ‘End of the postcolonial state’, p. 72.
[45] Cf. Crispin Bates and Marina Carter, ‘An uneasy commemoration: 1957, the British in India and the “sepoy mutiny”’, in Mutiny at the Margins: New Perspectives on the Indian Uprising of 1857. Volume VI, (eds) Crispin Bates and Marina Carter (New Delhi, 2014).
[46] Walter Benjamin, ‘On the Concept of History’, accessed from https://www.marxists.org/reference/archive/ benjamin/1940/history.htm (accessed 16 May 2023).
[47] Cited in Shoshana Felman, The Juridical Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century (Cambridge, MA, 2002), p. 33.
[48] Bose, Dead Reckoning, pp. 5–6.
[49] Ibid., p. 5
[50] Ibid., p. 181
[51] Ibid., p. 6.
[52] Ibid., p. 7.
[53] Ibid., p. 11.
[54] Ibid., p. 12.
[55] Žižek, Violence, p. 4.
[56] Bose, Dead Reckoning, pp. 142–143
[57] Naeem Mohaiemen, ‘Flying blind: waiting for a real reckoning on 1971’, Economic and Political Weekly 46.36 (3 September 2011), p. 48.
[58] Bose, Dead Reckoning, p. 21.
[59] Ibid., p. 170.
[60] Ibid., p. 189.
[61] Georges Sorel, Reflections on Violence (Cambridge, 2004), p. 14
[62] Bose, Dead Reckoning, p. 112.
[63] Ibid., p. 159.
[64] Ibid., p. 180.
[65] Judith Butler, The Force of Non-Violence: An Ethico-Political Bind (London, 2020), p. 74.
[66] Bose, Dead Reckoning, p. 163.
[67] Bose, Dead Reckoning, p. 27.
[68] Ibid.
[69] মুজিবের কারাবাসের সময় তাঁর দায়িত্বে থাকা অফিসার মার্চ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালের একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যখন মুজিবকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারটি প্রায় ছয় বছর আগে একটি বেসরকারি পাকিস্তানি চ্যানেলে রেকর্ড ও সম্প্রচার করা হয়েছিল: https://www.youtube.com/watch?v=NoINiarhCS4 (অ্যাক্সেস করা হয়েছে ১৬ মে ২০২৩)।
[70] Cf. Kabir, Birth of Bangladesh, especially chapter VIII.
[71] Bose, Dead Reckoning, p. 125.
[72] Ibid., p. 122.
[73] Ibid., p. 19.
[74] Raja, A Stranger in My Own Country, p. 61.
[75] Bina D’ Costa, Nationbuilding, Gender and War Crimes in South Asia (New York, 2011); Jalal Alamgir and Bina D’ Costa, ‘The 1971 genocide: war crimes and political crimes’, Economic and Political Weekly 46.13 (26 March–1 April 2011), pp. 38–41.
[76] Yasmin Saikia, Women, War and the Making of Bangladesh: Remembering 1971 (Karachi, 2011); Nayanika Mookherjee, The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories and the Bangladesh War of 1971 (Durham, 2015)
[77] Felman, The Juridical Unconscious, p. 125.
[78] Žižek, Violence, p. 4.
[79] Felman, The Juridical Unconscious, p. 33.
[80] Ibid., p. 133.
[81] Saikia, Women, War and the Making of Bangladesh, p. 278
[82] Derrida, ‘Force of law’, p. 60.
[83] On the statelessness of Biharis living in Bangladesh, cf. Victoria Redclift, Statelessness and Citizenship: Camps and the Creation of Political Space (Abingdon, 2015); Antara Datta, Refugees and Borders in South Asia: The Great Exodus of 1971 (Abingdon, 2013).
[84] Saleem Mansur Khalid, Al-badar (Lahore, 1985).
[85] Mohaieman, ‘Flying blind’, p. 41
[86] Cited in Veena Das, Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary (Berkeley, 2007), pp. 39–40.
[87] Ibid., p. 40.
[88] Vilashini Coopan, ‘Time-maps: a field guide to the decolonial imaginary’, Critical Times 2.3 (December 2019), p. 413.
[89] Nayanika Mookherjee, ‘1971: Pakistan’s past and knowing what not to narrate’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 39.1 (1 May 2019), p. 212.
[90] Hannah Arendt, Responsibility and Judgment (New York, 2003), p. 21
[91] Ibid., p. 28.
[92] Karl Jaspers, The Question of German Guilt (New York, 2001), pp. 25–26.
[93] Jasper, The Question of German Guilt, p. 56.
[94] Hannah Arendt, Responsibility and Judgment (New York, 2003), p. 44.
[95] Jaspers, The Question of German Guilt, p. 26
[96] Cited Andrew Schaap, ‘Guilty subjects and political responsibility: Arendt, Jaspers and the resonance of the “German Question” in politics of reconciliation’, Political Studies 49.4 (2001), p. 758.
[97] Kabir, Birth of Bangladesh, p. 1034.
[98] Ibid., p. 1046.
[99] Ibid., p. 1047.
[100] Žižek, Violence, pp. 4–5.
নোট – বাংলা অনুবাদের প্রাথমিক খসড়া তৈরিতে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেয়া হয়েছে। অনুবাদ সম্পাদনা করেছেন সহুল আহমদ এবং মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান।
This post has already been read 29 times!