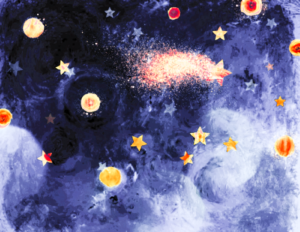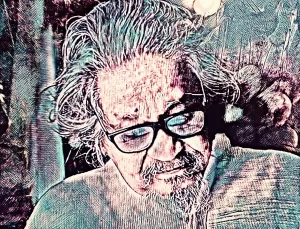গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় এবং শোলাকিয়ার জঙ্গি হামলার কথিত ‘মূল পরিকল্পনাকারী’ তামিম চৌধুরীকে খুঁজে বের করে হত্যার অভিযান বাংলাদেশে চলমান জঙ্গি পরিস্থিতি এবং জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে একটা বড় ঘটনা; নিরাপত্তা বাহিনীর এই অভিযান তাদের একটি বড় সাফল্য। তামিম চৌধুরী যে সংগঠনের সদস্য ছিলেন, সেই সংগঠনের জন্য এটি একটি বড় রকমের ধাক্কা। সরকারের পক্ষ থেকে তামিম চৌধুরীকে ‘নতুন জেএমবি’র নেতা বলা হয়েছে। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, কথিত ইসলামিক স্টেটের প্রচারণা মুখপত্র ‘দাবিক’ যাকে আইএসের বাংলাদেশ শাখার ‘আমির’ হিসেবে উল্লেখ করেছে, তিনিই এই তামিম চৌধুরী। অভিযানের পরপরই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আইজিপি জানিয়েছেন যে তামিম সিরিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তা ছাড়া, গণমাধ্যম ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যেও এটা অনুমান করা হয়েছে যে জন্মসূত্রে বাংলাদেশি কানাডার নাগরিক তামিম চৌধুরী সিরিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে আইএসকে সংগঠিত করার জন্যই এসেছিলেন। তামিম চৌধুরী আইএসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না বা বাংলাদেশি জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ আছে কি না, সেই বিষয়ে পুরোনো বিতর্ক আপাতত সরিয়ে রেখে আমরা দুটো বিষয় নিঃসন্দেহে বলতে পারি। প্রথমত, তাঁকে চিহ্নিত করা, খুঁজে বের করা, তাঁকে অনুসরণ করা এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে জালে আটকে ফেলে হত্যা করার যে অভিযান, তাতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো সাফল্য দেখিয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, গণমাধ্যমের দেওয়া খবর অনুযায়ী অভিযানটি সুচারুভাবে পরিচালিত হয়েছে। অভিযানে গৃহীত কৌশল বিষয়ে ভবিষ্যতে নিশ্চয় আরও জানা যাবে এবং সেই সময় এ বিষয়ে আরও সুনির্দিষ্ট আলোচনার অবকাশ থাকবে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, তামিম চৌধুরী মৃত্যুর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে?
এ ধরনের অভিযানের পরে এই আলোচনা প্রায়ই করা হয়ে থাকে এবং এই প্রশ্ন তোলা হয় কেন অভিযুক্তকে বাঁচিয়ে রেখে তথ্য সংগ্রহ করা হলো না। তবে তামিম চৌধুরীর মৃত্যুর পরেও কেউ কেউ অবশ্য এমন অনুমান প্রকাশ করেছেন যে তামিম সম্ভবত আগেই আটক হয়েছিলেন। এসব আলোচনার কারণ আমাদের অজ্ঞাত নয়। আমরা দেখতে পেয়েছি যে গত কয়েক মাসে সরকারের কাউন্টার-টেররিজম কৌশলের একটি প্রধান দিক হয়ে উঠেছে আটকের পরে জঙ্গিদের হত্যা করা। ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘বন্দুকযুদ্ধ’ এ ক্ষেত্রে প্রধান উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, এ বছরের ৬ জুন থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত দুই মাসে সন্দেহভাজন ১৯ জন জঙ্গি বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছেন (সূত্র: প্রথম আলো, ৬ আগস্ট ২০১৬)। মানবাধিকারকর্মীরা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এমন প্রশ্নও উঠেছে যে এসব হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ‘পরিকল্পনাকারী’দের বাঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না (এ ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যার বিরুদ্ধে আমার লেখা, দেখুন ‘ক্রসফায়ার-সমর্থক ও সমালোচকদের কাছে দুটি প্রশ্ন,’ প্রথম আলো ২৫ জুন, ২০১৬)।
কিন্তু আমরা এ-ও জানি, নিরাপত্তা অভিযানের সময় এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যে নিরাপত্তা বাহিনী সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ঘিরে ফেললে তারা আক্রমণ চালায় এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের বিকল্প থাকে না। যেমন গত বছর নভেম্বরে প্যারিসে জঙ্গি হামলার পাঁচ দিন পর পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে ওই হামলার কথিত পরিকল্পনাকারী আব্দেল হামিদ আব্বাউদ মারা যান। কিন্তু এ ছাড়া অনেক সময় আগে থেকেই কোনো কোনো সন্ত্রাসীকে ‘আটক’ করার বদলে ‘হত্যা’ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেমন—ওসামা বিন লাদেনের বিষয়ে যখন ঘোষণা করা হয়েছিল যে তাঁকে ‘জীবিত বা মৃত’ খুঁজে বের করা হবে, তখনই স্পষ্ট ছিল যে তাঁকে হত্যার ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এটা স্বীকার না করলেও সহজেই বোধগম্য যে, অ্যাবোটাবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনীর হামলার উদ্দেশ্য ওসামা বিন লাদেনকে আটক করা ছিল না।
একইভাবে ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক আনোয়ার আল-আওলাকিকে ২০১১ সালে ড্রোন হামলায় হত্যা সিদ্ধান্ত নিয়েই করা হয়েছিল। তাঁর হত্যা নিয়ে এই প্রশ্ন উঠেছিল যে আত্মপক্ষ সমর্থনের আইনানুগ সুযোগ না দিয়ে একজন মার্কিন নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র সরকার হত্যা করতে পারে কি না। অনেক সময়ই যখন কোনো সন্ত্রাসীকে আটক করা সম্ভব নয় বলে বিবেচিত হয়েছে, সেই সময়েই তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইরাকে ২০০৬ সালে আল-কায়েদা নেতা আবু মুসাব আল জারকাবি, ২০০৯ সালে পাকিস্তান তালেবানের নেতা বায়তুল্লাহ মাসউদ, ২০১৩ সালে তাঁর উত্তরসূরি ও ভাই হেকমতউল্লাহ মাসউদ, ২০১৬ সালে আফগান তালেবান নেতা মোল্লা মানসুরকে হত্যার ঘটনা এর উদাহরণ। এগুলো যথাযথ হয়েছে বা সেগুলো বৈধ এমন বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এটাও লক্ষণীয় যে, এসব হত্যার ঘটনা ঘটেছে যখন সন্ত্রাসীরা তাদের নিজেদের নিরাপত্তাবলয়ের ভেতরে থেকেছে এবং তাদের আটক করার কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই।
জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় বাংলাদেশ অন্য ধরনের অভিজ্ঞতাও উপহার দিয়েছে। ২০০৫ সালে জেএমবির উত্থানের সময় ক্ষমতাসীন বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার এর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে কেবল জেএমবি নিষিদ্ধই ঘোষণা করেনি, সংগঠনের ছয়জন শীর্ষ নেতাকে আটক করে দ্রুত বিচারের সম্মুখীন করে। তাঁদের মৃত্যুদণ্ড পরের বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কার্যকর হয়। এই ধারা আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদে বহাল থাকার কারণে পরের বছরগুলোতে সব মিলে ১৭৯ জন জেএমবির নেতা ও কর্মীকে বিভিন্ন আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৩০০ জঙ্গির আপিল উচ্চ আদালতে বিবেচনাধীন রয়েছে। (সমকাল, ১৭ জুলাই, ২০১৬) তদুপরি, কাউন্টার-টেররিজমের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে জঙ্গিদের ওপরে কড়া নজরদারি, আটক, বিচার অব্যাহত রাখার ফলে জেএমবি কার্যত দুর্বল হয়ে পড়ে। গত কয়েক বছরে কাউন্টার-টেররিজমের দৃষ্টি অন্যদিকে সরে যাওয়া এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন আবার সংগঠিত হয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইএসের উত্থানের কারণে তারা শক্তি সঞ্চয় করে।
সন্ত্রাসীদের, বিশেষত যেসব হাই-প্রোফাইল সন্ত্রাসী বিভিন্ন অভিযানে নিহত হয়েছে, তাদের আমরা মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি; এদের একদল হচ্ছে অনুপ্রেরণাদানকারী, অন্যরা হচ্ছে সামরিক অভিযানের নেতা। ওসামা বিন লাদেন এবং আনোয়ার আল আওলাকি প্রথম শ্রেণিভুক্ত; অন্য যাঁদের কথা আগে উল্লেখ করেছি, তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত। লাদেন নিহত হওয়ার আগে থেকেই আর সাংগঠনিক নেতা ছিলেন না; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর প্রতীকী গুরুত্ব বিশাল। আওলাকির বড় পরিচয় ছিল যে তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ও নিয়োগ করতে সক্ষম হতেন। তাঁদের মৃত্যু অবশ্যই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্য বড় ধরনের ধাক্কা, কিন্তু তাতে অনুপ্রেরণাকারী হিসেবে তাঁদের ভূমিকার অবসান ঘটেছে, এমন মনে করার কারণ নেই। বাংলাদেশের আনসারুল্লাহ বাংলা টিম যা এখন আনসার-আল-ইসলাম নামে পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার বাংলাদেশ শাখা বলে দাবিদার এ সংগঠনটির অনুপ্রেরণা হচ্ছে আওলাকি। দেখা গেছে, এ ধরনের সন্ত্রাসীদের আবেদন তাঁদের মৃত্যুর পরে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় ধরনের সন্ত্রাসীরা হচ্ছে অপারেশনাল কমান্ডার, তারা মারা যাওয়ার পরে খুব দ্রুতই কেউ না কেউ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে তালেবান নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা তার প্রমাণ।
বাংলাদেশে নিহত জঙ্গি তামিম চৌধুরী এই বিভাজনে কোন শ্রেণিভুক্ত হবেন? অবশ্যই তামিম চৌধুরী অনুপ্রেরণাদায়ী নেতৃত্বের সারিভুক্ত নন; বরং তাঁকে অপারেশনাল কমান্ডার বলে চিহ্নিত করাই যথাযথ। গুলশান এবং শোলাকিয়ার হামলা তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হয়েছে বলে নিরাপত্তা বাহিনী তথ্য দিয়েছে। তা ছাড়া, আইএসের মুখপত্র দাবিকের ভাষ্য অনুযায়ী, আইএসের উদ্ভব ঘটেছে জেএমবির বিভিন্ন অংশকে একত্র করে, তবে তার সঙ্গে যে নতুন সদস্য যুক্ত হয়েছে, সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফলে তামিম চৌধুরী সম্ভবত সাংগঠনিকভাবে যেকোনো অপারেশনাল কমান্ডারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের বাইরের এবং বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে সম্ভবত খুব শিগগির কেউ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন।
এর বাইরে যে প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা হলো—জঙ্গি সংগঠনগুলোর কৌশলে পরিবর্তন, অর্থাৎ ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মতো বড় ধরনের হামলা থেকে সরে এসে নিজেদের সংগঠিত করা। এ ছাড়া আরও বড় ধরনের, দুর্ধর্ষ ধরনের হামলা চালিয়ে দেখানো যে তারা এখনো শক্তিশালী। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাদের জন্য ইতিবাচক—সিরিয়ায় ক্রমাগতভাবে পরাজয়ের কারণে আইএসের নতুন কৌশল হচ্ছে পৃথিবীর অন্যত্র তাদের শক্তি দেখানো। মনে রাখা দরকার, তামিমের মতো আরও বেশ কয়েকজন, যাঁরা বিদেশে ছিলেন বা আছেন, তাঁরা এখন সক্রিয়। বাংলাদেশে সরকারের ভাষায় নতুন জেএমবি বা আইএস এবং আল-কায়েদার শক্তি বিষয়ে আমরা অবগত নই। এসব বিবেচনায় তামিম চৌধুরীর মৃত্যু ও অভিযানের সাফল্য সত্ত্বেও এখনই আত্মতৃপ্তিতে ভোগার বা অতিমাত্রায় আনন্দিত হওয়ার কারণ নেই।
নিরাপত্তা অভিযানের সাফল্য, জঙ্গিদের হত্যা, জঙ্গি সংগঠনে নেতৃত্বে শূন্যতা তৈরির বিষয়গুলো আলোচনা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেগুলোর পাশাপাশি একই রকম বা বেশি গুরুত্ব দিয়ে উত্তর খোঁজা দরকার এসব প্রশ্নের যে, এই হত্যা অন্যদের এই ধরনের সংগঠনে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে কি? জঙ্গি সংগঠনগুলোর বিস্তারে এবং কোনো ব্যক্তির কাছে জঙ্গি সংগঠনের আবেদন তৈরিতে যেসব অনুকূল রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ কাজ করে, তার অবসান হবে কি? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান এবং সেভাবে কৌশল নির্ধারণ হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদে জঙ্গিবাদ মোকাবিলার কার্যকর পথ।
প্রথম আলো’তে প্রকাশিত, ২৯ আগষ্ট ২০১৬