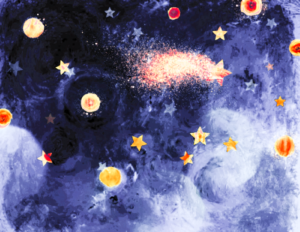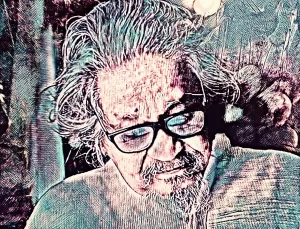আইএস না থাকলেও জঙ্গি আছে
ইতালির এক নাগরিককে হত্যার এক সপ্তাহের মধ্যে এক জাপানিকে হত্যার ঘটনা এবং এসবের দায় স্বীকার করে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) দেওয়া কথিত বিবৃতির প্রেক্ষাপটে কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হচ্ছে। এক বিরল ঐকমত্যের ঘটনা ঘটিয়ে বিএনপি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকার-সমর্থকেরা বলছেন যে দেশে জঙ্গি নেই, দেশ জঙ্গিবাদের কবলে পড়েনি। কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন যে দেশে কখনোই জঙ্গিবাদ ছিল না। কেননা, বাংলাদেশের মানুষ জঙ্গিবাদের সমর্থক নয়। বাংলাদেশের মানুষ যে চরমপন্থী মতামতকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে না, সেটা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত আমরা সরকারিভাবেই দেশে আইএস এবং ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার শাখার লোকজন রয়েছে বলে বলতে শুনেছি।
২০১৪ সালের জুলাই থেকে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত এক বছরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরগুলো আমাদের এ বিষয়ে পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করতে পারে। দৈনিক প্রথম আলো, জনকণ্ঠ ও নিউ এজ-এ এই সময়ে জঙ্গি আটক বিষয়ে যেসব খবর ছাপা হয়েছে, আমরা তার দিকে নজর দিলে দেখতে পাই যে এ বিষয়ে ৬৭টি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম আলোয় ২৯টি, জনকণ্ঠ পত্রিকায় ২০টি ও নিউ এজ-এ ১৮টি। এসব খবর অনুযায়ী জঙ্গি সন্দেহে আটকের সংখ্যা ১০০ জন এবং সন্দেহভাজন ১২ জন, যাদের আটক করা যায়নি। এই আটক জঙ্গিদের সম্পর্কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিশেষ করে র্যাবের পক্ষে থেকে যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে যে এরা কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত হতে আগ্রহী। সাংগঠনিক সংশ্লিষ্টতার হিসাব পাওয়া গেছে ১০৪ জনের (এর মধ্যে ১২ জন আটক হয়নি, তবে তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছে)। এই হিসাব অনুযায়ী জেএমবির সঙ্গে যুক্ত ২৫ জন, আইএসের সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত হতে আগ্রহী ২২, শহীদ হামজা ব্রিগেডের সঙ্গে যুক্ত ১৯ জন, আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সঙ্গে জড়িত ১৪ জন, হরকাতুল জিহাদ বা হুজির সঙ্গে জড়িত ১৩ জন এবং বাংলাদেশ জিহাদ গ্রুপের সঙ্গে জড়িত ১১ জন।
এই হিসাবের দিকে তাকালে দেখা যায় যে আটক জঙ্গিদের মধ্যে আইএসের সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত হতে আগ্রহীরা রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আটক জঙ্গিদের মধ্যে একাধিক সদস্যকে বাংলাদেশে আইএসের সমন্বয়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে আটক শাখাওয়াতুল কবিরকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেভাবেই পরিচয় করিয়ে দেয়। আবার মে মাসে যখন আবদুল্লাহ আল গালিব বলে এক সদস্যকে আটক করা হয়, তাঁকেও একইভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ২৬ মে কোমল পানীয় উৎপাদনকারী একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত আমিনুল ইসলাম বেগকে আটক করার পর গণমাধ্যমে তাঁকে আইএসের ‘রিক্রুটার’ চিহ্নিত করা হয়।
এসব তথ্য এ ধারণাই তৈরি করে যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকার আইএস ও আল-কায়েদার উপস্থিতি বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল আছে। শুধু তা-ই নয়, সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের নেতাদের এই বলে সমালোচনা করা হয়েছে যে তাঁরা তালেবান এবং আইএসের ‘পুতুল’ মাত্র।
আমরা জানি যে যেকোনো দেশে এসব আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের উপস্থিতির পরিণতি ভয়াবহ অবস্থার তৈরি করে। এটাও আমরা জানি যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো সেখানেই উপস্থিত হয়, যেখানে তাদের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। অন্যপক্ষে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি বিদেশি শক্তিগুলোকে সংঘাতে টেনে আনে। আইএসের উত্থান ঘটেছে ইরাকে, যখন দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামো বিরাজমান সংকটের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রেক্ষাপট অবশ্যই ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। পশ্চিমা দেশগুলোর স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইএসের উত্থান বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন এবং যাঁরা করেন না, তাঁরা এ বিষয়ে একমত হবেন যে এ ধরনের পরিস্থিতি বিশ্বশক্তিকে এমনভাবে যুক্ত করে যে তা থেকে সহজে বেরিয়ে আসা যায় না। সিরিয়ায় পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি রাশিয়ার অংশগ্রহণ তার বড় প্রমাণ।
এক-দেড় বছর ধরে আইএসের উপস্থিতি বা সম্ভাব্য উপস্থিতির কথা বলার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দল ও সরকার এর কারণ অনুসন্ধান, কারা এ ধরনের সংগঠনে যুক্ত হতে পারে, তা চিহ্নিত করা এবং তা মোকাবিলায় কী ব্যবস্থা বিবেচনা করেছে তা সাধারণের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি বিষয়ে বক্তব্য পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ আছে, তার সদুত্তর পাওয়া যায় না। ২০১৪ সালের একপক্ষীয় নির্বাচনের কারণে পশ্চিমা দেশগুলো বর্তমান সরকারের বিষয়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করত, সেগুলো নিষ্পত্তিতে সরকার উৎসাহ দেখায়নি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সরকার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান যে জোরদার, সেটা বারবার বলার চেষ্টা করেছে। এতে পশ্চিমাদের পাশাপাশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মনোযোগও আকর্ষিত হয়েছে কি না, সেটাও ভাবা দরকার।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে কেবল সন্দেহভাজনদের আটক, তাদের বিচার কিংবা সাধারণের মনে ভীতি তৈরি করে জঙ্গিবাদ—তা দেশীয় সংগঠনের বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের—মোকাবিলা করা যায় না। এ বিষয়ে বাংলাদেশে যতটা আলোচনা হয়, ততটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকে না। দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা অনেক সময়ই এই দুর্বলতার কারণ। এই পটভূমিতেই আমরা প্রথমে ইতালির এক নাগরিক হত্যা এবং পরে এক জাপানিকে হত্যার ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। ইতালির নাগরিকের হত্যার পরই যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত একটি বেসরকারি সংগঠন—যার বিষয়ে অনেক নিরাপত্তা বিশ্লেষকের মনে প্রশ্ন রয়েছে—এই মর্মে জানায় যে এ হত্যার দায় আইএস স্বীকার করেছে। আর জাপানের নাগরিক হত্যার পর বার্ত সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে যে আইএস নিজেদের টুইট একাউন্ট থেকে এ হত্যার দায় স্বীকার করেছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ব্লগার হত্যার ঘটনা এবং সেসব হত্যার দায়িত্ব স্বীকারসূচক বিবৃতির প্রেক্ষাপটে এই বিবৃতিকেও কেউ কেউ গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, কারও কারও মনে সংশয় তৈরি হয়েছে। তারপর সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবেই বলা হলো যে দেশে আইএসের অস্তিত্ব নেই।
এখন প্রশ্ন হতে পারে যে সরকার কি ‘অস্বীকারের’ সংস্কৃতির বশবর্তী হয়ে এ বক্তব্য দিচ্ছে? এ ধরনের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য নতুন নয়, ২০০৫ সালে ক্ষমতাসীনেরা অভ্যন্তরীণ জঙ্গিদের উপস্থিতি বিষয়ে এ কৌশল নিয়েছিল। সরকারের মনে কি এ ধারণা তৈরি হয়েছে যে আইএসের উপস্থিতির স্বীকৃতি ২০০৯ সাল থেকে জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় তারা যে সাফল্য দাবি করে এসেছে, তাকে ম্লান করে দেয়? নাকি তারা অনুধাবন করছে যে এ ধরনের সংগঠনের উপস্থিতি প্রমাণিত হলে এযাবৎকালে আমরা অন্যত্র যে ধরনের পরিণতি দেখেছি, সে দিকেই দেশ এগোতে শুরু করবে? তাহলে জঙ্গিবাদের প্রশ্নকে প্রাধান্য দিয়ে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি করা হয়েছে, তা বাস্তব নয়?
বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতি এবং এই হত্যাকাণ্ড বিষয়ে দেওয়া কথিত বিবৃতি বিষয়ে যাঁরা সংশয়ী, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। কিন্তু বাংলাদেশে বিদেশি জঙ্গিদের উপস্থিতি বা তার আশঙ্কাকে যাঁরা এক কথায় নাকচ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে অপারগ। কেননা, গত দুই দশকে বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যক্রমের একটা ইতিহাস আছে এবং সেখানে বিভিন্নভাবেই বিদেশি যোগাযোগের প্রমাণ উপস্থিত।
দেশীয় জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ
কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ে আলোচনায় প্রকাশিত মতামত থেকে এই রকমের ধারণা জন্মাতে পারে যে বিদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গি বা উগ্রপন্থীদের যোগাযোগের প্রশ্নই অবান্তর। বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতি নাকচ করতে গিয়ে কেউ কেউ এমন বলছেন, যেন বাংলাদেশে বিদেশি জঙ্গিদের উপস্থিতি বা তৎপরতার কথা এই প্রথম শোনা গেল। এ বক্তব্য যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকে কিছুদিন আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জঙ্গিদের উপস্থিতি রয়েছে বলেই বলার চেষ্টা করেছেন। সরকারের অবস্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেভাবে এ রকম আশঙ্কাকে নাকচ করে দিচ্ছেন, সেটা উদ্বেগজনক। কেননা, বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যক্রমের যে ইতিহাস, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গিদের সম্পর্ক ছিল।
নিরাপত্তা বিশ্লেষক, দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা, সন্ত্রাসবাদ বিষয়ের সাংবাদিক, নিরাপত্তা নীতিমালা তৈরির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের কাছে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিষয়টি প্রায় দুই দশকের পুরোনো। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সূচনা নব্বইয়ের দশকের কথাই বলবেন। এটাও উল্লেখ করা দরকার যে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সূচনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বিদেশি সংশ্লিষ্টতা। এ দেশে জঙ্গিবাদের উৎসমুখ বলে যাকে চিহ্নিত করা যায়, সেই হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর (হুজি) কার্যত প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকায়, জাতীয় প্রেসক্লাবে।
আফগান মুজাহিদদের কাবুল বিজয়ে উল্লসিত ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি ‘স্বেচ্ছাসেবী’দের একাংশ সংবাদ সম্মেলন করেছিল সেদিন। সাংগঠনিকভাবে হুজি সংগঠিত হচ্ছিল আরও কয়েক বছর আগ থেকে। পাকিস্তানে হুজির প্রাথমিক রূপ তৈরি হয় ১৯৮০ সালে, কিন্তু এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৮ সালে এবং এর প্রসার ঘটে পরবর্তী চার বছরে। এই সময়েই সাংগঠনিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশে বিস্তারের পরিকল্পনা করা হয় এবং তার অংশ হিসেবেই বাংলাদেশে হুজির যাত্রা শুরু। পাকিস্তানে হুজির সংগঠকেরা প্রধানত বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল রোহিঙ্গাদের লড়াইকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারকে অস্থিতিশীল করতে।
বাংলাদেশে হুজির বিস্তার দ্রুততা লাভ করে অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিষ্ঠিত জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) সঙ্গে এর সাংগঠনিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর। জেএমবির প্রতিষ্ঠা ১৯৯৮ সালে, এর নামকরণ হয় ২০০১ সালে। কিন্তু জেএমবি ও হুজির সম্পর্ক গড়ে ওঠার পটভূমি তৈরি হয় জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবদুর রহমান যখন জেএমবি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের দিকে দেশের কিছু আলেম ও ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। সেই সূত্রেই হুজির নেতা মুফতি হান্নানের সঙ্গে আবদুর রহমানের যোগাযোগ। ১৯৯৬ সালের ১৯ জানুয়ারি কক্সবাজারের উখিয়ায় হুজির যে ৪১ জন কর্মী সশস্ত্র অবস্থায় আটক হন, তাঁদের মামলা তদারকির জন্য আবদুর রহমান হুজির প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যান। এই যোগাযোগের পরিণতিতেই হুজি ও জেএমবির মধ্যে সাংগঠনিক সংশ্লিষ্টতা তৈরি হয়।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য জঙ্গিদের দেশের বাইরে যোগাযোগ শুরু হয় ১৯৯৭-৯৮ সালে। ভারতীয় নাগরিক আবদুল করিম টুন্ডার সঙ্গে আবদুর রহমানের ১৯৯৬ সালে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠা এ দেশে জঙ্গিবাদের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। টুন্ডা পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তাইয়েবার শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মনে করে যে ১৯৯৪ সালে টুন্ডা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তাঁর হাত ধরেই আবদুর রহমান পাকিস্তানে প্রশিক্ষণের জন্য যান এবং মারকাজ আদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ, যা লস্কর-ই-তাইয়েবার উৎস সংগঠন, এর সঙ্গে যুক্ত হন, পরিচিত হন হাফিজ সাঈদের সঙ্গে। ভারতীয় গোয়েন্দারা সব সময় অভিযোগ করে এসেছে যে টুন্ডা বাংলাদেশ থেকে ভারতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছেন। তারা দাবি করে যে ১৯৯৮ সালে দিল্লিতে আটক দুই বাংলাদেশি জেএমবির সদস্য এবং তাঁরা টুন্ডার মাধ্যমে ভারতে এসেছিলেন। ২০১৩ সালে টুন্ডা আটক হয়ে বর্তমানে ভারতে বিচারাধীন আছেন।
বাংলাদেশে বিদেশি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতির বিষয়টি আমরা আরও জানতে পারি ২০০৮ ও ২০০৯ সালে। আবদুর রউফ দাউদ মার্চেন্ট ও জাহেদ শেখ নামে দুজন ভারতীয় জঙ্গির আটকের ঘটনা ঘটে। ২০০৯ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় কথিত আরেফ রেজা কমান্ডো ফোর্সের মুফতি ওবায়েদুল্লাহসহ আটক হন মোট ছয়জন, তাঁদের মধ্যে একাধিক সদস্য স্বীকার করেন যে তাঁরা অনেক দিন ধরে বাংলাদেশে বাস করছেন; ওবায়েদুল্লাহ ১৯৯৫ সালে ও হাবিবুল্লাহ ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশে আছেন বলে দাবি করেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। বাংলাদেশকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য লস্কর-ই-তাইয়েবার উৎসাহ কখনোই হ্রাস পায়নি, আর তারা যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছে, তা সুবিদিত। ফলে বাংলাদেশের এই জঙ্গিদের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের সম্পর্ক যে অব্যাহত ছিল, সেটা আমরা বুঝতে পারি।
বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে বিদেশি যোগাযোগের আরেকটি পথ হচ্ছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম চালিয়ে এসেছে। মিয়ানমার সরকারের অন্যায় ও অমানবিক আচরণ রোহিঙ্গাদের লড়াইয়ের ন্যায়সংগত কারণ তৈরি করেছে, কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের ভূমিকা নিরাপত্তার জন্য হয়েছে হুমকি। রোহিঙ্গা যোদ্ধাদের সঙ্গে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী জঙ্গিদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি। তাদের উপলক্ষ করেই পাকিস্তানের হুজি এ দেশে তাদের কাজ সম্প্রসারণ করছিল।
কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলো অস্ত্র সংগ্রহের জন্য যে কেবল তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শিকভাবে ঐকমত্য পোষণকারীদের সঙ্গেই কাজ করেছে, তা নয়। এদের হাতে আসা অস্ত্রের এক বড় অংশ এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্রের কালোবাজার থেকে। এ ক্ষেত্রে থাইল্যান্ডের গোপন অস্ত্রবাজারগুলো সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু গোপন বাজারই এদের একমাত্র উৎস ছিল না। যেগুলোকে ‘গ্রে মার্কেট’ বা ‘ধূসর বাজার’, অর্থাৎ যেগুলো কোনো কোনো দেশের গোয়েন্দা সংস্থার জ্ঞাতসারে, এমনকি প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে, দেশের স্বার্থ বিবেচনায় হস্তান্তরিত হয়, সেগুলোও কাজ করেছে। সাধারণভাবে গ্রে মার্কেটের উদাহরণ হিসেবে দেশে দেশে বিপ্লবী থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী থেকে মাদক পাচারকারীদের হাতে গোয়েন্দাদের অস্ত্র তুলে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা যায়।
এই অঞ্চলে মিয়ানমারের ওপর চীনের প্রভাব হ্রাসের জন্য সরকারকে চাপে রাখতে আশির দশকের শেষ পর্যায় থেকে প্রায় দেড় দশক ধরে কারেন গেরিলাদের প্রতি ভারতের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল; ভারত তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে বলেও অভিযোগ আছে। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য কারেন গেরিলাদের সঙ্গে রোহিঙ্গারা সহযোগিতা করেছে এবং কক্সবাজারের প্রত্যন্ত উপকূলকে ব্যবহার করা হয়েছে অস্ত্র হস্তান্তরের কেন্দ্র হিসেবে।
১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত মহাসাগরের নারকোনডাম দ্বীপের কাছে একটি এবং তার তিন মাস পরে প্রায় ওই একই এলাকায় আরেকটি—মোট দুটি অবৈধ অস্ত্রের চালান আটকের ঘটনা ঘটে। ভারতের নৌবাহিনীর আটক করা এসব অস্ত্রের চালান আরাকান আর্মি ও কারেন গেরিলাদের জন্য যাচ্ছিল এবং সেগুলোর গন্তব্য ছিল কক্সবাজার। এই অস্ত্র আটক এবং আটককৃত ব্যক্তিদের বিষয়ে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ এবং নৌবাহিনীর মধ্যে সে সময় টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়েছে।
কারেনদের সঙ্গে আদর্শিক পার্থক্যকে সরিয়ে রেখে যেমন রোহিঙ্গারা একত্রে কাজ করেছে, ঠিক একইভাবে তাদের সঙ্গে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে ওঠার ঘটনা ঘটেছে। বিস্ময়কর এই যে, ভারতের যেসব জঙ্গিগোষ্ঠী ভারতের উত্তরাঞ্চলে বাঙালি, বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি ইসলামপন্থী জঙ্গিরা দ্বিধান্বিত হয়নি।
এই ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জঙ্গিগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হলে তারা কেবল আদর্শিক বিবেচনাতেই সহযোগিতা করবে তা নয়, বিভিন্ন বিবেচনায় দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে সহযোগিতার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাতে অর্থ-অস্ত্র-নিরাপদ আশ্রয় অনেক কিছুই বিনিময় হতে পারে। ফলে সীমান্ত ছাড়িয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। অস্বীকার করলেই তা অপসৃত হবে না। ফলে জঙ্গিবাদ মোকাবিলার প্রথম বিবেচনা হচ্ছে কী কী কারণে জঙ্গিবাদ বা সহিংস চরমপন্থার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়, কী কী উপাদান দেশের অভ্যন্তরে জঙ্গিবাদকে আদর্শিকভাবে বা কৌশল হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, সেগুলোকে চিহ্নিত করা, তার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
কোন পরিস্থিতি জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটায়
একটি দেশে কেন জঙ্গিবাদ বা সহিংস উগ্রপন্থা বিস্তার লাভ করে, কেন এ ধরনের আদর্শ মানুষকে আকর্ষণ করে, কারা জঙ্গিবাদের প্রতি আকর্ষিত হয়? কয়েক দশক ধরেই সমাজবিজ্ঞানী, নিরাপত্তাবিষয়ক গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারকেরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে গত শতকের ষাটের দশকে, যখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি মানুষের আকর্ষণ তৈরি হয় এবং বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের পথে সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু তার আগেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সহিংসতার ব্যবহারকে (যেমন: আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি, বাস্ক গেরিলাদের সংগঠন) বোঝার জন্যও একই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। সত্তরের দশকে ইতালির রেড ব্রিগেড, জার্মানির বাদের-মেইনহফ, জাপানে রেড আর্মিকে যাঁরা অনুসরণ করেছেন, সেসব গবেষকও এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। ফলে এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে কখনোই ঘাটতি ছিল না।
এই প্রশ্নগুলো নতুন করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর; আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আল-কায়েদার আবির্ভাব, আফগানিস্তানে তালেবানের গ্রহণযোগ্যতা এই প্রশ্নগুলোতে নতুন মাত্রা যোগ করে দেয়। এই পর্যায়ে রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে ধর্মের প্রশ্ন। কেউ কেউ এই প্রশ্নও তোলেন যে রাজনৈতিক আদর্শ ও ধর্মের মধ্যে কোনো বিভাজন টানা উচিত হবে কি না।
রাজনৈতিক ইসলামের মধ্য থেকে একটি ধারা আগেও সহিংসতাকে তাদের কৌশল হিসেবেই শুধু বেছে নিয়েছিল তা নয়, তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় একেই একমাত্র পথ বলেও বিবেচনা করে সে পথেই অগ্রসর হয়েছে। তালেবান সেই ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। ২০০১ সালের ঘটনাবলির কারণে তাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হয়। এই ধারার লক্ষ্য সীমিত বলেই বিবেচিত হওয়া দরকার, কেননা নিজস্ব রাষ্ট্রের মধ্যেই তারা তাদের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং চেয়েছে। অন্যপক্ষে, আমরা দেখতে পাই ইসলামের রাজনৈতিক দিককে আশ্রয় করে আরও সংগঠনের আবির্ভাব বা পুনরুত্থান ঘটে, যাদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রসীমাকে অস্বীকার করে তাদের ভাষায় ‘খেলাফত’ প্রতিষ্ঠা। একই সঙ্গে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক কাঠামোকে তারা চ্যালেঞ্জ করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। কৌশল ও কর্মপদ্ধতি তাদের জন্য গৌণ বিষয়। হিযবুত তাহ্রীর সেই ধারার প্রতিনিধি।
এই ঘটনাপ্রবাহ ইসলামপন্থী রাজনীতির মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধারার জন্ম দেয়, তেমনি এসব ধারার আবেদন বোঝার তাগিদ তৈরি হয়। অবশ্যই এই ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়নি। চলমান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি, অর্থনীতির বিশ্বায়ন, প্রযুক্তির উৎকর্ষ—সবই তাকে প্রভাবিত করেছে। ২০১০ সাল নাগাদ আমরা দেখতে পাই যে আরও একধরনের সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে, যারা যুদ্ধবিধ্বস্ত কিংবা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত অঞ্চলগুলোয় তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের রাষ্ট্র, যাকে তারা ‘খেলাফত’ বলে বর্ণনা করে, প্রতিষ্ঠা করে এবং সারা পৃথিবীর মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হয়ে ওঠে। নাইজেরিয়ার বোকো হারাম ও ইরাকে ইসলামি রাষ্ট্র এর উদাহরণ।
এই ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি ২০০১ সাল থেকে ইসলামপন্থী সহিংস চরমপন্থী সংগঠনগুলো নিয়ে গবেষণার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসব গবেষণার ফলাফলের দিকে দৃকপাত না করে অনেক বিশ্লেষক, রাজনীতিবিদ সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে তাঁদের ধারণাকে প্রকৃত কারণ বলে বর্ণনা করতে শুরু করেন। এই প্রবণতার সবচেয়ে বড় দিক হলো এই যে তাঁরা ধরে নিলেন যে দারিদ্র্যই হচ্ছে সহিংস চরমপন্থার কারণ এবং সুযোগবঞ্চিত মানুষেরা জঙ্গি সংগঠনের আদর্শের প্রতি আকর্ষিত হয়। তালেবান নেতৃত্ব, পাকিস্তানের বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাংগঠনিক কাঠামো ও আফগান যুদ্ধে পাকিস্তানি কয়েকটি মাদ্রাসার ভূমিকার ওপরে নির্ভর করে অনেকে মাদ্রাসাকেই ইসলামপন্থী সহিংস চরমপন্থার উৎস বলে প্রচার করতে থাকে। এসব ধারণা শিগগিরই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে শুরু করে; কেননা দেখা যায় যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের অধিকাংশ নেতা কিংবা আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত কিংবা ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত নয়।
পরবর্তী কয়েক বছরে গবেষকেরা তাঁদের অতীত গবেষণা, সংগৃহীত তথ্য ইত্যাদির আলোকে কিছু সাধারণ উপসংহারে উপনীত হন। যাতে ধারণা দেওয়া হয় যে সন্ত্রাসবাদের কিছু ভিত্তিগত (ইংরেজিতে আন্ডারলায়িং), অন্যভাবে বললে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল কারণ রয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে আরও সুনির্দিষ্ট, বাস্তবতানির্ভর ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণাকাজের পরে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের মূল কারণ চিহ্নিত করার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন একই রকমের আর্থসামাজিক অবস্থা সবাইকে সন্ত্রাসী করে তুলছে না। তা ছাড়া যারা এই ধরনের সন্ত্রাসী কাজে যুক্ত হয়, তারা কেবল পরিস্থিতির চাপে যোগ দেয় না, ক্ষেত্রবিশেষে কিছুর আকর্ষণে যুক্ত হয়। সেটা বিশেষ করে কোনো নেতার আকর্ষণ হতে পারে, হতে পারে যে এই ধরনের সংগঠন তাকে এমন কিছু দিতে পারে, যা তাকে সমাজের অন্য কোনো সংস্থা, পরিবার বা বন্ধু দিতে পারছে না। তা ছাড়া মানুষ স্বেচ্ছায় অনেক কিছু করে, কেবল পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করে না। সন্ত্রাসের মূল কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টার একটা বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে, ধরে নেওয়া হয় যে সম্ভাব্য সন্ত্রাসীরা কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা দিয়ে প্রভাবিত হয়।
এসব দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে গবেষকেরা গত কয়েক দশকে বিভিন্ন দেশে যেখানে জঙ্গিবাদ প্রসারিত হয়েছে, যেসব ব্যক্তি জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হয়েছে, যেসব জঙ্গি সংগঠন শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে, তাদের ওপর গবেষণা করে এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে জঙ্গি হয়ে ওঠা এবং জঙ্গিবাদের প্রসারের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় চালকের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো ব্যক্তিকে সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দেয়, সমাজে জঙ্গিবাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে এবং সন্ত্রাসী সংগঠন তৈরি করে। এই ড্রাইভার বা চালিকাগুলোকে ভাগ করা হয়েছে চারটি ভাগে: অভ্যন্তরীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈশ্বিক।
অভ্যন্তরীণ চালকের মধ্যে রয়েছে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্নতা বা প্রান্তিকতা অনুভব করা, সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়া, হতাশার বোধ, অন্যদের তুলনায় বঞ্চিত অনুভব করা। রাজনৈতিক চালকগুলোর মধ্যে আছে রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, সরকারের কঠোর নিপীড়ন ও সুস্পষ্টভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সর্বব্যাপী দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের দায়মুক্তির ব্যবস্থা, স্থানীয়ভাবে অব্যাহত সংঘাত, সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এলাকা তৈরি হওয়া। সাংস্কৃতিক চালকের মধ্যে আছে এই ধারণা বিরাজ করা বা তৈরি হওয়া যে ইসলাম আক্রমণের বা বিপদের মুখোমুখি, নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হুমকির মুখে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজের ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ বা সমাজে অন্যদের ওপরে নিজের ইসলামি সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়া।
বৈশ্বিক চালকের মধ্যে আছে নিজেদের ভিকটিম বলে মনে করা। একার্থে এটি সাংস্কৃতিক চালকের সঙ্গে যুক্ত। ইসলাম বিপদের মুখে—এই ধারণার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় যে মুসলিম জনগোষ্ঠী অন্যত্র অন্যায় ও বৈষম্যের শিকার, যদি এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে বিশ্বব্যবস্থা মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য অন্যায্য, তাহলে তা এক শক্তিশালী চালকের ভূমিকা পালন করতে পারে।
এ ছাড়া বৈশ্বিক চালকের আরেকটি হচ্ছে ‘কাছের শত্রু-দূরের শত্রু’র ধারণা। যখন অভ্যন্তরীণভাবে দেশের ভেতরে নিপীড়ন বৃদ্ধি পায়, যখন ‘কাছের শত্রু’কে পরাজিত করতে সক্ষম হয় না, তখন দেশের বাইরে ‘দূরের শত্রু’র বিরুদ্ধে তাদের অভিযান চালানোর আগ্রহ তৈরি হয়। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শত্রু বলে বিবেচনা করে, তার কারণগুলোর মধ্যে নিপীড়ক সরকারগুলোর প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সমর্থন অন্যতম বলেই তাদের দলিলপত্র, প্রচারণা ও সদস্য সংগ্রহের প্রচারণায় স্পষ্ট। এই চালকগুলো একক ও সম্মিলিতভাবে কাজ করে এবং সব জায়গায় সবগুলো না থাকলেও তার কার্যকারিতা অক্ষত থাকে বলেই দেখা গেছে।
আজ যখন বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেট বা আল-কায়েদার মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সে সময় বোঝা দরকার কোন ধরনের পরিস্থিতিতে কোন ধরনের চালক দেশীয় বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের জন্য অনুকূল অবস্থার জন্ম দেয়। জঙ্গিবাদ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে চাইলে এসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।
প্রথম আলো’তে তিন পর্বে প্রকাশিত; ৫, ৬, ৭ অক্টোবর ২০১৫