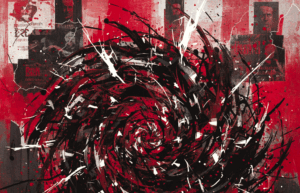This post has already been read 16 times!
ফেনীর সোনাগাজীতে একটি মাদ্রাসায় আগুনে পুড়িয়ে নুসরাত জাহান রাফিকে হত্যার ঘটনাপ্রবাহ চারটি বিষয় সামনে এনেছে: এক নারীর যৌন নিপীড়ন, মাদ্রাসার ভেতরে অধ্যক্ষের দ্বারা ছাত্রীর যৌন নিপীড়ন, স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের দায়িত্বহীন ভূমিকা এবং স্থানীয় রাজনীতির কলুষিত বৃত্তচক্র। এর প্রতিটি বিষয় আলাদাভাবে আমাদের মনোযোগ দাবি করে। এগুলো নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সংগত কারণেই উদ্বেগ ও আশঙ্কা আছে। কিন্তু চারটি বিষয় কি আসলেই বিচ্ছিন্ন, কোথাও কি এসব বিষয় একটি জায়গায় মিলিত হয়? আলাদাভাবে বিবেচনা করে কি এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব?
বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে যৌন নির্যাতনের মাত্রা, বিশেষ করে ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে। নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বড় শিকারে পরিণত হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব থেকে দেখা যায়, পাঁচ বছরে ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার শিকার নারীর সংখ্যা মোট প্রায় চার হাজার। ২০১৮ সালে ধর্ষণের সংখ্যা ৭৩২, তাদের মধ্যে ৬৬ জনকে ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ‘প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রেই ঘটনার শিকার নারীর বয়স দেওয়া নেই। কিন্তু বাকিদের ৮৬ শতাংশ শিশু-কিশোরী। ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার নারীরও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এই বয়সী। এদের বড় অংশটিরই বয়স ১২ বছরের মধ্যে। এই বয়সীদের মধ্যে গণধর্ষণের শিকারও আছে’ (কুর্রাতুল–আইন–তাহ্মিনা ও মানসুরা হোসাইন, ‘শিশুরাই বড় শিকার’, প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারি ২০১৯)।
এ বিষয়ে অন্য সূত্রগুলো যেসব তথ্য দেয়, তাতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ বলেই প্রতীয়মান হয়। ছয়টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) জানিয়েছে, সারা দেশে ২ থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত ১৫ দিনে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ৪৭টি শিশু। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩৯টি শিশু (প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০১৯)। এসব পরিসংখ্যান জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে করা। ফলে এতে পুরো মাত্রাটি ধরা পড়ে না। যদিও আমরা প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো ঘটনার খবর সংবাদমাধ্যমে দেখছি তথাপি বাস্তবতা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী পরিবারগুলো পুলিশের শরণাপন্ন হয় না এবং সেগুলো গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। বাংলাদেশে শিশুদের মধ্যে ছেলেরা এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়, সেটা জানা থাকলেও তার কোনো আলাদা পরিসংখ্যান নেই।
এই ভয়াবহতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রকাশিত হচ্ছে নুসরাতের হত্যাকাণ্ডের পরে। এই প্রথম ঘটল, তা নয়। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লা সেনানিবাসে ধর্ষণের পর সোহাগী জাহান তনুকে হত্যার ঘটনার পরও ব্যাপক সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কিন্তু অপরাধীদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশের তদন্ত, ফরেনসিক রিপোর্ট, এমনকি আদালতের আচরণ ও ঘটনাপ্রবাহ ধারণা দেয় যে তনু নামে আদৌ কেউ মারাই যায়নি, ধর্ষণ-হত্যা তো অনেক পরের ব্যাপার। এই ধরনের আরও ঘটনা আছে, যেগুলো জাতীয়ভাবে আলোচিত বলে সবার মনে আছে। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা জাতীয়ভাবে আলোচিত নয় বলে অনেক ধর্ষণের ও হত্যার ঘটনা আমাদের জানাই নেই। নুসরাতের হত্যার পরে আদালতের বক্তব্যে এখন এটা স্পষ্ট, তনু হত্যা মামলা ‘হারিয়ে গেছে’। বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ বলেছেন, ‘আমরা কোনোভাবেই চাই না সাগর-রুনি, মিতু ও তনুর মতো মামলাটা যেন হারিয়ে যায়’ (ইত্তেফাক, ১১ এপ্রিল ২০১৯)।
যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার ব্যাপকতা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচার না হওয়ার কারণেই মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ দৃশ্যমান। সে কারণেই এই প্রতিবাদ যে কেবল একজনের হত্যা বা সোনাগাজীর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ক্ষোভ, তা নয়। ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর পক্ষে এ ধরনের ‘মামলা হারিয়ে যাওয়া’ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, জনসাধারণের পক্ষেও নয়। ‘বিচার না হওয়া’ বা ‘অপরাধীদের পার পাওয়ার’ বিষয়গুলো তাদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয় না।
ধর্ষণের শিকার নারী ও তার পরিবারকে যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাতে পুলিশের মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি, অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকেই কার্যত অপরাধীর মতো করে বিবেচনা করা, অভিযুক্তদের বাঁচানোর লক্ষ্যে এজাহারে না রাখা, পুলিশের দীর্ঘসূত্রতার সুযোগে অভিযুক্তদের পলায়ন, মামলা দায়েরের পরে বাদীর ওপরে চাপ প্রয়োগের সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং মামলার প্রক্রিয়া—এসব থেকে এই ধারণাই হয় যে বিদ্যমান আইন ও বিচারব্যবস্থা ভুক্তভোগীর পক্ষে তো নয়ই, বরং উল্টো। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ধর্ষণের দায় ধর্ষণের শিকার নারীর ওপরে চাপানোর একটি অসুস্থ সামাজিক মানসিকতা। এগুলো সাধারণ মানুষের ভেতরে এই ধারণাই দেয় যে রাষ্ট্র ও সমাজে যাঁরা ক্ষমতাশালী, তাঁরা কার্যত অপরাধীর পক্ষেই। গণমাধ্যমে এঁদেরই ‘প্রভাবশালী মহল’ বলে এক অশরীরী ধারণা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অথচ এঁরা রক্ত-মাংসের মানুষ এবং অন্যদের চেয়ে বেশি পরিচিত। বিত্ত ও রাজনীতির ক্ষমতা যাঁদের আছে, বিরাজমান আইন ও বিচারব্যবস্থা তাঁদের পক্ষেই থাকে বলে ধারণা সর্বব্যাপ্ত। সেই কারণেই নুসরাতের হত্যার বিচারের দাবি এতটা জোরালো হয়েছে।
মাদ্রাসার ভেতরে মাদ্রাসার শিক্ষকের দ্বারা নারী নির্যাতনের ঘটনা স্পর্শকাতর বিষয় বলে গণ্য হচ্ছে; এটা সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মাত্রা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। এর কারণ একাধিক। প্রথমত, যাঁরা মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে, তাঁরা এই ঘটনাকে তাঁদের দাবির সমর্থনে একটি প্রমাণ হিসেবে দেখছেন। মাদ্রাসাশিক্ষার পাঠ্যক্রমের ব্যাপারেই তাঁদের প্রধান আপত্তি; তবে তাঁরা এই ধরনের আচরণকে ওই পাঠ্যক্রমেরই ফল বলে মনে করেন। দ্বিতীয়ত, যাঁরা মাদ্রাসাশিক্ষা বিষয়ে কোনোরকম নেতিবাচক অবস্থান নিতে চান না, তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে আরও বেশি নৈতিক আচরণ আশা করেন, তাঁরা সম্ভবত এগুলোকে ব্যত্যয় মনে করেন। তাঁরা মনে করেন যে এগুলো কেবল অনাকাঙ্ক্ষিতই নয়, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।
গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের দিকে নজর দিলে এ কথা মনে হয় যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে বেশি যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। এই বিষয়ে আরও তথ্যনির্ভর প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু সমাজের ভেতরে বিরাজমান কথিত ‘ধর্মীয় অনুভূতির’ কারণে না রাষ্ট্রীয়ভাবে, না স্বাধীন গবেষকেরা এ নিয়ে গবেষণা করতে সক্ষম হচ্ছেন। এ ধরনের গবেষণা করতে চাইলেও রাষ্ট্র ও সরকারের সমর্থন পাওয়া যাবে, এমন মনে হয় না। বাংলাদেশের আলেম সমাজ, যাঁরা মনে করেন যে এই ধরনের আচরণকে কোনোভাবেই ইসলাম সমর্থন করে না এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিরা ইসলামের অবমাননাই করছে, তাঁরাও যে সহযোগিতা করতে চান তার কোনো নজির নেই। এসব ঘটনার ব্যাপারে তাদের বেদনাদায়ক নীরবতা সহজেই লক্ষণীয়, কঠোর প্রতিবাদ কিংবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তো দূরের কথা।
ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেকোনো ধরনের অনৈতিক কাজ, বিশেষত যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটলে তা যে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। এর কারণ, সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের নৈতিক অবস্থান শক্তিশালী এবং জৈবিক তাড়না নিয়ন্ত্রণে তাঁরা আরও বেশি সচেতন। কিন্তু সব সময়ই তা সত্য নয়। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ক্যাথলিক চার্চ। কয়েক দশক ধরে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন চার্চে ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা শুধু যে কিশোর (এবং কিশোরীদের) যৌন নিপীড়ন করেছেন তা–ই নয়, তা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এমন সব ব্যবস্থা নিয়েছেন, যা আইন ও নীতিনৈতিকতার বিবেচনায় অপরাধ। ১৯৮০–এর দশক থেকে এ বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ ও সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কাঠামো এই নিয়ে কথা বলেনি। ২০০২ সালে বোস্টন গ্লোব–এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পর এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আলোচনা জোরদার হয়। পোপ জন পল ২০০১ সালে এ বিষয়ে প্রথম দুঃখ প্রকাশ করেন। শুধু যে ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে তা নয়, অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্নভাবে হলেও যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণের প্রমাণ আছে—প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই সব আচরণ রক্ষার ব্যবস্থাও আছে। এগুলো প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় সংস্থার কাছে যে ধরনের উচ্চ নৈতিকতার প্রত্যাশা করে, তা সব সময় পূরণ হয় না। সেই প্রত্যাশা পূরণ নিশ্চিত করার উপায় হচ্ছে ওই সব সংস্থার স্বচ্ছতার ব্যবস্থা করা, তাদের ওপর মানুষের নজরদারির ব্যবস্থা করা, তাদের সমাজের কাছে দায়বদ্ধ করা।
ধর্মীয় বা ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেই সব প্রতিষ্ঠানেই বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন, এমনকি যৌন নিপীড়ন বেশি ঘটে, প্রধানত আবাসিক এবং কেবল ধর্মীয় অনুভূতি বিবেচনায় যেগুলোর ওপরে নজরদারির ব্যবস্থা হয় দুর্বল নতুবা অনুপস্থিত। যদিও নুসরাতের ওপরে নির্যাতন এবং তাঁকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে আলিয়া মাদ্রাসা ধারার একটি প্রতিষ্ঠানে, তথাপি এই আলোচনায় উঠে এসেছে যে বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতনের সংবাদই সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। আলিয়া মাদ্রাসাগুলো সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার অধীন এবং সেগুলো সরকারিভাবে এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধানেই থাকার কথা, কিন্তু তত্ত্বাবধানের অনুপস্থিতি এই ঘটনায় এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। তার কারণ প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক বিবেচনা, ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা নয়। সমাজের সব প্রতিষ্ঠানকেই রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের এবং দলীয়ভাবে সাজানোর যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তার ফলেই আজ এই পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নিয়েছে।
মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ওই প্রতিষ্ঠানে কী ঘটে, কারা নিযুক্ত হন, তাঁরা দায়িত্ব পালন করেন কি না, সেই বিষয়ে জানেন বলে মনে হয় না। অন্যথায় একজন ব্যক্তি, যাঁর বিরুদ্ধে অতীতে অন্যত্র যৌন হয়রানির অভিযোগ ছিল, তিনি কী করে অধ্যক্ষের চাকরি পান? এখন জানা যাচ্ছে যে ‘১৯৯৬ সালে ফেনী সদরের দৌলতপুর সালামতিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে অনিয়ম এবং ছাত্র বলাৎকারের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছিল’ (যুগান্তর, ১৩ এপ্রিল ২০১৯); ‘ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি, আর্থিক দুর্নীতি এবং নাশকতা ও পুলিশের ওপর হামলা–মামলায় তিন দফা কারাভোগ করেছেন সিরাজ উদদৌলা’ (প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৯)। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে অভিভাবকেরা যুক্ত থাকেন বটে, এই যুক্ত থাকা নামমাত্র কি না, তাঁরা তাঁদের বক্তব্য দিতে পারেন কি না, তা–ও আমরা জানি না। কিন্তু সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ঘটনা থেকে এটা জানি যে তাঁদের অভিযোগ আমলে নেওয়া হয় না। এইগুলো জবাবদিহি, স্বচ্ছতার অনুপস্থিতির প্রমাণ। ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই যে এই মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতি হচ্ছেন ফেনীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।
শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে আরেকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে, তা হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। যেসব প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ শিশুর মানসিক উৎকর্ষের অনুকূল নয়, সেগুলোর বিষয়ে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কী? এই নিয়ে আলোচনার জন্য আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে? মাদ্রাসাবিষয়ক আলোচনায় প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ আলোচিত হয় না। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে হলে, জীবনাচরণ শিখতে হলে তা কেন শিশুদের ও অন্য শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত মানস গঠনের দরজা বন্ধের মাধ্যমে করতে হবে? ইসলামের ইতিহাস থেকে এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে না।
এই মর্মান্তিক ঘটনার তৃতীয় দিক স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা। ‘স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদদৌলার বিরুদ্ধে অতীতে আনীত অভিযোগ তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে বা ধামাচাপা দিয়েছে। এই সব অভিযোগের মধ্যে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ছিল একাধিক’ (যুগান্তর, ১৩ এপ্রিল ২০১৯)। অভিযোগ আছে অর্থ আত্মসাতের। পুলিশের কর্মকর্তা নুসরাতকে জেরা করার নামে হেনস্তা করেছেন, একজন সাংবাদিককে দিয়ে হত্যাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন, সংবাদমাধ্যমে এটা হত্যা না আত্মহত্যা বলে সংশয় প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় পুলিশের এই আচরণে যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে নুসরাত জাহানের পরিবারকে দোষারোপ করে পুলিশ সদর দপ্তরে চিঠি দিয়েছিলেন ফেনী জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) জাহাঙ্গীর আলম। ১১ এপ্রিল পুলিশ সদর দপ্তর, বিশেষ শাখা ও চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজির দপ্তরে পাঠানো ওই প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, নুসরাতকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় মামলা করতে পরিবার ‘কালক্ষেপণ’ করেছে। পুলিশের এই ভূমিকার পেছনে এটা স্পষ্ট যে পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দিলে তাদের কোনো রকম ক্ষতির শিকার হতে হবে না, সেই বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল। ঘটনাপ্রবাহে নুসরাতের ক্ষেত্রে আমরা তা জানতে পারছি, কিন্তু এটি কি ব্যতিক্রম? অবশ্যই ব্যতিক্রম মনে করার কারণ নেই। কী কারণে পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসন তা মনে করতে পারে? তার উত্তর আছে এই ঘটনার চতুর্থ দিকে—স্থানীয় রাজনীতির কলুষিত বৃত্তচক্র।
সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে সিরাজ উদদৌলার নিয়োগ এবং কার্যক্রমই কেবল প্রশ্নবিদ্ধ নয়, নিয়োগের পর থেকেই স্থানীয় রাজনীতি, সুনির্দিষ্টভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এখন সুবিদিত। জামায়াতে ইসলামী থেকে ‘অপকর্মের কারণে’ বহিষ্কৃত একজন ব্যক্তিকে (‘কে এই সিরাজ?’, একুশে টেলিভিশন, ১৭ এপ্রিল ২০১৯) কোনো দল ও তার নেতারা গ্রহণ করবেন কি না, সেটা দলের আদর্শের প্রশ্ন। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল ও উপদলীয় কোন্দলের সঙ্গে জড়িত এই ব্যক্তি যে অন্যায় ও বেআইনি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পেরেছেন তার কারণ হচ্ছে, এখন সারা দেশেই ক্ষমতাসীন দলের সদস্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে আইনের ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া। এর অনেক উদাহরণ আছে, একটি সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করলে বুঝতে সহজ হবে। ১৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে পুলিশের এক কর্মকর্তাসহ দুই কনস্টেবলকে মারধর করেন স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতা ও তাঁর সহযোগীরা। তাঁদের আটক করার পর ছেড়ে দিয়েছেন থানার ওসি, কারণ কী? তাঁর ভাষ্যে, ‘সব নিজেরা নিজেরা। বিএনপি হইত একটা কথা আছিল, ব্যবস্থা নিতে পারতাম।’ অর্থ, ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি মিলেমিশে যে একাকার হয়ে গেছে এবং সেখানে নীতিনৈতিকতা যে আর কারও বিবেচ্য বিষয় নয়, এই হচ্ছে তার উদাহরণ।
কিন্তু এটি ব্যতিক্রম নয়, সিরাজ উদদৌলা একা নন। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজনীতির অবসান হওয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক বুঝতে না পারার কারণ নেই। ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সাধারণ নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না, ফলে তাঁদের জন্য যা লাভজনক, তা–ই এখন নির্ধারকের ভূমিকা নিয়েছে। প্রশাসন এই নিয়ে আপত্তি করবে, এমন সম্ভাবনাও নেই—‘সব নিজেরা নিজেরা’।
সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাতের হত্যাকারীদের, হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারীদের, তার মদদদাতাদের বিচার হোক সেটা আশা করি। আদালতের মতোই আশা করি ‘এই মামলা হারিয়ে যাবে না’। কিন্তু জবাবদিহির অনুপস্থিতির যে সংস্কৃতি—সেটা যৌন নিপীড়নের বিচার, মাদ্রাসার শিক্ষা, স্থানীয় প্রশাসনের আচরণ ও পুলিশের কার্যক্রম এবং স্থানীয় রাজনীতির বিষাক্ত চক্রের মধ্যে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এই চারটি দিক যেখানে এসে এক জায়গায় মিলেছে, তার কী হবে? এই বৃত্তচক্রকে বহাল রেখে কতজন নুসরাতের হত্যার বিচার করা সম্ভব?
প্রথম আলো’তে প্রকাশিত, ২১ এপ্রিল এবং ২৩ এপ্রিল ২০১৯
This post has already been read 16 times!