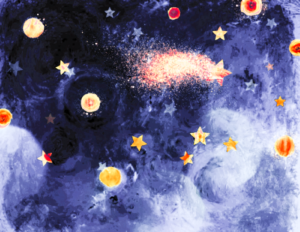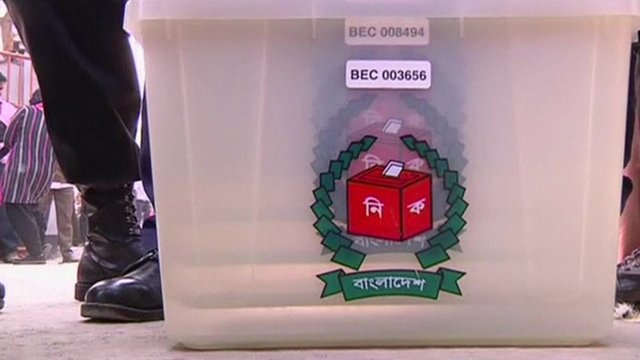
বাংলাদেশের গণমাধ্যমের সংবাদ অনুসরণ করলে এমন মনে হতে পারে যে দেশে একটি নির্বাচন অত্যাসন্ন; দেশের রাজনীতিবিদদের কথাবার্তা থেকেই এই ধারণার জন্ম হচ্ছে। একদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা, এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌকার পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। অন্যদিকে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ধানের শীষের পক্ষে ভোট দেওয়ার কথা যেমন বলছেন, তেমনি এ-ও বলেছেন যে বিএনপিকে বাইরে রেখেই আবার নির্বাচন করতে চায় আওয়ামী লীগ এবং সেই নির্বাচন ‘করতে দেওয়া হবে না’।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। সাংবিধানিক বিবেচনায় নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত সময় ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর থেকে শুরু করে ২০১৯ সালের ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। নির্বাচন কমিশনের রোডম্যাপ থেকে অনুমান করা যায় যে নির্বাচন ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে হবে—এমনভাবেই কমিশন প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের বোঝা দরকার, নির্বাচনবিষয়ক আলোচনার সূচনা কোথায় হওয়া দরকার, কী কী বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার এবং কী কী সম্ভাব্য দৃশ্যপট বা সিনারিও আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে।
নির্বাচনবিষয়ক এই আলোচনার সূচনা বোধগম্য কারণেই ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। বিএনপি যেহেতু ২০১৪ সালের নির্বাচনের পরদিন থেকেই নতুন নির্বাচনের দাবি জানিয়ে এসেছে, সেহেতু এখন এই আলোচনা যে গতি পেয়েছে, সেটার কৃতিত্ব তারা দাবি করতে পারে না। ২০১৫ সালের ‘আন্দোলনের’ ব্যর্থতার কারণে তাদের বরঞ্চ অনেকটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। অন্যদিকে রাজনীতিতে এমন কোনো ঘটনা লক্ষণীয় নয়, যা থেকে ক্ষমতাসীন দল এখন নির্বাচন নিয়ে চিন্তিত হতে পারে। ফলে নির্বাচনবিষয়ক আলোচনা থেকে এই উপসংহারে পৌঁছানোই সঠিক যে সরকার এখন বরং নির্বাচনের বিষয় সামনে রাখতেই পছন্দ করবে। এর ইতিবাচক দিক যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা হচ্ছে ২০১৮–১৯ সালে নির্বাচনের আগে এমন অজুহাত দেখানোর অবকাশ থাকবে না যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কাজ সময়াভাবে করা সম্ভব হয়নি। অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য এবং সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে চাইলে তার জন্য যথেষ্ট সময় আছে। কিন্তু এই আলোচনার ফলে দেশে বিরাজমান অন্যান্য বিষয় ক্রমেই আড়ালে চলে যাচ্ছে কি না, সেটা যেমন লক্ষ করার বিষয়, তেমনি বিবেচনা করা দরকার, আমরা এক দুষ্টচক্রে প্রবেশ করছি কি না।
ক্ষমতাসীন দল জানে যে নির্বাচনবিষয়ক আলোচনার প্রধান বিষয় হবে নির্বাচনকালীন সরকারের রূপ কী হবে এবং বিএনপি তাতে অংশ নেবে কি না। এই দুই বিষয়ের কোনোটাই ২০১৪ সালের নির্বাচনের পরিণতি কী হয়েছে কিংবা ওই নির্বাচন থেকে কী শিক্ষা নেওয়া হয়েছে, তাকে সামনে নিয়ে আসে না; বরং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেওয়ার মতো সহজ উত্তর তৈরি আছে এবং আলোচনাটি সেই বৃত্তের মধ্যেই ঘুরতে থাকে। আলোচনাকে এই বৃত্তের মধ্যে রাখলে সময়ক্ষেপণ হয়, কিন্তু এমন নির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হয় না, যা মর্মবস্তুর দিক থেকে ২০১৪ সালের নির্বাচনের চেয়ে ভিন্ন। তদুপরি মনে রাখতে হবে যে কোনো নির্বাচন কেবল বিজয়ী ও বিজিত নির্ধারণ করে না, বিভিন্নভাবেই আগামী দিনের শাসনের ধরনের ইঙ্গিত দেয়। আমি মনে করি যে ২০১৪ সালের নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা না করে ২০১৪ সালের পুনরাবৃত্তি রোধের আশা বাতুলতা মাত্র; সে ক্ষেত্রে বড়জোর দৃশ্যত ভিন্ন রকমের একটা নির্বাচন আশা করতে পারি।
নির্বাচন নিয়ে সাম্প্রতিক কথাবার্তায় যেটা এখন সুস্পষ্টভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হলো ২০১৪ সালের নির্বাচন কেবল একতরফাই ছিল না, তা ছিল সব বিচারেই অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় এমন এক নির্বাচন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী ‘দায়িত্ব নিয়েছিলেন’ এবং বিজয়ী সংসদ সদস্যরা জানেন না তাঁরা কীভাবে পাস করেছেন। শুধু তা-ই নয়, এ কথাও এখন স্পষ্ট যে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করুক, ক্ষমতাসীন দলের সেটাই কাঙ্ক্ষিত ছিল। আওয়ামী লীগ যেকোনো মূল্যে নির্বাচন করতে চেয়েছে এবং তাতে সক্ষমও হয়েছে। এসবের অধিকাংশ আমাদের কমবেশি সবার আগেই জানা ছিল, কিন্তু অনেকেই তা বলার ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ছিলেন এই কারণে যে তাতে করে ক্ষমতাসীন দলের নৈতিক বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ত। ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সহানুভূতিশীলেরা এই বৈধতার প্রশ্ন সামনে আনতে চাননি, তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা সেটা বুঝতে পারেননি বা এখনো পারছেন না। যেকোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক ভ্রান্তির ফল নির্ধারিত হয় ওই ভ্রান্তি দিয়ে, আমাদের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির ওপরে তার ফল নির্ভর করে না। ফলে ২০১৪ সালের নির্বাচনের ফল আমাদের ইচ্ছে-নিরপেক্ষভাবেই নির্ধারিত হয়েছে।
এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সবচেয়ে বেশি অভাব হচ্ছে জবাবদিহির। দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কর্মীরা যেমন মনে করছেন যে তাঁরা সব ধরনের জবাবদিহির ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন, তেমনি তাঁদের রক্ষা করতে গিয়ে প্রশাসনকেও নিরপেক্ষ জায়গায় রাখা সম্ভব হয়নি কিংবা রাখা হয়নি। দলের কর্মীদের আচরণের জন্য ‘অনুপ্রবেশকারীদের’ অভিযুক্ত করে দলের নেতারা প্রকারান্তরে এই ধরনের আচরণকেই বৈধতা দিয়েছেন, কর্মীরা তা বুঝতে মোটেই ভুল করেননি। কর্মীদের ‘দায়মুক্তি’ দেওয়া এবং প্রশাসনের দলীয়করণের ফলে অন্যরাও আইন ও বিচারের তোয়াক্কা করার প্রয়োজন বোধ করছেন না। সেটি সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, শিশু নির্যাতন এবং নানা ধরনের ঘটনা থেকেই স্পষ্ট। দেশে যে ক্ষমতা ও বিত্তের অভাবনীয় দাপট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এগুলো তার প্রমাণ।
বিরাজমান ব্যবস্থাকে আদর্শিকভাবে বৈধতা দেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীনেরা গণতন্ত্রের বিপরীতে উন্নয়নের ধারণা এবং রাজনৈতিক ইসলাম বা ইসলামপন্থার বিপরীতে সেক্যুলারিজমের একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই দুইয়ের আবেদন ক্রমান্বয়েই অবসায়িত হয়েছে। গত বছরগুলোতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থেকেছে এবং বৃহদাকারের বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু একই সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে এমন দাবি করা যাবে না। সাম্প্রতিক শ্রমবাজার জরিপেই দেখা যাচ্ছে, গত বছরগুলোতে কর্মসংস্থানের হার আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে (রিজওয়ানুল ইসলাম, ‘বাংলাদেশে কি কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি হচ্ছে?’ প্রথম আলো, ৪ জুন ২০১৭), দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটেছে এবং সম্পদের কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের দিকে তাকালেও দেখা যাবে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের নামে কর ও ভ্যাট আরোপের হার দাঁড়িয়েছে উদ্বেগজনক, যার এক বড় অংশই ব্যয় হবে এমন সব খাতে, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ মানুষের জীবনের মানের উন্নয়ন ঘটায় না। রাজনৈতিক ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আগের অবস্থান থেকে সরে আসার লক্ষণ হচ্ছে, ইসলামপন্থীদের সবচেয়ে রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে সাম্প্রতিক আপস এবং ধর্মীয় অনুভূতি বিষয়ে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারার উপর্যুপরি ব্যবহার।
গত বছরগুলোতে ক্ষমতাসীন দল ও সরকার ক্রমে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বলপ্রয়োগের ওপর। এই বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের ওপরে প্রয়োগ হয়েছে, একই সঙ্গে যেকোনো ধরনের ভিন্নমত, এমনকি তা যৌক্তিক হলেও বিপদগ্রস্ত হয়েছে। যেকোনো দেশে শাসনের উপায় হিসেবে বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা যখন প্রাধান্য পায়, তখন বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতাই শুধু বৃদ্ধি পায় না, একাদিক্রমে সেগুলোই হয়ে ওঠে নীতিনির্ধারক। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটেনি। তবে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো গত কয়েক বছরে আমরা একই সঙ্গে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সরকার দেখতে পাচ্ছি, যার হাতে অপরিমেয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আবার অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের অনেক শক্তির চাপ মোকাবিলায় সরকারের দুর্বলতা দুর্নিরীক্ষ নয়। জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে বিভিন্ন কোম্পানিকে বিনা টেন্ডারে কাজ দেওয়ার ঘটনা এবং কোনো কোনো দেশের কাছ থেকে এ ধরনের আবদারকে সেভাবেই বিবেচনা করা যায়।
গত কয়েক বছরের এসব ঘটনার পেছনে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা, প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভূমিকা নেই তা নয়। অতীতে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদের ভেতরেও এ ধরনের প্রবণতা ছিল, কিন্তু অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর পরে হলেও নাগরিকদের মুখোমুখি হতে হবে—এই ধারণা মাত্রাগতভাবে তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা জবাবদিহির অনুপস্থিতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ফলে এবং ২০১৪ সালের মতো কোনো ধরনের ব্যবস্থায় এই জবাবদিহিহীন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যাবে বলে মনে হওয়ার কারণে এই আচরণগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ফলে নির্বাচনবিষয়ক আলোচনার সূচনা হওয়া দরকার এইখানে যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের ফল কেবল ফলাফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। এই উপলব্ধি ছাড়া ভবিষ্যৎ নির্বাচনের আলোচনা একটি বিশেষ দুষ্টচক্রের বাইরে যেতে পারবে না।
২
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনেকটা সময় বাকি থাকলেও সাম্প্রতিক কালে নির্বাচনবিষয়ক আলোচনায় যথাযথ কারণেই নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত খসড়া রোডম্যাপের বিষয় আলোচিত হচ্ছে। রোডম্যাপ অনুযায়ী আগামী মাস থেকে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করবে। এসব আলোচনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সংসদীয় আসনের সীমানার পুনর্বিন্যাসকরণ। এটি যে একটি দুরূহ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়, অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞজনেরা সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন (এম সাখাওয়াত হোসেন, ‘ইসির রোডম্যাপ: শুরুতেই যা করণীয়’, প্রথম আলো, ৭ জুন ২০১৭)।
কিন্তু এই কাজেরও আগে নির্বাচন কমিশনকে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে কমিশন সবার অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চায় এবং সে জন্য আইনের আওতায় দেওয়া সব রকমের ক্ষমতার ব্যবহারে কমিশনের সদস্যরা পিছপা হবেন না। কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিশনের পাঁচ বছরের সবচেয়ে বড় ‘সাফল্য’ হচ্ছে নির্বাচনব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থার অবসান। স্মরণ করা দরকার, রকিবউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিশন ২০১৩ সালের চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন এবং ২০১৬ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচন ছাড়া আর কোনো নির্বাচনই সুষ্ঠুভাবে করতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, অভিযোগ আছে, সাংবিধানিকভাবে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগেও কমিশনের অনীহা ছিল। দলীয় সরকারের নিয়োগ করা একটি কমিশনের মেয়াদ পূর্ণ করার ইতিহাস যেমন তাঁরা রচনা করেছেন, তেমনি তাঁরা এটাও প্রমাণ করেছেন যে ক্ষমতাসীনেরা না চাইলে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন করা অসম্ভব।
দলীয় সরকারের অধীনে যেসব নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছিল—রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ব্যবহার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যথাযথ সক্রিয় উপস্থিতি। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল (দেখুন আমার নিবন্ধ, ‘নির্বাচন কমিশন কেন আগে পারেনি?’, প্রথম আলো, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬)। আমাদের মনে রাখতে হবে যে নির্বাচন যেমন এক দিনের ঘটনা নয়, তা একটি প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়, তেমনি কমিশন একা কখনোই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারে না। নির্বাচনের সময় যে হাজার হাজার কর্মকর্তা নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা আসলে সরকারি কর্মচারী। দলীয়করণের বিবেচনা বাদ দিলেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রশাসনের ‘অভিশাপ’ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা ছাড়া তাঁদের পক্ষে নির্ভয়ে দায়িত্ব পালন কতটা সম্ভব, সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারি।
রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রথম ধাপ হচ্ছে সরকার ও সরকারি দলের আচরণ। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনের কথা বলার পাশাপাশি যখন একটি প্রধান দলের প্রধানের রাজনৈতিক দপ্তরে রহস্যময় ‘তল্লাশি’ চালানো হয় এবং তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তখন এই সদিচ্ছা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। সংবিধানে যদিও বলা হয়েছে যে ক্ষমতাসীন দলের অধীনেই নির্বাচন হবে, সেখানে সেই সরকারের কাঠামো ও দায়িত্ব যে অন্য যেকোনো সময়ের মতো হতে পারে না, সেটা নিশ্চয় সরকার স্বীকার করে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে, যখন বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জানিয়ে আন্দোলন করেছিল, তখন প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সরকার ও নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করার প্রস্তাব প্রমাণ করে যে নীতিগতভাবে আওয়ামী লীগও মনে করে যে নির্বাচনকালীন সরকারের সঙ্গে অন্য সময়ের সরকারের একটা পার্থক্য থাকা দরকার। সেই নীতির ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচনের সময় সরকার গঠিত হবে কি না, সেটা আমরা জানি না। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা দরকার, বিএনপি ইতিমধ্যেই তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, দলটি এখন ‘নির্বাচন সহায়ক’ সরকারের দাবি জানিয়েছে। সেটা তাদের ব্যর্থতা, না বাস্তবতা মেনে নেওয়া, তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এতে করে ওই বাস্তবতা বদল হয় না যে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক হয়নি।
নির্বাচন কমিশনের প্রশ্নে এসব আলোচনা অবতারণার অর্থ এই নয় যে সরকারের ধরন কী হবে, সেটা কমিশন নির্ধারণ করতে পারবে। সাংবিধানিকভাবে সেই অধিকার নির্বাচন কমিশনের নেই। কিন্তু জুলাই থেকে নভেম্বরে রাজনৈতিক দল ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনার পর কমিশন কি এ কথা বলতে পারে যে নির্বাচনের একটি অংশীদার হিসেবে তারা সরকারের কাছ থেকে কী চায়? সেটি সরকারকে জানানোর পাশাপাশি নাগরিকদেরও অবগত করতে পারে? এই ধরনের অনুরোধ তারা পাঠায় নির্বাচনের অব্যবহিত আগে, কিন্তু নির্বাচন–প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যদি আলোচনা শুরু করা যায়, তবে এই বিষয়ে একটি ধারণাপত্র কেন আগেই উপস্থাপন করা যাবে না?
এটার জন্য আলাদা করে আইনের অপেক্ষা না করে স্বচ্ছতার প্রমাণ হিসেবে এবং কমিশনের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের এই পদক্ষেপ ইতিবাচক বলেই বিবেচিত হবে বলে আমার ধারণা। নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে যে জাতীয় নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠেয় চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই যথেষ্ট, তাহলে তারা ভুল করবে, কেননা রকিব কমিশনের স্মৃতি কেউ ভুলেছেন বলে মনে করার কারণ নেই।
২০১৪ সালে নির্বাচনে যেসব দল অংশগ্রহণ করেনি, তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তেছে। সেই দায়িত্ব কোনো একক দলের নয়। আলাদা করেই তাদের উচিত হবে এখনই এটা স্পষ্ট করা, যে কী ধরনের পদক্ষেপ তারা প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আশা করে। অনুমান করা যায় যে তারা এসব বিষয় কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় জানাবে। কিন্তু কমিশনকে জানানোর আগেই দলগুলো কি সাধারণ ভোটারদের কাছে তাদের ধারণাপত্র তুলে ধরতে পারে?
এসব আলোচনার বদলে সরকারের ধরন কী হবে আর বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে কি না, সেই আলোচনার বৃত্তে ঘুরপাক খেলে ২০১৪ সালের চেয়ে ভিন্ন কোনো ধরনের নির্বাচন তারা আশা করতে পারে না। কিন্তু এটাও ঠিক যে একেবারে ২০১৪ সালের পুনরাবৃত্তি হবে না, কেননা সেটা এমনকি ক্ষমতাসীনেরাও চায় না। ফলে তিন ধরনের সম্ভাবনা বা তিনটি সম্ভাব্য দৃশ্যপট আমরা অনুমান করতে পারি। প্রথমটি হচ্ছে সব দলের অংশগ্রহণে একটি নির্বাচন, যাতে বিএনপিও অংশ নেবে; দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মিত্ররা ছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন, যাতে বিএনপি অংশ নেবে না; তৃতীয়টি হচ্ছে বিএনপি এবং অধিকাংশ দলকে বাইরে রেখে ২০১৪ সালের মতো, কিন্তু তুলনামূলকভাবে সংগঠিত নির্বাচন।
এই তিনটি সম্ভাব্য দৃশ্যপট নিয়ে চূড়ান্ত কথা বলার সময় আসেনি, কেননা রাজনীতিতে কখনো কখনো এক দিন অনেক দীর্ঘ, আর নির্বাচনের নির্ধারিত সময়ের এখনো বাকি অন্ততপক্ষে দেড় বছর। ফলে সামনে আরও অনেক ঘটনাই বাকি। কিন্তু নির্বাচনের ধরন নির্ধারণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে ক্ষমতাসীন দল। কিন্তু নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের মনে রাখা দরকার, কী ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, সেটা নির্ধারণ করে দেবে পরের সময়টা কেমন যাবে।
প্রথম আলো’তে প্রকাশিত, ১৮-১৯ জুন ২০১৭