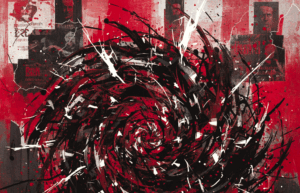Republican U.S. presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally at the Treasure Island Hotel & Casino in Las Vegas, Nevada June 18, 2016. REUTERS/David Becker - RTX2GYKG
This post has already been read 44 times!
১। ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ নীতি
যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতিকে অভাবনীয় বলে বর্ণনা করলে কমই বলা হবে। উদ্বেগ, আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা এক বিরাট সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে; কিন্ত এগুলো শুধু অভিবাসীদের বিষয় নয়। দেশের নাগরিকদের এক বড় অংশই এখন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা এবং সমাজের ভারসাম্য নিয়ে চিন্তিত।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থান এবং নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা মার্কিন রাজনীতি ও সমাজে বড় ধরণের পরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করছি। এইসব পরিবর্তনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চিহ্নিত করা যায়; সেগুলো হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদের উত্থান, অভিবাসী বিরোধী মনোভাবের বিস্তার, এবং সমাজে ধর্ম ও বর্নের ভিত্তিতে বিভাজনকে উস্কে দেয়া।
মার্কিন সমাজে ও রাজনীতিতে এই সব প্রবণতার উপস্থিতি দীর্ঘদিনের। কিন্ত একই সঙ্গে সমাজে এই ধরণের প্রবণতার বিরুদ্ধে সব সময়ই প্রতিরোধ উপস্থিত থেকেছে। গত কয়েক মাসের ঘটনাবলি, বিশেষত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেয়া পদক্ষেপসমূহের গুরুত্ব ও তার পথরেখা বুঝতে হলে সমাজে বিরাজমান এই সব প্রবণতা এবং সেগুলোর বিপরীতে অগ্রগতির বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় আড়াইশো বছরের ইতিহাস বিবেচনা করলে দেখা যাবে সমাজে বিভিন্ন কারণে বিভক্তি থেকেছে এবং সেই বিভক্তিকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্র এই সব বিভাজন এবং অন্যায্য ব্যবস্থাকে বৈধতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। দাসত্বের আইনী বৈধতা, দেশের দক্ষিনাঞ্চলে পাবলিক লিঞ্চিং বা পিটিয়ে মারার ইতিহাস, কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী বংশোদ্ভূতদের বন্দী শিবিরে পাঠানোর ঘটনা তার প্রমাণ। আইন করেই ১৮৮২ সালে চীন থেকে দশ বছরের জন্যে অভিবাসন বন্ধে করে দেয়া হয়েছিলো, যা পরে আরো দশ বছর বাড়ানো হয়। ১৯৩০-এর দশকে চার লক্ষ মেক্সিকানকে আটক করে মেক্সিকোতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল এই যুক্তিতে যে তাঁরা ‘মার্কিনিদের’ চাকুরি নিয়ে নিচ্ছেন। সমাজে এক সময় ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের বিষয়ে যে ঘৃনা এবং বিদ্বেষ উপস্থিত ছিলো তাতে প্রমানিত হয় যে এই সমাজে যাদেরকে ‘বহিরাগত’ বলে চিহ্নিত করা হয় তাঁদেরকে গ্রহণের ক্ষেত্রে সব সময়ই ইতিবাচক মনোভাব ছিলো না; একই বিষয় আমরা চিহ্নিত করতে পারি আইরিশ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমাজের মনোভাবের ভেতরেও। কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার, এমনকি ভোটাধিকারের অনুপস্থিতি; নারীদের সমানাধিকারের প্রশ্নকে অবজ্ঞা করা এই সবই স্মরণ করিয়ে দেয় যে নাগরিকের অধিকারের এবং সমতার সংগ্রামের ইতিহাস একরৈখিক নয়।
একদিকে যেমন আমরা এই ধরণের প্রবণতা এবং আইনী ব্যবস্থা দেখতে পাই তেমনি দেখতে পাই যে সমাজে ও রাজনীতিতে এর বিরুদ্ধে মনোভাব । সংবিধানের ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনী – যা দাসত্বের অবসান ঘটিয়েছে, কৃষ্ণাঙ্গদের সমান নাগরিকের মর্যাদা দিয়েছে এবং তাঁদের ভোটাধিকারের আইনী ব্যবস্থা করেছে – সেগুলো প্রমাণ করে যে সমাজে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় শক্তি আছে; আবার তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা এবং ব্যর্থতা স্মরণ করিয়ে দেয় যে কেবল আইনের শক্তিই যথেষ্ট নয়। দেশের সংবিধান প্রণেতারা ধর্ম এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে দেয়াল তৈরি করে ছিলেন তার পটভূমি যাই হোক, তা যে সব ধর্মের মানুষের জন্যেই রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে তা উপলব্ধি করা দরকার।
রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা থেকে অভিবাসনকে বিচ্ছিন্ন করার উপায় নেই। যে শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী এখন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে চিহ্নিত তাঁদের ইতিহাসও অভিবাসনের ইতিহাস। সেটি যে প্রীতিকর নয় সেটাও জ্ঞাত এবং আলোচিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দেশে অভিবাসন কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ‘অভিবাসীদেরই দেশ’ সেটি স্বীকৃত হয়েছে, একে চিহ্নিত করা হয়েছে ‘মেল্টিং পট’ বলে। অর্থনীতি, শিক্ষা, গবেষণা, সমাজ কল্যাণ এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে অভিবাসীদের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বীকৃতি লাভ করেছে। মার্কিন সমাজ বলতে বহুজাতিক, বহুসাংস্কৃতিক একটি জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। এ দেশে ‘কমিউনিটি’ বলতে যা বোঝায় তা কেবল এক ভাষার, এক ধর্মের, এক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ নয় – এই বোধ এবং বাস্তবতা ধীরে ধীরে হলেও গৃহীত হয়েছে এবং তার প্রকাশ আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে।
উগ্র চরমপন্থা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এক লজ্জ্বাজনক বাস্তবতা। এদেশে উগ্র শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের উত্থান ও উপস্থিতির ইতিহাস পুরনো। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হচ্ছে কু ক্লাক্স ক্ল্যান (কেকেকে)। ১৮৬০ এর দশকে এর প্রথম প্রকাশ ঘটে, দ্বিতীয়বার এই গোষ্ঠীর শক্তি ও উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১৫ সালের দিকে, তৃতীয় দফায় এই গোষ্ঠী সকলের মনোযোগ আকর্ষন করে ১৯৫০ এর দিকে। যদিও একে একটি সংগঠন বলেই মনে হয় আসলে এঁদের বিভিন্ন ধরণের সংগঠন রয়েছে। উগ্রপন্থীরা মিলিশিয়া গঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং সমাজের বহুত্ববাদীতাকে চ্যালেঞ্জ করে এসেছে গোড়া থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ‘সিলভার শার্ট লিজিয়ন’ এবং ‘ক্রিশ্চিয়ান রাইট’ নামের সংগঠন বিকশিত হয়, ১৯৫০ এর দশকে আমরা দেখতে পাই ‘ক্যালিফোর্নিয়া রেঞ্জার’, ‘মিনিটম্যান’ এর উত্থান এবং ১৯৮০ এর দশকে আসে ‘ক্রিশ্চিয়ান প্যাট্রিয়ট ডিফেন্স লীগ’, ‘টেক্সাস ইমারজেন্সি রিজার্ভ’, এবং ‘হোয়াইট প্যাট্রিয়ট পার্টি’। ১৯৯০ এর দশকে এই ধরণের গোষ্ঠীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। সেই সময়েই আমার একাধিক ঘটনা দেখতে পাই যার মধ্যে ওকলাহোমাতে ফেডারেল বিল্ডিং-এ টিমোথি ম্যাকভেই’র বোমা বিস্ফোরন গুরুত্বপূর্ণ।
শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী সহিংস গোষ্ঠীগুলোর বিকাশের পাশপাশি আমরা দেখাতে পাই যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্ত তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে মার্কিন সমাজের ভেতরে থেকে প্রতিরোধের একটি ধারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১৯৫৪ সালে ব্রাউন বনাম বোর্ড অব এডুকেশনের মামলা থেকে শুরু করে ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন জনসন কর্তৃক সিভিল রাইটস এ্যাক্টে স্বাক্ষর করা পর্যন্ত চৌদ্দ বছরে ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দেয় যে জনসমাজের বা সিভিল সোসাইটির নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায় ও তা রক্ষার একটি শক্তিশালী ধারা এই দেশে বিরাজমান। এই সংগ্রামের অংশীদার সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই – ১৯১০ সালে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেন্ট অব কালারড পিপল (এনএএসিপি), ১৯২০ সালে এমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (এসিএলইউ), ১৯২৮ সালে দি লিগ অব ইউনাইটেড ল্যাটিন আমেরিকান সিটিজেনস (লুলাক), ১৯৩৯ সালে লিগেল ডিফেন্স ফান্ড (এলডিএফ), ১৯৬৬ সালে ন্যাশনাল অর্গানাইজেশ ফর উইমেন (নাউ) – নাগরিকের অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আইনী লড়াই চালিয়েছে, জনসচেতনতা তৈরি করেছে, গণসম্পৃক্ত আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। এইসব আন্দোলনের চেহারা হচ্ছে বহুবর্ণের, বহু ধর্মের । একইভাবে ১৯৭০-এর দশকে ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সেটি কোনো গোষ্ঠীর নয়, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের নয়। ১৯৭১ সালে থেকে বর্ণবাদ, অভিবাসীদের অধিকার এবং হেইট ক্রাইমের বিরুদ্ধে সাদার্ন পভার্টি ল সেন্টার (এসপিএলসি)-এর কাজ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এসব কেবল যে গত শতাব্দির বিষয় তা নয় – ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বরের পরে দেশে হেইট ক্রাইমের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের অবস্থানও স্মরণ করা দরকার।
মার্কিন সমাজের ইতিহাস থেকে আমার দেখতে পাই যে, মার্কিন সমাজে উগ্রপন্থার ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষায় তিনটি বিষয় কাজ করেছে। এগুলো হচ্ছে প্রথমত মার্কিন প্রশাসনিক ব্যবস্থা – রাষ্ট্রের যে তিনটি প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে ভারসাম্য যাকে আমার চেক এ্যান্ড ব্যালেন্স বলে বর্ণনা করি; নির্বাহী বিভাগ (প্রেসিডেন্ট), আইন প্রনয়নকারী বিভাগ (কংগ্রেস) এবং বিচার বিভাগ (আদালত)-এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত । নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে অন্য দুই বিভাগ সব সময় সক্রিয় থেকেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে প্রশাসনের নিরপক্ষেতা – অর্থাৎ প্রশাসনে কর্মরতদের পেশাদারীত্ব। তৃতীয়ত হচ্ছে জনসমাজ বা সিভিল সোসাইটির শক্তিশালী ভূমিকা, যা এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কার্যকর থেকেছে । এর বাইরেই তার প্রকাশ ঘটেছে যেমন অকুপাই ওয়ালষ্ট্রীট আন্দোলন। তবে জনসমাজের সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে গণমাধ্যম – সরকার, রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিবিদদের জবাবদিহির ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অসামান্য।
তবে ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম বিবেচনার ক্ষেত্রে এটা উল্লেখ করা দরকার যে, আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। ভিন্নতার দিক পাঁচটি । প্রথমত সমাজে অসহিষ্ণুতা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে সাদার্ন পভার্টি ল সেন্টারের দেয়া হিসেব মতে দেশে মোট হেইট গ্রুপের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯শ ১৭টি, একই সময়ে আমরা মুসলিম বিরোধী গোষ্ঠীর সংখ্যা তিনগুন বাড়তে দেখেছি – ২০১৫ সালে ৩৪টি থেকে ২০১৬ সালে ১শ একটি’তে। শুধু তাই নয়, এই অসহিষ্ণুতার একটি বৈশ্বিক দিকও আছে। ইউরোপসহ অন্যত্রও আমরা একই প্রবনতা লক্ষ্য করছি। দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে অসহিষ্ণুতা এখন মূল ধারায় বিশেষত প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে কেবল জায়গাই করে নিয়েছে নয় তাঁদের এক ধরণের পক্ষপাতও লক্ষ করা যাচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা অতীতে সমাজের ফ্রিঞ্জ বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বলে বিবেচিত হত। কিন্ত এবারের নির্বাচনী প্রচারণা এবং পরে প্রশাসনে ব্রেইটবার্ট ওয়েব সাইটের লোকজনের বিশেষত স্টিভ বেনানের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে এই প্রশাসনের রাজনৈতিক এজেন্ডা তাঁদের দ্বারাই নির্ধারিত হচ্ছে। এটি ইতিমধ্যেই উগ্র দক্ষিনপন্থীদের জন্যে এক ধরণের উৎসাহ হিসেবে কাজ করেছে। একাধিক ভারতীয় বংশোদ্ভুত মার্কিন নাগরিককে হত্যা, ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের সেন্টার ও সেমেটারি এবং বিভিন্ন মসজিদে হামলার পর হোয়াইট হাউসের নিরবতা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয়ত কংগ্রেসে রিপাবলিকান দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নয়, রিপাবলিকান দলের সদস্যরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে এখনও সুস্পষ্টভাবে ভিন্নমত প্রকাশে অনীহ বলেই প্রতীয়ামান। চতুর্থত ট্রাম্পের কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের একাধিক বক্তৃতা এবং কর্মকান্ডে এটাই দেখা যাচ্ছে যে তিনি কর্তৃত্ববাদী নেতাদের কেবল পছন্দই করেন না তিনি নিজেও সেইভাবেই দেশ চালানোয় উৎসাহী। পঞ্চম বিষয়টি হচ্ছে রাষ্ট্র কাঠামো প্রশ্নে এই প্রশাসনের নীতিগত অবস্থান। স্টিভ বেনন কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল এ্যকশান কনফারেন্সে বলেছেন তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে ‘প্রশাসনিক রাষ্ট্র ভেঙ্গে ফেলা’ (ডি-কনশট্রাকশান অব এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টেট)। যার অর্থ হচ্ছে এতদিন ধরে গড়ে ওঠা ব্যবস্থাকে তারা অকার্যকর করে ফেলতে চান, যা প্রকারান্তরে ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে নির্বাহী বিভাগকে শক্তিশালী করে তুলবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরণের নির্বাহী আদেশ সেই দিকেই ইঙ্গিত দেয়। আর তা যে কোনো কারো জন্যেই উদ্বেগের।
২। ট্রাম্পের পররাষ্ট্র নীতি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্র নীতি কী? অস্থিতিশীল বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক কি সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে? যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে দীর্ঘ যুদ্ধের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বা তার মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্র মন্ত্রী রেক্স টিলারসনের কি কোনো বক্তব্য দিয়েছেন? প্রতিবেশি মেক্সিকোর সঙ্গে সীমান্ত দেয়াল তোলা ছাড়া লাতিন আমেরিকা বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের কি কোন অবস্থান রয়েছে?
আপাতদৃষ্টে এই সব প্রশ্নকে সরল, এমন কি অতি সরল বলে মনে হলেও এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর আসলেই পাওয়া যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পয়তাল্লিশ দিন পার হয়ে গেলেও এবং কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে এক ঘন্টার বক্তৃতা দেয়া স্বত্বেও এই সব প্রশ্নের সরকারী কোন উত্তর নেই। উত্তর হিসেবে গণমাধ্যমে যা পাওয়া যাচ্ছে তা বিশ্লেষকদের ধারণা বা অনুমান, বড়জোর ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার সময়ে দেয়া বক্তব্যেরই পরিবর্ধিত সংস্করণ। নিকট অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে কারোই স্মরণে আসেনা। কংগ্রেসে দেয়া ভাষনে ট্রাম্প যখন বলেন ‘আমার কাজ পৃথিবীকে প্রতিনিধিত্ব করা নয়, আমার কাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করা’ তখন বোঝা যায় যে তিনি নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় যে আইসোলেসানিস্ট পলিসি বা ‘একলা চলার নীতি’র কথা বলেছিলেন সেটাই পুনর্ব্যক্ত করলেন। কিন্ত তার কর্মকাঠামো কী হবে সেটার কোনো ইঙ্গিত এই বক্তৃতায় পাওয়া যায়না। শুধু তাই নয়, ২০ জানুয়ারির পর থেকে ট্রাম্প এবং তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরা পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যও দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিজের অবস্থানের ক্ষেত্রেও এই স্ব-বিরোধীতা লক্ষ্য করা গেছে।
বৈশ্বিক রাজনীতিতে কোনো দেশের সুস্পষ্ট নীতি ও অবস্থানের যেমন প্রভাব থাকে, তেমনি তার অনুপস্থিতিরও প্রভাব পড়ে। এটি বিশেষ করে সেই সব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে শক্তিশালী। সেই দিক থেকে আমাদের প্রথমেই দেখা দরকার যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কি – বৈশ্বিক জিডিপির ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের, তার পরে আছে চীন যার অংশ হচ্ছে ১৫ দশমিক ১ শতাংশ। সামরিক শক্তির দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান শীর্ষে, মোট বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে ৫৯৬ বিলিয়ন ডলার যা পরবর্তী সাতটি দেশ – চীন, সৌদি আরব, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ভারত, ফ্রান্স এবং জাপানের সম্মিলিত ব্যয় – ৫৬৭ বিলিয়নের চেয়ে বেশি। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে পলিটিকো’তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে ডেভিড ভাইন দেখিয়েছিলেন যে পৃথিবীর ৭০টি দেশে ছোট বড় মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি আছে আটশো। প্রত্যক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্র একাধিক সংঘাতে যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে আফগানিস্তানের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সংযুক্তি ইতিহাসের দীর্ঘতম। ইরাকেও যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা উপস্থিত আছে। সরকারী হিসেবে সাড়ে ১৩ হাজার মার্কিন সৈন্য ‘ওয়ার জোন’ বা যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে। উল্লেখ্য যে দক্ষিন এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ৯ হাজার পাঁচশোর বেশি সৈন্য রয়েছে। বৈশ্বিক রাজনীতিতে যুক্ত্ররাষ্ট্রের প্রভাব আগের তুলনায় হ্রাস পেলেই জাতিসংঘ সহ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তার প্রভাব এখনও অন্যদের চেয়ে বেশি, আর্থিক কারণে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের যুক্তরাষ্ট্র-নির্ভরতাও বেশি। এর বাইরেও পররাষ্ট্র নীতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যুক্তরাষ্ট্র কোন ধরণের জোটের সঙ্গে যুক্ত, কারা তাঁর মিত্র, অন্য দেশগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি। পররাষ্ট্র নীতি যেমন একটি দেশের প্রতিরক্ষা নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তেমনি সংশ্লিষ্ট তার বানিজ্য নীতির সঙ্গেও।
এতটা গুরুত্বপূর্ন হওয়া স্বত্বেও পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের নীরবতা বিস্ময়কর। ফলে আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে আকার ইঙ্গিতের ওপরেই। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে সাতটি মুসলিম প্রধান দেশ থেকে যাতায়তের ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ আদালতে স্থগিত হয়ে গেলেও তা সংশোধিত ভাবে আবারও জারি করা হয়েছে সোমবার যাতে ইরাককে তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপে স্পষ্ট যে ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসন বৈরিতার পথই বেছে নিয়েছেন। উপরন্ত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এবং সহিংস উগ্রপন্থাকে ‘র্যাডিকাল ইসলামিক টেরোরিজম’ বলে চিহ্নিত করার মাধ্যমে তিনি মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এক ধরণের দূরত্বই শুধু তৈরি করছেন না, সন্ত্রাসীদের হাতে প্রচারের অস্ত্রও তুলে দিচ্ছেন। ২০১৭ সালে প্রতিশ্রুতির চেয়ে কম শরনার্থী গ্রহণের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিকভাবে যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেগুলো পুনর্বিবেচনার নামান্তর, একই ভাবে আমার জলবায়ু চুক্তির বিষয়টিকেও দেখতে পারি কেননা জলবায়ূ বিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের নির্বাহী সেক্রেটারি প্যাট্রিসিয়া এস্পিনোজা জানিয়েছেন যে তিনি রেক্স টিলারসনের সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়েছিলেন কিন্ত তাঁর পক্ষ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) থেকে প্রত্যাহার কেবল বাণিজ্যিক জাতীয়তাবাদের ইঙ্গিত নয়, অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র তাঁর প্রভাব বিস্তারের জন্যে সফট পাওয়ারের চেয়ে হার্ড পাওয়ারের দিকেই ঝুকে পড়ছে বলে মনে হয়।
এসব ঘটনার পাশাপাশি আমার দেখি যে নির্বাচনের পর এখন পর্যন্ত পররাষ্ট্র দফতর কোন প্রেস ব্রিফিং করেনি, যা হওয়ার কথা প্রতিদিন। ১৯৫০ সালের পর এত দীর্ঘ সময় ব্রিফিং বন্ধ ছিলোনা। গত সপ্তাহে পররাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন ছিলেন অনুপস্থিত। যা থেকে বোঝা যায় যে মানবাধিকারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এত দিনের অবস্থানে সম্ভবত পরিবর্তন আসছে; এই বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসন খুব বেশি উৎসাহী নয় বলেই ধারণা। রাশিয়া বা এই ধরণের দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা বলার পাশাপাশি মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনার জায়গা সীমিত হয়ে আসে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমন ধারণা দেয়া হচ্ছে যে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল ত্যাগের কথা সক্রিয়ভাবে ভাবা হচ্ছে। জাতিসংঘের প্রধান আন্তনিও গুতেরাসের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিলারসনের কোনো বৈঠক হয় নি; গত মাসে জার্মানির বন শহরে জি-২০’র বৈঠকের পাশাপাশি তাঁদের বৈঠকের প্রস্তাব টিলারসনের পক্ষ থেকেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। জেনেভা থেকে বিবিসি সংবাদদাতা ইমোগেন ফকস ২৭ ফেব্রুয়ারি এক প্রতিবেদনে জানান যে কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের রাজধানী বলে বিবেচিত জেনেভায় মার্কিন কূটনীতিকরা অনুপস্থিত।
ফলে কূটনীতি ট্রাম্প প্রশাসনের অগ্রাধিকার তালিকায় আছে এমন মনে হয় না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কংগ্রেসে যে বাজেট প্রস্তাব পাঠাবেন তাতে পররাষ্ট্র দফতর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ যেমন ইউএসএআইডি’র বাজেট কমানো হবে কমপক্ষে তিরিশ শতাংশ, অন্যপক্ষে প্রতিরক্ষা বাজটে বাড়বে ১০ শতাংশ – কমপক্ষে ৫৪ বিলিয়ন ডলার। কূটনীতি, মানবিক সাহায্য এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের চেয়ে শক্তি প্রদর্শনই এই প্রশাসনের নীতি বলে আমরা ধরে নিতে পারি। একদিকে একলা চল বলে বিশের বহুজাতিক সংস্থা গুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্র দূরে সরে থাকছে অন্যদিকে সামরিক শক্তি আরো বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতির ক্ষেত্রে এই শুন্যতার একটা বড় কারণ হচ্ছে ট্রাম্পের রাশিয়া বিষয়ক জটিলতা। রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর নির্বাচনী প্রচার দলের যোগাযোগের বিষয়টি এখন কেবল সন্দেহের বিষয়ে সীমিত নেই; ইতিমধ্যেই আইনমন্ত্রী জেফ সেশন থেকে অনেকেরই রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে। এই নিয়ে রিপবালিকান পার্টির কোনো কোনো নেতা আনুষ্ঠানিক তদন্তের দাবিতে ডেমোক্রেটদের সুরে কথা বলতে শুরু করেছেন। কংগ্রেসের সামনে এই নিয়ে সেশনের বক্তব্য ‘মিথ্যাচার’ কিনা সেই প্রশ্নও উঠছে। এই সব বিতর্কের মধ্যেই ট্রাম্প কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামার বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছেন, যা এমন কি এফবিআই প্রধান পর্যন্ত সঠিক নয় বলেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক শুন্যতার প্রতিক্রিয়া কেবল যে যুক্তরাষ্ট্রের ওপরেই পড়ছে তা নয়। তাঁর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে অন্য দেশগুলোর ওপরেও ন্যাটো বিষয়ক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ও অবস্থানের কারণে ইউরোপের দেশগুলোই কেবল সংশয়ে আছে তা নয়, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো তাঁদের নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত। কেননা ন্যাটো এবং যুক্ত্ররাষ্ট্রের দুর্বল অবস্থানের সুযোগে রাশিয়া তাঁদের ওপরে চাপ সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে। অন্যদিকে এশিয়ায় চীনের প্রভাব বলয় বৃদ্ধির যে সুযোগ তৈরি হয়েছে তা কেবল অর্থনৈতিক নয়, সামরিকও বটে। বিভিন্ন অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি বা সংশ্লিষ্টতা যে সব সময়ই ইতিবাচক হয়েছে এমন যেমন দাবী করা যাবেনা, তেমনি কোনে অঞ্চলে এককভাবে বড় একটি শক্তির – আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক – একচ্ছত্র আধিপত্যও ছোট দেশগুলোর জন্যে কোনো ইতিবাচক কিছু নয় সেটাও মনে রাখা দরকার।
বৈশ্বিক শক্তিগুলোর মধ্যে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রভাব বলয় বাড়ানোর যে প্রতিযোগিতা চলছে সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে সরিয়ে রাখতে চায় কিনা সেটাই বোঝার জন্যে দরকার একটি সুস্পষ্ট পররাষ্ট্র নীতি যা ট্রাম্প প্রশাসন এখনও তুলে ধরেনি। এই শুন্যতার ফলে আঞ্চলিক শক্তিগুলো নিজ নিজ অঞ্চলে তাঁদের আধিপত্য বাড়াতে পদক্ষেপ নেবে। ইতিমধ্যেই আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে তার লক্ষন দেখতে পাচ্ছি। সিরিয়াকে কেন্দ্র করে ইরান-তুরস্ক-সৌদি আরবের আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। দক্ষিন এশিয়ায় চীন ও ভারতের দ্বন্দ্ব এবং রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সহজেই চোখে পড়ে। আফগানিস্তানে সম্প্রতি চীনা সৈন্যদের উপস্থিতির যে খবর বেরিয়েছে তাকে চীন ‘মহড়ার অংশ’ বলে বর্ণনা করলেও অনেকেই একে দক্ষিন এশিয়ায় প্রভাব বাড়ানোর চীনের বর্তমান নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন বলেই মনে করেন। অতীতে যুক্ত্ররাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগে ভারত এই অঞ্চলে বিশেষত প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও নেপালের ওপরে রাজনৈতিক এবং সামরিক আধিপত্য বৃদ্ধির জন্যে উদযোগী হয়ে উঠেছে। বৈশ্বিক রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য না থাকলে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর পক্ষে এই ধরণের চাপ সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয় ।
প্রথম আলো’তে প্রকাশিত, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৭
This post has already been read 44 times!