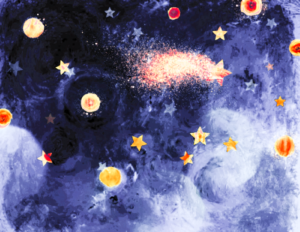দীর্ঘ সময় ধরে চলা স্বাধিকার আন্দোলনের ফলে একাত্তরে যে দেশ আমরা পেয়েছি, তার পরিচালন পদ্ধতি নির্ণয় করতে গিয়ে আমাদের বেগ পাওয়ার কথা ছিল না। আমাদের আন্দোলনের পেছনে যেসব কারণ ছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সেসবের উত্তরণের ব্যবস্থা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় থাকবে— এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোথায় যেন বাদ সেধেছে আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনীতি। এ-যাবত্কালে দেশে যা কিছু হয়েছে, তার সবই গণতন্ত্রায়ণের নামে। অথচ প্রকৃত গণতন্ত্রের উপস্থিতিই সেভাবে ছিল না বলা চলে। বলা হয়ে থাকে, নব্বই-পরবর্তী সময়ে এ দেশে গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে দেশ নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে শাসিত হয়েছে। কিন্তু আসলেই কি তাই? আমরা কি নব্বই-পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি? তাহলে এখন সাংবিধানিক নিয়ম রক্ষার নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে না পারা এবং এরই ফলে দীর্ঘ সময়ের সহিংসতা, প্রাণহানি— কেন? এসবের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের শাসন ব্যবস্থার গোড়ায় দৃষ্টি দিতে হবে।
বর্তমানে আমরা দেখছি, গণতন্ত্রের নামে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে মত্ত। অথচ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সব রকমের সুযোগ এবং সেই অপরিসীম ক্ষমতা চালু রাখার সব রকমের বৈধতা দিয়েছে আমাদের সংবিধান। যদি সংবিধানসম্মত বলে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে কারো কোনো কাজের জবাবদিহিতার দরকার হয় না। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র নিজেই যেখানে ক্ষমতা বিন্যাসে চরম অসমতা তৈরি করেছে, যেখানে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে হতে তার সীমা ছাড়িয়েছে, সেখানে এই সংবিধান তার বর্তমান রূপ নিয়ে বলবৎ থাকা অবস্থায় আমরা এ রকম রাজনীতিই দেখব। এটি আমাদের সংবিধানের অন্তর্নিহিত ত্রুটি। তাই বর্তমান সংবিধান বলবৎ থাকা অবস্থায় যে ধরনের ব্যবস্থার কথাই বলা হোক না কেন, তা ফলপ্রসূ হবে না। তাই সবার আগে চাই সংবিধানের গণতান্ত্রিকীকরণ।
এখন দেখা যাক, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল, সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন আমাদের সংবিধানে হয়েছে কিনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রক্ষমতা যখন থেকে ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে পরিণত হলো, তখন থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতা কাঠামো গড়ে উঠতে লাগল। এই ক্ষমতার রাশ টানা সম্ভব ছিল সংবিধানে ক্ষমতা পৃথকীকরণ, সীমা নির্ধারণ এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিধিবিধান সংযোজনের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা সে পথে গেলেন না। উল্টো সংবিধানে সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলেন। ফল যা হওয়ার তা-ই হয়েছে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতাচর্চা অব্যাহত থেকেছে এবং ক্রমে তা শক্তিশালী ধারণায় রূপ নিয়েছে। এ ধারণার বাইরে যে কিছু থাকতে পারে, আমরা এখন তা-ই ভাবতে পারছি না। কখনো কখনো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রচর্চা না থাকার কথা বলা হয়। যদি আমাদের সংবিধানের ‘ক্ষমতা বিন্যাস’ কেউ সঠিকভাবে পরখ করে দেখেন, তাহলে বুঝবেন— আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা থাকা সম্ভব নয়। আমাদের সংবিধান সেই চর্চা হতে দেবে না। সংবিধান মেনে রাষ্ট্রের সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে একভাবে যদি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে সেখানে অন্যের মতামত শোনার সুযোগ নেই। দরকারও পড়ে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে দলীয় প্রধানের হাতে যে পরিমাণ ক্ষমতা আমাদের সংবিধান ন্যস্ত করেছে, তাতে সাংবিধানিক শাসন কথাটি উপহাসে পরিণত হয়েছে।
বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে— ভোটারবিহীন, অংশগ্রহণবিহীন ২০১৪-এর ৫ জানুয়ারির নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থা বিলোপ, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে দমন-পীড়ন ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, নব্বই-পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার নামে যে তথাকথিত নৈর্বাচনিক যে তন্ত্র দেশে চালু হয়েছে, তা সংবিধানের নিয়ম রক্ষা করেই। যদি বর্তমান সংবিধান মেনে কেউ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চান, তাহলে তিনি ক্রমে স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠতে বাধ্য। ব্যবস্থাটাই সে রকমভাবে করা আছে। দল পরিবর্তন হলেও শাসনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটির কারণে ফলাফল একই হতে বাধ্য। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন যদি সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হতো আর যদি সেখানে বিএনপি জোট নির্বাচনে জয় লাভ করত, তবে এখন আমরা আওয়ামী লীগকে জ্বালাও-পোড়াও করতে দেখতাম। উছিলার অভাব হতো না। আমাদের দেশে সংবিধানের দোহাই দিয়ে যে পরিমাণ নিবর্তনমূলক আইন করা হয়েছে, তার প্রয়োগ শুরু করলেই বিরুদ্ধ মত দমন করা যায় এবং সেটির অজুহাতে দেশকে সহিংস করে তোলা খুবই সহজ। প্রচলিত আইনগুলোর চরিত্র এতটাই স্বৈরতান্ত্রিক যে, এর ব্যবহার যেকোনো সরকারকে স্বৈরাচার বানিয়ে তুলতে সক্ষম। পরিহাসের বিষয়, সংবিধানের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীন প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।’ এখন ১৫২ নং অনুচ্ছেদ এ ‘আইন’ এবং ‘প্রচলিত আইন’-এর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে— ‘আইন’ অর্থ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোনো প্রথা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ সংবিধান প্রবর্তনের আগে থেকে যেসব আইন ব্রিটিশ ভারত কিংবা পাকিস্তান আমলে প্রচলিত ছিল, তা বহাল থাকছে। যেসব আইন গণবিরোধী কিংবা ঔপনিবেশিক, যা কিনা আমাদের স্বাধিকারের আন্দোলন সংগ্রামকে দমন-পীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয়ে এসেছে, তার সবই বলবৎ থাকল এ সংবিধানের মাধ্যমে। এমন হাজার হাজার ঔপনিবেশিক আইন তার পুরনো চরিত্রসমেত এখনো বলবৎ আছে। এভাবেই ব্রিটিশ আর পাকিস্তানের ভূত তাড়া করে ফেরে আমাদের প্রতি মুহূর্তে। সার্বক্ষণিকভাবে আমরা নানা প্রকার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই, সেটি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন। আর সেসব আইনের মূল ভিত্তি এখনো সেই ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তানি শাসকদের দমন-পীড়নমূলক আইন। এসব আদিভৌতিক আইন অনেক ক্ষেত্রে নতুন মোড়কে হাজির হয়েছে, যেমন— বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা পেয়েছি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, দ্রুত বিচার আইন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনসহ ইত্যাকার নিবর্তনমূলক আইন, যার মূল উদ্দেশ্যই বিরুদ্ধ মত দমন।
দেখা যাচ্ছে, সংবিধানের অধিকাংশ বিধান একে অন্যের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। এ কারণে সেখানে মৌলিক অধিকারের যেসব স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তা মূলত অর্থহীন। জাতিসংঘের মৌলিক অধিকার সনদের প্রায় ১৭টি মৌলিক অধিকার আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তার পরও কেন মৌলিক অধিকার খর্ব হওয়ার মতো ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে? কেউ কেউ হয়তো বলবেন, আমাদের দেশে আইনের প্রয়োগ নেই। কথাটি একদিকে সত্যি, কিন্তু আমাদের সংবিধান এক্ষেত্রে কম ভূমিকা রাখছে না। যেমন ধরুন, বিশেষ ক্ষমতা আইনে নিবর্তনমূলক আটকের যে বিধান রাখা হয়েছে, তা বর্তমান সংবিধানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই। সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদে সাধারণ আইনে আটক ব্যক্তির জন্য চারটি রক্ষাকবচ থাকলেও নিবর্তনমূলক আইনে আটক ব্যক্তির জন্য তিনটি রক্ষাকবচ রাখা হয়েছে, যথা— ১. উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, ২. যথাসম্ভব শীঘ্র আটকের কারণ জানানো, ৩. আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার। তবে আটককৃত কোনো ব্যক্তি এ অধিকারগুলো ভোগ করতে পারে না। কেননা সংবিধানের ৩৩(৫) উপ-অনুচ্ছেদে একটি শর্ত জুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে, ‘তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি প্রকাশ জনস্বাথের্র বিরোধী বলে মনে হলে কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবেন।’ এখানে তথ্য অধিকার আইনও কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। শর্তটির কারণে ২ এবং ৩ নং অধিকার অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ কর্তৃপক্ষ তথ্যাদি প্রকাশ না করে শুধু আটকের কারণ জানালে আটককৃত ব্যক্তির পক্ষে আদালতে বক্তব্য পেশের সুযোগ থাকে না। এছাড়া এ আইনের ৮(২) উপধারা অনুসারে আটক ব্যক্তিকে আটকের কারণ জানাতে হবে ১৫ দিনের মধ্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ আইনে আটক ব্যক্তির তিনটি সাংবিধানিক রক্ষাকবচের দুটি অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়েছে এবং কেবল একটি অধিকার সে ভোগ করতে পারে। তা হলো, উপদেষ্টা পরিষদ-সংক্রান্ত। কিন্তু সেই অধিকারের প্রশ্ন আসে আটকের ছয় মাস পরে; তার আগে নয়। উপদেষ্টা পরিষদ একটা আধা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে, উপদেষ্টা পরিষদের সামনে আটককৃত ব্যক্তি কোনো আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন না। এটা কোনো আদালত হিসাবেও কাজ করে না আবার বন্দির বিচারও করে না। পরিষদ কেবল আটকাদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত আটকাদেশের বিষয়টি বিবেচনা করেন। ফলে এটি সরকারের নিবর্তনমূলক আটকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। তাছাড়া প্রত্যেক দেশে নিবর্তনমূলক আটকের একটি সর্বোচ্চ মেয়াদ থাকে, যেমন ভারতে এর মেয়াদ দুই বছর। কিন্তু আমাদের দেশে সে রকম কোনো বিধান নেই। ভারতে এ আইনের অধীনে একজন ব্যক্তিকে তিন মাস আর আমাদের দেশে ছয় মাস পর্যন্ত কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা যায়। উপরন্তু, অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতো সুনির্দিষ্ট করে বলে দেয়া নেই— কখন এ আইনের অধীনে কাউকে আটক করা যাবে না। লক্ষণীয়, বিশ্বের কোনো দেশেই নিবর্তনমূলক আইনকে সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা যায় না। আমাদের দেশে সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ মোতাবেক সংবিধানের ২৬ ও ৩৩ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান চালু করা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে সংবিধান নাগরিকের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিচ্ছে, সেই একই সংবিধান আবার নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে তা খর্ব করছে। এই স্ববিরোধিতা সংবিধানের প্রায় পুরো অবয়বে দেখা যায়।
আমরা যদি আমাদের সংবিধানের ক্ষমতা বিন্যাসের দিকে চোখ বুলাই, তাহলে দেখাতে পাব— সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এ বলা হয়েছে, ‘কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।’ মনে হতে পারে, রাষ্ট্রপতি নিজের ক্ষমতাবলে কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির দণ্ড ক্ষমা করে দিতে পারেন (অনুচ্ছেদ ৪৯), তিনি প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক (অনুচ্ছেদ ৬১), তিনি বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগদান করেন (অনুচ্ছেদ ৬৪, ৯৫)। কিন্তু কার্যত স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা সংবিধান তাকে দেয়নি। তিনি যা কিছু করেন, তার সবই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে। অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাও মূলত ছলচাতুরী। কেননা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষমতা মূলত সংসদ সদস্যদের। অনুচ্ছেদ ৫৬(৩) পড়লে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়, যেখানে বলা আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। তাহলে এখানে রাষ্ট্রপতির নিজের বিবেচনার সুযোগ কোথায়? বস্তুত রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তা উপহাসমাত্র। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বোধকরি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ে সবচেয়ে ভালো উক্তি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, ‘রাষ্ট্রপতির কেবল কবর জিয়ারত করার ক্ষমতা আছে সংবিধানমতে।’ কিন্তু আমরা দেখেছি, রাষ্ট্রপতির সত্যিকার অর্থে কবর জিয়ারতেরও ক্ষমতা নেই। এরই মধ্যে সাবেক একজন রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে কবর জিয়ারত করতে গিয়ে পদ হারিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, রাষ্ট্রপতির আসলে সেই ক্ষমতাও নেই।
জনগণের সঙ্গে সবচেয়ে বড় প্রতারণাটি বোধ হয় করা হয়েছে, তাদেরকে প্রজাতন্ত্রের মালিক আখ্যা দিয়ে। মূলত ৭(১) নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের মালিক হিসেবে জনগণের রাষ্ট্র পরিচালনার অংশীদার করার কথা লিখে রাখা ছাড়া তাদের অন্য কোনো ক্ষমতায়ন করা হয়নি। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান থাকলেও সেই জনপ্রতিনিধির অযোগ্যতা বা ব্যর্থতার কারণে তাকে প্রত্যাহারের কোনো ক্ষমতা জনগণের হাতে দেয়া হয়নি। সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজনৈতিক আনুগত্য হারালে কিংবা মারা না গেলে বা বিনা নোটিসে দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত থাকা ব্যতীত কোনো জনপ্রতিনিধির পদ শূন্য হওয়ার উপায় নেই। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে একজন সংসদ সদস্য সংবিধানের বদৌলতে নিমিষে দলীয় প্রধানের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ছেন। জনস্বার্থে যে প্রতিনিধির কাজ করার কথা, তিনি যদি জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করে থাকেন, তাহলেও তাকে অপসারণের কোনো ব্যবস্থা এ সংবিধানে নেই। এসব আলোচনার বিরুদ্ধে দলকানা বোদ্ধারা প্রায়ই বলেন, আগে নির্বাচিত হয়ে আসেন, তার পর বড় বড় কথা বলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় আপনি, আমি বা সাধারণ অর্থে সাধারণ মানুষ চাইলেই প্রার্থী হতে পারবেন কিনা কিংবা নিজের পছন্দমতো প্রার্থী নির্বাচন করার প্রকৃত কোনো সুযোগ আছে কিনা? করলেও সেই প্রার্থীর জয়লাভের কোনো সুযোগ আছে কিনা? যদি না-ই থাকে, তাহলে সংবিধান জনগণের কেমন ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে?
সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত আছে। সেসবের প্রাথমিক পাঠ করলে মনে হবে, সবই তো আছে, সমস্যা কোথায়? কিন্তু আমরা যদি ১৭টি মৌলিক অধিকার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখতে পাব, তার মধ্যে অন্তত ১৫টি অধিকার প্রচলিত আইনের হাতে বন্দি। ২৬ নং অনুচ্ছেদ পড়ে মনে হতে পারে, সংবিধান মৌলিক অধিকারকে নিরঙ্কুশ করেছে, কিন্তু দেখা যায়, ‘আইনের দৃষ্টিতে সব নাগরিক সমান’, ‘ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্র কারো প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবে না’ বা ‘প্রত্যেকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার আছে’— এ রকম কয়েকটি অধিকার ছাড়া বাকি সব গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রচলিত আইন, নৈতিকতা, জনস্বার্থে আরোপিত বিধি-নিষেধ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা বা বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ইত্যাকার শর্তাধীন করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রচলিত আইন বলতে আবার সেসব আইনকে বোঝানো হয়েছে, যা ঔপনিবেশিক আমল কিংবা পাকিস্তান আমল থেকে সংবিধানের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলবৎ আছে। যেসব আইন আমাদের মৌলিক অধিকার খর্ব করে বিধায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনা এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, সেই স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দিচ্ছে পুরনো শোষণ ও দমনমূলক আইন-কানুন! এ কোন স্বাধীনতা আমরা ভোগ করছি? এছাড়া যেসব শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে, তা কালে কালে ক্ষমতাসীনদের দমন-পীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয়ে এসেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধও পাল্টায়, আর তাই নৈতিকতার প্রশ্ন কোনো স্থির বিষয় নয়। জনস্বার্থ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা সবসময়ই বহুল ব্যবহূত মোক্ষম একটি অস্ত্র, যার মাধ্যমে যেকোনো সমালোচনা খতম করা যায়। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি বিধিতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কিংবা জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। এখন দেখার বিষয়, সেই ব্যাখ্যা এখনো আমাদের স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য কিনা? ব্রিটিশ প্রভুরা সাধারণ নাগরিকদের (নেটিভদের) যে দৃষ্টিতে দেখতেন, বর্তমান শাসকরা যদি সেই একই দৃষ্টিতে দেখেন, তাহলে ধরে নিতে হবে সেসব আইনি ব্যাখ্যা ঠিকই আছে। বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হলো কেন, তা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়। এটি পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত বিষয় এবং পররাষ্ট্রনীতিতে কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে স্থায়ী সুসম্পর্ক বলে কোনো কথা নেই। নিজ দেশের সুবিধার ভারসাম্যের ওপরই মূলত অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক কী রকম হবে, তা নির্ভর করে। মনে হতে পারে, এসব শর্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্গত বিষয়, কিন্তু তা নয়। তাছাড়া সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে উল্লিখিত মূলনীতিগুলো ৮(২) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালতের মাধ্যমে বলবেযাগ্য নয়, অর্থাৎ এসবের আইনগত কোনো ভিত্তি নেই।
সংবিধানের ৪৬ নং অনুচ্ছেদে দায়মুক্তির যে বিধান দেয়া হয়েছে, তা যদি বিবেচনায় নিই, তাহলে তৃতীয় ভাগে যেসব মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তা অসার মনে হবে। বাস্তবে হচ্ছেও তা-ই। এ বিধান সংযোজনের ফলে রাষ্ট্র নাগরিকদের প্রতি চরম অন্যায় করেও পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ বিধানের জোরে রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক গুম, খুন, অপহরণ, ক্রসফায়ার কিংবা কুইক রেন্টাল সবকিছুরই দায়মুক্তি দিয়ে আইন করতে পারে এবং তা বৈধ হবে। এই অসাংবিধানিক ক্ষমতা বলবৎ থাকলে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের আশ্বাস প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।
এত দিনকার সংবিধান নিয়ে আলোচনা মূলত বিদ্যমান সংবিধানকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে এর মধ্যে সমাধান খোঁজার চেষ্টা। কিন্তু যে সংবিধান নিজেই এতটা অগণতান্ত্রিক, সেখানে এর ভেতর গণতন্ত্র খুঁজতে গেলে কী পাওয়া যাবে, তার কিছু নমুনা এখানে আলোচনা করা হলো। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সত্যিকার একাত্তরের চেতনাকে ধারণ করে সংবিধানের অগণতান্ত্রিক বিধানগুলো বিলোপ করে একে গণতান্ত্রিকীকরণের বিষয়টি সামনে না আনলে চলমান রাজনৈতিক সংকটের স্থায়ী সমাধান বের করা সম্ভব হবে না। নব্বই-পরবর্তী সময় থেকে আজ অবধি শাসন ব্যবস্থার যে সংকট আমরা ঘনীভূত হতে দেখছি, তা মূলত সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট। তাই এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সংবিধানের গণতান্ত্রিক রূপান্তর ছাড়া উপায় নেই। সংবিধান নিয়ে কথা বলার সাংবিধানিক অধিকারও সংকুচিত হয়ে এসেছে নানাভাবে, সেই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়াও ভীষণভাবে জরুরি।
২২ ও ২৩শে জুন বনিকবার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত।
থাম্বনেইল সূত্রঃ লিঙ্ক