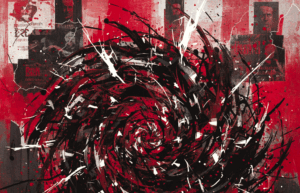This post has already been read 42 times!
দিনটি ছিল ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২, হটাৎ করে জ্বলে উঠেছিল রামুর তেরটি বৌদ্ধ মন্দির আর বেশ কিছু বাড়ী-দোকান। গৃহহীন ভয়ার্ত মানুষ সেদিন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচারের কথা স্মরণ করেছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহবল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নিজের চোখ-কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না- রামুতে এরকম কিছু ঘটতে পারে। শত বছরের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে যে শান্তির পরিবেশ রামুতে গড়ে উঠেছিল তা যেন এক রাতের আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। বিশ্বাসে চিড় ধরল সবার মনে। ফেসবুকে পবিত্র কোরআন অবমাননার অভিযোগে যে তাণ্ডবের শুরু তা রামুর গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে উখিয়া, টেকনাফ ও চট্টগ্রামের পটিয়াতেও।
সেদিনের সেই ভয়াল রাতের শেষে পোড়া ভিটে মাটির উপর উঠেছে সরকারী উদ্যেগে নতুন ঘর, কোথাওবা নির্মিত হয়েছে ইট-পাথরের নতুন বৌদ্ধ মন্দির। অনেক আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি জীবনে কখনো হয়ত পোড়া ভিটার উপর ইটের দালান নির্মাণ করতে পারতেন না- সরকারী উদ্যেগে সেটি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, তার মনের গহিনে কোথাও যেন অবিশ্বাস চিরতরে ছাপ ফেলে গেছে যা নতুন ইটের দালান প্রাপ্তির খুশীর নিচে চাপা পড়বে বলে মনে হয় না।
মন্দিরের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে- আমাদের তিনশ বছরের পুরনো কাঠের স্থাপনার জায়গায় আমরা ইটের দালান পেয়েছি। সেসবে নিয়মিতভাবে জনমানুষের যাতায়তও শুরু হয়েছে। এখন দেখার বিষয় হল- এই দালানগুলো কতদিনে মন্দির হয়ে উঠতে পারে? পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার ভয় আর শঙ্কা কুরে কুরে খেয়েছে এই শান্ত জনপদের মানুষগুলোকে। এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি, রামুর শান্তিপ্রিয় মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কারণে রামু সবার কাছে অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়েছিল- তা এক নিমিষে ধ্বংস হয়ে গেল।
এত গেল রামুর স্থানীয় মানুষদের মনোজগতের চালচিত্র। এই সহিংসতার পর থেকে যে প্রশ্নটি সবার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল- তা হল- পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসন সুযোগ থাকতেও কেন কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিলেন না? ঘটনার পরপর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে অনেকগুলো স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রকাশ পেয়েছে- তাতে দেখা গেছে কোথাও কোথাও আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতেই সহিংস হামলা হয়েছে। তারা সে হামলা ঠেকালেন না কেন? অনেকে উপরের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না থাকার কথা বলেছেন বিভিন্ন তদন্ত কমিটির নিকট। আমাদের বোঝা দরকার- এটি কি কেবলই প্রশাসনিক জটিলতার বিষয় না আরও বেশী কিছু? ধীরে ধীরে আমাদের পুলিশ ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার উত্তান ঘটেছে কিনা? বা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ আগেই প্রোথিত আছে সেটি ক্রমশ মূল চরিত্র হিসেবে জায়গা করে নিচ্ছে কিনা? স্থানীয় প্রতিনিধিদের যে হতাশাজনক ভূমিকা ছিল তারও চুলচেরা নির্মোহ বিচার বিশ্লেষণ হওয়া দরকার ছিল। অভিযোগের তীর তাদের দিকেই বেশী ছিল এবং এখনো আছে। তৎকালীন স্থানীয় সংসদ সদস্য ঘটনাস্থলে সহিংসতা শুরু হওয়ার পূর্বে থেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সহিংসতা শুরুর সাথে সাথে তিনি সদলবলে রামু থেকে কক্সবাজার শহরে চলে যান। এক ব্যক্তিগত আলাপে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম- তিনি কেন চলে গিয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন- তিনি ভয় পেয়েছিলেন এবং বুঝে উঠতে পারছিলেন না কি করবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের উত্তরাধিকারী ও জনপ্রতিনিধি কিসের ভয়ে ভীত ছিলেন- তা আজো বুঝে উঠতে পারিনি। পুরো ব্যপারটাই এখনো কেমন যেন ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে এবং পুলিশি তদন্তে রোহিঙ্গাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠে এসেছে- এটি নিয়েও বিস্তারিত তদন্ত হয়নি। পাশের দেশ থেকে সহিংসতার কারণে আমাদের দেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা সত্যিকার অর্থে কতটা জড়িত ছিলেন, না উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা সেটা জানা যায়নি এখনো। রোহিঙ্গারা তাদের জন্য নির্মিত অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে এদেশের মানুষের সাথে মিশে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন প্রকার অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছেন বলে স্থানিয়ভাবে অভিযোগ আছে। কিন্তু তাই বলে তারা উগ্র ধর্মীয় অনুভূতির কারণে এত বড় আকারের সহিংসতার পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করতে পারেন- এটি ভাবতে এখনো কষ্ট হচ্ছে। মিয়ানমারে রাখাইন বৌদ্ধদের সাথে রোহিঙ্গাদের যে জাতিগত সংঘাত তাকে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো বরাবরেই ধর্মীয় সহিংসতা বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। রাখাইনরা জাতিগতভাবে বৌদ্ধ বলে “জাতিগত ও ধর্মীয়” এ দুটি বিষয়কে অনেকেই আলাদা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মনে এই কারণে ক্রোধ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু, সেটি তারা বাঙালী বৌদ্ধদের উপর সহিংস হামলা করে, তাদের বাড়ী-দোকান ও বৌদ্ধ মন্দির জ্বালিয়ে প্রতিশোধ নেবেন- এটিও যুক্তির বিচারে ধোপে টেকে না। স্থানীয়দের পরিকল্পনা অনুযায়ী রোহিঙ্গারা সহিংসতায় ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তারা মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন এমনটি ভাবা সঠিক হবে না।
এরই সাথে আলোচনায় আসে- সমগ্র কক্সবাজার এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা জামাত-শিবিরের অপরাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং গোয়েন্দাদের চোখ বুজে থাকার বিষয়টি। উখিয়ার রাবেতা হাসপাতালে যে “সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ক্যাম্প” এর কথা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি- তা দেশের গোয়েন্দাদের অজানা থাকার কথা নয়। সামাজিক বৈষম্যের কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে জামাত-শিবিরকে তাদের তথাকথিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন কর্মী সংগ্রহে কোন বেগ পেতে হয়নি। এই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা সামাজিক বৈষম্যের শিকার হওয়ার কারণে এবং ধর্মাশ্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থায় এমনিতেই বেশ স্পর্শকাতর, এদের ধর্মীয় উস্কানি হোক আর অন্য কোন লোভের ফাঁদে ফেলে হোক, একটি স্বার্থান্বেষী মহল তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। আমরাও চোখ বুজে থেকেছি নিজেদের ভোগ বিলাসে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন কিংবা সাধারণ শিক্ষায় এই বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে না পারলে- এই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা আমাদের জন্য বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াতে খুব বেশী সময় লাগবে না। যে শিশুরা সারাদিন ক্লাস শেষে চাঁদার বই হাতে রাস্তায় রাস্তায় কাটিয়ে আধপেটা খেয়ে অপুষ্টি আর অবহেলায় বেড়ে উঠে তাতে তারা সমাজের প্রতি সহিষ্ণু হবে, সকল মানবিক গুণ ধারণ করবে- এটি মাত্রাতিরিক্ত চাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের সমাজই তাদের প্রতি সহিষ্ণু নয়। রাষ্ট্রও তাদের কেবল নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে, ভালবেসে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়নি। অথচ তাদের সংখ্যা সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সমাজে আত্তীকরণের প্রক্রিয়া যত দ্রুত করা যাবে তত দ্রুতই আমরা এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানে আসতে পারব।
এবার আসি- রামুর সহিংসতা পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনায়। রামু, উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় সংঘটিত সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি থানায় পুলিশ মোট ১৯টি মামলা করেছে, তার মধ্যে কেবল রামু থানাতেই মামলা হয়েছে ৭টি। এই সব মামলার তদন্তে আছেন অপরাধ তদন্ত বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট থানা। বিগত ৩ অক্টোবর ২০১৩ মোট ৭টি মামলায় পুলিশ তদন্ত শেষে ৩৬৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন। বলে নেয়া ভাল, রামুর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পরপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি, পুলিশের আইজি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে একটি এবং মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলা নং- ১২৭৩৮/২০১২ এ নির্দেশে অপর একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় তদন্ত দুটি ঘটনার কারণ উতঘাটন, কারা জড়িত ও কি করা দরকার তা নিয়ে সুপারিশ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি প্রতিবেদনে সহিংসতার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নামের একটি তালিকা দিয়েছেন, যাতে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা কর্মীদের নাম আছে। বলা বাহুল্য, ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা দুটি প্রতিবেদনেই শীর্ষে আছেন। যে নামের তালিকার কথা বলছি তা যেনতেন কোন পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন নয়- একটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি, অপরটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি। সুতরাং ধরে নিতে হবে, তারা নিয়মিত পুলিশ বাহিনীর চেয়েও তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক বেশী অভিজ্ঞ। তাহলে যে পাঁচটি মামলায় রামু থানার পুলিশ ও অপরাধ তদন্ত বিভাগ অভিযোগপত্র দাখিল করলেন এবং তাতে যাদের সম্পৃক্ততার উল্লেখ করলেন তারা উপরোক্ত দুটি প্রতিবেদনের নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না সাংঘর্ষিক তা এখনো পরিস্কার নয়। যদি কোন কারণে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে কোন তালিকাটি প্রাধান্য পাবে। যদি যোগ্যতার বিচারে দুটি প্রতিবেদন প্রাধান্য পায় তবে সেই দুটি প্রতিবেদনে যে তালিকা দেয়া হয়েছে তা আগে থকে বিবেচনায় নেয়া হল না কেন? আমরা দেখছি- মূল অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এখনো অবাধে ঘোরাফেরা করছে এবং তাদের কোন প্রকার আইনি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় এখানে প্রধান প্রতিবন্ধকতা নাকি তদন্তে ভিন্ন কিছু বের হয়ে এসেছে তা আমরা এখনো জানতে পারিনি। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় যারা জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ ছিল- বিশেষত দিনাজপুর জেলায়- তাদের অনেকে বি,এন,পি, রাজনীতি ছেড়ে আওয়ামীলীগে যোগদান করেছিলেন বলে অভিযোগ আছে। এর ফলে এসব চিহ্নিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। রামু, উখিয়া ও টেকনাফ থানায় দাখিল করা মামলাগুলোর কিছু বর্তমানে বিচারাধীন আর কিছু এখনো তদন্তের পর্যায়ে আছে। হাইকোর্টে যে রিট মামলাটি ছিল সেটিও এখনো শুনানির অপেক্ষায় আছে। বস্তুত, যে কোর্টে মামলাটি বিচারাধীন সেই কোর্টের “সাধারণ রিট মামলা” শুনানি করার অধিকার না থাকার কারণে সেটি গত বছরের মে মাস থেকে শুনানি করা যাচ্ছে না।
উপরের আলোচনা থেকে আইনি প্রক্রিয়ার যে চিত্র পাওয়া যায় তা এক কথায় হতাশা জনক। এই বিচারহীনতা স্থানীয়দের মাঝে জন্ম দিয়েছে চরম হতাশা আর পারস্পরিক অবিশ্বাস। ঘটনা যেকারণেই ঘটানো হোক না কেন, স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এর প্রভাব সুদুর প্রসারী। এত বড় মাপের একটি সহিংস ঘটনার পর আমরা আশা করেছিলাম- এরপর সরকার অনেক বেশী সচেষ্ট থাকবে এবং পরবর্তীতে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক সহিংসতা যেন না ঘটে সেজন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু বিধি বাম। দুমাস যেতে না যেতেই রংপুরে আহমদিয়া জামাতের লোকজনের উপর হামলা চালানো হয়, জ্বালিয়ে দেয়া হয় তাদের বাড়ী ও প্রার্থনার স্থান। দীর্ঘ একমাস পরেও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন তাদের বাড়ী ফিরতে পারেননি বলে স্থানীয় সূত্রে জেনেছি। এরপর হামলা চালানো হয় চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে- সেখানে আমরা দেখেছি হিন্দুদের বাড়ী, মন্দির জ্বালানোর পাশাপাশি গর্ভবতী গাভী পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সহিংসতার ভয়াবহতা আমাদের সীমাহীনভাবে আতঙ্কিত করেছে। প্রতিবারই আমরা ভেবেছি এটিই বুঝি শেষ সহিংস সাম্প্রদায়িক হামলা। কিন্তু আমাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হতে খুব বেশী সময় লাগেনি। ৩ আগস্ট মাটিরাঙ্গার তাইন্দঙ্গে প্রায় চারশ মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়ে ঘর ছাড়া করা হয়, আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয় একটি বৌদ্ধ মন্দির। রাজনৈতিক সহিংসতার জের ধরে বায়তুল মোকারম মসজিদে আগুন দেয়ার ঘটনাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ২০১৩ সালে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারকে কেন্দ্র করে সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন শুরু হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসেবে দেখা যায়, ৫১টি জেলায় মোট ১৪৬টি মন্দির, ২৬২টি ঘরবাড়ী ভাংচুর, ২১৯টি দোকান লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়, তাতে ৫০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত, ৫ জন নিহত, ৬৫ জন আহত হয়। এরপর আমরা প্রত্যক্ষ করেছি পাবনার সাঁথিয়ায় বিগত ২ নভেম্বর ২০১৩ রামুর মত কোরআন অবমাননার অজুহাতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ৩০-৩৫ বাড়ী, ৪টি মন্দির, বেশ কটি দোকানে অগ্নি সংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়। তারপর ২৫ নভেম্বরের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে দেশের অনেকগুল এলাকা হয়ে ওঠে ভয়ের জনপদ। সাতক্ষীরা, লক্ষ্মীপুর, মাগুরা, চাপাই নাবাবগঞ্জ, কক্সবাজার, চট্টগ্রামসহ অনেক জায়গায় সহিংসতায় মারা যান অনেক মানুষ। জানুয়ারির ৫ তারিখ নির্বাচনের দিন ও তারপর থেকে এখন অবধি নির্বাচনের নামে রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে চলতে থাকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর অকথ্য নির্যাতন। গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে চলতে থাকে হামলা, ভাংচুর আর লুটপাট। সবচেয়ে বেশী সহিংসতা হয়েছে যশোরের অভয়নগর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, ও সাতক্ষীরা এলাকায়। যৌথ বাহিনীর উপস্থিতিতেই যশোরে দুইজন নারী গণ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। বিগত ২৫ নভেম্বরের পর থেকে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মোট ৩২টি জেলায় হামলা হয়েছে। এসময় ৪৮৫টিরও অধিক হিন্দুদের ঘর বাড়ী ৫৭৮টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ১৫২টি মন্দির ও উপাসনালয়ে হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালানো হয়েছে। সংখ্যা বিচারে এটি ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার সাথে তুলনা করলে হয়ত কম মনে হতে পারে কিন্তু সহিংসতার গতি-প্রকৃতি এবার নতুন রুপ ধারণ করায় সেটি বরাবরের মতই ভয়াবহ। নির্বাচনকে ঘিরে যেমন এই সহিংসতা চালানো হয়েছে তেমনি এর একটি চিরায়ত রূপও আছে- যা দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের জাতিসত্তার গভীরে বহমান।
সাম্প্রতিক নির্বাচনকালীন সময়ে যেসব সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হয়েছে তার সাথে রামু, সাঁথিয়া কিংবা হাটাজারির ঘটনার সাথে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তি কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর পোষ্য বুদ্ধিজীবিরা একে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বলতে নারাজ। তারা একে কেবল রাজনৈতিক সহিংসতা হিসেবেই দেখতে চান। তাদের যুক্তি হল- যেহেতু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আওয়ামীলীগের একদলীয় নির্বাচনে ভোট দিয়েছে তাই তাদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। সুতরাং এটি রাজনৈতিক সহিংসতা। এই যুক্তির পেছনেও এবার একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে- যেসব আসনে নির্বাচন হয়েছে তাদের অধিকাংশই দেখা গেছে- যিনি রাজনৈতিক প্রার্থী তিনি যেমন আওয়ামীলীগের নেতা তেমনি যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনিও আওয়ামীলীগের নেতা। তাই যিনি নির্বাচনে হেরেছেন তিনি হিন্দুদের দোষারোপ করেছেন। অপরদিকে জামাত, বি,এন,পির স্থানীয় নেতারা আগে থেকেই হিন্দুদের হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন তারা যদি ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যান তাহলে তাদের দেখে নেয়া হবে। এই ত্রিপাক্ষিক হুমকি সত্ত্বেও তাদের অনেকেই ভোট কেন্দ্রে গেছেন ভোট দিতে। ভরসা ছিল আওয়ামীলীগের নেতাকেই তো ভোট দিতে গেছেন- নিজের লোক বলে কথা। কিন্তু, ক্রমেই সেই ভরসার জায়গায় স্থান করে নিয়েছে চরম হতাশা আর ভয়। প্রাণের ভয়, সম্ভ্রম হারানোর ভয়, সবকিছু খোয়ানোর ভয়। যশোরে স্পষ্ট অভিযোগ আছে আওয়ামীলীগ নেতার বিরুদ্ধে সহিংসতার জন্যে, দিনাজপুরেও তাই। জামাত কিংবা বি,এন,পি আন্দোলনের নামে সহিংসতা চালিয়ে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু তাতে আওয়ামীলীগও যুক্ত হবে এমনটা কেউ ভাবেননি। এবারের সহিংসতার ফল তাই বেশ মারাত্মক। সাঁথিয়ার সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পর সেখানে সরেজমিনে দেখতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম-“গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই, কোন না কোন ব্যবসার সাথে জড়িত, তাহলে পাকা বাড়ী না করে, টিনের ঘর কেন?” তিনি অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে বললেন- “আওয়ামীলীগতো এতো দিন ক্ষমতায় ছিল না। যাওবা এল একটানা থাকতে পারে না। তাই সবাই ইনভেস্ট করতে ভয় পায়। যদি সব ছেড়ে যেতে হয়!” এতে বোঝা গেল- মুসলিম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে আওয়ামী সেকুলারিজম এখনো পুরোপুরি মিথ নয় তাতে (অন্ধ) বিশ্বাস এখনো কাজ করে। স্বাধীনতার পর থেকে এই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধ্বজাধারী আওায়ামী লীগের কাছেই হিন্দু সম্প্রদায়সহ সবাই আশ্রয় খুঁজেছে নিরাপত্তার আশায়। অথচ ক্ষমতা দখলের রাজনীতির হিসেব-নিকেশ যখন মুখ্য হয়ে উঠল তখন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের চরিত্র হারিয়েছে অনেক আগেই। ভোটের রাজনীতিতে তাই হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-আদিবাসীরা থাকলে “ভোট ব্যাংক”, সহিংসতায় মারা গেলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অব্যর্থ অস্ত্র, আর দেশ ত্যাগ করলে সম্পত্তি দখল। শত্রু সম্পত্তি (নামান্তরে অর্পিত সম্পত্তি) আইন, একাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে অদ্যাবধি। ১৯৭১-এ পাকিস্তানিদের অতর্কিত হামলার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু মুসলমান অনেকেই দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন। তারা শরণার্থী শিবিরে কেউবা মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের ভুমিকা পালন করেছেন আর কেউবা মানবেতর জীবন জাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। সবাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এদের মধ্যে কেউ কেউ দেশে ফিরে আসতে পেরেছেন আর কেউ কেউ পারেননি। ১৯৪৭-এ ভারত ভাগের পর থেকে এই দেশত্যাগের ঘটনা চলে আসছে এবং সেটিকে “স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ” বলার কোন উপায় নেই, তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলিমই হোক। এরই ধারাবাহিকতায়, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-আদিবাসিদের কপালে যাই ঘটুকনা কেন, লাভ প্রধানত আওয়ামীলীগেরই এবং একই ধারার রাজনৈতিক দল ও শক্তির। এই বাস্তবতা যদি কেউ ধরতে না পারে তবে তার বাড়ী, দোকান পুড়বে, বারবার সর্বস্ব লুট হতে থাকবে, এটাইতো স্বাভাবিক।
উপরের আলোচনার একটি অংশে “ভোট ব্যাংক” কথাটি উল্লেখ করেছি। সমাজ বিজ্ঞানী স্বপন আদনানের মতে, হিন্দুদের সংখ্যা স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার কারণে এখন হিন্দুরা আর “ভোট ব্যাংক” নন। তাদের বর্তমান ৮.৫% সংখ্যা কোন অঞ্চলের ভোটে কোন প্রার্থীকে জেতানোর জন্য যথেষ্ট নন। তাই, নির্বাচনে তাদের আর “ভোট ব্যাংক” ভাবা হয় না। এই যুক্তি সংখ্যানুপাতিক হারে ক্রমহ্রাসমানতার জন্য হয়ত ঠিক কিন্তু, তারপরও তাদের আওয়ামীলীগের সমর্থক গোষ্ঠী হিসেবে আজীবন মার খেয়ে যেতে হবে- এটাই নিয়তি।
উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে এবারের হামলার একটি রাজনৈতিক রুপ রয়েছে। কিন্তু তাহলে আমরা এটিকে সাম্প্রদায়িক হামলা বলছি কেন? এতে আমদের সামগ্রিক অর্জনইবা কি? সাম্প্রদায়িক শব্দটির মধ্যেই সম্প্রদায়ের একটি আবরণ আছে। আদি যুগ থেকে মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করেছে তখন থেকেই দলবদ্ধ হয়ে বাস করার প্রবণতা রয়েছে। এটি তাদের নিরাপত্তা ও একই গোত্রের আচার-রীতি-নীতির কারনেও বটে। তাই কোন এক ব্যক্তির অপরাধের কারণে, কিংবা দশজন মানুষের ভোট দেয়ার অপরাধে যখন একটি আস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয় তখন এটি কেবল রাজনৈতিক সহিংসতার চেহারা থেকে বেরিয়ে এসে সাম্প্রদায়িক রুপ ধারন করে। বিরোধী দলগুলো যখন আন্দোলনের নামে সহিংসতা করে মানুষ মেরেছিল তখন অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীও আক্রান্ত হয়েছিলেন- সেসবকে আমরা সাম্প্রদায়িক হামলা বলিনি। কেননা, সেখানে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় টার্গেট ছিল না। সংখ্যাধিক্যের জোরে যখন আক্রমণকারীরা ভাবতে শুরু করেন একটি সাহা পাড়া কিংবা পাল পাড়া আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া যায়, কেননা তারা হিন্দু এবং তারা প্রতিরোধ করতে পারবে না- ঠিক তখনই এই হামলা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ে। তবে এধরণের হামলাকে কেবল সাম্প্রদায়িক হামলা বলে চিহ্নিত করলেও এক ধরণের অসুবিধা আছে-তাতে মনে হতে পারে এটি একদল ধর্মান্ধ লোকের ধর্মীয় উগ্রতার কারণে আকস্মিক উত্তেজনায় ঘটিয়ে ফেলা কোন অপরাধ। এটি পরিকল্পিত নয়। কিন্তু, স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ কালে যতগুলো সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটি কোন ভাবেই স্বাধীনতা পূর্ব “দাঙ্গা” ছিল না। দাঙ্গাতে উভয় পক্ষের হানাহানির ব্যপার থাকে। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে সংখ্যাগুরু মুসলিমদের হাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খৃষ্টানরা কেবল মারই খেয়েছে। দিতে পারেনি। এটি পুরোটাই ছিল একতরফা আক্রমণ। আদিবাসীরা কিছু সময় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেও “শান্তিচুক্তি” হওয়ার পর থেকে তাদের অবস্থাও অন্যান্যদের মত। যে যাই হোক- এসব হামলার পেছনে রাজনীতি যেমন থাকে তেমনি থাকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিস্বার্থ। ভূমির অপ্রতুলতা ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ভবিষ্যতে এধরণের হামলা আরও বাড়াবে বৈ কমবে না।
কারণ যাই হোক- এবার দেখা যাক এসব হামলার পর কি কি আইনী প্রতিকার আছে। প্রথমত যদি একে রাজনৈতিক হামলা বলে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে স্থানীয় অপরাধীরা একধরনের সুবিধা পান- কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে তাদের আইনি প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেন। এজন্য হয়ত প্রকৃত অপরাধীদেরও কিছুটা ছাড় দিতে হয়- তাদের দল বদলের ঝামেলাটুকু মেনে নিতে হয়। এর ফলে যে “কালচার অব ইম্পিউনিটি” সৃষ্টি হয়েছে তার ধারাবাহিকতা এখনো বিদ্যমান। ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার কথাই যদি ধরি তাহলে দেখব-২০০১ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ২০০২ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত সহিংসতায় ৩৫৫টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ৩২৭০টি ধর্ষণ ছাড়াও অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ২০০১ সালের এই নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা তদন্তের জন্য “হিউম্যান রাইট্স অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ” এর দায়ের করা এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৬ মে ২০০৯ মহামান্য হাইকোর্ট একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন। সেমতে ২৭ ডিসেম্বর ২০০৯ সরকার ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশনের কাছে ৫৫৭১টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জমা পড়ে। তাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ২০,০০০ এরও অধিক। কমিশন মোট ৩৬২৫টি সহিংস ঘটনার তদন্ত করে। বিগত ২৯ এপ্রিল ২০১১, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে আর তাতে বিএনপির প্রথম সারির কিছু নেতা যেমন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আলতাফ হোসেন, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, তরিকুল ইসলাম, জয়নাল আবেদিন, রুহুল কুদ্দুস দুলু এবং জামাতের নেতা আলি আহসান মুজাহিদ ও যশোরের সাখাওয়াত হোসেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অভিযুক্ত করা হয়। ২৯ এপ্রিল ২০১১, এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন- “৮ম সংসদ নির্বাচনোত্তর সহিংসতা সাম্প্রদায়িক ছিল না। এটি ছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত।“ এ থেকে বোঝা যায়- সহিংসতার মূল পরিকল্পনাকারীরা কোন সময়েই বিচারের মুখোমুখি হন না। তাই এ ধারা চলতেই থাকে। সাম্প্রতিক রামু, সাঁথিয়া কিংবা পরবর্তী সবক্ষেত্রেই তাই দেখা যাচ্ছে- মূল আসামীরা নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একজন ব্যক্তি যেকোন ফৌজদারি অপরাধের কারণে দেশের প্রচলিত আইনে যেটুকু আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হন, তিনি রাজনৈতিক কিংবা সাম্প্রদায়িক কারণে একই অপরাধ করলে, তাকে ভিন্ন কোন আইনে বেশী শাস্তি দেয়ার কোন আইনি বিধান নেই। তাই একটি ঘৃণ্য ফৌজদারি অপরাধকে যে নামেই ডাকি না কেন তার শাস্তি বাংলাদেশ দন্ডবিধির বিধি বিধান মোতাবেকই হয়। আক্রান্তরাও কোন আলাদা বা বেশী সুবিধা পান না। তাই অপরাধীর শাস্তি হওয়াটাই বড় কথা।
সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবেলা করতে হলে প্রথমেই দরকার-এটি মেনে নেয়া যে আমাদের সমাজে সাম্প্রদায়িকতা আছে। সাম্প্রদায়িকতাকে যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে না পারার কারণে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে। একদল রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী একথা বলতে ভীষণ আমোদ বোধ করেন যে, আমাদের দেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এবং এখানে কখনো সাম্প্রদায়িকতা সেভাবে ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা একটি অনেক বড় বিষয় তাই এটিকে বৃহৎ আকারেই মোকাবেলা করা প্রয়োজন। উপনিবেশিক সময় থেকেই যদি ধরি তাহলে দেখতে পাব- সাম্প্রদায়িকতা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও রাষ্ট্র জীবনে- কখনো জাতি ও জাতীয়তাবাদের নামে, কখনোবা ধর্মের আবরণে। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ধর্মীয় মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতাকে গুলিয়ে ফেলি। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আমরা সময়ে সময়ে কথা বললেও জাতি ও জাতীয়তাবাদের নামে স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে যে সাম্প্রদায়িকতার সংস্কৃতি চালু আছে তা নিয়ে তেমন চর্চা হয় না বললেই চলে। সাম্প্রদায়িকতা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংশ- এই কথাটি মানতে না চাইলে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা যাবে না। বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে আমরা যে প্রচেষ্টা চালাই তা জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সত্যকে মেনে নিতে না পারলে সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবেলা করা যাবে না। আমাদের বদ্ধমূল ধারণাজাত বিশ্বাস দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে আড়াল করলে তা ধীরে ধীরে আমাদের সমস্ত চিন্তা চেতনাকেই এক সময় গ্রাস করবে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার শেকড় কতটা প্রোথিত তা বোঝার জন্য খুব বেশি পড়াশোনার প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন ব্যাখ্যায় আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী অধিকাংশ সময়ে এই অমোঘ সত্যকে আড়াল করতে চান। শরীরের ক্ষত লুকিয়ে রাখলে ক্ষত শুকায় না, এর চিকিৎসা করতে হলে একে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা নিতান্ত জরুরি।
এছাড়াও স্বাধীনতা-উত্তর সরকারগুলো ভোটের রাজনীতির কারণে প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে। ধর্মান্ধতা- রাজনীতি, প্রশাসন ও আমাদের যাপিত জীবনে এমনভাবে প্রোথিত যে সেটাকে আর আলাদা করে দেখার উপায় নেই। ১৯৭৯-এ সংবিধানে “বিসমিল্লাহির-রহ্মানির রাহিম” শব্দগুলো সংযোজনের মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের পথ চলা শুরু, ১৯৮৮-তে এসে সেটা রাষ্ট্রধর্ম “ইসলাম” ঘোষণার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। ১৯৭২-এর সংবিধানের এই বিচ্যুতি আমাদেরকে যতটা না ধর্মপ্রাণ অভিধায় সিক্ত করেছে তার চেয়েও করেছে চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক। আন্তর্জাতিক প্রচারে আমরা মধ্যপন্থী নামে পরিচিত হলেও বাস্তব অবস্থা ছিল ভিন্ন। শিক্ষিত মহলের একাংশ ভাবতে ভালবাসেন যে, বাংলাদেশ একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র এবং সেখানে সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করছে। এই ভাবনার সমস্যা হলো এই যে, তাতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া সমস্ত নির্যাতনকে অস্বীকার করা হয়। এই সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, সমাজ জীবনে, অর্থনীতিতে, এমনকি দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতায়। জাতির উপর সব চেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক আঘাতটি এলো ২০১১ সালে, যেখানে সংবিধান পুনরায় সংশোধন করে বলা হলো, “বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।“ বলার অপেক্ষা রাখে না, এই সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও বিলুপ্ত হলো। এদেশের সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে সবাইকে “বাঙালী” বানানোর অপচেষ্টা, যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নয়, ধর্মান্ধদের হাটাজারিতে, রামুতে, বাঁশখালী, সাঁথিয়ায়, অভয়নগরে, ঠাকুরগাঁয়ে বাড়ী ঘরে, মন্দিরে আগুন দিতে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং রংপুরে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বাড়ীতে, মসজিদে আগুন জ্বালানোর দুঃসাহস যুগিয়েছে। তাই এই সাম্প্রদায়িক সংবিধান চালু রেখে সাম্প্রদায়িকতার সমাধান কতটুকু কর আজাবে তা নিয়ে আমি সন্দিহান।
তাথাপি, এই ত্রাহি অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের পাশাপাশি দরকার আইনি সংস্কার। সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা দরকার যেখানে পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান থাকবে এবং দ্রুত বিচারের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। তার পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, আদিবাসীসহ সকল গোষ্ঠীর সম্পত্তি সংরক্ষণের নিমিত্তে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও আলাদা নজরদারীর ব্যবস্থা চালু করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা পরবর্তী আঘাতটি সম্পত্তির উপরই বেশী আসে। পাশাপাশি, সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিষয়ে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে তাদের হাতে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তবে আমরা এও জানি কেবল আইন করে বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ দিয়ে এই সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ঠেকানো যাবে না। তাই এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতা রোধে দেশের সর্বস্তরে জনগণের প্রতিরোধ প্রয়োজন। এছাড়াও প্রয়োজনে দেশের সবকটি জেলায় জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ জন প্রতিরোধ কমিটি গঠনের উদ্যেগ নেয়া যেতে পারে।
পাক্ষিক একপক্ষ ম্যাগাজিন- জানুয়ারি ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।
This post has already been read 42 times!