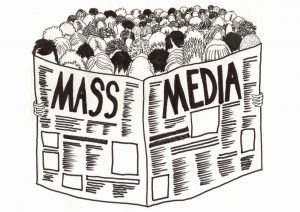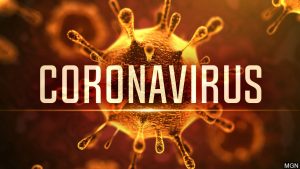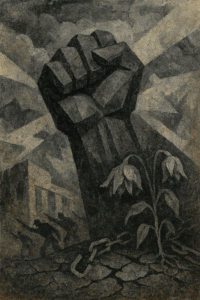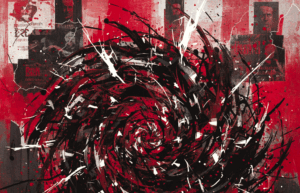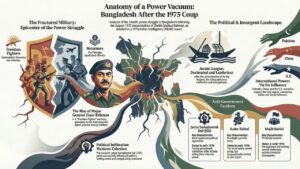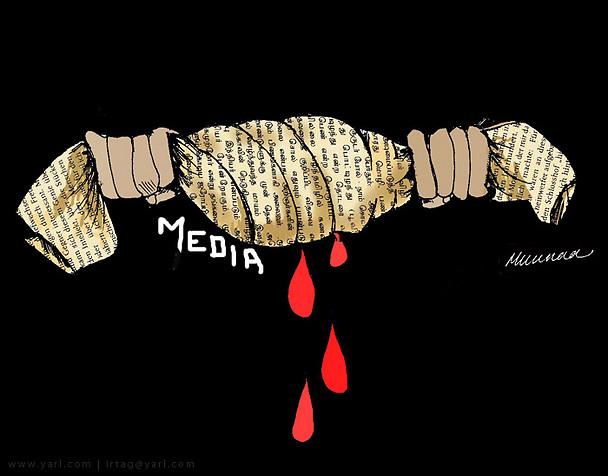
http://goo.gl/mVvwRW
This post has already been read 3 times!
মিডিয়াসংশ্লিষ্ট ও সচেতন নাগরিকদের প্রবল আপত্তির মুখেও ৭ আগস্ট জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ অনুমোদন লাভ করেছে। সরকার পক্ষ থেকে এর সমর্থনে যেমন বিভিন্ন যুক্তি হাজির করা হয়েছে, তেমনি নাগরিকদের পক্ষ থেকেও এর ক্ষতিকারক দিকগুলো নিয়ে পত্রিকায়, সভায় ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, এখনো সময় আছে সরকারকে এর পরিবর্তন বা সংশোধন নিয়ে প্রস্তাবনা দেয়ার। টিআইবির পক্ষ থেকে এই নীতিমালার সমালোচনার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনাও দেয়া হয়েছে। বিগত বছরে অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের সংশোধনীর প্রস্তাবনা দেয়ার ক্ষেত্রে আমার সংশ্লিষ্ট থাকার সুযোগ হয়েছে— একটি শ্রম আইন ও অন্যটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন। আইন দুটি সংশোধনী প্রকাশের পর দেখা গেছে, তাতে সরকার কারো কোনো বিশেষ প্রস্তাবনাই আমলে নেয়নি। এই অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করা যায়, এবারো সরকার কোনো পরামর্শই কার্যত গ্রহণ করবে না। ভাবখানা এমন যে, আইন করবে সরকার, তাতে কার কী বলার আছে?
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক নির্ধারণে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমাদের সরকারও বিগত সময়গুলোয় বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, তারা জনগণের কল্যাণের সরকার। এ কথার সূত্র ধরে বলা যায়, নব্বই-পরবর্তী সরকারগুলোর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে মাঝে মধ্যেই এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। অতিরিক্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত হলে কোনো সরকারই সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। এ কারণে সরকার নিবর্তনমূলক আইনের মাধ্যমে প্রথমে খড়্গহস্ত হয় নাগরিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর। তেমনই সাম্প্রতিক একটি আইন হলো, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, যার পুনঃপুনঃ অপ্রয়োগ দৃষ্টিকটুভাবে দৃশ্যমান। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ তেমনই স্রোতের বিপরীতে যাওয়া অপরাপর নিবর্তনমূলক আইনে নতুন সংযোজন মাত্র। ২০১৩ সালে আমরা দেখেছি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর কতিপয় ধারা সংশোধন করে এটিকে আরো দুর্বিষহ একটি আইনে পরিণত করা হয়েছে। সেই আইনের ৫৭ ধারার একটি কালো ছায়া যেন এই সম্প্রচার নীতিমালায়ও পড়েছে। ৫৭ ধারায় অনেক বিষয়কে একসঙ্গে সংযুক্ত করতে গিয়ে এটিকে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে।
আমাদের দেশে আইন প্রণয়ন যতটা না নাগরিকের মৌলিক অধিকার বিকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তার চেয়েও বেশি হলো নিয়ন্ত্রণের জন্য। ফলে নাগরিকদের মধ্যেও আইন মেনে চলার সংস্কৃতি সেভাবে বিকাশ ঘটছে না। নব্বই-পরবর্তী নৈর্বাচনিক স্বৈরতন্ত্র চালু থাকার কারণে নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকার ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়েছে, যা মূলত বিভিন্নভাবে স্বৈরতন্ত্র বিকাশের সহায়ক হয়েছে। আমাদের নিবর্তনমূলক আইনের বিপরীতে একমাত্র রক্ষাকবচ হলো সংবিধান। কিন্তু সম্প্রচার নীতিমালায় খুব কৌশলে এমন সব ব্যাখ্যা হাজির করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের ব্যর্থ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের অবস্থা এখন পুলিশের হাতে মার খেয়ে পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চাওয়ার মতো। স্বয়ং সংবিধান যেখানে ক্ষেত্রবিশেষে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ, সেখানে সংবিধানে আশ্রয় খোঁজা কতটুকু কার্যকর হবে তা সহজেই অনুমেয়। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাক, সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ আমাদের চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। সম্প্রচার নীতিমালার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এর হুবহু প্রয়োগ দেখা যায়। ৩৯ অনুচ্ছেদ থেকে দেখা যায়, বাক স্বাধীনতা কোনো অবারিত স্বাধীনতা নয়, এখানে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে আইন দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপের সুযোগ রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ কে নির্ধারণ করবে? যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে, সেই সরকারের কাছে যা যুক্তিসঙ্গত মনে হবে, সেইমতে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হবে। এখানেই ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই সুযোগে নতুন নতুন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়নের পথ তৈরি হয়েছে। সম্প্রচার নীতিমালায় যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তা আদৌ যুক্তিসঙ্গত কিনা, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাছাড়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সব সময়ই নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি মোক্ষম হাতিয়ার। এ-যাবত্কালে ব্যক্তিমালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেলগুলো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, সে রকম কোনো কাজে লিপ্ত ছিল না বা তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি।
এবার সম্প্রচার নীতিমালার কতিপয় অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করা যাক। নীতিমালার শুরুতে এর পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে— অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন, বহুমুখী, দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল সম্প্রচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের সম্প্রচার মাধ্যমগুলোকে একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় আনার জন্য এ নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। অথচ এই নীতিমালা অনুমোদন পাওয়ার পর থেকে অংশীজনদের প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি।
নীতিমালার তৃতীয় অধ্যায়ে সংবাদ ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩.২.১ অনুসারে অনুষ্ঠানে সরাসরি বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোনোভাবেই দেশবিরোধী ও জনস্বার্থবিরোধী বক্তব্য প্রচার করা যাবে না। কিন্তু নীতিমালার কোথাও কোন বক্তব্যকে দেশবিরোধী বা জনস্বার্থবিরোধী বলা হবে তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাছাড়া এটি কোনো আইনে উল্লেখ না থাকলেও অনুল্লিখিত আইন (রসঢ়ষরবফ ষধ)ি হিসেবে ধরে নেয়া যায় যে, কোনো সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ দেশবিরোধী বা জনস্বার্থবিরোধী কোনো বক্তব্য প্রচার করবে না— এটি তাদের লাইসেন্স প্রদানের একটি অন্যতম শর্ত। তাই নতুন করে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে না।
অনুচ্ছেদ ৩.২.২ অনুযায়ী, আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য বা উপাত্ত দেয়া পরিহার করতে হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে সব পক্ষের যুক্তিগুলো যথাযথভাবে উপস্থাপনের সুযোগ থাকতে হবে। এখানে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য বা উপাত্ত বলতে কী বোঝানো হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া কোন তথ্য বা উপাত্তটি বিভ্রান্তিকর ও অসত্য, তা কে নির্ধারণ করবে বা নির্ধারণ প্রক্রিয়াটা কীভাবে হবে— এ-সংক্রান্তও কিছুই বলা হয়নি। বস্তুত, এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সরকার তাদের কাজের সমালোচনাকারী বা অপছন্দের ব্যক্তিদের মুখ বন্ধ করতে পারবে। তাছাড়া এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মূলত ‘টকশো’ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্প্রচার মাধ্যমগুলোয় সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হচ্ছে টকশো। সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই টকশো দেখে বলেই আমার ধারণা। এতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের উপস্থিতির পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। সরকারদলীয় ও বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষের অনেক খোলামেলা বক্তব্য দেশের নাগরিকরা এই টকশোর মাধ্যমে অবগত হতে পারে এবং এটি রাজনৈতিক মতামত নির্মাণেও ভূমিকা রাখছে। এটিই বোধকরি সরকারের সবচেয়ে অস্বস্তির কারণ।
অনুচ্ছেদ ৩.২.৩ অনুযায়ী, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যেমন— রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের ভাষণ, জরুরি আবহাওয়া বার্তা, স্বাস্থ্য বার্তা, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, প্রেস নোট ও অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান জনস্বার্থে যথাযথভাবে সম্প্রচার/প্রচার করতে হবে। অনুচ্ছেদটিতে সরকারের সম্প্রচার মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্প্রচার মাধ্যম জরুরি আবহাওয়া বার্তা বা স্বাস্থ্য বার্তা জনস্বার্থে হয়তো সম্প্রচার করতে পারে, কিন্তু তাদের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের ভাষণ, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, প্রেস নোট ও অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে বাধ্য করা যায় না। বর্তমানে বিটিভির সংবাদ প্রচারে যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তাও সরকারের চাপিয়ে দেয়া জবরদস্তিমূলক সিদ্ধান্ত। বিটিভির সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা কেবল নয়, এর মান নিয়েও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এতে চ্যানেলগুলোর আর্থিক ক্ষতির বিষয়টিও ভেবে দেখা দরকার।
অনুচ্ছেদ ৩.৬.৭-এ বলা হয়েছে, দেশী ও বিদেশী ছবি/অনুষ্ঠানে অশ্লীল দৃশ্য, হিংসাত্মক, সন্ত্রাসমূলক এবং দেশীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। এটি একটি দ্বৈত নীতি। দেশে ক্যাবল চ্যানেলের মাধ্যমে অসংখ্য বিদেশী চ্যানেল সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। সেগুলো দেশীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। অথচ একই ছবি বা তথ্য সম্প্রচার করলে দেশী চ্যানেলগুলো আইনভঙ্গের আওতায় পড়বে। তাছাড়া কোন দৃশ্যকে অশ্লীল বলা হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। ফলে কোনো চ্যানেলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চাইলে এই একটি অনুচ্ছেদই যথেষ্ট। এছাড়া কাহিনীর প্রয়োজনে চলচ্চিত্রে এমন দৃশ্য সংযোজিত হতে পারে, যা পরিস্থিতির বিচারে দর্শকদের কাছে অশ্লীল মনে নাও হতে পারে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কাছে যদি সেটি অশ্লীল মনে হয়, তাহলেই শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এই অনুচ্ছেদে অন্য একটি বিষয় যোগ করা হয়েছে, তা হলো— দেশীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। কোনো দেশের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কোনো স্থির বিষয় নয়, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল। কিন্তু প্রত্যেক জেনারেশনে সমাজের একটি অংশ ফেলে আশা দিনগুলোয় আটকে থাকে, পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। এক্ষেত্রে কোনটি দেশীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, তা নির্ধারণ করাও দুরূহ ব্যাপার হবে। আইনে অস্পষ্টতা থাকলে এর অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।
অনুচ্ছেদ ৩.৭-এর মাধ্যমে সম্প্রচার মাধ্যমগুলোকে ক্রীড়া ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করার বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়েছে। এটিও চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত। যেসব চ্যানেল শুধু সংবাদ পরিবেশন করে, তারা নিশ্চয়ই ক্রীড়া ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করবে না। তাছাড়া একটি চ্যানেল কী ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করবে বা করবে না, তা যদি সরকার নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে সেই চ্যানেলের স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকে না।
অনুচ্ছেদ ৪.১.১-এ বলা হয়েছে, বিজ্ঞাপনের ভাষা, দৃশ্য কিংবা নির্দেশনা ধর্মীয় অনুভূতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও রাজনৈতিক অনুভূতির প্রতি পীড়াদায়ক হতে পারবে না। প্রথমত. ধর্মীয় অনুভূতি মানুষভেদে ভিন্ন রকম হতে পারে। এটি নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন কোন ভাষা, দৃশ্য কিংবা নির্দেশনা ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানবে। এর মাধ্যমে সরকারের যখন খুশি কাউকে হেনস্তা করার সুযোগ থাকছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা বর্তমান সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যে দেশের রাষ্ট্র ধর্ম নির্দিষ্ট করা আছে, যেখানে অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করার নামে আইন প্রণয়ন নিতান্তই হাস্যকর একটি ব্যাপার। বৃহৎ বাঙালি নৃগোষ্ঠীর এ দেশে অপরাপর সব সম্প্রদায়ই কোনো না কোনোভাবে সাম্প্রদায়িকতার শিকার।
রাজনৈতিক অনুভূতিকে প্রশ্ন না করে কোনো আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এর প্রচলন অপরিসীম। অন্যের কুত্সা গাওয়ার মধ্যেই নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করেন রাজনীতিকরা। তাই এটি সম্প্রচার নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত না হয়ে রাজনীতিবিদদের জন্য নতুন আচরণবিধি প্রণয়ন করে সেখানে সন্নিবেশিত করলে সুফল পাওয়া যেত।
অনুচ্ছেদ ৫.১.৩-এ বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বা মর্যাদা হানিকর তথ্য প্রচার করা যাবে না। এটিও খুবই অস্পষ্ট একটি বিধান। ব্যক্তির গোপনীয়তা যদি কোনো ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে তা প্রকাশ করাই হবে সম্প্রচার মাধ্যমের দায়বদ্ধতা। এই বিধান মেনে যদি আইন করা হয়, তবে অনেক ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারি যেমন— হল-মার্ক কিংবা ডেসটিনির মতো ঘটনা কোনোদিনই প্রকাশ পাবে না। এতে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি বাড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
অনুচ্ছেদ ৫.১.৪-এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের সামরিক, বেসামরিক বা সরকারি তথ্য প্রচার করা যাবে না। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরাই বিধানটির সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করেছেন। এ বিধানের মাধ্যমে যতটা না রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের চেষ্টা করা হয়েছে, তার চেয়েও বেশি বিশেষ বাহিনীকে আলাদা সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা মিডিয়ায় প্রচার না হলে এত তাড়াতাড়ি এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সে সময় নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ছিল বিধায় মিডিয়ায় সম্প্রচারিত তথ্য ও সচিত্র প্রতিবেদন সমাধান নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এই অনুচ্ছেদের বিধান কার্যকর হলে ভবিষ্যতে সম্প্রচার মাধ্যমগুলো এ ধরনের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভূমিকা রাখতে পারবে না।
অনুচ্ছেদ ৫.১.৫-এ বলা হয়েছে, কোনো অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপনে সশস্ত্র বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কোনো সংস্থা এবং অপরাধ রোধ, অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং অপরাধীকে দণ্ড প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রতি কটাক্ষ বা বিদ্রুপ কিংবা তাদের পেশাগত ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে পারে এমন কোনো দৃশ্য প্রদর্শন কিংবা প্রচার করা যাবে না। এ নীতি কার্যকর হলে পুলিশের হেফাজতে নিয়মিত বন্দিদের নির্যাতন ও মৃত্যু, সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, র্যাব ও পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার, অব্যাহত গুম-খুনের সঙ্গে তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ কোনো কিছুই প্রচার করা যাবে না। বন্দি নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু প্রতিরোধে ২০১৩ সালে কঠিন আইন প্রণয়ন করা হলেও যেখানে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা দিনের পর দিন বাড়ছে, সেখানে এসব অপকর্মের লাগাম টানতে সম্প্রচার মাধ্যমের অনেক বেশি সক্রিয় থেকে তথ্য প্রচার অব্যাহত রাখা দরকার। এই বিধান যদি বিগত বছরগুলোয় বলবৎ থাকত, তাহলে সাম্প্রতিক নারায়ণগঞ্জের সাত খুন, র্যাবের হাতে লিমনের নির্যাতিত হওয়া, মিরপুরে ঝুট ব্যবসায়ীর পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু কিংবা অতীতের ১০ ট্রাক অস্ত্র পাচারের সঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থার জড়িত থাকার কথা, একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা, মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির সঙ্গে সামরিক ও অন্যান্য বাহিনীর জড়িত থাকার কথা আমরা কখনই জানতে পারতাম না। আর এসব তথ্য সম্প্র্রচারের ফলে জনমত থেকে সৃষ্ট চাপ না থাকলে ওইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত নিরাপত্তা বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের কর্তাব্যক্তিদের কখনই বিচারের মুখোমুখি করা যেত না।
অনুচ্ছেদ ৫.১.৭-এ বলা হয়েছে, কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে এমন ধরনের প্রচারণা, যা বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে বিরোধের কোনো একটি বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে অথবা একটি বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন ধরনের প্রচারণা, যার ফলে সে রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে— এমন দৃশ্য বা বক্তব্য সম্প্রচার করা যাবে না। বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে— সেটি একটি আপেক্ষিক বিষয় এবং সময়ে সময়ে সেটি পরিবর্তনশীল। তাছাড়া একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি নিজ দেশের ভালো-মন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়। এ নীতির ফলে ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্রের ব্যাখ্যায় ফেলে রামপাল বিদ্যুেকন্দ্র স্থাপন, সীমান্তে অব্যাহত হত্যা, নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা, বিনামূল্যে ট্রানজিট দেয়াসহ আরো যেসব অন্যায্য সুবিধা দেয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য বা তথ্য প্রচার করা যাবে না। সুদূরতম ভবিষ্যতে যদি কখনো সরকার পরিবর্তন হয়, তাহলে পাকিস্তানের জন্য একই নীতি প্রযোজ্য হলে তাদের মন রক্ষার্থে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত করে সবাইকে খালাশ দেয়া হলে বর্তমান সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কী বক্তব্য থাকবে, তা জানার আগ্রহ রইল।
অনুচ্ছেদ ৫.১.৯-এ বলা হয়েছে, জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো বিদ্রোহ, নৈরাজ্য এবং হিংসাত্মক ঘটনা প্রদর্শন পরিহার করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে একে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট মনে হলেও এতে শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। জনস্বার্থ সংরক্ষণের অজুহাতে সব রকম সরকারবিরোধী বা জনগণের আন্দোলন সংগ্রামের সংবাদ বা তথ্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাই এই নীতির মূল উদ্দেশ্য বলে সন্দেহ হয়।
অনুচ্ছেদ ৬.১.১-এ একটি স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে, অথচ সেটি কবে বা কত দিনের মধ্যে গঠন করা হবে সে বিষয়ে কোনো কথা বলা হয়নি। এ নীতির সঙ্গে অনুচ্ছেদ ৭.৪ মিলিয়ে পড়তে হবে, যেখানে বলা হয়েছে, এ নীতিমালায় উল্লেখ নেই অথবা অন্য কোনো নীতিমালার বা আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। এই সুযোগ যদি থাকে তাহলে সম্প্রচার কমিশন গঠনে ধীরগতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। অনুচ্ছেদ ৬.১.৬-এ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের বিধান নিয়ে বলা হলেও চেয়ারম্যান কিংবা সদস্যদের যোগ্যতা কী হবে, সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের যোগ্যতা হিসেবে তার আইনজীবী বা বিচারক হিসেবে অভিজ্ঞতা থাকাটা জরুরি ছিল। কেননা চেয়ারম্যান একটি আদালত পরিচালনা করেন, যেখানে রায় প্রদানের বিধান রয়েছে। আদালতসংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকলে সঠিকভাবে আদালত পরিচালনা অসম্ভব ব্যাপার। সম্প্রচার কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি এড়ানো যেত।
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সম্প্রচার নীতিমালা আছে, কিন্তু সেখানে সম্প্রচারের বিষয় নিয়ন্ত্রণের কোনো বিধান নেই। উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচার নীতিমালার কথা ধরা যাক, কমিউনিকেশন অ্যাক্টের ৩২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকার সম্প্রচারের বিষয়াদিতে কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে না এবং সম্প্রচারের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। যুক্তরাজ্যের আইনেও একই রকম নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো বিশেষ বিষয়ের সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সম্প্রচার মাধ্যম কী সম্প্রচার করবে, সে সম্পর্কে কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। আমাদের সম্প্রচার নীতিমালা বিদ্যমান অস্পষ্টতা নিয়ে একটি দমনমূলক নীতিমালা হিসেবে নজির স্থাপন করতে যাচ্ছে। সম্প্রচার মাধ্যম সরকারি ভাষ্যের পাশাপাশি বিকল্প তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করে। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি, অন্যথায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ‘বোবার শত্রু থাকে না’ প্রবাদটির মধ্যে এক ধরনের সত্যতা আছে। কিন্তু সম্প্রচার কিংবা সংবাদ মাধ্যমের যদি শত্রুবিহীন পথ চলার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে তাদের সম্প্রচার বন্ধ করাই হবে একমাত্র পথ। অন্যথায় তাদের সম্প্রচারের কারণে কেউ না কেউ মনক্ষুণ্ন হবেন— এটি নিশ্চিত। বর্তমান নীতিমালার পরিপূর্ণ আইনি ক্ষমতা না থাকলেও এরই মধ্যে আমরা এর ব্যবহার দেখতে শুরু করেছি। এ আইনের ব্যবহার সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে সবচেয়ে সত্যি কথাটি বলেছেন মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী মো. মহসিন আলী। তিনি বাঁশ তত্ত্বের মাধ্যমে পরিষ্কার করেছেন, ভবিষ্যতে সম্প্রচার মাধ্যমের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে। আমরা আশা করব, বিদ্যমান সরকার জাতীয় পর্যায়ে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করার নীতিমালা থেকে সরে আসবে এবং গণতন্ত্র বিকাশের পথে হাঁটবে।
বনিক বার্তায় ২৩ আগস্ট’১৪ প্রকাশিত। [থাম্বনেইলের ছবির সূত্রঃ http://goo.gl/mVvwRW]
This post has already been read 3 times!