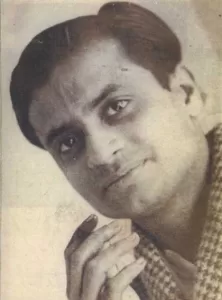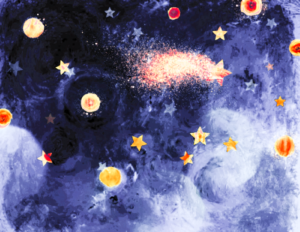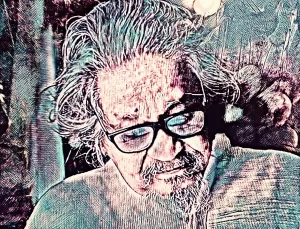স্কটল্যান্ডের গণভোট যে সারা পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষন করেছিলো তার কারণ কেবল এটাই নয় যে গত তিনশো বছরে ব্রিটেনের ইতিহাসে এমন ঘটনার কোনো উদাহরণ নেই; এই কারনেও যে এর ফলাফল, বিশেষত যদি স্কটল্যান্ডের ভোটাররা স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া কেবল স্কটল্যান্ডে বা ব্রিটেনেই থাকবেনা। স্পেনের কাটালোনিয়া প্রদেশের এবং কানাডার কুইবেক প্রদেশের স্বাধীনতাকামীদের জন্যে তা হয়ে উঠবে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। ইউরোপে গত কয়েক দশকে যেখানে চেষ্টা হচ্ছে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে যত ধরণের সীমান্ত আছে তার অবসান ঘটাতে, আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ গঠনে সেখানে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত হবে বিপরীতমুখী। বিশ্ব বাজারেরও তার প্রভাব পড়বে বলেই অনুমান করা হচ্ছিলো। স্বাধীনতার পক্ষে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির শক্তিশালী অবস্থান ও প্রচারনা স্বত্বেও গোড়াতে মনে হচ্ছিলো যে এই গণভোট আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্ত শেষ সপ্তাহগুলোতে অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তনের আভাস মেলে জনমত জরিপগুলোতে – বলা হয় যে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি; অনেকেই আভাস দেন যে ‘হ্যাঁ’ ভোটই জিতবে। সেটাই আরো বেশি করে সারা পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষন করতে সক্ষম হয়।
এখন গনভোট শেষ হয়েছে। আমরা সবাই জানি যে, স্কটল্যান্ডের ভোটারদের অধিকাংশ গণভোটে স্বাধীনতার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। ভোটের ব্যবধান জনমত জরিপে যা অনুমান করা হয়েছিল, তারচেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। পক্ষে ভোট পড়েছে ৪৫ শতাংশ, বিপক্ষে ৫৫ শতাংশ। ভৌগলিকভাবে দেখলে স্কটল্যান্ডের ৩২টি কাউন্সিলের মধ্যে মাত্র চারটি ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিয়েছে। শহরগুলোর মধ্যে বড় চারটি শহরের দুটি স্বাধীনতার প্রস্তাবের পক্ষে গেছে, দুটি গেছে বিরুদ্ধে। দেশের সবচেয়ে বড় শহর গ্লাসগো এবং চতুর্থ বৃহত্তম শহর ডান্ডি স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিয়েছে। এডিনবারা’তে ‘না’ ভোট পড়েছে বেশি। গ্লাসগোতে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ভোট ‘না’-এর চেয়ে খুব বেশি নয়। ব্রিটিশ গণমাধ্যমে ফলাফলের যে সব তালিকা আমরা দেখতে পাই তাতে স্পষ্ট যে ১৬ থেকে ৫৪ বছর বয়সীদের মধ্যে স্বাধীনতার পক্ষেই বেশি ভোট পড়েছে; একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ১৮-২৪ বছর বয়সীরা। স্বাধীনতার পক্ষে সবচেয়ে বেশি ভোট দিয়েছে ১৬-১৭ বছরের বয়সীরা; তাঁদের ৭১ শতাংশ স্বাধীনতার পক্ষে। কিন্ত ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে মাত্র ৪৮ শতাংশ ছিলো ছিলো স্বাধীনতার পক্ষে। ব্রিটেনের সঙ্গে একত্রে থাকার পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেছে ৫৫ বছরের উর্ধে যাঁদের বয়স। ৬৫ বছরের বেশি যাঁদের বয়স তাঁদের মধ্যে মাত্র ২৭ শতাংশ হ্যাঁ ভোট দিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে যেখানে বেকারত্বের হার বেশি সেসব এলাকার মানুষ বেশি ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়েছে – উদাহরণ গ্লাসগো এবং ডাণ্ডি (বেকারত্বের হার যথাক্রমে ১৯ দশমিক ১ এবং ১৭ শতাংশ; সারা স্কটল্যান্ডের হার ১২ দশমিক ৮ শতাংশ)। একইভাবে দারিদ্রপীড়িত এলাকায় বেশি ভোট পড়েছে বেশি হ্যাঁ-এর পক্ষে। দৈনিক টেলিগ্রাফের ভাষায় যারা ভোট দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে তরুণ, দরিদ্র এবং বেকারদের মধ্যে হ্যাঁ ভোটে দেবার প্রবণতা ছিলো বেশি।
গণভোটের প্রচারনার শেষ দিকে ‘হ্যাঁ’ ভোটের সম্ভাবনা বেশি থাকলেও শেষ পর্যন্ত ফলাফল তা হল না কেন সেটা অনেকভাবেই বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে খুব জোরদার তথ্য নেই; যারা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা নিশ্চয় খুব শিগগিরই তা খুঁজবেন। কিন্ত আপাতদৃষ্টে কয়েকটা বিষয়কে কারণ বলে মনে হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে স্কটল্যান্ডের বাইরের প্রতিক্রিয়া। স্কটল্যান্ড স্বাধীন হলে দেশটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য পদের চেষ্টা করবে এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন স্বাধীনতার পক্ষের নেতার; কিন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে আশাবাদী করতে পারেনি যে তাঁরা সেই সদস্যপদ পাবে। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তার দেশ স্কটল্যান্ডকে ইউনিয়নে ঢোকার পথে বাধা দেবে। অনেকে এও বলেছে যে লন্ডনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ব্রাসেলসের হাতে বন্দি হবার জন্যেই কী স্কটল্যান্ড স্বাধীনতা চাইছে? অর্থনীতির প্রশ্নটিও সম্ভবত ভোটারদের প্রভাবিত করেছে। ব্রিটেনের সরকার ও রাজনীতিবিদরা বলেছে যে স্বাধীনতার পর স্কটল্যান্ড অর্থনীতি সংকটে পড়বে কেননা এখন অনেক কিছুই তার ব্রিটেনের সঙ্গে ভাগ করে যার ভার স্কটল্যান্ডকেই বইতে হবে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিরা বলেছে উত্তর সাগর বা নর্থ সি’র স্কটল্যান্ডের ভাগে যে এলাকা তা থেকে উত্তোলিত তেল থেকেই দেশের অর্থনীতি চালানো যাবে। কিন্ত সেটা যে ভোটারদের মনে খুব ধরেনি সেটা বোঝা যায় যে এবারডিন শহরের ভোটাররা শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধেই ভোট দিয়েছে। তাছাড়া যে ধরণের কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, তার জন্যে অর্থের সংস্থান হবে কিভাবে সেটা ভোটারদের কাছে স্পষ্ট হয় নি বলে অনুমান করা যায়।
এখনকার প্রশ্ন সামনে কী ঘটবে? যে কোনো নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত শেষ পর্যন্ত নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে; কিন্ত তাঁর অর্থ কিন্ত এই নয় যে, সংখ্যালঘুদের মতামত মোটেই গুরুত্বপূর্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের অর্থ ‘সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার’ (বা ‘tyranny of majority’) নয় বরঞ্চ সংখ্যালঘুর অধিকার ও কন্ঠস্বরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তাঁদের বক্তব্যকে শাসনের মধ্যে প্রতিফলিত করাই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় গুন। সেই বিচারে স্কটল্যান্ডের সংখ্যালঘুদের কণ্ঠস্বর কিভাবে এখন বিরাজমান কাঠামোর মধ্যে প্রতিফলন করা হবে সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ।
এই গণভোটের আগে বৃটেনের প্রধান তিন দলই এই বিষয়ে নতুন ভাবনার এবং ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। লেবার নেতা এড মিলিব্যান্ড, কনজারভেটিভ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এবং লিবারেল ডেমোক্রেট নেতা নিক ক্লেগ গণভোটের ঠিক আগে ১৬ সেপ্টেম্বর স্কটল্যান্ডের ডেইলী রেকর্ড পত্রিকায় যৌথভাবে এক বিবৃতিতে স্কটল্যান্ডের আধা-স্বায়ত্তশাসিত পার্লেমেন্টের হাতে কর আরোপ এবং ব্যয়ের ব্যাপারে আরো বেশি ক্ষমতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরা বলেন যে স্কটল্যান্ডের মানুষ যদি ব্রিটেনের সঙ্গে থাকতে চায় তবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। এখন তাঁদের দায়িত্ব হল এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আইনি এবং কাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে দ্রুত এগিয়ে আসা। কাজটা মোটেই সহজ হবেনা। কেননা অনেক পার্লেমেন্ট সদস্যই আশংকা করছেন যে তাড়াহুড়া করে সাংবিধানিক সংস্কার করা হবে। কনজারভেটিভ দলের সদস্যদের মনে এটাও প্রশ্ন যে লেবার দলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের এজেন্ডা তাঁরা কেন বাস্তবায়ন করবেন। অন্য দিকে লেবার পার্টির জন্যে যে কোন ভাবে হোক স্কটল্যান্ডের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে; কেননা আগামী বছরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে জিততে হলে তাঁদের স্কটল্যান্ডের সমর্থন লাগবেই। অতীতে টনি ব্লেয়ারের জেতার পেছনে স্কটল্যান্ডের ভোট ছিলো নির্নায়ক।
ইতিমধ্যে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির নেতা এলেক্স স্যামন্ড তাঁর দল এবং স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন; এটাই স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক আচরণ। তাঁর জায়গায় যিনি আসবেন তাকে নিশ্চিত করতে হবে তাঁর দল যে দাবিতে ১৬ লাখ ১৭ হাজার ৯৮৯ জন ভোটারের সমর্থন পেয়েছেন তাঁদের আকাঙ্ক্ষাকে বিরাজমান কাঠামোর মধ্যে কী করে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে; অন্য দিকে নেতা হিসেবে এলিস্টার ডারলিংয়ের কাজ হচ্ছে ‘হ্যাঁ’ ভোট যারা দিয়েছেন তাঁদের এবং ‘না’ ভোট দেয়া তাঁর পক্ষের প্রায় ২০ লাখ মানুষের আস্থাকে সঙ্গে নিয়ে কী করে তিনি ইংল্যান্ডের ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতার বাইরের দলগুলোর কাছ থেকে স্কটল্যান্ডের অনুকূলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে পারেন এবং কত তাড়াতাড়ি তা সম্ভব হয়।
এটা বলা মোটেই অতিরঞ্জন নয় যে, স্কটল্যান্ডের গণভোটে স্বাধীনতার প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি, কিন্ত এই ভোট স্থায়ীভাবে বৃটেনকে, বৃটেনের শাসন এবং রাজনীতিকে বদলে দিয়েছে; বৃটেন, বিশেষত ইংল্যান্ড, আর কখনোই ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪-এ রাজনীতিতে ফিরে যাবে না।
প্রথম আলো’তে প্রকাশিত, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪