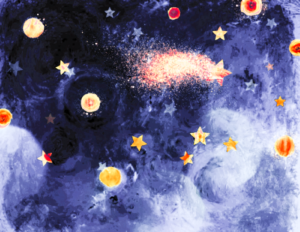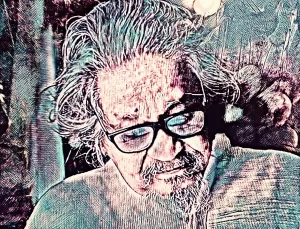১৯৫২ সালে আমেরিকান অর্থায়নে কাপ্তাই বিদ্যুত্ প্রকল্পের অধীনে বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়ে তা ১৯৫৮-এ শেষ হয়। পরবর্তী সময়ে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাঁধটি ভেঙে গেলে আইয়ুব খান পুনরায় এর নির্মাণকাজ শুরু করেন, যা ১৯৬১-৬২ সাল নাগাদ শেষ হয়। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে ৫৪ হাজার একর কৃষিজমি, যা ওই এলাকার মোট কৃষিজমির ৪০ শতাংশ এবং সরকারি সংরক্ষিত বনের ২৯ বর্গমাইল এলাকা ও অশ্রেণীভুক্ত ২৩৪ বর্গমাইল বনাঞ্চল জলের নিচে তলিয়ে যায়। অনুমান ১৮ হাজার পরিবারের মোট এক লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। সেই থেকে পার্বত্য অঞ্চলে দুঃখের দিন শুরু। গৃহহীন মানুষের মিছিল দীর্ঘ হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ক্ষোভ আর সুদৃঢ় হতে থাকে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। দশ হাজার একরের একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে এসব ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই কাপ্তাই বাঁধ থেকে সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদ বাঙালিদের নয়ন ভরালেও পাহাড়িদের দুঃখ ঘোচেনি।
একাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভাবা হয়েছিল দেশে সব ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে সমতা আসবে, কিন্তু বাহাত্তরে জাতির পিতা পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যেতে বলার পর তাদের সেই বিশ্বাস আর রইল না। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে চার দফা দাবিসংবলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামা পেশ করা হলে বঙ্গবন্ধু এম এন লারমাকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘লারমা তুমি যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো তাহলে এক লাখ, দুই লাখ, তিন লাখ, দশ লাখ বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকিয়ে দেব। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমি তোমাদের সংখ্যালঘু করে ছাড়ব।’ এর পর থেকে শুরু হলো আন্দোলন, সংগ্রাম। ১৯৭৩ সালে শান্তি বাহিনী গঠনের মাধ্যমে শুরু হয় সশস্ত্র সংগ্রাম। এর পরের ইতিহাস খুবই নির্মম আর সহিংস। বঙ্গবন্ধু যে কাজ করবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন, তার উত্তরসূরিরা সে কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন।
১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যকর না হওয়ায় আর পাকিস্তান বা বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে সচেতন না করায় কেউই জমিজমার দলিলপত্র বা বন্দোবস্ত প্রথার বিষয়ে জানতেই পারেনি। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে (সিএস) না হওয়ার ফলে পাহাড়িদের ভূমির ওপর মালিকানা নির্ধারণে জটিলতা ছিলই। তার ওপর ১৮৮৫ সালে যখন জমিদারি প্রথা বিলোপ করে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করা হয় তখনো উদ্দেশ্যমূলকভাবে পার্বত্য অঞ্চলকে এ আইনের আওতায় আনা হয়নি। পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ সালে নতুন করে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করা হলেও তাতে আদিবাসীদের সম্পত্তির অধিকারের বিষয় স্থান পায়নি। সর্বোপরি, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ দেশীয় শিক্ষার মানদণ্ডে শিক্ষিত না হওয়ায় এবং রাজতন্ত্রের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব ভূমি ব্যবস্থা চালু থাকায় যে জমিতে পাহাড়িরা বসবাস করছে, সেই জমি সরকারের কাছে খাসজমি হিসেবে গণ্য হয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্পত্তির অধিকার-সংক্রান্ত যে ধারণা, তা সমতলের বাঙালির চেয়ে ভিন্ন হওয়ায় জটিলতা আরো তীব্র হয়েছে। একক সম্পত্তির অধিকারের পরিবর্তে আদিবাসীরা সমষ্টিগত সম্পত্তির অধিকারে বিশ্বাসী ছিল, যা কোনো এককে বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা কিংবা মালিকানা নির্ধারণের আইনগুলোয় আদিবাসীদের এরূপ সম্পত্তির অধিকারের কোনো স্বীকৃতি নেই। তাই জোরপূর্বক আদিবাসীদের জায়গায় বাঙালি সেটলার বসানো সম্ভব হয়েছে। যে জমিটি আদিবাসীরা বংশপরম্পরায় ভোগ করে আসছে, রাজাকে খাজনা দিয়ে যাচ্ছে, সেই জমিটি এক মুহূর্তে কোনো এক বাঙালির হয়ে যেতে পেরেছে।
পার্বত্য সমস্যা প্রসঙ্গ আলোচনায় এটিকে ‘পাহাড়ি-বাঙালি’ সমস্যা হিসেবে দেখানোর একটি স্থায়ী প্রবণতা আছে। এর পেছনে যে সূক্ষ্ম রাজনীতি শুরুতে ছিল, তা বর্তমান। এতে মূল সমস্যা আড়াল হয়ে যায় এবং সমাধান বের হয়ে আসে না। পার্বত্য সমস্যা কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণে হচ্ছে— এমন সরলীকরণ বেশ দুরূহ। তবে সবকিছু ছাপিয়ে ভূমি গ্রাস একটি মূল কারণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। তাই শুরু থেকে এই ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া চালু করতে রাষ্ট্রীয় যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ হওয়া দরকার।
ব্রিটিশ শাসনামল, পাকিস্তান কিংবা একাত্তরের পর স্বাধীন বাংলাদেশ, আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও তাদের জীবনের মান উন্নয়নের প্রশ্নে সব সরকারই উদাসীন ছিল এবং এখনো তা-ই আছে। তাই তাদের স্থায়ীভাবে পাহাড়ে বসবাসে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে যত রকম অপকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব, তার সবটাই ব্যবহার হতে দেখেছি পাহাড়ে। যদি পাহাড়ে কোনো অধিবাসী কোনো সম্পত্তিকে তার নিজের বলে দাবি করতে চান, তবে তাকে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী মালিকানা স্বত্ব বা রেকর্ড অফ রাইট প্রচলিত অর্থে খতিয়ান দেখাতে হবে। আমাদের দেশে খতিয়ান বলতে আমরা ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু হওয়া ভূমি জরিপ যা সিএস, যা ১৮৮৮ সালে শুরু হয়ে সংশোধনীসহ ১৯৪০ সালে সম্পন্ন হয়, পাকিস্তান আমলের স্টেট এক্যুজিশন (এসএ), যা ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ২৭-৩১ ধারা অনুযায়ী ১৯৫৬-৬০ সালে প্রস্তুত করা হয়; এরপর ওই এসএ খতিয়ানে অতিরিক্ত পরিমাণ ভুল রেকর্ড থাকার কারণে পুনরায় ১৯৬৫ সালে শুরু হয়ে বাংলাদেশ আমলে রিভিশনাল সার্ভে (আরএস) সম্পন্ন করা হয়, এরপর ভূমি জরিপ হালনাগাদ করার লক্ষ্যে ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশ সার্ভে (বিএস) শুরু হয়, যা চলমান। এসব জরিপ বা খতিয়ানের পাশাপাশি শহরাঞ্চলে মহানগর জরিপ, নদী বিধৌত অঞ্চলে দিয়ারা জরিপ হয়েছে, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে সে রকম কোনো তত্পরতা এ-যাবত্কালে দেখা যায়নি। ফলে তিন পার্বত্য জেলায় আদিবাসীদের জীবনমানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তাদের সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।
এবার জেনে নেয়া যাক খতিয়ানে কী কী বিষয় উল্লেখ থাকে
খতিয়ানে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, সে সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিধিমালার ১৮ নম্বর বিধিতে নিম্নলিখিত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে—
ক. প্রজা বা দখলদারের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা।
খ. প্রজা বা দখলদার কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।
গ. প্রজা বা দখলদার কর্তৃক জমির অবস্থান শ্রেণী, পরিমাণ ও সীমানা।
ঘ. প্রজার জমির মালিকের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা।
ঙ. এস্টেটের মালিকের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা।
চ. খতিয়ান প্রস্তুতের সময় খাজনা এবং ২৮, ২৯, ৩০ বিধি মোতাবেক নির্ধারিত খাজনা।
ছ. গোচরণ ভূমি, বনভূমি ও মত্স্য খামারের জন্য ধারণকৃত অর্থ।
জ. যে পদ্ধতিতে খাজনা ধার্য করা হয়েছে তার বিবরণ।
ঝ. যদি খাজনা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে যে সময়ে ও যে যে পদক্ষেপে বৃদ্ধি পায় তার বিবরণ।
ঞ. কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে প্রজা কর্তৃক পানির ব্যবহার এবং পানি সরবরাহের জন্য যন্ত্রপাতি সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত প্রজা ও জমির মালিকের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের বিবরণ।
ট. প্রজাস্বত্ব সম্পর্কিত বিশেষ শর্ত ও তার পরিণতি।
ঠ. পথ চলার অধিকার ও জমিসংলগ্ন অন্যান্য ইজমেন্টের অধিকার।
ড. নিজস্ব জমি হলে তার বিবরণ।
ঢ. ২৬ নং ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা।
এছাড়া একটি খতিয়ানে তার নিজস্ব খতিয়ান নম্বর, দাগ, বাট্টা, এরিয়া, মৌজা ও জেএল নম্বর থাকে।
এসবের সঙ্গে মালিকানার দলিল, নামজারি পত্র, খাজনার রশিদসহ আরো কিছু দলিল থাকে, যা কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির ওপর মালিকানা ও অধিকার আইনানুগভাবে নিশ্চিত করে।
যদি বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে তিন পার্বত্য জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো এবং উল্লিখিত সব বিষয় সরকারি জরিপে সন্নিবেশ করা হতো তাহলে পরবর্তী সময়ে আদিবাসীদের ভূমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা সহজ হতো এবং রাষ্ট্রীয় মদতে তাদের ভূসম্পত্তি যুগ যুগ ধরে নির্বিবাদে কেড়ে নেয়া সম্ভব হতো না। ১৯৭৯ সালে তত্কালীন সরকার পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের পার্বত্য অঞ্চলে সেটেলমেন্ট দিতে শুরু করে। ৩০ হাজার বাঙালি পরিবারকে প্রাথমিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এজন্য ৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এই ৩০ হাজার বাঙালি পরিবারকে পুনর্বাসনের পর থেকেই মূলত পাহাড়ি-বাঙালি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়া শুরু হয়। সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে সেখানে শুরু হয় হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন। আঞ্চলিক নিরাপত্তার নামে সেখানে বিপুলসংখ্যক সেনা ক্যাম্প নির্মাণ (মোট সেনাবাহিনীর তিন ভাগের এক অংশ) করা হয়, যা মূলত আদিবাসীদের দমনপীড়ন ও সরকারের ভূমিগ্রাসের নীল নকশা বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছে এবং এখনো তা-ই করে যাচ্ছে। সেনা নিয়ন্ত্রিত কিংবা তথাকথিত গণতান্ত্রিক যে সরকারই আসুক না কেন, আদিবাসীদের নিধন কিংবা তাদের সম্পদ গ্রাস করার ক্ষেত্রে তাদের চরিত্র আলাদা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা সবসময় একই রকম আচরণ করেছেন ও করছেন।
এই হত্যা নির্যাতনের রূপ কেমন তা নিয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে— ‘গভীর রাতে ৫০ জনের মতো আর্মি এসে গ্রামের সব মানুষকে এক জায়গায় জড়ো করল। ভোর নাগাদ সবাই গ্রেফতার। আমাকে উলঙ্গ করে হাত-পা বেঁধে রাখা হলো। আমাকে তারা ধর্ষণ করল। সেখানে আরো তিনজন নারী ছিল। সবার সামনে এমনকি আমার শ্বশুরের সামনে আমাকে ধর্ষণ করল। আমার চোখের সামনে বাকি তিনজন নারীকেও ধর্ষণ করল তারা।’ ১৯৮৬ সালে সহিংসতাকালীন একটি ঘটনার ভিকটিমের বর্ণনা, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের, ‘জীবন আমাদের নয়’ শিরোনামের একটি লেখায় ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। সে সময় ৯৬ হাজার আদিবাসী আক্রমণের শিকার হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যায়।
১৯৯৭ সালে জনসংহতি সমিতি তথা শান্তি বাহিনীর সঙ্গে তত্কালীন আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চুক্তি হয় এবং আদিবাসীরা তাদের সম্পত্তির অধিকারসহ অন্য অনেক দাবিদাওয়া পূরণের শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধাপে যেসব শর্ত পূরণ করার কথা ছিল সরকারের, তার মৌলিক অধিকাংশ শর্তই এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে। ফলে পাহাড়ে শান্তি আসা দূরে থাক, নিজেদের মধ্যে বিভাজন সুস্পষ্ট হয়েছে। চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে থাকা আদিবাসী আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আত্মঘাতী সংঘাতের ফলে চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নে কার্যকর চাপ সৃষ্টি করা যায়নি। ফলে এ চুক্তির আগে যেমন সংঘবদ্ধ নিপীড়ন-নির্যাতন ছিল, তা এর পরে কমার কোনো লক্ষণই দেখা যায়নি বিগত দুই দশকে।
আদিবাসীদের হত্যা ও নিপীড়ন প্রসঙ্গে বিগত সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও কাপেং ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক মনে করছি— ২৫/৩/১৯৮০ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আর সেটলারদের দ্বারা সর্ব প্রথম গণহত্যা হয়েছিল কাউখালী বাজার কলমপতিতে (রাঙ্গামাটি)। আদিবাসীদের একটি সমাবেশে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ৩০০ জন এবং ১০০০-এর বেশি পাহাড়ি মানুষ রিফিউজি হিসেবে ভারতের ত্রিপুরায় পালিয়ে যায়। যেসব আদিবাসী দেশ ত্যাগ করেন, তাদের সম্পত্তি আজ বাঙালিদের দখলে। পরিকল্পনাকারী সেনা কর্মকর্তারা প্রমোশন পেয়েছিলেন বলে কথিত আছে। ২৬/৬/১৯৮১ তারিখে প্রথম বাঙালি সেটেলমেন্ট এর পর বানরাইপাড়া, বেলতলী ও বেলছড়িতে সেটলার বাঙালিরা সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় ৫০০ পাহাড়িকে হত্যা ও গুম করেছিল এবং ৪ হাজার ৫০০ পাহাড়ি সে সময় ভারতে শরণার্থী হিসেবে চলে যেতে বাধ্য হয়।
১৯/৯/১৯৮১ তারিখে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটলার বাঙালিরা তেলাফং, আসালং, গৌরাঙ্গপাড়া, তবলছড়ি, বরনালাসহ মোট ৩৫টি পাহাড়ি গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় এবং এক হাজার আদিবাসীকে হত্যা করে। এ আক্রমণের ফলে অগণিত পাহাড়ি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তবে বাংলাদেশ সরকার কখনই এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেনি।
৩১/৫/১৯৮৪ তারিখে ভোরে শান্তিবাহিনী গোরস্তান, ভূষণছড়া ও ছোটহরিনার তিন বিডিআর ক্যামপ আর ক্যাম্পের কাছের সেটলারদের গুচ্ছগ্রামে আক্রমণ করে। এতে সরকারি হিসাবে ৩২ এবং বেসরকারি হিসাবে ১০০ জনের মতো সেটলার বাঙালি নিহত হয়। এর প্রতিশোধ হিসেবে সেনা-সেটলার মিলিত বাহিনী, ৩০৫ নং সেনা ব্রিগেড, ২৬ নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও বিডিআরের (বর্তমান বিজিবি) ১৭ নং ব্যাটালিয়ন মিলে নিরস্ত্র পাহাড়ি গ্রাম (হাটবাড়িয়া, সুগুরী পাড়া, তেরেঙ্গা ঘাট, ভূষণছড়া, গোরস্তান, ভূষণবাঘ ইত্যাদি) আগুনে জালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ আছে। সরকারি হিসাবে ৫২ আর বেসরকারি হিসাবে সে সময় ৪০০ পাহাড়ি নিহত হয়েছিল।
২৯/০৪/১৯৮৬ তারিখে শান্তিবাহিনী পানছড়িতে বিডিআর ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল। এর ফলে সেনা আর সেটলাররা সেখানকার গোলাকপতিমাছড়া, কালানাল, ছোট কর্মপাড়া, কেদেরাছড়া, পুজগাং, লোগাং, হাতিমুক্তিপাড়া, নাপিতপাড়া, দেওয়ানপাড়া প্রভৃতি পাহাড়ি গ্রামের মানুষজনকে একটা মাঠে ডেকে জড়ো করে তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চলায়। ফলে ১০০ পাহাড়ি মারা যায়, যেখানে মিরিজবিল এলাকার এক ৭০ বছরের পাহাড়ি বৃদ্ধাও ছিল।
২/৫/১৯৮৬ তারিখে পানছড়ির ঘটনার ঠিক একদিন পর মাটিরাঙায় যেই পাহাড়িরা ভারতে পালাচ্ছিল, সেই নিরস্ত্র দেশত্যাগী মানুষের ওপর সেনারা এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে ৭০ জন পাহাড়িকে হত্যা করে।
এ হত্যাযজ্ঞের দুই সপ্তাহ পার হতে না হতেই ১৮/০৫/১৯৮৬ ও ১৯/০৫/১৯৮৬ তারিখে মাটিরাঙা থেকে প্রায় ২০০ জন ত্রিপুরা নারী-পুরুষ, যারা বাঁচার আশায় শিলছড়ি থেকে ভারতীয় সীমান্তের দিকে পার হচ্ছিল, তারা তাইদং, কুমিল্লাটিলা গ্রামের মাঝামাঝি এক সরু পাহাড়ি পথ পাড়ি দেয়ার সময় বিডিআরের ৩১ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাদের ওপর হামলা চালায়। ফলে প্রায় ১৬০ জন পাহাড়ি নিহত হয়, এমনকি গুলির হাত থেকে বেঁচে যাওয়া আহতদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ও দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ৮, ৯, ১০ আগস্ট ১৯৮৮ সালে হিরাচর, শ্রাবটতলী, খাগড়াছড়ি, পাবলাখালীতে আনুমানিক ১০০ পাহাড়িকে নির্মমভাবে হত্যা ও গুম করা হয়। সেনা ও সেটলার দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয় অনেক পাহাড়ি নারী।
২৭/১২/১৯৯০ তারিখে পুনর্বাসিত বাঙালি কর্তৃক চার পাহাড়ি হত্যা। ১০/০৪/১৯৯২ সালে লোগাঙে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়: এক পাহাড়ি মহিলা গ্রামের অদূরে গবাদিপশু চরাতে গেলে সেখানে দুজন সেটলার বাঙালি তাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালালে এক পাহাড়ি যুবক বাধা দেয় এবং বাঙালিরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে।
১৭/১১/১৯৯৩ তারিখে নানিয়াচর বাজারে পাহাড়িদের শান্তিপূর্ণ র্যালিতে অতর্কিতে হামলা চালায় সেটলাররা। পাহাড়ি ছাত্ররা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে পাশের সেনাক্যাম্প থেকে পাহাড়ি ছাত্রদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালানো হয়। এতে ২৯ জন পাহাড়ি নিহত এবং আহত হয় শতাধিক।
১৫/০৩/১৯৯৫ তারিখে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা সন্মেলনকে কেন্দ্র করে পুনর্বাসিত বাঙালিদের সংগঠন পার্বত্য গণপরিষদের হরতাল আহ্বান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মিছিলে হামলা করা হয়। এতে পাহাড়ি চার ছাত্রের মৃত্যু, ২৮ জন আহত এবং ২৪৭টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১১/০৭/১৯৯৬ তারিখে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থানার লাইল্যেঘোনা থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করা হয়। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়। তারপর থেকে আজ অবধি এ হত্যা, ধর্ষণ আর নির্যাতনের তালিকা কেবল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। আদিবাসীদের সংখ্যা তিন পার্বত্য জেলায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এখন বাঙালিদের চেয়ে কম। পাহাড়ে আদিবাসীদের সংখ্যালঘু বানানোর বঙ্গবন্ধুর হুমকি কি নিপুণভাবে ফলে গেছে!
বাঙালিদের পুনর্বাসনের নামে তিন পার্বত্য অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ভূমি দখল, হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন হয়ে আসছে ১৯৭৯ সাল থেকে। পার্বত্য সমস্যা কেবল আঞ্চলিক কোনো সমস্যা নয়। এটি আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যা। এর সমাধানকল্পে কী করণীয়, তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ নিয়ে সমাধান প্রস্তাবনাও কম নয়। ফলে কী করণীয়, তা আমাদের সরকার জানে। এসব পুঞ্জীভূত সমস্যার কারণে মওলানা ভাসানীর নির্দেশে একবার পাহাড়িরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। আমরা আশা করব, সে রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হোক। তবে আমরা নিজেরাই তাদেরকে সেদিকে আবার জোর করে ঠেলে দিচ্ছি কিনা, তাও ভেবে দেখা দরকার।
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, বণিক বার্তা পত্রিকার “অষ্ট প্রহর” ম্যাগাজিনে প্রকাশিত।