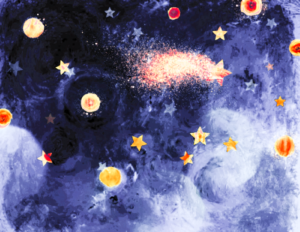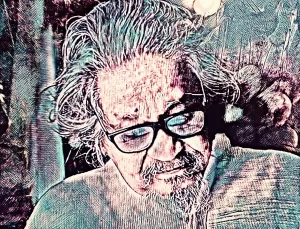ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ১০০ বছরের ইতিহাসের অন্যতম দিক হচ্ছে, এর অর্ধেক সময় কেটেছে ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায়—ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি, বাকি অর্ধেক স্বাধীন বাংলাদেশে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আত্মসমীক্ষার সময়; শতবার্ষিকী এই আত্মসমীক্ষাকে আরও বেশি প্রয়োজনীয় করে তোলে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও দরকার আত্মসমীক্ষার। এর জন্য যে প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া অত্যাবশ্যক, তা হলো—গত ১০০ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন কী।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের অর্জনের হিসাব করতে গেলে বিবেচনা করতে হবে যে নতুন জ্ঞান উৎপাদনের লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য যে অত্যাবশ্যকীয় শর্ত—বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা বা একাডেমিক ফ্রিডম—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেটা নিশ্চিত করতে পেরেছে কি না। একাডেমিক ফ্রিডমের ধারণার উপাদান দুটি—শিক্ষা দেওয়ার স্বাধীনতা এবং জ্ঞানার্জনের স্বাধীনতা। তা ছাড়া একাডেমিক ফ্রিডমের দুটি দিক হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন। প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আলাদা করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। ফলে বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা বা একাডেমিক ফ্রিডমের আলোচনার কেন্দ্রে সব সময় থেকেছে প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পেরেছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে আইনি ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে। গত ১০০ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে আইন হয়েছে তিনটি—ব্রিটিশ আমলে ১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে, ১৯৬১ সালে পাকিস্তান আমলে সেনাশাসনের আওতায় এবং ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে। মোটা রেখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের যে তিনটি পর্ব, এই আইনগুলো তারই প্রতিনিধিত্ব করে।
সূচনাপর্ব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত আছে ১৯০৫ সালের ‘বঙ্গভঙ্গ’। ১৯১১ সালে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়, তারপরে এই অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছিল। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, যেহেতু রাজনৈতিক বিবেচনাই এর প্রথম দিক ছিল, শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে রাষ্ট্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কী হবে, সেই আলোচনা উঠেছিল। ১৯১২ সালে গঠিত নাথান কমিটির সুপারিশ ছিল ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার; এই কমিটি তার প্রতিবেদনে ‘স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের’ পক্ষেই সুপারিশ করেছিল। কিন্তু ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশনকে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে পরামর্শ দিতে বলা হয়, কমিশন তখন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে মত দিয়েছিল। এই আলোচনার প্রেক্ষাপটেই ঢাকা কলেজের দুজন শিক্ষক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং টি সি উইলিয়ামস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে জোরালো বক্তব্য দেন।
১৯২০ সালের মার্চে প্রণীত আইনে ভারতের গভর্নর জেনারেলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ভিজিটর’ বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। আইনে বলা হয়েছিল, বাংলার গভর্নর হবেন চ্যান্সেলর। ভাইস চ্যান্সেলরকে নিয়োগ দেবেন চ্যান্সেলর, নির্বাহী কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে। কিন্তু নির্বাহী কাউন্সিলকে প্রভাবিত করার ব্যবস্থা আইনের মধ্যেই লুকানো ছিল। এই আইনে বলা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কোর্ট থাকবে; কোর্ট বলতে এমন এক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছিল, এখন যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বলা হয়ে থাকে, তার মতো। এতে দুই ধরনের সদস্য থাকবেন—পদাধিকারবলে এর সদস্য হবেন চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার (যিনি চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত), রেজিস্ট্রার (যাঁকে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করবেন চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে), প্রভোস্ট এবং ওয়ার্ডেনরা (যাঁরা ভাইস চ্যান্সেলরের নিয়োগকৃত), অধ্যাপকেরা এবং রিডাররা। এর বাইরে দ্বিতীয় শ্রেণির সদস্য হবেন নির্বাচিত রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট, ৫ জন নির্বাচিত লেকচারার, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি এবং জীবন সদস্য ১০ জন, যাঁদের চ্যান্সেলর নিয়োগ করবেন। এগুলো থেকে সহজেই দেখা যাচ্ছে চ্যান্সেলরের প্রভাব কতটা। নির্বাহী কাউন্সিলের ওপরে দায়িত্ব ছিল, ভাইস চ্যান্সেলরের নাম চ্যান্সেলরের কাছে সুপারিশ করবেন, কিন্তু এই কাউন্সিলের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল কোর্টের ওপরে। ফলে ঘুরেফিরে চ্যান্সেলরের অর্থাৎ সরকারের প্রভাব ছিল অভাবনীয়। এই সব ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য অনুকূল ছিল না। ফলে ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো উপাচার্যের ভূমিকা প্রশংসনীয় হলেও প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়নি।
পাকিস্তান আমল
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও এই আইনের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়েছে, একাদিক্রমে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ প্রভাব অব্যাহত ছিল। এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটে ১৯৬১ সালে—আইয়ুব খানের সামরিক সরকার কর্তৃক জারি করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে বদলে দেয় এবং আরও প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই আইনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল কোর্ট (বর্তমান সিনেটের মতো) বাতিল করে দেওয়া। নির্বাহী কাউন্সিল বাতিল করে দিয়ে তাকে সিন্ডিকেট নামকরণ করা হয়, তার সব সদস্য নির্ধারণ করা হয় পদাধিকারবলে ও প্রশাসনের মনোনীত হিসেবে এবং তার ক্ষমতা কেবল উপদেশ দেওয়ার। এই আইনে ভাইস চ্যান্সেলর সরাসরি চ্যান্সেলর কর্তৃক চার বছরের জন্য নিয়োগ হবেন। ভাইস চ্যান্সেলরের হাতে অভাবনীয় ক্ষমতা প্রদান এবং তাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষকদের আপত্তির জায়গা না থাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকার এবং ভাইস চ্যান্সেলরের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। এই আইনি ব্যবস্থাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। এই সময়ে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। তা ছাড়া শিক্ষকদের রাজনীতি করার ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক পদত্যাগ করেন এবং কয়েকজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ১৯৭৩
দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের বেশি সময় পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ জারি করা হয়। ১৯৬৯ সালের গণ–আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের দাবি ওঠে। ইতিমধ্যে অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদের নেতৃত্বে শিক্ষকদের একটি কমিটি স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন দিকের ১৪ দফাসংবলিত একটি খসড়া তৈরি করেন এবং তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের প্রতিনিধি এয়ার মার্শাল নূর খানের সঙ্গে দেখা করে এই সব প্রস্তাব পেশ করেন (মনিরুজ্জামান মিয়া, রিভিজিটিং দ্য ডি ইউ অর্ডার, ১৯৭৩, দ্য ডেইলি স্টার, ১২ মে ২০০৮)। কিন্তু এই বিষয়ে অগ্রগ্রতি হওয়ার আগেই স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনা হয়। স্বাধীনতার পরে এই খসড়াকে ভিত্তি করেই শিক্ষকদের মধ্য থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই সময়ে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এর একটি শিক্ষকদের পক্ষ থেকে, যার প্রধান ছিলেন অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক; অন্যটি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে। শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে প্রশাসনিক কমিটি শিক্ষকদের দাবি সরকারের কাছে উত্থাপন করে, যার ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করা হয়, তবে তার কার্যকারিতা শুরু ভূতাপেক্ষভাবে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে।
১৯৭৩ সালের আদেশ কেবল যে সিনেট প্রতিষ্ঠা করে, তা–ই নয়; সিনেট, সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষক ও গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এমনকি ডিন পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, বিভাগীয় প্রধানের পদে যাতে একক ব্যক্তির দীর্ঘ মেয়াদে আধিপত্য না থাকে, সে জন্য তা চাকরির মেয়াদের বিবেচনায় রোটেশনের ব্যবস্থা করে। ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের যে পদ্ধতি তৈরি করা হয়, তাতে সিনেটের পক্ষ থেকে তিনজনের একটি প্যানেল চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানো হবে, যেখান থেকে তিনি একজনকে নিয়োগ দেবেন। এই সব ব্যবস্থা স্পষ্টত অংশগ্রহণমূলক এবং দৃশ্যত গণতান্ত্রিক; কিন্তু এর মধ্যেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগে চ্যান্সেলরের কর্তৃত্বকে বিবেচনা করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে যে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান এবং বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে যে রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই কাজ করবেন। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ সব স্তরে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার ফলে এমন সব পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেগুলোতে নিয়োগের বিবেচনা হওয়া উচিত ছিল একাডেমিক ক্ষেত্রে সাফল্য; এর মধ্যে ডিন পদের নির্বাচনের কথা সহজেই উল্লেখ্য।
নতুন ব্যবস্থায় শুরু থেকেই উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই যে প্রাধান্য পেতে শুরু করে, তা সহজেই দৃষ্ট। অধ্যাপক আহমেদ কামাল, যিনি ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রথম সিন্ডিকেটে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিদের একজন ছিলেন, তিনি লিখেছেন, ‘তখন [১৯৭৩ সালে] উপাচার্য প্রফেসর আব্দুল মতিন চৌধুরী তৎকালীন সরকারি দলের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে সরকারি দলের নিয়মিত হস্তক্ষেপকে প্রশ্রয় দেন।’ ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসনের পরে উপাচার্য পদ থেকে আব্দুল মতিন চৌধুরীর অপসারণ এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অন্যায় ব্যবস্থার পেছনেও ছিল রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের পদ এতটাই দলের রাজনীতিনির্ভর হয়েছে যে উপাচার্য পদে কারা নিয়োগ পাবেন, তা এখন সহজেই বলা যায়। অধ্যাপক মইনুল ইসলাম লিখেছেন, ‘এখন কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দাবি করতে পারবেন যে সরকার তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে উপাচার্য নিয়োগ করেছে?’ (মইনুল ইসলাম, শিক্ষকদের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি, প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০১৮)।
২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং দলীয়করণের কথা বহুল আলোচিত। উপাচার্য নিয়োগ নিয়েই এই বিষয়ে বেশি আলোচনা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয়করণ কেবল উপাচার্য কিংবা পরে যখন সহ–উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়েছে, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কেননা উপাচার্য প্রশাসনে এমন ব্যক্তিকেই নিয়োগ দিতে আগ্রহী হয়েছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমত পোষণ করবেন না এবং ক্ষমতাসীনদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন—এই ধারা প্রশাসনের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে, এক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। মেরিটোক্রেসি বা মেধার চেয়ে দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য লাভ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রক্রিয়া ক্ষমতাসীনদের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার ধারা জোরদার হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের একটি গ্রহণযোগ্য কাঠামো ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশে ছিল। এ রকম একটি আইনের দাবি ছিল ১৯৬৯ সাল থেকেই। তার জন্য উদ্যোগও তখন থেকেই নেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর যখন এর একটি সুস্পষ্ট আইনি রূপ তৈরি হলো এবং তা বাস্তবায়িত হতে শুরু করল, তখন দেখা গেল যে আইনের ভেতরে সরকারের নিয়ন্ত্রণের যতটা ব্যবস্থা করা আছে, তারও ব্যবহার শুরু হয়েছে। উপাচার্য নিয়োগপ্রক্রিয়ার রাজনৈতিকীকরণের সূচনা ১৯৭৩ সালেই। এরপর এই অবস্থার ব্যতিক্রম হয়নি, ক্ষমতায় কে আছেন সেটা বিবেচ্য নয়। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে একই প্রক্রিয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি হিসেবে অন্তত একজন উপাচার্য এ ধরনের চাপের মোকাবিলা করেছেন; নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে পদত্যাগ করেছেন। গত ৫০ বছরে কমপক্ষে ১৪ জন স্থায়ী উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই সময়ে কাঠামোগতভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাব তাতে হ্রাস পায়নি, বরং ক্রমেই বেড়েছে। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে তা ক্রমাগতভাবে এক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। উপাচার্যদের নিয়োগ এবং তাঁদের দায়িত্বের অবসানের ইতিহাসের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়।
বিশ্ববিদ্যালয় যখন দলীয়করণের হাতিয়ার
১৯৬১ সালের অধ্যাদেশে শিক্ষকদের রাজনীতি করার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালে এই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয়করণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। যে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলগুলোর বিষয়ে গণমাধ্যমে পরিচিতি দেওয়া হয় আওয়ামী লীগ–সমর্থিত অথবা বিএনপি–সমর্থিত বলে। দুর্ভাগ্যজনক যে ১৯৯১ সালের পর তার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ক্ষমতাসীনেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সর্বব্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ রাখতে চেয়েছে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে এই যে ১৯৯১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশে নির্বাচিত বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় থেকেছে এবং গণতন্ত্র চর্চার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত সংস্থা ডাকসুতে নির্বাচন হয়নি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয়করণ প্রক্রিয়ার ধারা গত দেড় দশকে ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রক্রিয়ার দলীয়করণের পেছনে যা কাজ করেছে তা হচ্ছে শিক্ষকদের দলীয় আনুগত্য। শিক্ষকেরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছেন সেটা অস্বাভাবিক নয়, সুস্থ ভিন্নমতের অনুপস্থিতি বরং বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করা যেত। কিন্তু তাঁদের এই বিভক্তি দলের বিবেচনাপ্রসূত—তাঁদের পেশার উন্নয়নের প্রশ্নে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের বিষয় নিয়ে ভিন্নমত থেকে তৈরি নয়। যদিও এসব বিভক্তিকে আদর্শিক মোড়ক দেওয়া হয়, কিন্তু তার কতটা আদর্শিক সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এসব বিভক্তির উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে। দলের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই পাওয়া যাবে তা নয়, অন্যত্র নিয়োগের মধ্য দিয়েও তা করা হয়েছে।
জবাবদিহির অনুপস্থিতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষক ২০১৯ সালে লিখেছেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বশাসনের অধিকারবোধটি প্রায় হারিয়ে গেছে জ্ঞানের অচর্চায়, ক্ষমতার আকর্ষণে। স্বাধীন জ্ঞানচর্চার সঙ্গে কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রক্ষমতার যে বিরোধ রয়েছে, আমরা তা বেমালুম ভুলে গেছি। নীতিহীন ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক অন্ধ দলীয় রাজনীতির জন্য মুক্তচিন্তা আর বিবেকের স্বচ্ছতাকে বিসর্জন দিতে আমাদের একবিন্দুও বাধে না’ (‘সাম্প্রতিক ভর্তি জালিয়াতি ও বিবেকের বৈকল্য’, প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।
এর পেছনে কাজ করেছে ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশকে কেবল নির্বাচনের বিষয় বলে বিবেচনা করা, জবাবদিহির অনুপস্থিতিকে আমলে না নেওয়া। আহমেদ কামালের দীর্ঘ বর্ণনা এই কারণে উদ্ধৃত করা দরকার যে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়: ‘তিয়াত্তরের অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রশাসনে ব্যাপক গণতন্ত্রায়ণ হলো, কিন্তু সে গণতন্ত্রায়ণ ছিল নিতান্তই আনুষ্ঠানিক—কতগুলো নির্বাচনের সমাহার মাত্র। সেই নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় জড়িয়ে আমরা ভুলে গেলাম যে শুধু ভোট দিলেই গণতন্ত্রায়ণ হয় না, গণতন্ত্রায়ণের জন্য প্রয়োজন যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ তা আমরা অচিরেই বিসর্জন দিলাম—অবহেলিত হলো গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, তৈরি হলো না যুগোপযোগী কারিকুলাম, হলো না মেধার মূল্যায়ন। অনিয়মের অভিযোগ এল শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে—মেধা প্রায়ই হটে গেল দলীয় শক্তির দাপটে। এই প্রক্রিয়ায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মান হলো নিম্নগামী, শিক্ষকের মর্যাদা হলো ভূলুণ্ঠিত। জাতীয় রাজনীতি ও ছাত্ররাজনীতির অদূরদর্শী আঁতাতে শিক্ষাঙ্গন হলো সন্ত্রাসের আখড়া। কিছু শিক্ষকের জন্য ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত হীনস্বার্থ চরিতার্থতার কৌশল। নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাত্রা যে গতিতে বাড়ল, সেই গতিতেই হারিয়ে গেল শিক্ষকদের জবাবদিহির প্রক্রিয়া। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শুরু হলো রাজনৈতিক দলের বেপরোয়া লেজুড়বৃত্তি, রাজনৈতিক দলের কর্মীদের জন্য সৃষ্টি করতে হলো অন্যায় সুযোগ-সুবিধা। আর নিজেদের জন্য এই অন্যায় সুযোগ-সুবিধার খেলায় অনেক শিক্ষকই পিছপা ছিলেন না। এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় সহায়ক হলো তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশে আমাদের জন্য সবই ছিল, ছিল না শুধু জবাবদিহির ব্যবস্থা।’
প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনের বদলে সরকারি নিয়ন্ত্রণের পরিণাম কেবল যে শিক্ষকদের ওপর প্রভাব ফেলেছে, তা নয়। এর প্রভাব ফেলেছে ছাত্ররাজনীতির ওপরও। যেহেতু উপাচার্য এবং প্রশাসন ক্ষমতাসীন দলের আনুকূল্যের ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন, সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে। ছাত্রাবাসের কক্ষ বরাদ্দ কিংবা কথিত গণরুমে শিক্ষার্থীদের জায়গা দেওয়া, এমনকি ছাত্রাবাসে ‘টর্চার সেল’ থাকার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মৌন সম্মতির কারণ হচ্ছে, তার কুশীলবদের হাতেই প্রশাসনের ভাগ্য নির্ভরশীল। যে বিশ্ববিদ্যালয় তার সবচেয়ে বড় সাফল্যের তালিকায় ছাত্রছাত্রীদের ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনের কথাই বলে থাকে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে ক্যাম্পাসে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রকর্মীদের বাইরে আর অন্য কোনো দলের প্রায় উপস্থিতিই নেই।
দলীয় আনুগত্যের কারণে শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রকর্মীদের সম্পর্ক শিক্ষক-ছাত্রের চেয়ে একই দলের সহযোদ্ধার মতো হয়ে উঠেছে। তদুপরি ক্ষমতাসীনদের কাছে ছাত্রনেতারা যত সহজে পৌঁছাতে পারেন, একই দলের অনুগত শিক্ষকেরাও প্রায়ই সেই সুযোগ পান না। ফলে ছাত্রনেতারা হয়ে ওঠেন তাঁদের যোগাযোগের বাহন। দলীয় বিবেচনায় প্রশাসনিক পদে নিযুক্তির কারণে নিয়োগকৃতদের রক্ষা করার অলিখিত দায়িত্ব বর্তায় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রনেতা ও কর্মীদের ওপর। এ সবই হয়েছে প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক বিষয় তার অনুপস্থিতির কারণে।
সামনের চ্যালেঞ্জ
একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে আমরা বাস করছি, প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং বিশ্বায়নের কারণে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সব প্রতিষ্ঠানের সামনেই এখন বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ উপস্থিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জ্ঞান সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে যুক্ত হওয়া, শিক্ষার্থীদের সেই সমাজের জন্য প্রস্তুত করা। কিন্তু একই সময়ে সারা বিশ্বেই এক ধরনের জ্ঞান বৈষম্য তৈরি হচ্ছে, ডিজিটাল ডিভাইড তার একটি উদাহরণ। ২০২০ সাল থেকে করোনাভাইরাস মহামারি এই বৈষম্য এবং পরিবর্তন দুইয়ের তাগিদকে জরুরি করে তুলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার যোগ্য মানুষ তৈরি করতে হবে। উন্নয়নশীল একটি দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এই দায়িত্ব তার ওপরই বর্তায়।
এই চ্যালেঞ্জ কেবল নতুন নতুন বিভাগ তৈরি করে মোকাবিলা করা যাবে না, তার জন্য দরকার হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীন জ্ঞানচর্চার স্থানে পরিণত করা; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কাঠামো তৈরি এবং তা চর্চার ব্যবস্থা করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কাঠামো, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিচালন ব্যবস্থা এর অনুকূল নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের ভাষা ধার করে বলতে হচ্ছে, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন আর ফটকের দরজা হয়তো খোলা আছে ঠিকই, কিন্তু চিন্তা, নিয়মনীতি, গবেষণা আর সৃজনশীল চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন স্থায়ী ধর্মঘট চলছে, সেই ধর্মঘট ভাঙা আজ সময়ের দাবি’ (‘সাম্প্রতিক ভর্তি জালিয়াতি ও বিবেকের বৈকল্য’, প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর ব্যাপক অপব্যবহার, এই আইন লঙ্ঘনে ক্ষমতাসীনদের উৎসাহ, শিক্ষকদের মধ্যে দলের প্রতি বিবেকহীন আনুগত্য অব্যাহত রেখে অগ্রসর হওয়ার পথ নেই।
কোনো প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত নয়; ভবিষ্যৎ হচ্ছে সচেতন সক্রিয়তার ফসল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। গণতন্ত্র, বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। এই বিষয়ও নিশ্চয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটি রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে আলাদা করে একটি বা দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এগুলো অর্জন করতে পারে কি না। এটি বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস তার একটি কারণ, অন্যটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোনো দ্বীপ নয় যে সমাজের এই চাহিদা থেকে সে বিযুক্ত থাকতে পারবে; এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্যও নয়। এই দায়িত্ব কেবল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপরও বর্তায়। আগামী দিনগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই ভূমিকা পালন করুক—শতবার্ষিকীতে সেটাই প্রত্যাশা।
[প্রথম আলো’তে প্রকাশিত, ২৯-৩০ জুন ২০২১]