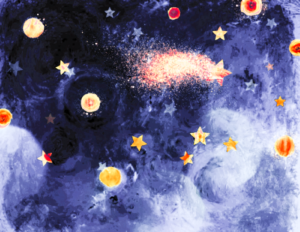dated 1945. New York, Museum of Modern Art (MoMA)
রাজনীতি অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে না কেন?
বাংলাদেশের রাজনীতি যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেন এবং গত কয়েক বছরের ঘটনাবলির দিকে যাঁরা নজর রেখেছেন, তাঁদের কাছে এটা স্পষ্ট যে দেশে দুটি বড় ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে। একটি বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট, অন্যটি রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের ব্যাপক প্রভাব। এই দুই প্রবণতার প্রেক্ষাপট হচ্ছে প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। এই প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ১৯৯০ সালের পরে, যখন সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশে একধরনের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যাকে আমরা গণতান্ত্রিক শাসন বলে চিহ্নিত করি, তার সূচনা হয়। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আড়াই দশক পরে এখন সমাজ ও রাজনীতিতে যে দুই প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো কি পরস্পর-সম্পর্কিত? সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে এবং অন্যান্য দেশের এত দিনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি। এটাও বোঝা দরকার যে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির এসব পরিবর্তন সাময়িক না দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী।
উনিশ শতকে পশ্চিমা বিশ্বে ‘সেক্যুলারিজমের’ যে ধারণা বিস্তার লাভ করে, তার আলোকে বলা হয় যে উনিশ ও বিশ শতকে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাবে। সমাজের অগ্রগতির লক্ষণ হিসেবে ‘আধুনিকায়ন’ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল; ‘আধুনিকায়ন’ ধীরে ধীরে ধর্মকে জনপরিসর থেকে বিদায় করবে, এটাই ছিল মূল যুক্তি। আধুনিকায়ন অবশ্যই কেবল অর্থনীতির বিষয় নয়, এর সঙ্গে যুক্ত সমাজের মূল্যবোধের প্রশ্ন। কিন্তু আধুনিকায়নের যে সীমাবদ্ধ ধারণা সেক্যুলারিজমের বিস্তারের কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি এবং ক্ষেত্রবিশেষে একচ্ছত্র বলে প্রচারিত হয়েছিল, তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। বিশ শতকের শেষভাগে এসে আমরা দেখতে পেলাম, সমাজ থেকে ধর্মের অবসান তো ঘটেইনি, বরং তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। ধর্মের প্রভাব বেড়েছে, রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে এর আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মের উত্থান, বিশেষত ‘উন্নয়নশীল’ দেশগুলোতে এই উত্থানের পেছনে রাষ্ট্রের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এটি কেবল সেসব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, যেখানে রাষ্ট্র নিজেই ধর্মকে সামনে নিয়ে এসেছে; সেখানেও প্রযোজ্য, যেখানে রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।
১৯৬০-এর দশকে এই ধারণার ব্যাপক প্রচার শুরু হয় যে গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনীতির বিভিন্ন ধরনের যোগসূত্র আছে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক গভীর। যোগসূত্রগুলোর বিভিন্ন দিকের সারসংক্ষেপ এই রকম: গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার দরকার হয় না, অর্থাৎ কেবল ধনী দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে, তা নয়। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন গণতন্ত্রের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে, এই সম্ভাবনার পেছনের কারণ শিক্ষার প্রসার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং নাগরিকের আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে কর্তৃত্ববাদী দেশ ক্রমেই গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এও বলা হয় যে ‘বুর্জোয়ারা না থাকলে গণতন্ত্র হবে না’। যেভাবেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, (অর্থনৈতিকভাবে) উন্নত দেশে গণতন্ত্র টিকে থাকে।
গণতন্ত্রের পক্ষে মধ্যবিত্তের এই ভূমিকা কেন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধারণত যে প্রধান কারণের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে বৈষয়িক লাভ। মধ্যবিত্ত যেহেতু সম্পদের মালিকানা ভোগ করে, সেহেতু তারা চায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক, যেন খামখেয়ালি ব্যবস্থার শিকার হয়ে তাদের কিছু হারাতে না হয়। এই তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে গোড়াতে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষত ইউরোপের উদাহরণ দেওয়া হতো। কিন্তু আশি-নব্বইয়ের দশকে অর্থনৈতিকভাবে সফল বেশ কিছু দেশে আন্দোলনের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসানকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে সেসব দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং তাদের চাপের মুখেই গণতন্ত্রায়ণের পথ প্রশস্ত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৮৭ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য উল্লেখ করা হয়। স্যামুয়েল হান্টিংটন গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ বা থার্ড ওয়েভ অব ডেমোক্রেসির যেসব কারণ হাজির করেন, তার একটি হচ্ছে নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের বিকাশ। এসব আলোচনায় প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এই ধারণাই দেওয়া হয় যে কোনো দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করে, তবে সেখানে গণতন্ত্রায়ণ ঘটে বা তার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, প্রচলিত (কিন্তু একেবারে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়) তত্ত্বগুলো বলছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হলে গণতন্ত্র ও ‘সেক্যুলারিজমের’ একটি রূপ প্রতিষ্ঠিত হয় বা তার সম্ভাবনা বাড়ে।
বাংলাদেশের গত কয়েক দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে প্রচলিত হিসাব আমরা দেখি, তাতে আমরা দেখতে পাই যে সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে। তার একটা উদাহরণ কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতি অ্যাকাউন্টধারী ছিলেন মাত্র পাঁচজন। ২০১৬ সালে তা দাঁড়ায় ১ লাখ ১৯ হাজারের বেশি। বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক পরিমাণে সম্পদ পাচার হচ্ছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটির (জিএফআই) হিসাব অনুযায়ী, ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় ৭ হাজার ৫৮৫ কোটি ডলার বা ৬ লাখ ৬ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০১৪ সালেই পাচার হয়েছে প্রায় ৯১১ কোটি ডলার বা প্রায় ৭২ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা।
বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু এই হ্রাসের হার এখন কমতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাবে (এইচআইইএস ২০১৬), ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের তুলনায় সর্বশেষ ছয় বছরে (২০১১-১৬) বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হ্রাসের গতি কমেছে। আমরা দেখছি সমাজে বৈষম্য বাড়ছে। এই বৈষম্য পরিমাপের একটি পদ্ধতি জিনি সূচক, যেখানে শূন্য হচ্ছে বৈষম্যহীনতা আর এক হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈষম্য। জিনি সূচকে দেখা যাচ্ছে, জাতীয়ভাবে ২০০৫ সালে বৈষম্য ছিল দশমিক ৪৬৭। ২০১৬ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে দশমিক ৪৮৩। গত কয়েক বছরে নগর এলাকায় এই বৈষম্য বেড়েছে গ্রামের তুলনায় বেশি। তবে গ্রামাঞ্চলে ২০০৫ সালের চেয়ে ২০১৬ সালে উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছে। জাতীয় আয়ে দরিদ্র এক-পঞ্চমাংশ মানুষের ভাগও কমেছে। ১৯৯১ সালে দরিদ্র ২০ শতাংশের ভাগ ছিল ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ, ২০১০ সালে ৫ দশমিক ২২ শতাংশ। একেবারে দরিদ্র ৫ শতাংশের ভাগ ২০১০ সালে ছিল দশমিক ৭৮ শতাংশ, এখন তা হচ্ছে দশমিক ২৩ শতাংশ। এর বিপরীতে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশের হাতে জাতীয় আয় ২৪ দশমিক ৬১ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে কেবল একধরনের বৈষম্যই তৈরি করছে তা নয়, গত কয়েক বছরে এই প্রবৃদ্ধি দেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে খুব আশাব্যঞ্জক সাফল্য দেখাতে পারেনি। দেশে তরুণদের, বিশেষত শিক্ষিত তরুণদের এক বড় অংশ বেকার জীবনযাপন করছে এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ দুই বছরে মাত্র ৬ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, অথচ এই সময়ে দেশের কর্মবাজারে প্রবেশ করেছে প্রায় ২৭ লাখ মানুষ। অর্থাৎ মাত্র দুই বছরে দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ৪৮ লাখ। অথচ ২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর চাকরি বা কাজ পেয়েছে ১৩ লাখ ৮০ হাজার মানুষ।
অর্থনীতির এসব প্রবণতার মধ্যেই বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার বেড়েছে। বোস্টন পরামর্শক গ্রুপ, যার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন দেশে ভোক্তা ও বাজারের সম্ভাবনা বিচার করা এবং বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেওয়া, ২০১৫ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেছে যে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৭ শতাংশ বা ১ কোটি ২০ লাখ হচ্ছে ‘মধ্য ও বিত্তশালী ভোক্তা’ (‘মিডল অ্যান্ড অ্যাফলুয়েন্ট কনজিউমার’) ; এই ভোক্তা শ্রেণির বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১১-১২ শতাংশ; ফলে ২০২০ সালে তা দাঁড়াবে মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ, অর্থাৎ ১ কোটি ৯৩ লাখে; ২০২৫ সালে ৩ কোটি ৪০ লাখে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের গবেষক বিনায়ক সেনের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫ সালে মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশকে মধ্যবিত্ত বলে বিবেচনা করা যায়, যা ২০২৫ সালে দাঁড়াবে ২৫ শতাংশে (ডেইলি স্টার, ৬ নভেম্বর ২০১৫)। তিনি বলেছেন, এক দশক আগে মধ্যবিত্ত ছিল ৯ শতাংশ, ২০৩০ সালে দাঁড়াবে ৩৩ শতাংশে (ঢাকা ট্রিবিউন, ৬ নভেম্বর ২০১৫)।
তত্ত্বগতভাবে বিবেচনা করলে এবং অন্যান্য দেশের অতীত অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিলে এই বিকাশমান মধ্যবিত্তের ভূমিকা অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক পদ্ধতি ও উদার সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষেই থাকার কথা। কিন্তু বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট এবং সমাজে ধর্মের প্রসার সে ইঙ্গিত দেয় না। কিন্তু কেন? সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা দরকার।
নতুন মধ্যবিত্ত উদার গণতন্ত্রে আগ্রহী নয়?
বাংলাদেশে গত কয়েক দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা থেকে আমরা দেখতে পাই, মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার বড় হচ্ছে, অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমে দুর্বল হয়েছে এবং এখন একধরনের ‘দোআঁশলা’ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, যার কিছু উপাদান কর্তৃত্ববাদী। সমাজে ধর্মের দৃশ্যমানতা স্পষ্ট এবং ধর্মের সেই ব্যাখ্যাগুলোই প্রসার লাভ করছে, যেগুলো ধর্মের অনুদার দিকগুলোকেই প্রাধান্য দেয়। এগুলো সাধারণভাবে মধ্যবিত্তের প্রচলিত বিশ্ববীক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বলেই আমরা এত দিন জেনে এসেছি। তা সত্ত্বেও এই বিরাজমান অবস্থার প্রতি বিকাশমান মধ্যবিত্তের সমর্থন লক্ষণীয়।
মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক আছে। মধ্যবিত্তবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় ব্যবহৃত সংজ্ঞাগুলোকে দুই ভাবে ভাগ করা যায়-ব্যক্তিক (সাবজেক্টিভ) ও নৈর্ব্যক্তিক (অবজেক্টিভ)। ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণি হচ্ছে একধরনের মানসিক অবস্থান; একজন মানুষ নিজেকে মধ্যবিত্ত মনে করছে কি না, তার ওপর নির্ভর করছে তাকে আমরা সেই শ্রেণিভুক্ত করব কি না। অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক শ্রেণি নির্ধারিত হয় কতকগুলো সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচক দিয়ে। এই সূচক নির্ধারণের দুটি ধারা-একটি পরিমাণবাচক (কোয়ান্টিটেটিভ), যেমন আয়, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি। অন্যটি গুণবাচক (কোয়ালিটেটিভ), যেখানে বলা হচ্ছে যে মধ্যবিত্ত হচ্ছে তারাই, যারা কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যা তাদের অন্যান্য প্রবণতা থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করে। মধ্যবিত্তবিষয়ক আলোচনায় সাধারণত পরিমাণবাচক দিকটি প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বলতে আসলে অর্থনৈতিক বিবেচনায় মধ্যবিত্ত বোঝায়।
আমরা এই বিকাশমান শ্রেণির বিত্তের সম্ভাব্য উৎসের দিকে মনোযোগ দিতে পারি। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে কৃষি খাতের অবদান নাটকীয়ভাবে কমেছে এবং সেবা খাত প্রধান খাত হিসেবে বিকশিত হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম দশকে (১৯৭১-৮০) গড়ে মোট অভ্যন্তরীণ আয়ের ৪৫ শতাংশ আসত কৃষি থেকে, সেবা খাতের অবদান ছিল ৪৪ শতাংশ, শিল্প খাতের অবদান ছিল ১১ শতাংশ। ২০০০ সালে যেখানে কৃষি খাতের অবদান ছিল ২৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ, তা ২০১৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫ দশমিক ৫০ শতাংশে; সেবা খাত ৫২ দশমিক ৯১ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ। শিল্প খাতের অবদান ২৩ দশমিক ৩১ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ দশমিক ১৪ শতাংশ। মাঝারি আয়ের দেশগুলোতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অকৃষি খাতের অবদান বৃদ্ধি মোটেই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বাংলাদেশে গত দুই দশকে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছে, তার বিত্তের সূত্রের প্রধান উৎস বিকাশমান সেবা খাত। সেবা খাতের যে দুটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে, উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অভাব এবং বিশ্বায়নের ফলে তার বৈশ্বিক যোগাযোগ। এই দুই-ই এই শ্রেণির সদস্যদের বিশ্ববীক্ষা, মানস গঠন ও সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকায় প্রভাব ফেলবে বলে আমরা অনুমান করতে পারি।
বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট নতুন নয় এই অর্থে যে স্বাধীনতার পর থেকেই দেশটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৯০ সালের পর এই অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও গত আড়াই দশকে সাফল্য আশাব্যঞ্জক নয়। তদুপরি ২০১৪ সালে প্রায় সব বিরোধী দলের বর্জন সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন দল এককভাবেই নির্বাচন সম্পন্ন করে, যার ফলে সংসদে বিরোধী দলের কোনো অস্তিত্বই নেই। ওই নির্বাচনের আগে ও পরে ক্ষমতাসীন দল এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা মর্মবস্তুর দিক থেকে গণতান্ত্রিক বলে বিবেচিত হতে পারে কি না, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। এখন যে ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, তাকে আমরা ‘দোআঁশলা ব্যবস্থা’ (হাইব্রিড রেজিম) বলতে পারি। এর লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে এমন ব্যবস্থার উপস্থিতি, যেখানে দৃশ্যত গণতন্ত্রের কিছু দিক, যেমন নিয়মিত নির্বাচন, বিরোধী দলের উপস্থিতি, নিয়ন্ত্রিতভাবে মতপ্রকাশের উপায় এবং বিচার বিভাগের কাগুজে স্বাধীনতা থাকলেও শাসনব্যবস্থার মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়, নতুবা সেগুলো কার্যকর থাকে না, জবাবদিহির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও আইনের শাসন অনুপস্থিত থাকে এবং সাংবিধানিকভাবেই ব্যক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।
বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়া, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সততা (ইনটিগ্রিটি) প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া, ভিন্নমতের প্রকাশ সংকুচিত হওয়া, বিদ্যমান একাধিক আইনের অপব্যবহার (যেমন আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা, যার আওতায় মামলার সংখ্যা ২০১৬ সালে ছিল ৩৫ টি), ভিন্নমত নিয়ন্ত্রণমূলক নতুন আইনের প্রস্তাব (যেমন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬), ক্রমবর্ধমান বিচারবহির্ভূত হত্যা (২০১৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৭৮) এবং গুমের (২০১৬ সালে ছিল ৯০ জন) ঘটনা বৃদ্ধি সত্ত্বেও এসব বিষয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যথেষ্ট উদ্বেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।
এ থেকে প্রশ্ন তোলা যায়, গত এক দশকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে কি অনুৎসাহ লক্ষ করা যাচ্ছে? গণতন্ত্র সম্পর্কে কি ভিন্ন কোনো ধারণা তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে ‘উন্নয়ন’কে গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে উপস্থাপনের যে চেষ্টা হচ্ছে, তা কি এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে? একজন বিশ্লেষক বলছেন, ‘রাষ্ট্রের চরিত্র কী হবে, সেখানে গণতন্ত্র ও জবাবদিহি কীভাবে নিশ্চিত হবে, রাষ্ট্রপরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ কীভাবে বাড়ানো যাবে ইত্যাদি বিষয়েও সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্রমেই একধরনের নির্লিপ্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে’ (আবু তাহের খান, কালের কণ্ঠ, ৩ নভেম্বর ২০১৫)। একই সময়ে সরকার-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের একাংশের কাছ থেকে ‘গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের’ ধারণা প্রচার ও তা প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগ্রহ ও অবদান ছিল বেশি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিবিষয়ক গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলোয় সুস্পষ্টভাবে এটাই চিহ্নিত যে বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তদুপরি ১৯৮০-এর দশকে সেনাশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও এই শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
বাংলাদেশের সমাজে ধর্মের ভূমিকা ও অবস্থান বিষয়ে কথা উঠলে সাধারণত গত কয়েক দশকে সাংবিধানিক পরিবর্তন, রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক দলের বিকাশ, প্রধান দলগুলোর সঙ্গে তাদের সখ্য এবং তাদের ভূমিকার কথাই আলোচিত হয়। এসব বিষয়ের গুরুত্ব অস্বীকার না করেও বলা দরকার, এর বাইরে দৈনন্দিন জীবনাচরণেও আমরা ধর্মের উপস্থিতি দেখতে পাই। এখানে ইসলাম ধর্মের উপস্থিতি নতুন বিষয় নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক দুটি দিকের প্রতি আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত, ব্যক্তিগত জীবনাচরণের অংশ হিসেবে ধর্ম পালন করার চেয়ে তাকে সবার কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে হাজির করার প্রবণতা; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে ইসলাম ধর্মের যে সমন্বয়বাদী, উদার ধারা ও ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে, এখন তার বিপরীতে একধরনের আক্ষরিক এবং অনুদার ব্যাখ্যা, যার অধিকাংশ ইসলামপন্থী তাত্ত্বিকদের করা, তা প্রধান হয়ে উঠেছে। এই প্রবণতাগুলো সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই বেশি লক্ষণীয়। তাদের মধ্যে কেবল ধর্মের ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহই দেখা যাচ্ছে তা নয়, ধর্মাচরণকে জনসমক্ষে উপস্থাপনের মাধ্যমে তার একধরনের সামাজিক স্বীকৃতি লাভের চেষ্টাও স্পষ্ট। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বাক্য, বাগ্ধারা, সম্ভাষণ থেকেও এর পক্ষে প্রমাণ মেলে। এর সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ হচ্ছে কিছু কিছু আরবি শব্দের ব্যাপক প্রচলন। তদুপরি বাংলাদেশে প্রচলিত পোশাক-পরিচ্ছদেও এর প্রভাব দৃশ্যমান। একে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন ‘আরবিকরণ’ বলে।
গণতন্ত্র ও ধর্মের প্রশ্নে মধ্যবিত্তদের আচরণ বিষয়ে এসব পর্যবেক্ষণের অর্থ এই নয় যে গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্যই তা প্রযোজ্য। অবশ্যই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে একটি অংশ দৃশ্যত ভিন্ন আচরণ করে এবং তারা ঐতিহ্যগত ভূমিকা পালনে সচেষ্ট। কিন্তু গত এক দশকের বেশি সময়ের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমি মনে করি যে এসব প্রশ্নে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতরে একটা বড় ধরনের বিভক্তি তৈরি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে গত এক বা দেড় দশকে মধ্যবিত্তদের যে অংশের বিকাশ ঘটেছে, যাদের আমি ‘নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি’ বলে বর্ণনা করতে চাই, তাদের ভেতরেই গণতন্ত্রের উদারনৈতিক দিকগুলোর আবেদন কম এবং একই সঙ্গে তাদের মধ্য থেকেই সমাজে ও রাষ্ট্রে ধর্মের প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য ভূমিকার তাগিদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের এই নতুন বিকাশমান মধ্যবিত্তকে রেহমান সোবহান বর্ণনা করেছেন ‘এক্সক্লুসিভ’ এবং বিশ্বায়িত বা গ্লোবালাইজড বলে। এই দুই ধরনের মধ্যবিত্তের মধ্যকার পার্থক্যগুলো কী?
নতুন মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ভূমিকার অবসান?
যেকোনো সমাজে শ্রেণি হিসেবে মধ্যবিত্তকে বিবেচনা করা হয় একাদিক্রমে বিত্তের হিসাবে এবং সমাজে ওই শ্রেণির ভূমিকা দিয়ে। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে কেবল বিত্তই শ্রেণিবিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। বলা হয়ে থাকে, মধ্যবিত্ত হচ্ছে তারাই, যারা কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যা তাদের অন্য শ্রেণিগুলো থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন, বিশেষত সেবা খাতের বিকাশ, বিশ্বায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পরিপোষণের মধ্য দিয়ে যে নতুন মধ্যবিত্ত তৈরি হয়েছে, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী? তাদের সঙ্গে পুরোনো মধ্যবিত্তের পার্থক্য কী?
নতুন ও পুরোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যকার একটি বড় পার্থক্য মানস গঠনের। একে আমরা ‘সাংস্কৃতিক পুঁজির’ ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। আমি এই ধারণা ধার করেছি ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী পিয়েরে বর্দোর কাছ থেকে। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ করলে দাঁড়ায় এই রকম-সাংস্কৃতিক পুঁজি অর্জিত হয় জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তির জীবনযাপনের অভিজ্ঞতাই ব্যক্তির রুচি, অভ্যাস, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করে দেয়। আমি তাঁর বক্তব্য আরও সম্প্রসারিত করে বলতে চাই, এটা কেবল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটে তা নয়, একটি শ্রেণির ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। একটি শ্রেণি কীভাবে গড়ে উঠেছে, কীভাবে বিকশিত হয়েছে, সেটা ওই শ্রেণির সদস্যদের বিশ্ববীক্ষা ও সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয় বলে আমি মনে করি।
অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ২০১৪ সালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তবিষয়ক আলোচনায় এই সাংস্কৃতিক পুঁজির দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, ব্রিটেনের বাইরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হচ্ছে, ‘মানব, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পুঁজি’। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলাতে শুরু করেছে ১৯৮০-র দশকে, যখন ব্যাপকভাবে মধ্যবিত্তের একাংশের উন্নত দেশগুলোতে অভিবাসন এবং একটি ছোট অংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ ব্যবহার করে উঁচু শ্রেণিতে উঠে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। এর ফলে একটা শূন্যতার সূচনা হয়। সেই জায়গাতে আসে গ্রাম থেকে উঠে আসা মানুষ, যাদের মানসম্পন্ন শিক্ষার এবং রুচিগত পরিশীলনের (সফিস্টিকেশন) অভাব আছে। তারা অবশিষ্ট পুরোনো মধ্যবিত্তদের ‘নিমজ্জিত’ করে ফেলে। তিনি বলেন, ‘এখনো শিক্ষা (ডিগ্রির বিবেচনায়) ও পেশার (মূলত ব্যবসা) গুরুত্ব আছে, কিন্তু সেগুলো আর নির্ণায়ক বিষয় নয়। আয় ও সম্পদ, যা সম্প্রতি অর্জিত হয়েছে, তা-ই এই বিকাশমান মধ্যবিত্তের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে এবং সেগুলো পুরোনো মূল্যবোধ ও সেক্যুলার সংস্কৃতির জায়গাগুলো নিয়ে নিচ্ছে।’ ইসলামের এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আমি এখানে একমত যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এখন আরও সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার ভিন্নমত হচ্ছে সময়ের বিবেচনা। আমি অনুমান করি, এই পরিবর্তন হয়েছে ১৯৯০-এর দশকের পরে।
এই বিষয়ে সেলিম জাহানের প্রস্তাবিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভাজন আমাদের মনোযোগ দাবি করে। সেলিম জাহান ২০১১ সালে ইউএনডিপির একটি প্রকাশনায় বেশ কয়েকটি দেশে অর্থনীতিক উন্নয়নে মধ্যবিত্তের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বাংলাদেশ সেই গবেষণার বিষয় ছিল না। তবে তাঁর বক্তব্য বাংলাদেশকে বোঝার জন্য সাহায্য করে। সেলিম জাহান বলেছেন, গত কয়েক দশকে বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক উদারীকরণের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের ফলে ঐতিহ্যগতভাবে যে শ্রেণিকে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলে জানতাম, তাদের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি হয়েছে। এর এক অংশকে সেলিম জাহান বলছেন ‘সামাজিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি’, অন্যটিকে বলছেন ‘অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি’।
উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঐতিহ্যগতভাবে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল, তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ‘সাধারণ জীবনযাপন, উঁচু মানের চিন্তাভাবনা’ (‘সিম্পল লিভিং অ্যান্ড হাই থিংকিং’)। এই শ্রেণি কিছু আচারপদ্ধতি ও মূল্যবোধ ধারণ করে। সমাজের ক্রান্তিকালে এই সামাজিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে এবং সমাজের অন্য শ্রেণি, বিশেষত দরিদ্র শ্রেণি তাদের ওপর আস্থা রেখেছে। বিপরীতক্রমে যে নতুন ‘অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি’র বিকাশ ঘটেছে, তারা প্রধানত বয়সে তরুণ, উচ্চশিক্ষিত ও পেশাজীবী। কিন্তু সামাজিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি যেসব মূল্যবোধ ও আচারকে গুরুত্ব দিত, এরা তাকে একইভাবে গুরুত্ব দেয় না। ‘তারা অর্থের দ্বারা চালিত এবং ব্যবসা ও ভোগবাদ তাদের মননের অংশ’। তিনি বলছেন যে এদের ‘নতুন ধনিক’ বলে অভিহিত করা হয়। সেলিম জাহানের এই পর্যবেক্ষণের জন্য যেসব দেশকে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে এই নতুন শ্রেণির মধ্যবিত্তরা তরুণ ও প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য কি না, তা প্রশ্নসাপেক্ষ।
এই নতুন শ্রেণির ‘সাংস্কৃতিক পুঁজি’, যা প্রথাসিদ্ধ মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক পুঁজির চেয়ে ভিন্ন, তার ভেতরে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক (এবং অর্থনৈতিক) ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণেই কি আমরা গণতন্ত্রের বিষয়ে তাদের অনাগ্রহ লক্ষ করছি? তাহলে কি বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার সংকট স্থায়ী রূপ নিতে যাচ্ছে? একই সঙ্গে তারা যে সমাজে ধর্মের ভূমিকার প্রশ্নে মধ্যবিত্তের আগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন অবস্থা নিচ্ছে, সেটা কি একই কারণে? এই শ্রেণির সদস্যরা ধর্মকে ব্যক্তির আদর্শের চেয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শিক নির্দেশক হিসেবে দেখতে চান, নাকি কেবল ধর্মের ব্যাপারে দৃশ্যমানতার মাধ্যমে তাঁদের অন্যান্য আচরণকে বৈধতা দিতে চান?
বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বড় অংশের মধ্যে জনসমক্ষে ধর্মাচরণের প্রচারের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যকার বিভাজন বিষয়ে কী ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে? বাংলাদেশের সমাজে সেক্যুলারাইজেশনের প্রক্রিয়া কখনোই শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু সমন্বয়বাদী ইসলামের যে ধারাটি প্রধান ধারা বলে বিবেচিত হতো, মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বড় অংশই যদি আর সেই ধারা বহন না করে, তবে ভবিষ্যৎ পথরেখা কী? বাংলাদেশে কি মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক ভূমিকার অবসানের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে? বাংলাদেশের রাজনীতিতে গত কয়েক দশকে ধর্মের প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়েই উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু এই বিষয়ে বিতর্কমূলক আলোচনার বাইরে ধর্ম ও রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজ এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে ভূয়োদর্শনলব্ধ আলোচনা খুব সীমিত।
পূর্বধারণার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। বাংলাদেশের বিরাজমান পরিস্থিতি এসব বিষয়ে আলোচনা দাবি করে।
প্রথম আলো’তে প্রকাশিত, ৮, ৯ এবং ১০ জানুয়ারি ২০১৮