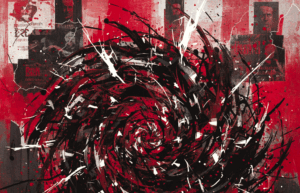This post has already been read 16 times!
সংসদীয় ব্যবস্থায় যে কোন প্রধান রাজনৈতিক দলই চাইবে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হতে যাতে করে ঐ দল দেশ শাসন করতে পারে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক। এই ধরণের ফলাফলকে দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের নেতৃত্বের সাফল্য বলেই বিবেচনা করে থাকেন। কিন্ত ক্ষেত্রে বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ই ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্যে যথেষ্ট হয়ে থাকে, ক্ষেত্রে বিশেষে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে অন্য দলের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে হয়। কিন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল কি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অতিরিক্ত, দুই-তৃতীয়াংশ আসনে, বিজয়ী হতে চায়? কোনো দেশে কোনো একক দল বা জোটের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ই হওয়া কি গণতন্ত্রের জন্যে ইতিবাচক? দুই-তৃতীয়াংশ কি আশির্বাদ বা অভিশাপ? বাংলাদেশে উপুর্যপুরিভাবে যখন তৃতীয়বারের মতো একটি সংসদ ‘নির্বাচিত’ হতে চলেছে যেখানে ক্ষমতাসীনরা দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারী হবে সেখানে এই প্রশ্নটি বিবেচনা করা জরুরি। বিবেচনা করা দরকার যে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশ থেকে ভিন্ন কিনা।
১৯৭১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত চার দশকে দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশ – বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকা-এ মোট পয়ত্রিশটি সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সব দেশের সংসদীয় নির্বাচন হয়েছে ‘ফার্স্ট পাস্ট দি পোস্ট’ পদ্ধতিতে যার অর্থ হল প্রত্যেকটি আসনে যে প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন তিনি বিজয়ী হবেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী দল, এমনকি যদি সেই দল যদি সব মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট নাও পায়, সরকার গঠন করবে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল শ্রীলংকা; সেদেশে ১৯৭৮ সালের সংবিধান পরিবর্তন করে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই পয়ত্রিষটি নির্বাচনের নয়টি হয়েছে বাংলাদেশে, ভারতে এগারোটি, পাকিস্তানে আটিটি এবং শ্রীলঙ্কায় সাতটি। এই সব নির্বাচনের মধ্যে এগারোটি নির্বাচনে বিজয়ী দল বা জোট দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয়েছে। এর মধ্যে দশটি ক্ষেত্রেই দুই-তৃতীয়াংশের শাসনে দেশটির অভিজ্ঞতা হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার, দেশে নাগরিক অধিকারের অবনতি ঘটেছে এবং সংবিধানের এমন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে যার রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া। বাংলাদেশে এই ধরণের দুই-তৃতীয়াংশের সংসদ তৈরি হয়েছে ছয় বার; ভারতে দুইবার; পাকিস্তানে দুইবার এবং শ্রীলঙ্কায় একবার।
দুই-তৃতীয়াংশের শাসনের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রথম পরিচয় ঘটে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই, দেশের প্রথম নির্বাচনে ১৯৭৩ সালে। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সংসদের ৯৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ আসন লাভ করে। এতে করে দলের পক্ষে সংবিধানের এতটাই পরিবর্তন সম্ভব হয় যে দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দেশটি এক-দলীয় ব্যবস্থায় উপনীত হয়। সংসদ তার নিজের মেয়াদ কাল বর্ধিত করে নেয় এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব সংসদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। দেশের গোটা শাসন কাঠামোই বদলে যায়। ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগের সদস্যদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদ যে সংবিধান তৈরি করেছিলো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাতে নাগরিকের মৈলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা হয়েছিল। কিন্ত দুটো সংশোধনী – দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সংশোধনী কার্যত এসব অধিকার সীমিত করে দেয়। চতুর্থ সংশোধনী বিচার বিভাগকেও নির্বাহী বিভাগের অধীনস্থ করে ফেলে। আওয়ামী লীগের শাসনের অবসান ঘটে নির্মম ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাঅভ্যুত্থানের সময় নির্মমভাবে হত্যা করা হয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি শেখ মুজিব, তার পরিবার এবং তার সহযোগী জাতীয় নেতাদের। বছরের শেষ পর্যন্ত দেশে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে অস্থিরতা চলতেই থাকে।
১৯৭৯ সালের নির্বাচনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), যার সৃষ্টি হয়েছিল সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, ৬৯ শতাংশ আসন লাভ করে। এই নির্বাচন গোড়া থেকেই সাজানো হয় যেন তা সেনা শাসনকে বৈধতা দিতে পারে। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে যে সমস্ত কার্যকলাপ করা হয়েছে সেগুলোকে বৈধতা দেয়া হয়, যার মধ্যে শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের দায়মুক্তির ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিলো। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং জাতীয়তা বিষয়ক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ পথরেখা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্রকে স্থায়ীভাবে বদলে দেয় এই সংশোধনী। ১৯৮৮ সালের নির্বাচন, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আরেক সেনা শাসক জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের আমলে, তাতে প্রধান বিরোধী দলগুলো যেমন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি অংশ নেয়নি। তাতে জেনারেল এরশাদের হাতে গড়া দল জাতীয় পার্টি ৮৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ আসনে অধিকারী হয়। এই নির্বাচনের বৈধতা প্রশ্নসাপেক্ষ থাকলেও শাসকেরা সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তত্কালীন বিরোধীরা যদিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁরা ক্ষমতায় গেলে এই ধারা তুলে দেবেন, কিন্ত তা আর কোনদিনই বাংলাদেশের সংবিধান থেকে অপসৃত হয়নি।
তবে দুই-তৃতীয়াংশ – বা সুপার মেজরিটির- সবচেয়ে বড় উদাহরণ হয়ে ওঠে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন যা অনুষ্ঠিত হয় খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের আমলে। সবচেয়ে কম ভোটারের সমর্থন নিয়ে গঠিত সংসদে বিএনপি ছাড়া আর কোনো দলই বিজয়ী হয়নি, কেননা প্রধান সব দলই তা বর্জন করে। সংসদের একশো শতাংশ আসনে বিজয়ী বিএনপি স্বল্পতম সময়ে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ায়। এই সংশোধনী নির্বাচনকালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে; বিরোধী দলের চাপের মুখে তাড়াহুড়ো করে করা এই সংশোধনীর ব্যাপারে সংসদ আর কারো মতামতই নেয় নি এবং তা যে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার বীজ বপন করেছিলো ২০১৩ সালে এসে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই চারটি নির্বাচনের মধ্যে দুটি নির্বাচন এবং তার ফলাফলকে আমরা ব্যত্যয় বলে ধরতে পারি এই বিবেচনায় যে সেগুলো হয়েছিলো সেনাশাসনের আমলে সেই সব শাসনকে বৈধতা দেবার জন্যে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনকে আমরা এই বলে বিবেচনার বাইরে রাখতে পারি যে তা ছিলো বিরোধীদের চাপের মুখে এবং সেই সংসদ দেশ শাসনের চেষ্টা করেনি।
কিন্ত এই সব কোনো বিবেচনাই আমরা তৈরি করতে পারিনা ২০০১ এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনের ব্যাপারে। সবচেয়ে সুষ্ঠু ও অবাধ বলে যে নির্বাচনগুলোকে মনে করা হয় তার মধ্যে এই দুই নির্বাচন অন্যতম। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি’র নেতৃত্বাধীন ৪-দলীয় জোট ৭০ দশমিক ৬৭ শতাংশ আসনে বিজয়ী হয়। বিএনপি’র নেতৃত্বাধীন এই সরকারে আমলে দেশে ইসলামপন্থী জঙ্গী গোষ্ঠীর উত্থানের ঘটনাই শুধু ঘটেনি, পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের পদে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন বিচারককে বসানোর উদ্দেশ্যে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাশ করা হয় যাতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বাড়ানো হয়। এতে করে যে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সূচনা হয় তার পরিণতিতেই ২০০৭ সালের নির্বাচনের তফসিল বাতিল করে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং দুই বছর দেশ শাসন করে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট; তাদের প্রাপ্ত আসনের পরিমাণ ৮১ শতাংশ। নির্বাচনের তিন বছরের মধ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলোপ ঘটায়। সংবিধান সংশোধনের জন্যে গঠিত সংসদীয় কমিটি, যার সব সদস্যই ছিলো ক্ষমতাসীন দলের, এই ব্যবস্থা রাখার পক্ষে মত দিলেও আদালতের একটি রায়ের ওপরে আংশিকভাবে নির্ভর করে এই ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানোর ফলে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করছে এবং দেশ জুড়ে এক সহিংস অস্থিরতার সূচনা হয়েছে।
লক্ষনীয় এই যে বাংলাদেশ সেনাশাসকরা সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের জোরে সংবিধানের যত পরিবর্তন ঘটিয়েছে দেশের বেসামরিক রাজনৈতিক দলগুলো তা থেকে মোটেই পিছিয়ে থাকেনি।
ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার অভিজ্ঞতা
সংসদীয় নির্বাচনে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভের জন্যে যে কোনো রাজনৈতিক দল চেষ্টা করবে সেটাই স্বাভাবিক। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাবার জন্যে যে কোনো দলেরই নেতৃত্ব চাইবে তার দলের প্রতি ভোটারদের নিরঙ্কুশ সমর্থন। কিন্ত কোনো দল বা জোট যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বেশি, অর্থাৎ সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন, লাভ করে তখন তা কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যে ইতিবাচক ফল বহন করে, নাকি তা দেশের জন্যে অভিশাপ হয়ে ওঠে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশ – বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা-র গত চার দশকের (১৯৭১-২০১১) পয়ত্রিশ নির্বাচনের দিকে মনোনিবেশ করেছি। তাতে দেখা যায় যে এগারোটি নির্বাচনে কোনো দল বা জোট দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করেছে। বাংলাদেশে এই ধরণের দুই-তৃতীয়াংশের সংসদ তৈরি হয়েছে ছয় বার; ভারতে দুইবার; পাকিস্তানে দুইবার এবং শ্রীলঙ্কায় একবার।
ভারতে ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী’র নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস লোক সভায় ৬৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ আসন লাভ করে। এই সুপার মেজরিটির কারণেই ক্ষমতাসীন দলটির পক্ষে সংবিধানের চব্বিশতম সংশোধনী পাশ করা সম্ভব হয়। এই সংশোধনীর সূত্রপাত হয় দেশের বিচার বিভাগের সাথে ক্ষমতাসীন দলের সংঘাত থেকে। সুপ্রিম কোর্ট একটি রায়ে বলে যে সংবিধানের মৌলিক অধিকার বিষয়ক ধারাগুলো সংশোধনের কোনো অধিকার সংসদের নেই। আদালত মৌলিক অধিকারগুলোকে প্রকৃতিগতভাবে ‘ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল’ বা অতিন্দ্রীয় বলে বর্ননা করে এবং রায় দেয় যে সংসদ মৌলিক অধিকারগুলো সংক্ষেপিত করার বা তা হরণ করার অধিকার রাখেনা। এই রায়ের পর ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সংবিধানের ১৩ এবং ৩৬৮ অনুচ্ছেদের সংশোধনী পাশ করে সংবিধানের ২৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে এবং এই অনুচ্ছেদগুলোর সংশোধনীর কারণেই সংসদ মৌলিক অধিকার স্থগিত করতে সক্ষম হয়। ১৯৭১ সালের এই সংশোধনীগুলোকে অনেকেই ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার প্রসার বলে বিবেচনা করে থাকেন। সংবিধানের সংশোধনীর কারণেই ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা সম্ভব হয়, যার আওতায় নাগরিক অধিকারগুলো এবং নির্বাচন মুলতবি করা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৭৫ সালের ১২ জুন এলাহাবাদের আদালত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে বাতিল করে দেন এবং তার আসন শুন্য ঘোষণা করেন। আদালত তাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের অধিকার দেয় কিন্ত তার সংসদ সদস্য পদ বাতিল করে দেয়। আদালত তাকে পরবর্তী ছয় বছর নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অযোগ্য বলেও ঘোষণা করে। তার ১৫ দিনের মধ্যেই দেশে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দেয়া হয়। উনিশ মাসের এই জরুরি অবস্থার আমলে জাতীয় সংসদ এবং রাজ্য পর্যায়ের নির্বাচনগুলো স্থগিত রাখা হয়।
ভারতে দ্বিতীয়বার কোনো দলের দুই তৃতীয়াংশ আসন পাবার ঘটনা ঘটে ১৯৮৪ সালে। রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৭৫ দশমিক ৮ শতাংশ আসন লাভ করে। এই ব্যাপক বিজয়ের পেছনে ছিল ভোটারদের সহানুভূতি। ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজীব গান্ধীর পাঁচ বছরের শাসনামলকে নেতৃত্বের দুর্বলতায় জরাজীর্ন বলে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে ক্ষমতাসীনরা বড় ধরণের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে বলেও অভিযোগ রয়েছে। রাজীব গান্ধী নিজে সুইডিশ এক অস্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বোফর্স-এর কাছ থেকে ১৯৮৬ সালে উৎকোচ নিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে এবং এখনও এই বিষয়টির কার্যত নিস্পত্তি হয়নি। কিন্ত এই সব সমালোচনার পাশাপাশি এই কৃতিত্ব রাজীব গান্ধীর প্রাপ্য যে দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও সংবিধানের পরিবর্তন ঘটান নি বা সংবিধান-বহির্ভূতভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করেন নি।
পাকিস্তানের ইতিহাসে সুপার মেজরিটির ঘটনা ঘটেছে দুইবার, কুড়ি বছরের ব্যবধানে, ১৯৭৭ এবং ১৯৯৭ সালে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচন ছিলো বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তানের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন। ১৯৭২ সাল থেকে জুলফিকার আলী ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ক্ষমতায় ছিলো কেননা ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনই ছিলো তাঁদের ক্ষমতার ভিত্তি। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে নতুন সংবিধান প্রণীত হয়েছে। তার আওতায় প্রথম নির্বাচনে পিপিপি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিশ্চিত করতে নির্বাচনে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে বলে বিরোধীরা অভিযোগ তোলে। সংসদের ৭৭ দশমিক ৫ শতাংশ আসন লাভের ফলাফল বিরোধীদের এই অভিযোগকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। ভূট্টো সরকার এই অভিযোগের জবাবে বিরোধীদের কঠোর হাতে দমণের নীতি গ্রহণ করে, অন্যদিকে বিরোধীরা রাজপথের আন্দোলন গড়ে তোলে। এই পটভূমিকায়, জনসাধারণের ক্ষোভকে পুঁজি করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। জেনারল জিয়াউল হকের সেনাশাসন চলে ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্টে এক রহস্যময় বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু পর্যন্ত। পাকিস্তানের রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে জিয়াউল হকের শান্নের ভূমিকা অতীতের যে কোন শাসকের যেয়ে বেশি। সম্ভবত আর কোনো শাসকই পাকিস্তানের রাজনীতি, সমাজ ও আইনী ব্যবস্থাকে বদলে দিতে সক্ষম হয়নি।
১৯৯৭ সালের নির্বাচনে মিয়া নাওয়াজ শরীফের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান মুসলিম লীগ দুই তৃতীয়াংশ আসনের চেয়ে একটি কম আসন পেয়ে বিজয়ী হলেও একজন সংসদ সদস্যের সমর্থন সংগ্রহ করতে দলকে বেগ পেতে হয়নি। এই আমলেই সংবিধানের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ সংশোধনী পাশ হয় যা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে করে তোলে নিরঙ্কুশ। ত্রয়োদশ সংশোধনীর প্রধান বিষয় ছিলো প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাস। এই সংশোধনীর আওতায় সরকার বরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়। একই সঙ্গে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানদের এবং প্রদেশের গভর্নরদের নিয়োগে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রধানমন্ত্রীর ‘পরামর্শ’-নির্ভর করা হয়। এই সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেনা শাসনামলে প্রেসিডেন্টকে দেয়া ক্ষমতা হ্রাসের বিধানকে অনেকেই ইতিবাচক বলে মনে করেন। কিন্ত চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে যখন সংসদের সদস্যদের দলবদল বন্ধের নামে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল তখন বোঝা গেলো যে প্রধানমন্ত্রী এখন সর্বম্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েছেন এবং তাকে নিয়ন্ত্রনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। এই সব ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী দেশের বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে ইচ্ছে করেই বিরোধে জড়িয়ে পড়েন যখন তিনি সুপ্রিম কোর্টে পাঁচ জন বিচারক নিয়োগের চেষ্টা চালান। এক পর্যায়ে নাওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে এম মামলার শুনানির সময়ে ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে সরকার সমর্থকরা সুপ্রিম কোর্ট ভবনে মিছিল করে চড়াও হয়। ঐ বছরের শেষ নাগাদ প্রধান বিচারপতির বরখাস্ত এবং প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের পেছনে প্রধানমন্ত্রী শরিফের হাত ছিলো বলেই বোঝা যায়। সব মিলে বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে দন্দ্বের বিষয়টি শাসনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের বাধা তৈরি করে। ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী সেনাপ্রধানকে অপসারনের চেষ্টা করলে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সেনা অভ্যুথান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।
শ্রীলংকায় ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ; তার মধ্যে অন্যতম হল যে এই নির্বাচনে জে আর জয়বর্ধনে’র নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউএনপি) সংসদে ৮৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ আসন লাভ করে। প্রধান বিরোধী দল এবং সাবেক ক্ষমতাসীন শ্রীলংকা ফ্রিডম পার্টি (এসএলএফপি)’র পাওয়া আসন ছিলো মাত্র ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ। সংসদ ১৯৭৭ সালে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধানে বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটায় যার মধ্য দিয়ে তৈরি করা হয় নির্বাহী প্রেসিডেন্টের পদ। অর্থাৎ কার্যত ওয়েস্টমিনিস্টার ধরণের সংসদীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসনের ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৭৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে গিয়ে জয়বর্ধনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন। তারপরে নতুন সংবিধান তৈরি প্রণয়ন করা হয় যাতে ‘ফার্স্ট পাস্ট দি পোস্ট’ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সেখানে চালু করা হয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা। এরপরে আরেক সংশোধনীর মাধ্যমে (১৯৮২ সালের চতুর্থ সংশোধনী) সংসদ তার মেয়াদ ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে নেয়। উপুর্যপুরি সংশোধনের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে দুর্বল করে ফেলা হয় এবং প্রেসিডেন্টের রেহাই বা ইম্যুনিটির পরিধি বাড়ানো হয় ১৯৮৮ সালে চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে। সব মিলে ১৯৭৭ সালের নির্বাচিত সংসদ দেশের রাজনীতি এবং শাসন ব্যবস্থার এতটাই পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় যে একথা বলা মোটেই অতিরঞ্জন হবে না যে ১৯৯৭-পূর্ববর্তী শ্রীলংকার সঙ্গে ১৯৭৮-পরবর্তী শ্রীলংকার ব্যবধান কেবল এক বছরের নয়।
চার দেশের চার দশকের ইতিহাস থেকে আমরা বলতে পারি যে সুপার মেজরিটির সংসদগুলো সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন করেছে এবং প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীলংকার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের) নির্বাহী ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়ে পড়েছে নিয়ন্ত্রনহীন।
কিন্ত অনেকেই বলতে পারেন যে এই সংসদগুলো নির্বাচিত হয়েছে জনসাধারনের ভোটে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে। ফলে এগুলো জনসাধারণের মতামতেরই প্রকাশ। আসলেই কী তাই?
জনগণের ইচ্ছায়ই সুপারমেজরিটি?
সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার নির্বাচনে কোন দল বা জোটের দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভের ঘটনার পর সেই সব দেশের রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে গত চার দশকে দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশেই। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার ৩৫টি নির্বাচনের ভেতরে যে এগারোটিতে বিজয়ী দল বা জোট দুই-তৃতীয়াংশ বা তার বেশ আসন পেয়েছে সেখানে নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে এবং তাঁদের আচরণে অগণতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতে ১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধীর শাসনামলে; শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বাড়িয়ে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সেই পদে আসীন হয়েছেন। কিন্ত এই নির্বাচনগুলোর ফলাফল যেহেতু জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন সেহেতু সুপার-মেজরিটিও জনগণের রায় – এই দাবি কেউ কেউ করতে পারেন।
কিন্ত এই নির্বাচনগুলোর ফলাফল খতিয়ে দেখলে যে ছবি উঠে আসে তা এই যুক্তির বিরুদ্ধেই বরঞ্চ প্রমাণ তৈরি করে দেয়। দক্ষিণ এশিয়ায় দেশগুলোতে গত চার দশকে কোনো সুষ্ঠু, অবাধ ও প্রতিদ্বন্ধিতামূলক নির্বাচনে কোন দল ভোটারদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট পায়নি। আমরা অবশ্যই এই বিবেচনা থেকে বাংলাদেশের ১৯৮৮ সালের এবং ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে বাদ রেখেছি। কেননা এই দুই ক্ষেত্রেই ভোটারদের সামনে কার্যকর কোনো বিকল্প ছিলনা, ফলে এই সময়ে সংশ্লিষ্ট বিজয়ী দল যে ৬৬ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে তাতে নির্বাচনে অসৎ উপায় ব্যবহারের প্রমাণ মেলে, তাঁদের প্রতি ভোটারদের সমর্থন নয়। বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। তবে ঐ নির্বাচনেও ভোট জালিয়াতি এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রভাবিত করার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে। তবু তাকেই আমরা ব্যতিক্রম বলতে পারি যেখানে ক্ষমতাসীনরা ১৯৭৩ সালে ৭৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, আসনের দিক থেকে ৯৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ২০০১ সালে বিএনপি’র নেতৃত্বাধীন জোট পেয়েছিল ৪৬ দশমিক ৬২ শতাংশ (আসনের ৭০ দশমিক ৬৭ শতাংশ); ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের পাওয়া ভোট ৫৭ শতাংশ।
ভারতে ১৯৭১ সালে কংগ্রেস পায় ৪৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ ভোট (আসনের ৬৭ দশমিক ৯৫); ১৯৮৪ সালে কংগ্রেসের বাক্সে পরে পঞ্চাশ শতাংশের কম ভোট – ৪৯ দশমিক ০১ শতাংশ; পায় আসনের ৭৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। পাকিস্তান পিপলস পার্টি ১৯৭৭ সালে পেয়েছিলো ৬০ দশমিক ১ শতাংশ ভোট – কিন্ত আসন পেয়েছিল ৭৭ দশমিক ৫ শতাংশ। পাকিস্তান মুসলিম লীগ যখন দুই-তৃতীইয়াংশের জোরে দেশ শাসন করেছে সেই ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে তার পাওয়া ভোটের হার ছিল ৪৫ দশমিক ৯ শতাংশ। শ্রীলংকায় ইউএনপি মাত্র ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ ভোটের জোরে ৮৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ আসনের অধিকারী হয়েছিল ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে।
এসব তথ্য নিসন্দেহে ‘ফার্স্ট পাস্ট দি পোস্ট’ ব্যবস্থার ভেতরে লুকানো একটা গভীর দুর্বলতার দিকে সবার মনোযোগ আকর্ষন করে। এই ব্যবস্থায় একটি দল সুপার মেজরিটির দাবি করতে পারে এবং সেই ভাবে দেশ শাসন করতে পারে যখন দেশের ভোটাররা তাঁদেরকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এমন কোনো ম্যন্ডেট দেয়নি। কিন্ত শুধু তাই নয়, এই সব উদাহরণ থেকে আমরা আরো একটি উপসংহারে পৌছুতে পারি। ক্রিস এ্যাডক গুয়েতেমালা, কলোম্বিয়া এবং আলজেরিয়া বিষয়ক আলোচনায় যে কথাগুলো বলেছেন তা এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে, ‘কার্যকর নির্বাচনী ব্যবস্থা থাকার অর্থ এই নয় যে তা নিজে নিজেই প্রকৃত গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা দেয় বা কর্তৃত্ববাদী (বা অথরিটারিয়ান) আচরণ বা কাঠামোর সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়’।
গত চার দশকের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এই তথ্যও জানাচ্ছে যে চারটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশিবার দুই-তৃতীয়াংশের শাসনের ঘটনা ঘটেছে; সেটা যেমন সেনাশাসকদের বৈধতা প্রদানের জন্যে, তাঁদের হাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রভাবিত হবার ঘটনা ঘটেছে তেমনি তা ঘটেছে বেসামরিক শাসকদের হাতেও। আর কোনো দেশেই এত ঘন ঘন এই ধরণের অবস্থার উদ্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, সংসদে এই ধরণের উপর্যুপুরি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই ধরণের ক্ষমতার প্রয়োগ দেশে সেনা শাসনের পথ সুগম করেছে, যার পরিণতি দেশটির জন্যে ভালো হয়নি। ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কলঙ্ক হলো ১৯ মাসের জরুরি অবস্থা এবং তার আওতায় যে সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
বাংলাদেশে আসন্ন দশম সংসদ নির্বাচনে যখন একদলের এবং তার শরিকদের সব আসনে বিজয়ী হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং ‘নির্বাচনী’ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তা হতে চলেছে তখন দক্ষিণ এশিয়ার গত চার দশকের ইতিহাস স্মরণ করা জরুরি। বাংলাদেশে গত দুই সংসদে ক্ষমতাসীনরা সুপার-মেজরিটির কারণে যে অবস্থার তৈরি হয়েছে তার পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে দেশের মানুষকে, এখনও তাঁরা তার পরিণাম ভোগ করছেন। দুর্নীতি, অস্থিতিশীল রাজনীতি, আইনের শাসনের অভাব এবং ক্ষমতাসীনদের আচরণ দেশের ভবিষ্যতকে বিভিন্নভাবে বিপন্ন করেছে। অন্যান্য দেশে যেমন এই ধরণের শাসনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাদি পরবর্তী সময়ে মোকাবেলা করা গেছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার সুযোগ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি।
সেই কারণেই এই আলোচনা যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ দেশের ভবিষ্যৎ পথরেখা বিবেচনার ক্ষেত্রে। একে এড়ানোর কোন উপায় নেই।
(প্রথম আলো’তে প্রকাশিত, ১৯, ২০ এবং ২১ ডিসেম্বর ২০১৩)
This post has already been read 16 times!