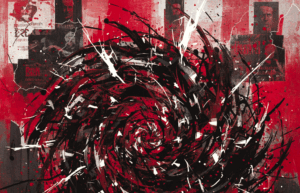This post has already been read 28 times!
বাংলাদেশের সংবিধানের বর্তমান ভাষ্য অনুযায়ী আগামী ৩৬৫ দিনের মধ্যে দেশে একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন দলের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেছেন। যদিও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী নির্বাচন কীভাবে হবে, তা নিয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই; তথাপি গণমাধ্যমের আলাপ-আলোচনা এবং সাধারণের কথাবার্তায় নির্বাচনের সময়কার সরকারের রূপ বিষয়ে অস্পষ্টতা ছিল। ১২ জানুয়ারি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ‘সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের আগে নির্বাচনকালীন সরকার গঠিত হবে’। এই বিষয়ে সংসদে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন: নির্বাচনকালীন সরকার আকারে ছোট হবে, রুটিনকাজের দায়িত্বে থাকবে এবং কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবে না। সংবিধানে যেহেতু ‘নির্বাচনকালীন সরকারের’ আলাদা কোনো ধারণাই উল্লেখিত নেই, সেহেতু যে ধরনের সরকার ক্ষমতাসীন দল এবং প্রধানমন্ত্রী তৈরি করবেন, তাকেই ‘নির্বাচনকালীন সরকার’ বলে বিবেচনা করতে হবে।
প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি থেকে সরে এসেছে অনেক দিন আগেই, কিন্তু দলের বক্তব্য হচ্ছে তারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন কোনো সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না। বিএনপি নেতাদের প্রতিশ্রুত ‘নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের’ এখনো কোনো ইঙ্গিত মেলেনি। দলের প্রধান খালেদা জিয়া এবং তাঁর দলের অন্যরা তাঁদের বিরুদ্ধে রুজু করা অসংখ্য মামলা মোকাবিলায় এমন ব্যস্ত যে তাঁদের পক্ষে এই দিকে নজর দেওয়া সম্ভব কি না, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। তদুপরি, ক্ষমতাসীন দলের বক্তব্য অনুযায়ী এই রূপরেখা দেওয়া না দেওয়ায় কার্যত কিছু আসে যায় না; শুধু বিএনপি দাবি করতে পারবে যে তারা একটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিল, যা ক্ষমতাসীন দল মানেনি। প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন বিষয়ে কোনো রকম আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। ফলে সংবিধান সংশোধিত না হলে বা প্রধানমন্ত্রী কোনো কারণে আগ্রহী না হলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারকে ক্ষমতায় রেখেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
বিএনপি নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই ধরনের নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে না। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়া দোষী সাব্যস্ত হওয়ার প্রশ্ন। ৮ ফেব্রুয়ারি (বা পরে) দেওয়া রায়ে তিনি যদি দণ্ডিত হন, তবে তাঁর পক্ষে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া সম্ভব হবে না। সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) (ঘ) অনুযায়ী, দুই বছর বা তার বেশি দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। বিএনপির বক্তব্য হচ্ছে খালেদা জিয়াকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে তারা নির্বাচনে যাবে না। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতা মহীউদ্দীন খান আলমগীরের অংশগ্রহণ এবং তাঁর সদস্য থাকা বিষয়ে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট; প্রথমত দণ্ড বাতিল না হলে সংসদ সদস্যের অযোগ্যতা বিষয়ে ৬৬ অনুচ্ছেদই চূড়ান্ত কথা-দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংসদ সদস্য থাকতে পারবেন না; দ্বিতীয়ত এর অর্থ এই নয় যে নির্বাচনে খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র দাখিলের সব পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
সাবেক আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ সম্প্রতি বলেছেন, ‘দণ্ডিত যদি উচ্চ আদালতে আবেদন করে এবং আবেদনের যুক্তি দেখে আদালত সন্তুষ্টি সাপেক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের অনুমতি দেন, সে ক্ষেত্রে [দণ্ডিত] নির্বাচনে অংশ নিতে পারে’ (আমাদের সময়, ২৮ জানুয়ারি ২০১৮)। খালেদা জিয়া দণ্ডিত হলে তাঁর আইনজীবীরা যে সেই পথেই অগ্রসর হবেন অনুমান করতে পারি; কিন্তু তাঁদের আবেদনের ‘যুক্তি’ আদালতের ‘সন্তুষ্টি’ অর্জন করবে বলে ভরসা করার বাস্তবসম্মত কোনো কারণ নেই। ফলে সম্ভবত আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে খালেদা জিয়ার অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই মামলার রায় যা-ই হোক, শিগগিরই জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলারও রায় হতে পারে। তাতে দণ্ডিত হলেও খালেদা জিয়ার জন্য একই ভাগ্য অপেক্ষা করছে; আরও মামলা আছে যা আগামী ৩৬৫ দিনে কী হবে তা আমাদের জানা নেই।
ফলে এই কিছুদিন আগে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপির আগ্রহ যতটা ছিল, এখন ঠিক ততটাই আছে তা মনে করার কারণ নেই। বিএনপি নেতারা এখনই সেটা স্পষ্ট করে বলবেন তা আমি মনে করি না। দলের কর্মীদের এক বড় অংশ বিভিন্ন মামলায় জর্জরিত, এখন দলীয় প্রধানের মাথায় কারাদণ্ড ঝুলিয়ে, তাঁকে আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতায় আবদ্ধ রেখে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হবে বলে আশা করা যায় না। উপরন্তু দলের নেতাদের মনে এই আশঙ্কাই তৈরি হয়েছে যে দলের নেতৃত্ব থেকে খালেদা জিয়াকে অপসারণ করে দলকে বিভক্ত করা হবে, সরকারি দলের নেতা হাছান মাহমুদ যখন বলেন যে বিএনপি কর্মীদের খালেদা এবং দলের মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে (ইত্তেফাক, ২৯ জানুয়ারি ২০১৮), তখন সেই আশঙ্কার উৎস বোঝা যায়। এই আশঙ্কার কারণেই বিএনপির নেতারা তড়িঘড়ি করে দলের গঠনতন্ত্রের ৭ (ঘ) ধারা বাতিল করে দিয়েছেন। বিএনপির গঠনতন্ত্রের ৭ (ঘ) নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল, ‘সমাজে দুর্নীতিপরায়ণ বা কুখ্যাত বলে পরিচিত কোনো ব্যক্তি দলের যেকোনো পর্যায়ে কমিটির সদস্য বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।’ নৈতিক অবস্থান এবং সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতার বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত বিএনপির জন্য ইতিবাচক নয়।
কিন্তু বিএনপির এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দলকে একত্রে রাখাকে এখন তারা জরুরি মনে করছে। এটা এ-ও ইঙ্গিত দেয় যদি আইনি ব্যবস্থায় খালেদা জিয়া মনোনয়নপত্র দিতে পারেন, তবে যেন দলের কোনো বিধান তাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। ফলে বিএনপির জন্য এখন সম্ভাব্য বিকল্প হচ্ছে দুটি; হয় ২০১৪ সালের মতো নির্বাচন বর্জন করা নতুবা (দণ্ডপ্রাপ্ত হলে) দণ্ডিত খালেদা জিয়াকে সামনে নিয়ে এই কারাদণ্ডকে একটা প্রতীকী বিষয়ে পরিণত করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা।
অনেকেই বলবেন যে বিএনপির ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না, এখনো ঠিক হবে না। গত চার বছরে ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতার বল্গাহীন ব্যবহার, শাসনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো সংকোচনের কারণ হিসেবে অনেকে বিএনপির নির্বাচন বর্জন এবং ২০১৫ সালের সহিংস আন্দোলনকে দায়ী করেন। কিন্তু প্রথমত বিএনপি বা কোনো দল নির্বাচন বর্জন করলেই ক্ষমতাসীন দলের অগণতান্ত্রিক আচরণের বা বলপ্রয়োগের বৈধতা তৈরি হয় না।
দ্বিতীয়ত ২০১৪ সালের নির্বাচন বিএনপি একা বর্জন করেনি। ফলে বিরাজমান অবস্থার দায় যদি বিএনপির হয়, তবে তার অংশভাগ বর্জনকারী অন্যান্য দলের ওপরেও বর্তায়। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর যাঁরা বলেছেন, বিএনপি আওয়ামী লীগের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিল, ২০১৮ সালের অবস্থাকে তাঁরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
বিএনপিকে তাঁরা কোন বিকল্প বেছে নিতে পরামর্শ দেবেন? ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জনকারী অন্য দলগুলোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম এই কারণে যে, যে যুক্তিতে তাঁরা সেই সময় নির্বাচন বর্জন করেছিলেন সেই অবস্থার বদল হয়নি; তাঁরা তাঁদের অবস্থান বদল করেছেন কি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপরে নির্ভর করছে আগামী দিনগুলোর রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ।
প্রথম আলো, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
This post has already been read 28 times!