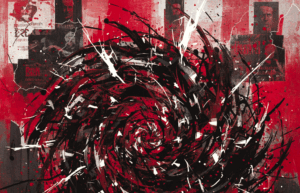This post has already been read 66 times!
মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিয়ানমার সরকারের সামরিক অভিযান, নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও পোড়ামাটি নীতির মতো করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার কারণে লাখ লাখ মানুষ এখন বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। জীবনরক্ষার তাগিদে পালিয়ে আসা এসব মানুষের নিরাপত্তা, খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রশ্নটিই এখন আশু বিবেচনার বিষয়। আশ্রয়শিবিরে খাদ্যাভাবের আশঙ্কা এবং শরণার্থীদের যথাযথভাবে তালিকাভুক্তির অনুপস্থিতি একাদিক্রমে আশু ও দীর্ঘমেয়াদি সংকটের ইঙ্গিত বহন করে। শুরুতে আন্তর্জাতিক সমাজের ক্ষমাহীন নীরবতা এবং দ্বিধান্বিত বাংলাদেশ সরকারের অপরিকল্পিত পদক্ষেপ শরণার্থী পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর ভার প্রায় এককভাবেই এসে পড়েছে বাংলাদেশের ওপর।
বিশ্বের অনেক দেশে এই সামরিক অভিযানকে ‘গণহত্যা’ বলে চিহ্নিত করে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। কিন্তু মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও সরকারের অবস্থানে সামান্য পরিবর্তন ঘটেনি; উপরন্তু অং সান সু চি দাবি করেছেন, তাঁর সরকার সবাইকে ‘নিরাপত্তা’ দিচ্ছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। সব স্বাভাবিক থাকলে যে মানুষ ‘শরণার্থী’ জীবন বেছে নেয় না, এটা বোঝার জন্য কাণ্ডজ্ঞানই যথেষ্ট। তদুপরি মিয়ানমার সরকারের আমন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের যেসব সাংবাদিক রাখাইন সফরের সুযোগ পেয়েছেন, মিয়ানমার থেকে তাঁদের পাঠানো প্রতিবেদনেই দেখা যাচ্ছে যে পুলিশের উপস্থিতিতেই বেসামরিক ব্যক্তিরা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে (জোনাথন হেডের প্রতিবেদন, ‘বিবিসি রিপোর্টার ইন মিয়ানমার—আ মুসলিম ভিলেজ ইন ওয়াজ বার্নিং,’ বিবিসি, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭)। মিয়ানমার সরকার এসব ধ্বংসযজ্ঞের দায় তাদের ভাষায় ‘জঙ্গি’দের ওপরই কেবল চাপাচ্ছে না তা নয়, একই সঙ্গে শরণার্থীদের ভবিষ্যতে দেশে ফেরার ওপর কিছু শর্ত আরোপ করতেও শুরু করেছে।
এসব ঘটনা বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়—রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে মিয়ানমার সরকারের পরিকল্পনা কী? সাম্প্রতিক এই সেনা অভিযান ‘জাতিগত নিধনের’ কোন ধরনের পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়? মিয়ানমার কি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল অনুসরণ করছে? এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের কেবল পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করবে তা নয়, শরণার্থী পরিস্থিতি মোকাবিলার কৌশল এবং পরিস্থিতির দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোন কোন বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে, তা নির্ধারণেও সাহায্য করবে।
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষয়ে আমাদের অনেকের কমবেশি ধারণা রয়েছে। ভূরাজনৈতিক স্বার্থ, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিবেচনা, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ক্ষমতা বিস্তারের কূটকৌশলের হিসাব-নিকাশ থেকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিগুলো তাদের নিজ নিজ অবস্থান সুস্পষ্ট করেছে। চীন, রাশিয়া, ভারতের অবস্থান তাদের ‘বন্ধু’ মিয়ানমার সরকারের পক্ষে এবং বর্তমান মানবিক সংকটের জন্য তারা ২৫ আগস্টের ‘চরমপন্থী সহিংসতাকেই’ দায়ী করেছে। তাদের বক্তব্য এই ধারণাই দেয় যে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সবকিছু ২৪ আগস্ট কিংবা গত বছরের ৯ অক্টোবরের আগে ছিল শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক। তাদের এই অবস্থান অবশ্যই নতুন নয়; কেননা, চীন ও রাশিয়া বরাবরই মিয়ানমার সরকারের এ ধরনের নীতি ও আচরণের পক্ষে সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে। চীন হচ্ছে মিয়ানমারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাদের ঘনিষ্ঠতার ইতিহাসও অর্ধশতাব্দীর বেশি সময়ের। ভারতের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্কের উষ্ণতা সাম্প্রতিক এবং তার কারণ বোধগম্য, গ্রহণযোগ্য না হলেও। চীনের প্রভাববলয়কে সংকুচিত করা, সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, যার দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ হচ্ছে এ বছরই মিয়ানমারের কাছে ৩৮ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের বিদ্রোহীদের দমনে মিয়ানমারের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা—এর সব কারণ না হলেও কিছু কারণ।
এর বিপরীতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর অবস্থান, তারা আগাগোড়াই জাতিগতভাবে রোহিঙ্গাদের অধিকারের কথা বলে এসেছে। এখন তীব্রভাবে মিয়ানমারের সমালোচনা করছে; যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আপাতদৃষ্টিতে কঠোর বলে মনে হলেও তার কার্যকারিতা ও আন্তরিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ এ কারণে যে ট্রাম্প প্রশাসন উত্তর কোরিয়া প্রশ্নে এতটাই ব্যস্ত যে তার পক্ষে এই অঞ্চলে নতুন কোনো সংকটে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা সীমিত। উত্তর কোরিয়া প্রশ্নে মার্কিনদের দরকার চীনের অকুণ্ঠ সমর্থন, সেখানে মিয়ানমার বিষয়ে চীনের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র খুব কঠোর অবস্থান নেবে বলে মনে হয় না। আসিয়ানের সদস্যরা অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ‘হস্তক্ষেপ’ না করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তা সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য মিয়ানমারের ওপর চাপ দিতে এগিয়ে এসেছে। ২০০৯ সাল থেকে আসিয়ানের বিভিন্ন ফোরামে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং ২০১৪ সালে আসিয়ান ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে চালানো সহিংসতার নিন্দা করেছে।
ওআইসির প্রধান হিসেবে তুরস্ক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, যদিও মানবাধিকার প্রশ্নে তুরস্কের ভূমিকা কোনো অবস্থাতেই অনুসরণীয় নয়, তবু তুরস্কের সক্রিয়তা আন্তর্জাতিক সমাজের ওপর যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, সেটা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ যে খুব কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে, এমন আশা করার কারণ নেই। অতীতে চীন ও রাশিয়া একত্রেই মিয়ানমারের পক্ষে তাদের ভেটো প্রয়োগ করেছে। পারস্য উপসাগরের দেশগুলো বা সৌদি আরবের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কূটনৈতিক উদ্যোগ আশা করার কারণ নেই, যদিও রোহিঙ্গাদের মুসলিম পরিচিতির কারণে অনেকেই এগিয়ে আসার দাবি করছে।
বৈশ্বিক রাজনীতির এই চিত্র মিয়ানমার সরকারের অনুকূলে; আর তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নের সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে তুলেছে। ফলে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও সরকারের যে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও কৌশল আছে, তা বাস্তবায়নে তারা ক্রমাগতভাবে আরও বেশি কঠোর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হচ্ছে। সেই পরিকল্পনা কী, সেটা বোঝার জন্য ২০১২ সালের জুলাই মাসে মিয়ানমারের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট থেইন সেনের বক্তব্য আমাদের স্মরণ করা দরকার। তিনি বলেছিলেন, রাখাইনের বিরাজমান সমস্যার ‘একমাত্র সমাধান’ হচ্ছে রোহিঙ্গাদের তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো অথবা দেশের ভেতরে জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক কমিশন ইউএনএইচসিআরের পরিচালিত শিবিরে ‘নিয়ন্ত্রণ’ (তাঁর ভাষায় কন্টেইন) করে রাখা (মিয়ানমার টাইমস, ১৬ জুলাই ২০১২, https://www. mmtimes. com/national-news/yangon/ 395-unhcr-seeks-true-community-reconciliation-in-rakhine-state. html)। এ কথা ২০১২ সালে বলা হলেও একার্থে এ ধরনের নীতি ১৯৭৪ সাল থেকেই সেনাবাহিনী অনুসরণ করে এসেছে। সেই সময়ে জরুরি অভিবাসন আইনের আওতায় রোহিঙ্গাদের জাতীয় রেজিস্ট্রেশন কার্ডের বদলে বিদেশি রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদান তার প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইনে তাদের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়া এবং ২০১৪ সালে আদমশুমারি থেকে রোহিঙ্গাদের বাদ দেওয়া এসব পদক্ষেপেরই অংশ।
তবে গত কয়েক দশকে বারবার বিভিন্ন ধরনের সামরিক অভিযান এবং মিয়ানমারের উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সেনাবাহিনী ও রাজনীতিবিদদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনের কারণে সৃষ্ট সংঘাতের পরিণতিতে রাখাইন প্রদেশ থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ১০ শতাংশের বেশি দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে—তারা এখন ‘তৃতীয় দেশে’ অবস্থান করছে। (এই নিবন্ধের সঙ্গে যুক্ত ছবি দেখুন, বর্তমান পরিস্থিতির আগে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গার সংখ্যা ৫ লাখ হিসাবে বিবেচনা করা হতো, এখন ঢুকে পড়েছে প্রায় ৩ লাখ। সেই হিসাবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ৮ লাখ ধরে নেওয়া যায়)। ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টারের হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালের মার্চ পর্যন্ত কমপক্ষে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৫০০ রোহিঙ্গা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যাদের একটা বড় অংশ বিভিন্ন শিবিরে জীবন যাপন করছে।
এই চিত্র আমাদের দেখিয়ে দেয় যে সাম্প্রতিক এই যে পরিস্থিতি, তার আশু কারণ যা-ই হোক, গত কয়েক দশকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ও সরকারের পরিকল্পনাই কার্যত বাস্তবায়িত হচ্ছে।
সেই পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়নের বিবেচনায় ইতিমধ্যে মিয়ানমার সরকার আরেকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। যেহেতু তারা বুঝতে পারছে যে লাখ লাখ মানুষ সীমান্ত পার হওয়ার পর এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব হবে যে এর কেউই মিয়ানমার থেকে যায়নি এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তাদের কিছু শরণার্থীকে গ্রহণ করতেই হবে, সেহেতু সরকারের নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা উ থুং তুন গত বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যে সেই সব শরণার্থীকে বাংলাদেশ থেকে ফেরত নেবেন, যাদের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র আছে (ফ্রন্টিয়ার মিয়ানমার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭)। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রথমত অসহায় পলায়নপর মানুষ তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নিয়ে দেশত্যাগ করেছে এমন মনে করা অবাস্তব; দ্বিতীয়ত, রোহিঙ্গাদের অনেকেই এমন অবস্থার মধ্যে ছিল, যাদের নাগরিকত্বের আবেদন বিবেচনাধীন ছিল; তৃতীয়ত, আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের নাগরিক বলেই স্বীকার করা হয় না। ফলে এটি হচ্ছে শরণার্থীদের এক বড় অংশকে ফেরত না নেওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি।
রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের প্রশ্ন বাদ দিয়ে এবং বিরাজমান অবস্থার রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্ন বাদ দিয়ে পুনর্বাসনের চেষ্টা সফল হবে না। বাংলাদেশকে গোড়া থেকেই এ বিষয়ে অবস্থান নিতে হবে যে মিয়ানমারকে শর্তহীনভাবে শরণার্থীদের গ্রহণ করতে হবে। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে সেই সময়ে বাংলাদেশে যেসব রোহিঙ্গা শরণার্থী ছিল, তাদের প্রত্যেককেই মিয়ানমারের আইনানুগ নাগরিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। যদিও চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে তাদের ‘নাগরিকত্বের রেজিস্ট্রেশন কার্ড’ দেখানোর কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু ২ লাখ শরণার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৭০ হাজার শরণার্থীর প্রত্যাবাসন প্রমাণ করে যে এই শর্ত যাতে অধিকাংশকে বঞ্চিত না করে, তা বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘ নিশ্চিত করেছিল।শুধু তা-ই নয়, মিয়ানমার সরকার প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়ার ১৯৭৪ সালের সংস্করণে রোহিঙ্গাদের একটি জাতিগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মিয়ানমারের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন মুসলিম ও রোহিঙ্গারা যে অংশগ্রহণ করেছে, তার সপক্ষেও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।
রোহিঙ্গাদের এই মুহূর্তে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া যেমন জরুরি, তেমনি দরকার মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও সরকারের এ ধরনের পরিকল্পনা বিষয়ে সজাগ থাকা।
প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত; সেপ্টেম্বর ১১, ২০১৭
This post has already been read 66 times!