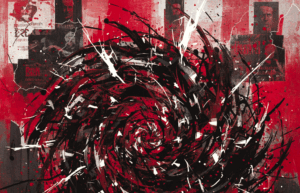This post has already been read 84 times!
Share the post "রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও অর্থনৈতিক ফলাফলঃ প্রতিযোগিতামূলক গোষ্ঠীতান্ত্রিক বিকাশ (১৯৯৫-২০০৫)"
১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে। এ গণজাগরণে মধ্যবর্তী শ্রেণীর সবার অংশগ্রহণের ফলে সম্ভাবনার বীজ রোপিত হয়। ওই অন্তর্ভুক্তিমূলক অভ্যুত্থানটি মধ্যবর্তী শ্রেণীর অংশীজনসমূহ তথা ছাত্র, পেশাজীবী, নারী এবং শ্রমিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়েও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পতনের পর সব দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে লাগসই এ উদ্ভাবনীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় এক অনন্য মাইলফলক। অতীতের যেকোনো নির্বাচনের তুলনায় জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। নির্বাচনটি জনমনে অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর ফলাফল হিসেবে জনমনে এক ধরনের আস্থার জন্ম নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ক্ষমতার অদল-বদল ঘটে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সংসদীয় নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দেয়া হয় এবং রীতি অনুযায়ী ভেঙে দেয়া সংসদের অধীনে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিপরিষদ সদস্য নিয়ে নির্বাচনকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রের রুটিন কাজ করে। যেহেতু তারা আর সংসদ সদস্য নেই, তারাও এক অর্থে অনির্বাচিত। অন্য দেশের থেকে বাংলাদেশের এই লাগসই নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পার্থক্য ছিল যে, তারা ভেঙে দেয়া সংসদের সদস্য নন এবং মূলত অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাময়িকভাবে সরকারের সদস্য। এ ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে ক্ষমতা কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে নিরঙ্কুশ হয়নি। যে দলটি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আছে, সে দলটিরও পরবর্তীতে সরকার গঠনের সম্ভাবনা জায়মান ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশে একটি নতুন ধরনের সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি হয়— প্রধান যেকোনো দলই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে পারবে।
এ নতুন ধরনের সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অর্থনৈতিক প্রতিফলনও দৃশ্যমান। এ সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিমাণগত প্রগতি লক্ষণীয়। প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রেই চলতি বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে অগ্রগতি সাধিত হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। এ রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ধারাবাহিকতা জন্ম দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রগতিকে টেকসই রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার পথে ছিল। পরিমাণগত প্রগতি শুরু হলেও গুণগত অগ্রগতির যাত্রা কণ্টকপূর্ণ ছিল। গুণগত প্রগতির জন্য দরকারি শর্ত তথা প্রতিষ্ঠানগুলো আগের মতোই রয়ে যাচ্ছিল; আমূল সংস্কারের লক্ষণের অনুপস্থিতি ছিল। তবে রাষ্ট্রের কলেবর বাড়ছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানহীনতার অভাবে রাষ্ট্রগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল ও রাষ্ট্রের সহিংসতা বিদ্যমান ছিল। ফলে জনগণের কাছে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা তৈরি হচ্ছিল না। নাগরিক রাষ্ট্র হওয়ার জন্য রাষ্ট্র নাগরিকের সঙ্গে চুক্তিতে জড়াতে আগ্রহী ছিল না। গোষ্ঠীগুলোর কাছে কুক্ষিগত হচ্ছিল, গোষ্ঠীভুক্তরা রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে সম্পদের পুঞ্জীভবন ঘটিয়ে চলছিল। নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থায় দেশোপযোগী লাগসই ব্যবস্থা উদ্ভাবন হলেও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ ঢেলে সাজানোর অনুপস্থিতিতে শাসনতান্ত্রিক সংকট জায়মান থেকেই গেল। আরেকটা সুযোগ হাতছাড়া হলো!
একই সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নীতিকাঠামোতেও বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তেলের ও তত্পরবর্তী বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন ভারসাম্যের সংকটের পর উন্নয়নশীল দেশগুলোর নীতিকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক ‘কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি’র নামে যে প্যাকেজ চালু করেছিল, তার নির্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হয়নি। বিশেষ করে, আফ্রিকায় আরোগ্য লাভের পরিবর্তে পরিস্থিতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরো খারাপ হয়ে ভয়াবহতার দিকে ধাবিত হলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে ‘কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি’, যা ‘ওয়াশিংটন ঐকমত্য’ নামেও পরিচিত, তার পুনর্বিবেচনা শুরু হয়। ওয়াশিংটন ঐকমত্যের মৌল ভিত্তি ছিল বাজারমুখীন অর্থনীতি চালু হলে গণতন্ত্র নিশ্চিত হবে, একই সঙ্গে উন্নয়ন টেকসই হবে। ধরে নেয়া হয়েছিল, বাজার ও গণতন্ত্র পরস্পর সমার্থক। অর্থাৎ বাজার কাজ করলে গণতন্ত্র ক্রিয়াশীল থাকবে। সে কারণেই তাদের সংস্কার কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দু ছিল ক্রিয়াশীল বাজারের মাধ্যমে দাম নির্ধারণ নিশ্চিত করা। অর্থাৎ ধারণা করা হয়েছিল, বাজারমুখীন সংস্কার কর্মসূচির প্রধান হাতিয়ারগুলো তথা বাণিজ্য উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিনিয়ন্ত্রণকরণের মাধ্যমে বাজারমুখীন অর্থনীতি চালু হলে গণতন্ত্র সংহত হবে। তবে লক্ষ করা গেল, অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছে না। সংস্কার কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়ছে। এ ব্যর্থতার আলোকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্যাকেজ ঢেলে সাজাল এবং বাজার অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে তারা এর সঙ্গে ‘সুশাসন’ যোগ করল। বাজার ব্যবস্থা সংহত করতে সুশাসন দরকার বলে বিশ্বব্যাংক ছয়টি উপাদানকে সুশাসন হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে। সূচকগুলো হলো— ভয়েস বা কণ্ঠ এবং জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি, সরকারের কার্যকারিতা, নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা, আইনের শাসন এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ। সুশাসনযুক্ত এ প্যাকেজ ‘উত্তর ওয়াশিংটন ঐকমত্য’ নামেও অভিহিত।
এদিকে ১৯৯১ সালের পর থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে ধরনের পরিমাণগত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল, তার আলোকে বাংলাদেশ নিয়ে নতুন একটি ন্যারেটিভ বা বয়ান বিভিন্ন নামে চালু হয়। এগুলো ‘বাংলাদেশ ধাঁধা’, ‘বাংলাদেশ বিস্ময়’ ইত্যাদি নামে প্রচলিত। তারা বলছেন, সুশাসনের ঘাটতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের উন্নয়ন একটি ধাঁধা বা বিস্ময়। এ বিষয়টি কতখানি যৌক্তিক, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হওয়া জরুরি। তবে মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হলে এ পার্শ্ববিষয়টিও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে মূলত তিনটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি। এক. কী কারণে সে সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকগুলোর অপেক্ষাকৃত পরিমাণগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল? দুই. কেন শাসনতান্ত্রিক ঘাটতি রয়ে গেল? এবং তিন. কেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক টেকসই অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে না, কেনইবা বারবার হোঁচট খাচ্ছে?
দুই.
এই দেড় দশকে গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন সাধিত হয়। যদিও মোট দেশজ উৎপাদন তথা পুঁজি গঠনের ক্ষেত্রে কৃষির অংশগ্রহণ ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে গ্রাম থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের নগরমুখী প্রবণতার পাশাপাশি বিদেশমুখী হওয়ার ফলে তাদের প্রেরিত অভিবাসী আয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজির ব্যাপক সরবরাহ ঘটে। সেই পুঁজি সাধারণত ব্যবহূত হয়েছে ভোগ ব্যয়ে। যার মাধ্যমে ওই মানুষের মৌলিক চাহিদা ভোগের মানের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। তবে জারি রয়েছে আপেক্ষিক দারিদ্র্য বা সম্পদ আয় ও বণ্টনের মধ্যকার বৈষম্য। তবে এভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজির সরবরাহের ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদনের বড় রকমের উল্লম্ফন পরিলক্ষিত হয়। অভিবাসী আয় গ্রামে আসায় মানুষের ভোগ চাহিদা বেড়েছে। এ ভোগ চাহিদা সরবরাহের জন্য উৎপাদনও বেড়েছে।
এর সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনৈতিতে ক্ষুদ্রঋণ বড় ব্যপ্তি লাভ করে। এর ব্যাপকতা যেমন বেড়েছে, একইভাবে অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সারা বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ছেয়ে গেছে। অনেক ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনের পটভূমি আছে। প্রসঙ্গত, গ্রামীণ অর্থনীতিতে মোটা দাগে প্রচলিত ছিল মহাজনি ঋণ ব্যবস্থা। যদিও কৃষি ব্যাংকের মতো বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ ব্যবস্থা চালু ছিল, কিন্তু তাদের জনগণের চাহিদা মেটানোর অদক্ষতা ও নিষ্পেষণ ব্যবস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রচলনের এক ধরনের নতুন সুযোগ করে দিতে সাহায্য করেছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এ সময়ে ব্যাপক পরিসরে এনজিও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি ঘটে। এগুলোও ক্ষুদ্রঋণ দিতে শুরু করে। এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ক্ষুদ্রঋণের উল্লম্ফনের ফলে গ্রামীণ জনগণ নতুনভাবে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। এনজিওগুলো একদিকে গ্রামের সাধারণ মানুষকে ঋণ দেয়, পাশাপাশি কঠোর নিয়মনীতির মাধ্যমে তারা সে ঋণ আদায় করে। কৃষি ব্যাংকের মতো বিশেষায়িত সংস্থার ঋণ আদায়ের হারও কম ছিল। যদিও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা মানুষের কতটুকু মৌলিক পরিবর্তন সাধনে ভূমিকা রেখেছে, তা এখনো প্রশ্নবিদ্ধই হয়ে আছে। কারণ ক্ষুদ্রঋণের সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে ক্ষুদ্রঋণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন কোনো গবেষণা বা জরিপ নেই, যার আলোকে এর সত্যিকারের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। তবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী এনজিওগুলো ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পেরেছে। অর্জিত উদ্বৃত্ত থেকে নতুন পুঁজি সরবরাহের সাংগঠনিক ক্ষমতা অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্বৃত্ত তৈরির সক্ষমতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়ে তহবিল গঠন করে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে উদ্বৃত্ত তৈরি করে চলছে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন এক ধরনের পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে অর্জিত পুঁজির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী অনেক এনজিও তাদের সাধারণ প্রথাগত কর্মক্ষেত্রের বাইরে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত করছে। এসব ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শহর-গ্রামে যেমন বিস্তৃত, তেমনই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সব খাত তথা কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতগুলোয় ব্যাপৃত।
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে তহবিল জোগানের নিশ্চয়তা, বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রণোদনা, নীতি সহায়তা তথা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তির কারণে এ সময়ে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের বড় ধরনের বিকাশ সাধিত হয়। এভাবে বাংলাদেশের রফতানি কাঠামোয় পোশাক শিল্পের সংযোজনের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা শ্রেণীর তৈরির পথ সুগম হয়। এর পাশাপাশি পোশাক শিল্পের আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি-সংক্রান্ত খাতেও অন্যান্য নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পোশাক শিল্পের বদৌলতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের প্রসার ঘটে। এভাবেই পুঁজির প্রসারের সূত্রপাত হতে থাকে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের শিল্প ব্যবস্থা এককেন্দ্রিকতার দিকেও ধাবিত হতে শুরু করে। অর্থাৎ গোটা শিল্প খাতে পোশাকশিল্প তার আধিপত্য নিশ্চিতের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রভাব বিস্তার শুরু করতে থাকে।
গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন, মধ্যবর্তী শ্রেণীর মধ্য থেকে নতুন উদ্যোক্তা শ্রেণী তৈরির মাধ্যমে পুঁজি সঞ্চয়ন ও বিকাশের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পুঁজিরও বড় রকমের বিকাশ ঘটে। এ সময় মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। ফলে জাতীয় কর কাঠামোয় বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। মূল্য সংযোজন করের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্প সময়ে এ কর জাতীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় এক নম্বর আয়ের উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ একটি পরোক্ষ করকে ডিঙ্গিয়ে আরেকটি পরোক্ষ করের শীর্ষ আরোহণ। কর কাঠামোর ব্যবস্থাগত ত্রুটি রয়েই গেল। বরং একদিক দিয়ে খারাপ হলো। বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আমদানির ওপর ধার্যকৃত আমদানি শুল্ক, যেটি একটি পরোক্ষ কর, এতদিন কর কাঠামোয় উপরে ছিল। মূল্য সংযোজন করও একটি পরোক্ষ কর। আয় নিরপেক্ষ ভোগের ওপর কর হওয়ায় ধনী-গরিব সবাইকে একই হারে কর দিতে হয়। অতএব এটি একটি প্রতিক্রিয়াশীল কর। প্রত্যক্ষ কর বাংলাদেশে সবসময়ই কম রয়ে গেছে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ও হারে ধনিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে, এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে করদাতার সংখ্যা বাড়েনি। এটি বাংলাদেশের এলিট শ্রেণী গঠনের কাঠামোগত দুর্বলতা ও তাদের গোষ্ঠীতান্ত্রিক চরিত্রকেই নির্দেশ করে।
গোষ্ঠীগত প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন প্রণোদনা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা নিতে তারা যতটা সচেষ্ট, জাতি ও দেশ গঠনে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির দায়িত্ব না নিয়ে কর ফাঁকি ও জালিয়াতিতে ততটাই পারঙ্গম। অন্যদিকে দেশে ও বিদেশে গ্রামীণ উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ফলে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষ কর বেড়ে যায়। মূল্য সংযোজন কর মূলত ভোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই এ কর কাঠামো ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের পুঁজি সরবরাহের বৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পুঁজির এ ব্যপ্তি সাধারণ জনগণের অর্থেই ঘটল। মূল্য সংযোজন কর সাধারণ জনগণই বেশি দিয়ে থাকে। এ সাধারণ জনগণই রাষ্ট্রকে নির্ভরতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে এসে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আরেকটি পথ সৃষ্টি করে দিল। নব্বই সালে যে রাষ্ট্রটি তার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল, সাধারণ মানুষের প্রদত্ত করের মাধ্যমে ওই নির্ভরতা থেকে বাংলাদেশ খানিকটা বেরিয়ে আসতে থাকে। এর মাধ্যমে ক্রমেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটা অংশের খরচ দেশের নিজস্ব সম্পদ থেকে মেটানো সম্ভব হয়। ফলে অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। রাষ্ট্রও বড় হতে শুরু করে। রাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যয়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলে।
অন্যদিকে এ মধ্যবর্তী শ্রেণী পুঁজি সংগ্রহ ও সম্পদশালী হওয়ার তাড়নায় এতটাই মরিয়া যে, তারা একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার করে জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পুঁজির ভাগ নিতে চেষ্টা করছে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন বন, জলাভূমি ইত্যাদির পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, যেমন— রেলের সম্পত্তি ইত্যাদি লোপাটের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করতে শশব্যস্ত।
তিন
ভবিষ্যত্মুখীন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা দরকার কী কারণে এ সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিমাণগত অগ্রগতি সাধিত হলো। অর্থাৎ এ সময়ে কী ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক খাতে প্রগতির সূত্রপাত হয়? বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সবচেয়ে শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে এ দেশের মানুষের সৃজনশীলতা ও অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকা। বাংলাদেশের যতগুলো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো অথবা জনগণের সৃজনশীলতা ব্যবহারের মাধ্যমে দেশোপযোগী প্রক্রিয়ায় তা সম্পন্ন হয়েছে। পোশাক শিল্পে সৃজনশীলতার মাধ্যমে তহবিল সংগঠন, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, প্রণোদনা এবং নীতির মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন লক্ষণীয়। একইভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক বন্দোবস্তে নব্বইয়ের দশকে যে মধ্যবর্তী শ্রেণী একত্র হয়েছিল, তারা সৃজনশীল কায়দার নতুনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিল। সাধারণ মানুষের প্রদত্ত করের মাধ্যমেই বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা থেকে বাংলাদেশ খানিকটা বেরিয়ে আসতে থাকে।
অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা দেখেছিল যে পুঁজিপতির কাছে অর্থ গেলে, তা খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে, তেমনি একজনের কাছে ক্ষমতা গেলে তা ক্রমেই স্বৈরতান্ত্রিকতার দিকে ধাবিত হয়। বিষয়টি অনুধাবনের ফলে মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলো নতুন ব্যবস্থা তৈরি করল। এছাড়া অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা অবগত ছিল যে, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্র সবসময়ই এককেন্দ্রিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এ প্রথা ভাঙতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করা হলো। ক্ষমতার পালাবদল ঘটানোর ক্ষেত্রে অদল-বদল সংস্কৃতি চালু হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আস্থাহীনতার বদলে স্থিতিশীলতার বীজ রোপিত হলো। সংশয় না থাকলে, নীতি কাঠামোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে, উদ্যোক্তা শ্রেণীর পক্ষে শ্রমশক্তির বিকাশের মাধ্যমে পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়া চালু রাখা সম্ভব। এখানে যে বিষয়টি প্রয়োজনীয়, তা হচ্ছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর এক ধরনের আস্থা থাকতে হবে। আস্থা থাকলে শ্রম ব্যবস্থার সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত অর্জন করা ও পুঁজি পাচার প্রতিরোধ করা যায়।
রাষ্ট্রীয় পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আমলাতন্ত্রের পরিবৃদ্ধি ঘটল, তেমনি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার পরিমাণও বেড়ে গেল। ব্যক্তি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করল। রাজনৈতিক নেতারা তাদের কর্তৃত্ব বজায় এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা স্কিম তথা মান্থলি পে অর্ডার (এমপিও)ভুক্ত করতে শুরু করে দিল। একই সঙ্গে রাষ্ট্র বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা ও নারীদের জন্য উপবৃত্তি চালু করল। বেসরকারি খাতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, স্কুল ইত্যাদি দেদার চালু হতে থাকল। এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগত বৃদ্ধির ফলে সামাজিক খাতের পরিমাণগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব রাখল। কিন্তু তেমন গুণগত প্রবৃদ্ধি ঘটল না। এবং যার পরবর্তী ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখছে সক্ষম হচ্ছে না। একদিকে শিক্ষিত বেকার বাড়ছে, অন্যদিকে উদ্যোক্তারা দক্ষ শ্রমশক্তি পাচ্ছেন না। বিদেশীরা ওই পদগুলোয় কাজ করে প্রচুর পরিমাণে রেমিট্যান্স নিয়ে যাচ্ছেন।
বর্ধিষ্ণু মধ্যবর্তী শ্রেণীর কাছে অর্থের সমাগম ঘটাতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা বিদেশমুখীন হয়ে উঠল। মধ্যবর্তী শ্রেণী থেকে উদ্ভূত এ এলিট দেশমুখীন না হওয়ার কারণে পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত আর টেকসই ব্যবস্থার দিকে যেতে পারল না। অর্থাৎ এ তথাকথিত এলিট শ্রেণী নিজস্ব আত্মতৃপ্তির জন্য জাতীয় উন্নয়নে মনোযোগ নিবেশ করল না। এদের পরবর্তী প্রজন্ম দেশের বাইরের যেকোনো ধরন ও মানের প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা ঘটল। এবং তারা দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানের গুণগত পরিবর্তনে সচেষ্ট হলো না। একই বাস্তবতা স্বাস্থ্য খাতেও। কারণ এ শ্রেণী চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রেও বেশির ভাগ সময়ই বিদেশের ওপর নির্ভর করে। এলিট শ্রেণীর এ উদাসীনতার কারণে জাতীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানোপযোগী হিসেবে গড়ে উঠছে না। গর্ব করার মতো আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানগুলোর নিম্নগামিতা লক্ষণীয়। নতুন নতুন ‘শ্রেষ্ঠত্ব কেন্দ্র’ বা সেন্টার অব এক্সিলেন্স গড়ে উঠছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা সক্ষমতা নেই বললেই চলে। ফলে র্যাংকিংয়ে তাদের অবস্থান নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিকাশ না হলে উন্নয়নের পরবর্তী স্তরে যাওয়া সম্ভব হবে না।
বাংলাদেশের মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করল, একদিকে তার অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনীয় শর্ত যেমন— পুঁজি, শ্রমশক্তি, প্রযুক্তির সঙ্গে প্রয়োজন দরকারি শর্ত- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। একের উপস্থিতিতে ও অন্যের অনুপস্থিতিতে অগ্রগতি সম্ভব নয়। অর্থাৎ এমন একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত জারি থাকা জরুরি, যার মাধ্যমে উদ্যোক্তা শ্রেণী পুঁজি ব্যবহারে নিয়োজিত থাকবে। সামাজিক খাতেও বিকাশ সাধিত হবে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, এমনটা করার জন্য যে ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রয়োজন, তত্কালীন সময়ে সে ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু এ রাজনৈতিক বন্দোবস্তের এক ধরনের গোষ্ঠীতান্ত্রিক চরিত্র বিদ্যমান থাকায় ‘উইনারস টেক অল’ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। রাজনৈতিক ও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যিনি জয়ী হবেন, তিনি সবকিছুর মালিকানা নেবেন এবং সর্বক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবেন, এ প্রবণতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল। অন্যদিকে গোষ্ঠীতন্ত্র পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণের মাধ্যম শিকড় কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত এক মহীরুহতে পরিণত হলো। মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলোর দ্রুত সম্পদ হাতড়ে নেয়ার ইঁদুর দৌড় গোষ্ঠীতান্ত্রিক বিকাশকে অতি দ্রুততার সঙ্গে ধেয়ে ধেয়ে প্রোথিত করল। ‘বিকৃত প্রণোদনা’ভিত্তিক তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও প্রাকৃতিক সম্পদ লোপাটের মাধ্যমে গোষ্ঠীতান্ত্রিক বিকাশ মধ্যবর্তী শ্রেণীর মধ্য থেকে এক পর্যুদস্ত এলিট তৈরি করল। তার দোআঁশলা শঙ্কর শরীর মুত্সুদ্দি চরিত্রের, তার কাছে টাকাই মানদণ্ড— টাকা দিয়ে সব কেনা যায় এবং দেশ ও জাতি গঠনও সম্পদ তৈরির উসিলা মাত্র। এক ধরনের বিচ্ছিন্ন মানসিকতার গোষ্ঠীতান্ত্রিকতার কারণে বড় ধরনের ঘাটতি থেকে গেল। দিন দিন যে দেশ ও জাতি গঠনের ঘাটতি প্রকটতর হচ্ছে।
চার
বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ঘাটতির চরিত্র বুঝতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের চরিত্র নিরূপণ প্রয়োজন। সুশাসনের তথাকথিত উপাদানের মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব নিহিত নেই। বাংলাদেশ ধাঁধা, বাংলাদেশ বিস্ময় ইত্যাদি কথামালার মধ্যে আশ্রয় খুঁজে সাময়িক লুকানো যেতে পারে। রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বিকৃত অধ্যয়নেও এর উত্তর পাওয়া যাবে না। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত মানে এলিটদের মধ্যকার চুক্তি নয়। রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে বহুত্ববাদী, গণতান্ত্রিক সরকারে পরিবর্তিত হওয়ার পদ্ধতিকেও বোঝায় না। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত কোনো নীতিনির্ধারণী চলক বা সূচক নয়। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বৈশ্লেষিক পদ্ধতি। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ক্ষমতার বণ্টনকে বিশ্লেষণ করতে এখানে ব্যবহূত হচ্ছে।
১৯৯০ সাল পরবর্তী রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও শাসনতান্ত্রিক ঘাটতির প্রকৃতি অনুসন্ধান শুরু হতে হবে ওই সময়ের মধ্যবর্তী শ্রেণীর চরিত্র অনুধাবনের মাধ্যমে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নব্বইয়ের আন্দোলন যেমন রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল, তেমনি পরবর্তীতে বড় ধরনের বিভক্তির মাধ্যমে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। মধ্যবর্তী শ্রেণী মোটা দাগে দুই রাজনৈতিক দলের অনুসারী হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষতের কোনো উপশম তথা কোনো দ্বিদলীয় ঐকমত্য লক্ষ করা যায়নি। বিভাজন বেড়েছে; প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে সংঘাতময় সহিংস প্রতিপক্ষে পর্যবসিত হয়েছে। অন্যের ওপর নিষ্পেষণ, নির্যাতন, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও জিঘাংসা নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মাত্রা ও ঘনত্ব দিন দিন বেড়েই চলছে।
১৯৯০ সাল-পরবর্তী এক ধরনের ‘ক্লায়েন্টেলিসটিক’ নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। এটা উলম্ব আকারে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। আনুভূমিকভাবে ক্ষমতাকাঠামোর ওই পর্যায়ের সবাই তথা রাজনীতিবিদ, আমলা, পুলিশ ইত্যাদি নেটওয়ার্কের সদস্য। এই উলম্ব ও আনুভূমিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টিত হয়। এর মানে যারা উলম্বভাবে এ নেটওয়ার্কে জড়িত, তারা তখনই আনুগত্য স্বীকার করছে, যখন সে উপরের ব্যক্তির কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হচ্ছে। এ নেটওয়ার্ক চালু থাকে ‘বিকৃত’ প্রণোদনা বা পারভাসিভ ইনসেনটিভের মাধ্যমে। ক্লায়েন্টেলিসটিক বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক নেটওয়ার্ক গড়েই উঠেছে অবৈধ পন্থায় পুঁজি সঞ্চয়ন এবং সম্পদ বৃদ্ধির জন্য। অর্থাৎ রাজনীতিকে ব্যবসায় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা যায়, পুঁজির সঞ্চয়ন ঘটানো যায়— এ উপলব্ধি থেকেই এ নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি। কখন, কে, কী অবস্থানে আছে, তা বোঝা যাবে না। একদা আমলা ছিলেন এখন তিনি রাজনীতিবিদ বনে গেছেন কিংবা ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি রাজনীতি করছেন। কেউবা উভয়ই। তবে এটা বলা যাবে, রাজনীতিতে ব্যবসায়ী ও আমলার সংখ্যা বেড়েছে। রাজনীতি করতে হলে প্রচুর অর্থের দরকার। রাজনীতিকে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন হিসেবে দেখা হচ্ছে। সে কারণে পরবর্তীতে সংসদ থেকে শুরু করে সব জায়গায় দেখা গেল, কে ব্যবসায়ী বা কে রাজনীতিবিদ, তার পার্থক্য করা যাচ্ছে না। কারণ প্রত্যেকেই যেহেতু বুঝে গেছে, রাজনীতি একটি বিনিয়োগযোগ্য পণ্য। তাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকল রাজনীতি। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে রাজনীতি করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা যার কাছে নেই, সে রাজনীতিতে অংশ নিতে অনুপযুক্ত হওয়ার পথে।
রাজনীতিকে বিনিয়োগযোগ্য পণ্যে পরিণত করা হলো বলে জনপ্রতিনিধিত্বশীলতার সঙ্গে জনগণের বড় ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হতে শুরু করল। জনপ্রতিনিধিত্বশীলতার পূর্বশর্ত হিসেবে আবির্ভূত হলো— ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ করার সক্ষমতা। পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণের পাশাপাশি ব্যক্তির হাতে যদি পর্যাপ্ত অর্থ থাকে, তাহলেই সে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। নব্বই সালে মধ্যবর্তী শ্রেণীর মধ্যে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা আবার হারিয়ে গেল এবং রাজনীতি টিকে থাকল অর্থ বা সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে। এভাবে অনেকগুলো ভাঙন ঘটল মধ্যবর্তী শ্রেণীর মধ্যে। মধ্যবর্তী শ্রেণী সবসময় রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে। সংগ্রামে শামিল হয়েছে। এভাবে ক্রমেই তাদের ভূমিকা নিঃশেষ হতে শুরু করল।
বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বা রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অথবা নতুন ধরনের সমঝোতা তৈরির জন্য ছাত্রসমাজ সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখত। ছাত্রসমাজ থেকেই রাজনৈতিক নেতা তৈরি হতো। অতীতে রাজনীতিতে যারা নেতা হয়ে এসেছেন, তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্দিষ্ট বিরতির মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সংসদ নির্বাচন চলছিল। কিন্তু নব্বই সালের পরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ হয়ে গেল। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্ব তৈরির যে সুযোগ ছিল, তা তিরোহিত করা হলো। রাষ্ট্রের ক্লায়েন্টেলিসটিক নেটওয়ার্ককে চ্যালেঞ্জ করার মতো নতুন নেতৃত্ব তৈরি করার আর সুযোগ থাকল না। সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন জাতি গঠনে খুবই প্রয়োজনীয়। ছাত্র সংসদগুলো শুধু ছাত্রদের নেতৃত্বই প্রদান করত না, নানা রকম সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার কর্মসূচি হাতে নিত। ছাত্র সংসদের মাধ্যমে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, হল, জেলা বা বিভাগ পর্যায়ে যে প্রতিযোগিতাগুলো অনুষ্ঠিত হতো, তার মাধ্যমে যে মানবিক বিকাশ ঘটত, সে বিকাশের পথও রুদ্ধ করে দেয়া হলো। ফলে একদিকে নতুন নেতৃত্ব তৈরির রাস্তা ও অন্যদিকে জাতি গঠনের যে সামাজিক মন ও মনুষ্যত্ব তৈরির প্রক্রিয়া জারি ছিল, তা থেমে গেল। এভাবে আরো একটি বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হলো।
বাংলাদেশের সব আন্দোলন ও নব্বইয়ের অভ্যুত্থানে শ্রমিক সমাজের অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল। নব্বইয়ে ছাত্রদের ক্ষেত্রে যেমন ‘সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য’ ছিল তেমনি শ্রমিকদেরও ‘শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ’ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ছাত্র রাজনীতির মতো শ্রম আন্দোলনও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির কাছে বিকিয়ে গেল। শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহক সংগঠন হিসেবে লেজুড়বৃত্তি করতে থাকল। শ্রমিক সংগঠনগুলোর সবচেয়ে বড় অংশ ওই দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হলো। রাজনৈতিক দলের শ্রমিকবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়ার ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলোও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলতে থাকল। একই সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার ফলে শ্রমিক রাজনীতি শ্রমিকের অধিকার আদায়ের অন্দোলনের চেয়ে পেশিশক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করল। ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ক্লায়েন্টেলিসটিক নেটওয়ার্কের একটি অংশ হিসেবে আবির্ভূত হলো।
পরবর্তীতে শ্রমিক আন্দোলন কখনই চাঙ্গা হতে পারল না। কারণ শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির মধ্যে হারিয়ে গেছে। পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিক অধিকারবঞ্চিত। যে মানুষগুলো অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত, কর্মক্ষেত্রে তাদের কোনো ধরনের অধিকার নেই। আবার আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও অধিকারহীনতা বিদ্যমান। এবং তাদেরকে তখনই অল্প-বিস্তর অধিকার প্রদান করা হয়, যখন বিদেশী কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা এক ধরনের বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। শ্রমিকদের অধিকার থেকে যেমন বঞ্চিত করা হলো, তেমনি উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের প্রাপ্য অংশটুকুও ক্রমেই হ্রাস পেতে শুরু করল। কারণ কার্যকর ট্রেড ইউনিয়নের অভাবে শ্রমিকের দর কষাকষির ক্ষমতা বা অধিকার আদায়ের সক্ষমতা হ্রাস পেল। অর্থাৎ শ্রমিকরা দুইভাবে অধিকার বঞ্চিত হলো। রাষ্ট্রযন্ত্রকে সর্বদা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তাদের আন্দোলন করার ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকল। এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের সক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান হলো।
নারী সংগঠনগুলো বাংলাদেশের আন্দোলন ও সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। সংগঠনগুলো স্বেচ্ছাব্রতের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নারী সংগঠনগুলোর ক্রমেই নির্ভরতা তৈরি হতে থাকল এবং অনেক নারী সংগঠনই এনজিওতে পরিণত হতে শুরু করল। নিজেদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্যে যথা একদিকে পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে অন্যদিকে পুঁজিতান্ত্রিকতা থেকে নারীদের মুক্তির সংগ্রামে নারী সংগঠনগুলো যে ধরনের ভূমিকা রাখত, তারও পরিবর্তন ঘটল। যেহেতু এনজিওগুলো রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনের মধ্যে চালিত প্রতিষ্ঠান, তাই নারী সংগঠনগুলোর স্বেচ্ছাসেবী ভূমিকা এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে নারীর নাগরিক অধিকার আদায় করার কার্যকারিতা প্রশমিত হলো। নারী সংগঠনগুলো আন্দোলন, সংগ্রাম ও প্রতিরোধ থেকে গুটিয়ে ক্রমাগত প্রচার অভিযান বা নীতি সংস্কারের অ্যাডভোকেসিতে নিয়োজিত করল। যদিও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, কিন্তু নারী শ্রম অধিকারবঞ্চিত হয়েছে। নারীর ওপর সহিংসতা যেমন দিন দিন বেড়ে গেছে, তেমনি নারী সংগঠনগুলো তাদের স্বেচ্ছাসেবী শ্রমের মাধ্যমে যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করত, তার পরিবর্তে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর সংগঠন হয়ে যাওয়ার আন্দোলন ও সংগ্রামে আর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে না।
সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজের ধারণা, এ সময়ে নতুন একটি প্রপঞ্চ, যা অতীতেও আলোচিত ছিল, তা বড় আকারে প্রকাশিত হলো। ধরে নেয়া হলো, সুশীল সমাজ যার ভয়েজ নেই, তার পক্ষে কথা বলবে, রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে পরখ করবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। কিন্তু এখানে দুটি বিষয় লক্ষ করা গেল। এক. সুশীল সমাজের যারা অংশ হতে পারে, যেমন— ছাত্র, শিক্ষক, নারী কিংবা শ্রমিক, তারা প্রধান প্রধান দলগুলোয় ভাগ হয়ে গেছে। সমাজের বিবেক হিসেবে রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে যেভাবে ভূমিকা রাখা দরকার, তার পরিবর্তে নিজেদেরকে তারা রাজনৈতিক আনুগত্যেই বেশি মাত্রায় নিয়োজিত রাখছে। যেহেতু ভয়ঙ্কর সহিংসতা তৈরির ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে, তারা ক্রমেই রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের অংশ হয়ে ক্রমেই নখদন্তহীন কাগুজে বাঘে পরিণত হলো। একই সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে এবং এনজিওদের মাধ্যম এক ধরনের সিভিল সোসাইটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হলো। যেহেতু এটা স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে গঠিত হলো না, অর্থাৎ বৈদেশিক আর্থিক সহায়তার নির্ভরশীলতা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনের মধ্যে বাঁধা থাকার কারণে তারা রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করতে সমর্থ নয়। জনগণের সঙ্গেও তাদের এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা আছে। দলের সদস্যতে পরিণত হওয়া ও বৈদেশিক অর্থ দিয়ে পরিচালিত হওয়ার কারণে তাদের নিজস্বতা এবং নৈতিক ক্ষমতা ক্রমেই নিঃশেষিত। ক্লায়েন্টেলিসটিক নেটওয়ার্কের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার বিপরীতে তারা পাল্টাপাল্টি কোনো ব্যবস্থা করতে পারল না বলেই সুশীল সমাজ ক্রমেই কো-অপ্টেড হচ্ছে। সবাই ক্রমাগত ক্লায়েন্টেলিসটিক নেটওয়ার্কের সদস্যে পরিণত হচ্ছে।
বাংলাদেশকে একটি নাগরিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য নব্বইয়ের দশকে মধ্যবর্তী শ্রেণীর অংশগুলো একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়। এর মাধ্যমে দেশোপযোগী একটি ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল। এতে এক ধরনের আস্থার জায়গা সৃষ্টি হয়। একটি নতুন রাষ্ট্রের পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, তাতে ফের ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং ২০০৬ সালে সে ধরনের অস্থিরতা আবার দেখা দিল।
বণিক বার্তা; বিশেষ সংখ্যা/উন্নয়ন অমনিবাস ৩;২১:৪৩:০০ মিনিট, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৮
Share the post "রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও অর্থনৈতিক ফলাফলঃ প্রতিযোগিতামূলক গোষ্ঠীতান্ত্রিক বিকাশ (১৯৯৫-২০০৫)"
This post has already been read 84 times!