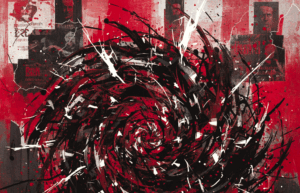This post has already been read 88 times!
যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিস শহরে পুলিশের নিপীড়নে জর্জ ফ্লয়েডের নিহত হওয়ার পরে এক সপ্তাহ ধরে সারা দেশে যে বিক্ষোভ চলছে, তার কারণ বোঝা দুরূহ নয়। কিন্তু গত কয়েক দিনের ঘটনা থেকে যে প্রশ্নগুলো ওঠে, তা হচ্ছে কী কারণে এই বিক্ষোভ জাতীয় রূপ নিয়েছে? গত কয়েক দিনে কেন সংঘাতময় অবস্থার সূচনা হয়েছে?
এই প্রতিবাদের আশু কারণ হচ্ছে জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু। কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েড মারা গেছেন পুলিশের নির্যাতনে ২৫ মে, সোমবার। তাঁকে আটক করে হাতকড়া পরানোর পরে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার ডেরেক শভিন প্রকাশ্যে সবার সামনে তাঁর ঘাড় এমনভাবে হাঁটু দিয়ে রাস্তায় চেপে ধরেন যে ফ্লয়েড ৮ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড শ্বাস নিতে পারেননি। আরও তিনজন পুলিশ শভিনকে সাহায্য করেন। ফ্লয়েড বারবার বলেছিলেন, ‘আমি শ্বাস নিতে পারছি না’।
এই মৃত্যুর ঘটনার পরে মিনিয়াপোলিসে যে প্রতিবাদের সূচনা, তা গত এক সপ্তাহে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে তা নয়, দেশের বাইরেও প্রতিবাদ হচ্ছে। প্রতিবাদ গত কয়েক দিনে বিস্তার লাভ করেছে, সংঘাতময় হয়ে উঠেছে, প্রতিবাদ মিছিলগুলো ক্রমেই আক্রমণাত্মক হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদকারীদের ওপরে পুলিশ চড়াও হয়েছে, মিনেপোলিসে পুলিশ ফাঁড়িতে অগ্নিসংযোগ হয়েছে, অনেক শহরে দোকানপাট লুট হয়েছে।
ফ্লয়েডের হত্যার এই দৃশ্যের ভিডিও মনে করিয়ে দিয়েছে ২০১৪ সালের ১৭ জুলাইয়ের নিউইয়র্ক শহরে একইভাবে পুলিশ কর্তৃক শ্বাসরোধ করে এরিক গার্নারের মৃত্যুর ঘটনা। পুলিশের ফ্লয়েডের মর্মান্তিক মৃত্যু, যাকে হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই বলার উপায় নেই, সারা দেশে হাজার হাজার মানুষকে পথে নামিয়েছে। এটি আশু কারণ, কিন্তু তার পটভূমি আছে।
চলমান বিক্ষোভের পেছনে পটভূমি হচ্ছে তিনটি—প্রথমত পুলিশি নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড, বিশেষত পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গদের নিহত হওয়ার ঘটনা। ২০১৯ সালে রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক এডওয়ার্ডস গবেষণা করে দেখিয়েছিলেন যে পুলিশের মুখোমুখি হলে একজন শ্বেতাঙ্গের চেয়ে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মারা যাওয়ার আশঙ্কা প্রায় আড়াই গুণ বেশি। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কেবল যে কৃষ্ণাঙ্গদেরই ক্ষোভ আছে তা নয়। সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যেই এই নিয়ে ক্ষোভ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়েছে; কেননা এখন এগুলোর ব্যাপারে পুলিশের ভাষ্যের পাশাপাশি ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে, যাতে দেখা যায় যে পুলিশের ভাষ্যের সঙ্গে তা অসংগতিপূর্ণ। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছেন অন্যরাও।
দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিচারব্যবস্থা। গোটা বিচারব্যবস্থা এবং আইনি বিধিবিধানগুলো সংখ্যালঘু, দরিদ্র এবং বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না। কারাগারে আটক ব্যক্তিদের এক বড় অংশই হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ। ২০০৬ সালের পর থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের হার কমেছে। কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে তা এখনো বিরাট, পার্থক্যও বড়। তদুপরি বিচারিক প্রক্রিয়া এবং আইনগুলো এমনভাবে তৈরি যে অভিযুক্ত হলে রায় পুলিশের পক্ষে যায় এবং এমনকি প্রকাশ্যে সংঘটিত ঘটনার পরেও পুলিশের সদস্যরা কোনো রকম শাস্তি ভোগ করেন না।
তৃতীয় হচ্ছে সমাজে বিরাজমান বৈষম্য, যার প্রধান শিকার কৃষ্ণাঙ্গরা। সমাজের এই বৈষম্য এক দিনে তৈরি হয়নি, আরও সঠিকভাবে বললে গত আড়াই শ বছরের ইতিহাস তা–ই। কিন্তু গত কয়েক দশকে তার আরও অবনতি হয়েছে, এই নিয়ে যত কথা হয়েছে, তার সামান্যই বাস্তবে বদল হয়েছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের এবং মৃত্যুবরণকারীদের হার সেটা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তদুপরি করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনীতিতে যে বড় ধরনের সংকটের সূচনা হয়েছে, তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গরাই।
এর পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গ এবং প্রগতিশীল মানুষদের জন্য যা সবচেয়ে বেশি পীড়াদায়ক এবং মার্কিন সমাজের এক গভীর ক্ষতের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে বর্ণবাদ বিষয়ে সমাজে এবং রাজনীতিতে একধরনের অস্বীকৃতির প্রবণতা। মার্কিন রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সমাজের এক বড় অংশের মধ্যেই সমাজে এবং কাঠামোগতভাবে আইন ও শাসনব্যবস্থায় উপস্থিত বর্ণবাদ নিয়ে আলোচনায় অনাগ্রহ রয়েছে। তাঁদের মনোভঙ্গি হচ্ছে এই নিয়ে কথা না বললেই যেন বর্ণবাদ অপসৃত হয়ে যাবে। সমাজের শ্বেতাঙ্গরা—ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়—শ্বেতাঙ্গ হওয়ার সুবিধা ভোগ করে থাকেন, যাকে বলা হয় হোয়াইট প্রিভিলেজ। কিন্তু অধিকাংশের মধ্যেই ধারণা যে এটি তাঁদের প্রাপ্য। এই অস্বীকৃতির কারণেই সমাজে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী চিন্তা টিকে থাকতে পেরেছে এবং এখন ভয়াবহ ও উগ্রভাবে তার উত্থান হয়েছে। এটি সমাজের সবার জন্যই এক বড় ধরনের বিপদ তৈরি করেছে।
বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বা পুলিশি নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন নয়। ২০১৪ সালে মিসৌরির ফার্গুসন শহরে মাইকেল ব্রাউন, নিউইয়র্কে এরিক গার্নার, ২০১৫ বাল্টিমোরে ফ্রেডি গ্রের মৃত্যুর পর একাধিক শহরে বিক্ষোভ এবং সংঘাত হলেও তা জাতীয় রূপ নেয়নি। কিন্তু এবার এক সপ্তাহ ধরে যে ধরনের বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে এবং সংঘাত যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তা ১৯৬০-এর দশকের পর আর দেখা যায়নি।
মিনিয়াপোলিসের ঘটনার জাতীয় রূপ নেওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে, অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্লথতা। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ফ্লয়েডের মৃত্যুর ঘটনার আগে মার্চ মাসে কেনটাকির লুইভিলে শহরে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নার্সকে তাঁর বাড়িতেই পুলিশি রেইডের সময় হত্যা করা হয় এবং সেই বিষয়ে মে মাস পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ পুলিশের ভাষ্যকেই গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ের এসব ঘটনা পুলিশি নির্যাতন এবং সেই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহার বিষয় সামনে নিয়ে আসে। তৃতীয়ত কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর, দেশে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী গোষ্ঠীগুলোর ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। মে মাসের মাঝামাঝি এই ধরনের গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে লকডাউন তুলে নেবার দাবিতে সশস্ত্রভাবেই বিক্ষোভ করে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাদের পক্ষ হয়েই টুইট করে গভর্নরদের ওপরে চাপ প্রয়োগে করেছেন। এগুলো সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিক্ষোভের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।
এসব বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হলেও এখন তা সংঘাতে রূপ নিয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির দায় এককভাবে বিক্ষোভকারীদের নয়। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের মধ্যে সংঘাত তৈরি করার মতো ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী উপস্থিত থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু পুলিশ এবং ন্যাশনাল গার্ডদের ভূমিকা ও তাদের মারমুখী অবস্থান পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়ক হয়নি।
বিভিন্ন জায়গায় এখন এ–ও দেখা যাচ্ছে যে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা বিক্ষোভে অংশ নিয়ে পরিস্থিতি সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন; লুটতরাজে অংশ নিচ্ছেন। তাঁরা চান বিভক্তি ও বিশৃঙ্খলা। পরিস্থিতিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি এমন পরিস্থিতিতে সংযম পালনের আহ্বানের বদলে ১৯৬০-এর দশকের বর্ণবাদী ভাষায় টুইট করে বিক্ষোভকারীদের ‘দুর্বৃত্ত’ বলে বর্ণনা করেছেন। বিভক্তির এই বিষবাষ্প ছড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবেন ভাবছেন। হবেন কি না সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু এখন তার ফল হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে; আক্ষরিক এবং প্রতীকী—দুই অর্থেই।
This post has already been read 88 times!