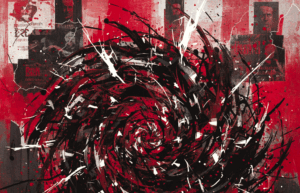This post has already been read 21 times!

বাকস্বাধীনতা মানে যে কোন বাক্যের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র একটি ব্যবস্থাই নেয়া যেতে পারে: আরেকটা বাক্য, লাগলে আরো একশ-হাজার বাক্য। বাকস্বাধীনতা মানে মানুষের লিখিত বা উচ্চারিত কোন বাক্যের বিরুদ্ধেই বাক্য ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। বাক্যের বিরুদ্ধে বাক্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম ফ্যাসিবাদ।
– বখতিয়ার আহমেদ, ফেসবুক, ১৬ জুন ২০২০
বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বাকস্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার বেহাল দশার খবর বহু আগেই দুনিয়াজুড়ে রটে গিয়েছে, করোনাকালে এর এক তীব্র রূপ আমরা প্রত্যক্ষ্য করেছি এবং কার্যত এখনো করছি। তবুও এখানে বাকস্বাধীনতার ফজিলত সম্পর্কে নানাবিধ সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। যেমন, বাক স্বাধীনতা পেলে মানুষ গালাগালি করবে, অশালীন বক্তব্য দিবে। বাকস্বাধীনতা থাকলে ইতিহাস বিকৃতি করবে। ‘অশিক্ষিত’ ও ‘মূর্খ’দের জন্য দরকার ‘সীমিত ও শর্তায়িত’ বাক ও মতের স্বাধীনতা। ফলে অনেকেই ‘শালীন’ ও ‘সংযত’ ভাষা ব্যবহারের নীতিমালাও দেখিয়ে থাকেন। এই প্রবণতা এতই প্রবল যে, রাষ্ট্রের সবচাইতে ‘মুক্ত ও গণতান্ত্রিক’ স্থান হওয়ার কথা যে বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলের তাতেও এর উপস্থিতি দেখা যায়। এই স্বাধীনতাকে খর্ব করার যত আইন করা হয় তার কারণ হিসেবে জনপ্রিয় চালু-মত হচ্ছে, মানুষ মূলত খারাপ, অফুরন্ত স্বাধীনতা পেলে সে যা ইচ্ছা তাই করবে। কিন্তু বাস্তবে ইতিহাস আমাদেরকে দেখায় যে, এমন আইন কেবল তাদের উপর প্রয়োগ করা হয় যারা মূলত বিভিন্নভাবে (লেখা-গান-কবিতা-ছবি-ব্যঙ্গোক্তি-কৌতুক ইত্যাদি) ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন।
এমন পরিস্থিতিতে আলোচ্য প্রবন্ধে বাকস্বাধীনতার দুয়েকটা ফজিলত তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। তবে শুরুতেই বলে নিচ্ছি, আলোচ্য ‘ফজিলত’গুলো মোটেও নতুন কোনো বিষয় নয়, বহুদিন-বহুবছর যাবত চিন্তার বাজারে চালু থাকা মত। সম্ভবত জনপ্রিয়ও বটে। বাংলাদেশের বিদ্যমান নাজুক আবহাওয়াই এমন চালু মতকে হাজির করতে প্রণোদনা দিচ্ছে।
অন লিবার্টি: একটি ধ্রুপদী পাঠ
বাকস্বাধীনতার ফজিলত সম্পর্কিত আলাপে সবচেয়ে ধ্রুপদী রচনা হচ্ছে স্টুয়ার্ট মিলের ‘অন লিবার্টি’।১ কথা বলা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে লিখিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে। ধ্রুপসী পাঠ হিসেবে তা এখনো কেবল স্মরণীয়ই নয়, কার্যত বাকস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতার যে কোনো আলাপে-তর্কে মিলের সেই পাঠ এখনো হাজিরা দেয়। মিল উপযোগবাদী, ফলে তিনি যখন কথা বলার স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেছেন তখনও মূল জিজ্ঞাসা ছিল এর উপযোগিতা কি? কেন কথা বলার বা মত প্রকাশের স্বাধীনতার দরকার? মত প্রকাশে বাধা দিলে, তা রাষ্ট্র কর্তৃক হোক বা সমাজ কর্তৃকই হোক, এতে ক্ষতি কি?
বাকস্বাধীনতা প্রশ্নে মিলের চিন্তার একেবারে দুটো গোড়ার জায়গা আছে। প্রথমত, সত্য জানা লাগবে, এবং দ্বিতীয়ত, সত্য সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত না। শতভাগ অভ্রান্ততা কেউ দিতে পারবেন না, এমনকি যিনি শতভাগ নিশ্চয়তার দাবি করেন তিনি সেটা নাও হতে পারেন। মিল স্থান কালের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বলেন, বিগত কালের অনেক ‘অভ্রান্ত’ সত্য বলে প্রতীয়মান কথা এইকালে এসে স্রেফ উড়ে গিয়েছে। এর ভ্রান্ততা নিয়ে এখন আর কেউ কোনো কথাই বলেন না। স্থানের বেলাতেও একই; কপালের ফেরে আরবদেশে জন্ম নেয়া ব্যক্তি আল্লা নিয়ে যে ‘অভ্রান্ত’ ধারণা, চীন দেশে জন্ম নেয়া কনফুসিয়াসবাদী ব্যক্তির সেটা আলাদা। ফলে, শতভাগ সত্যবচন বলে কিছু নেই, আজ যিনি দাবি করছেন তার বচন অভ্রান্ত, কয়েকযুগ পর সেটা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে পারে। এটাই ইতিহাসপ্রাপ্ত শিক্ষা।
মিলের কাছে ‘সত্য’ জানা জরুরি, এই জরুরতের কারণে তিনি বাকস্বাধীনতার পক্ষে। স্বাধীনতা পেয়ে সত্য-মিথ্যা দুটোই মানুষ বলতে পারে। সত্য বা মিথ্যে দুটো বলার স্বাধীনতা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বাধীনতা যদি না থাকে তাহলে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে। এক, যে আলাপটাকে রুদ্ধ করা হচ্ছে সেই আলাপ যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমরা খোদ সত্য থেকেই বঞ্চিত হবো। দুই, আলাপটা যদি মিথ্যে হয়ে থাকে তাহলে এই মিথ্যের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে সত্যের আরো স্পষ্ট ও নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হবে। ফলে দুটোই মিলের কাছে সমান জরুরি। সত্য হোক মিথ্যে হোক কোনো অবস্থাকেই বাকস্বাধীনতাকে বাধা দেয়া চলবে না। বাধা দিলে দিনশেষে ‘সত্য’প্রাপ্তি থেকেই আমরা বঞ্চিত হবো। ফলে মিল বলেন, যদি একজন ব্যতীত দুনিয়ার সকল মানুষও একটা মতের দিকে যান, তাহলে এই একজনের যেমন অন্যদের মতকে দমন করার এখতিয়ার নেই, তেমনি বাকিসকলের এখতিয়ার নেই সেই একজনের মতকে দমন করার।
মিলের যুক্তি হচ্ছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা চিন্তার আদান-প্রদানের বাজার যদি মুক্ত-স্বাধীন হয়ে থাকে তাহলে এটি যে কোনো বিষয়ে সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ ফল এনে দিতে পারে। ভুল-ত্রুটিকে কমিয়ে ‘সঠিক’ পথ বাতলাতে সাহায্য করবে। এমন জীবন্ত আলাপ-আলোচনার পরিসর বজায় রাখার পক্ষে এবং যে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করার পিছনে মিলের চারটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমত, নিষিদ্ধ মতটি সত্য হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এমনকি যদি সেই মতটি মিথ্যেও হয়ে থাকে, এতে কিছুটা সত্য থাকতেও পারে। তৃতীয়ত, যদি একেবারেই মিথ্যে হয়ে থাকে, তবুও এই নিষিদ্ধ মতটি সত্যকে ‘ডগমা’ হয়ে উঠা থেকে বিরত রাখতে পারবে। এবং চতুর্থত, ডগমা হিসেবে যে কোনো ‘আনচ্যলেঞ্জড’ মত তার অর্থ হারিয়ে ফেলে। মিল বলেন, এমনকি আমি যদি আমার মতের সত্যতা বা সঠিকতা নিয়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসীও থাকি এবং পুরদোমে বিশ্বাস করি যে এটাই ঠিক, তবু এটা স্বাধীনভাবে খোলা ময়দানে আলোচিত না হলে দিনশেষে একটা মৃত মতবাদ বা ডগমাতেই পর্যবসিত হবে। যে কোনো মত যদি নিয়মিত প্রশ্ন ও তর্কের সম্মুখীন না হয় তাহলে মিলের কথা অনুযায়ী সেটা তার অর্থ হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ মতেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারিয়ে যাবে, যা কিনা মানবজাতির জন্যই হুমকিস্বরূপ।
স্টুয়ার্ট মিলের ‘অন লিবার্টি’ গ্রন্থের বহু সমালোচনাও আছে, বর্ণবাদ ও উপনিবেশবাদের সমর্থক হিসেবে। আমরা সেদিকে যাবো না। আমাদের নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনার খাতিরে ‘অন লিবার্টি’ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আলাপেই সীমাবদ্ধ থাকবো। মিলের উপরোক্ত আলোচনা সংক্রান্ত একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ১৯৯৪ সালে হলোকাস্ট গবেষক ও ইতিহাসবিদ দেবোরা লিপস্টাড তাঁর বইতে আরেক ইতিহাসবিদ ডেভিড আরভিংকে ‘হলোকাস্ট অস্বীকারকারী’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আরভিং মানহানির মামলা করলে লিপস্টাডকে প্রমাণ করতে হয় যে তাঁর বক্তব্য সঠিক। মানে, আরভিং হলোকাস্ট অস্বীকার করেছেন। দীর্ঘ গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ের বহু সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দিয়ে লিপস্টাড প্রমাণ করেন যে, আরভিং ইতিহাস বিকৃতি করেছেন। এখানে, আরভিং একাডেমিক পদ্ধতিতে লিপস্টাডের সাথে তর্ক-বিতর্ক না করে সরাসরি আইনের আশ্রয় নেন তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্য। এই মামলার একটা বড় পার্শ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে বলা হয়, হলোকাস্ট গবেষকরা তাদের গবেষণা আরো বিস্তৃত করেছিলেন, যেটা অনেকক্ষেত্রে পূর্বে হয়নি। আবার, উল্টো আরেকটি ঘটনা ঘটে। অস্ট্রিয়াতে হলোকাস্ট ডিনায়েল আইন আছে। ফলে ২০০৬ সালে যখন আরভিং ভিয়েনা যান তখন সেই আইনের অধীনে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় আরভিং নিজেকে একধরনের ‘বাকস্বাধীনতার শহিদ’ হিসেবে হাজির করেন। এই দুটো ঘটনাই মিলের উপরোক্ত যুক্তির একটা বাস্তবতা হাজির করে। আরভিং এর বক্তব্য নির্জলা মিথ্যে হওয়া সত্ত্বেও লন্ডনের খোলামেলা তর্কবিতর্ক ‘সত্য’ উদঘাটন করতে সাহায্য করেছিল, অন্যদিকে অস্ট্রিয়ার আইন তাকে এক ধরনের নায়করূপ দেয়।২
বাকস্বাধীনতা, নাকি রাষ্ট্রের হাতে ‘সত্য-মিথ্যা’ নির্ধারণের ভার
১৯৭৮-১৯৭৯ এর দিকে রবার্ট ফুরিসন নামক এক ফরাসী অধ্যাপক তাঁর লেখায় এবং টিভি সাক্ষাতকারে হলোকাস্ট অস্বীকার করেন, বিশেষ করে নাৎসী বাহিনীর গ্যাস চেম্বারের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। এর ফলে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তিনি কয়েক স্থানে আক্রমণেরও শিকার হোন। তখন নোয়াম চমস্কি সহ প্রায় ৬০০ জন বুদ্ধিজীবী একটি খোলা চিঠিতে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান। তারা ফুরিসনের বাকস্বাধীনতার এবং মত প্রকাশের অধিকার পক্ষে দাড়ান, এবং তাকে নিরব করিয়ে দেয়ার চেষ্টার প্রতিবাদ জানান। এই খোলা চিঠি ফ্রান্সে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করে। তখন অনেকের অনুরোধে চমস্কি আরেকটি নিবন্ধ লিখেন, যেখানে বাকস্বাধীনতা নিয়ে একেবারে ‘এলিমেন্টারি’ কিছু কথাবার্তা বলেন। যে কেউ চাইলে তাঁর এই নিবন্ধ ব্যবহার করতে পারবেন, এই অনুমতি চমস্কি দেন।
১৯৮০ সালের দিকে যখন ফুরিসনের এই সংক্রান্ত বই প্রকাশিত হয় তখন চমস্কি লিখিত এই নিবন্ধ ‘মুখবন্ধ’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়; কিন্তু চমস্কি এটা জানতেন না। পরে জানার পর তিনি এটা সরানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কেননা এতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে যায়, বই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে চমস্কি বলেছিলেন, লেখা সরানোর অনুরোধ করাটা তার ঠিক হয় নি।
এই ঘটনার পর চমস্কিকে ঘিরে আরো বেশি বিতর্কের ঢেউ উঠে। চমস্কির বিভিন্ন সেমিনার-বক্তৃতায় ঘুরেফিরে এই প্রসঙ্গ হাজির হতো, দর্শক-শ্রোতার কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। আগ্রহী পাঠক চমস্কি ও ম্যানুফেকচারিং কনসেন্ট নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারি দেখতে পারেন। চমস্কিও বিভিন্ন সময়ে এই ঘটনা নিয়ে লিখেছেন, মন্তব্য করেছেন।
চমস্কির অবস্থান কি ছিল? চমস্কির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে যে, হলোকাস্ট অস্বীকারকারীকে সমর্থন করার মাধ্যমে তিনিও হলোকাস্ট অস্বীকার করেছেন। চমস্কি তার বিভিন্ন লেখা বা বক্তৃতায় দুটো বিষয় স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন। প্রথমত, কারো বাকস্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো মানে তার মতের পক্ষে দাঁড়ানো না, বা তার মতকে সমর্থন করাও না। আমি কারো মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিলাম, তার মানে এই নয় যে, আমি তার মতকে সমর্থন করি। তার প্রকাশিত মতকে সমর্থন না করেও আমি তার মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ জারি রাখতে পারি। রোজা লুক্সেমবার্গ যেমন করে বলেছিলেন, বাকস্বাধীনতার অর্থই হচ্ছে আসলে ভিন্নমতাবলম্বীর বাকস্বাধীনতা।
চমস্কি যে কেবল এই প্রথম এমন ‘বিতর্কিত’ অবস্থান নিয়েছেন, তা না। তিনি এর পূর্বে বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধীদের একাডেমিক স্বাধীনতা, গবেষণা করার স্বাধীনতা, সেই গবেষনার ফল প্রকাশ করার স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। বাক স্বাধীনতার প্রশ্নে চমস্কির এই অবস্থানকে অনেকেই ‘absolutist’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু, চমস্কি তার এই অবস্থান থেকে কখনোই সরে দাড়ান নি। হাল আমলে ক্যান্সেল কালচার নিয়ে চমস্কির অবস্থানও সমান বিতর্কের মধ্যে পড়ে। ঐতিহাসিকভাবে, বাক স্বাধীনতার প্রশ্নে চমস্কির এই অবস্থান মোটেও নতুন কিছু নয়। চমস্কির বারবার ভলতেয়ারকে উদ্ধৃত করেছেন, আমি তোমার মতের সাথে একমত নাও হতে পারি, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জান দিতে পারি।
দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, চমস্কি ফুরিসনের ঘটনাকে দেখছেন ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়া হিসেবে। তার মতে, বোধহয় এই প্রথম পশ্চিমা কোনো রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে স্ট্যালিনবাদী ও নাৎসীবাদী মতাদর্শ মেনে নিল। অর্থাৎ, রাষ্ট্রই ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করে দিবে এবং এর থেকে বিচ্যুতি ঘটলে শাস্তি দিবে, এই আদর্শ মেনে নিল। তিনি বলেন, হলোকাস্টের শহিদদের আত্মার প্রতি সবচেয়ে বড়ো বেইমানি হচ্ছে এটাই যে, তাদের খুনীদের মতাদর্শকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।৩
উন্নয়নেও বাকস্বাধীনতা
উন্নয়ন প্রশ্নটা আমাদের রাষ্ট্রে খুবই জরুরি ‘প্রসঙ্গ’; এতই জরুরি যে, যে রাষ্ট্র ক্রমাগত গণআন্দোলন ও জনযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে, যে রাষ্ট্রের জন্ম প্রক্রিয়াতে ‘গণতন্ত্র’ সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ও স্পষ্ট ছিল, সেই রাষ্ট্রে হঠাৎ করে খোদ ‘গণতন্ত্র’ই উন্নয়নের জন্য ‘উটকো ঝামেলা’ হিসেবে হাজির হয়েছে। তাই, ‘উন্নয়ন বনাম গণতন্ত্র’ এমন ডিসকোর্স শক্তিশালী হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু, যুক্তির খাতিরে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিলেও এই উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, বাকস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যকীয়; এটা আমার কথা নয়, অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের কথা।৪ উল্লেখ্য, অর্মত্য সেন যে জরুরি কাজটা করেছেন সেটা হচ্ছে, ‘উন্নয়ন’ নামক ধারণার সঙ্গে নীতি/ন্যায়ের একটা সম্পর্ক, তথা উন্নয়ের একটি ‘নৈতিক’ আবেদন তৈরি করেছিলেন।
উনিশ শতকে দুনিয়াজুড়ে খুব স্বাভাবিক বিষয় ছিল কোন কোন দেশ ‘গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত’ আর কোন কোন দেশ অনপযুক্ত তা নিয়ে আলাপ করা। এই বিশ শতকে এসে দেখা গেলো, খোদ এই প্রশ্নটাই সমস্যা-জর্জরিত, এবং ভুল। জনগণ গণতন্ত্রের জন্য ‘ফিট’ কি না এটা কোনো প্রশ্নই হতে পারে না, বরঞ্চ গণতন্ত্রের মাধ্যমেই জনগণকে ‘ফিট’ করে তুলতে হয়। ফলে, অর্মত্য সেনের কাছে বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক বোধের সার্বজনীনতা সাম্প্রতিক প্রপঞ্চ। তার মূল জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই গণতান্ত্রিক এবং বাকস্বাধীনতার বোধ কীভাবে উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে?
২০০১ সালে অর্মত্য সেন এক বক্তৃতায় মিডিয়া কেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সেটা ব্যাখ্যা করেছিলেন। নির্দিষ্টভাবে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করলেও আমরা এটাকে সার্বিকভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে পাঠ করতে পারি।
অর্মত্য সেন শুরুতে বলে নেন যে, বাক-স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে মানব স্বাধীনতারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই যে অপরের সাথে কথা বলতে পারা, অপরের কথা শুনতে পারার সক্ষমতা, এটি হচ্ছে মানুষ হিসেবে আমাদের মূল্যবান হওয়ার কেন্দ্রীয় কারণ। যেমন করে মনিষী এরিস্টটল বলে গিয়েছিলেন, আমরা সামাজিকভাবে পরষ্পরের উপর নির্ভরশীল বা ইন্টারেক্টিভ প্রাণী; জীবনের পূর্ণতার জন্যই ঘর ও বাইরের মানুষদের সাথে পারষ্পরিক সহযোগীতা, আলাপ-আলোচনা, সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সক্ষমতা অর্জন করতে হয়। কথা বলা তাই মানব জীবনেরই একটা অংশ, এবং বাক-স্বাধীনতা তাই মানব স্বাধীনতারই একটি মৌলিক অঙ্গ।
অর্মত্য সেনের মতে, উন্নয়নের জন্য চারটি কারণে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ হচ্ছে কথা বলা এবং যোগাযোগের সহজাত গুণের সাথে এই স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নয়নকে কেবল জিডপি বা জিএনপি ইত্যাদি দিয়ে মাপা যাবে না, বরং দেখতে হবে দায়িত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন সেটা করার স্বাধীনতা তার আছে কি না। উন্নয়ন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটার উপকারিতা নির্ভর করে উন্নয়নের সাথে জড়িত মানুষের জীবন ও স্বাধীনতার হালচালের উপর। তার কাছে স্বাধীনতা উন্নয়নের একেবারে কেন্দ্রীয় বিষয়। ফলে, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার উপর আঘাত বা বাকস্বাধীনতার দমন সরাসরি মানব স্বাধীনতাকেই হ্রাস করে, এবং উন্নয়নকেই দুর্বল করে দেয়।
দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম তথ্যের যোগান দেয়, যা সমাজে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে দিতে এবং পর্যালোচনামূলক কাজকারবারে উৎসাহ দেয়। তার মতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ রক্ষাকবচ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তাতেও ভূমিকা রাখে। অর্মত্য সেন ব্যাখ্যা দিয়ে দেখান যে, ১৯৫৮-৬১ সালের চীনের দূর্ভিক্ষের একটা বড়ো কারণ ছিল সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকা। সংবাদমাধ্যম যদি স্বাধীন ভাবে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারতো, তাহলে হয়তোবা এই দুর্ভিক্ষ এড়ানো যেতো। তিনি বলেন, কর্তৃত্বমূলক সরকারব্যবস্থা সেন্সরশিপের কারণে যে বিরাটসংখ্যক তথ্য থেকে বঞ্চিত হয়, তা আসলে খোদ সেই সরকারকেই দিনশেষে ভুল সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। সংবাদমাধ্যম স্বাধীন না থাকলে কেবল জনগণই অন্ধকারে থাকে না, খোদ সরকারও অন্ধকারে থাকে।
তৃতীয় কারণটা হচ্ছে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের ‘প্রটেক্টিভ’ ভূমিকা’; সংবাদমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলে জনগোষ্ঠীর অবহেলিত, উপেক্ষিত এবং সুবিধাবঞ্চিত অংশের জবান উঠে আসতে পারে, যা সামাজিক নিরাপত্তাকেই মজবুত করে। বিভিন্ন দুর্ভিক্ষের ইতিহাস থেকে অর্মত্য সেন দেখিয়েছেন, বাক স্বাধীনতা বা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকলে দুর্ভিক্ষের আশংকা বেড়ে যায়। কারণ, সেন্সরশিপ একদিকে সঠিক তথ্য তুলে আনতে বাধা প্রদান করে, অন্যদিকে সরকারি সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিয়ে আলাপ-আলোচনাও রুদ্ধ করে দেয়।
অর্মত্য সেনের কাছে চতুর্থ কারণ হচ্ছে এর ‘গঠনমূলক’ ভূমিকা; মুক্ত আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক সমাজে বিভিন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটাতে, মূল্যবোধ গঠনে এবং জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে সামাজিক ন্যায়বিচার সহজলভ্য হয়। কোথায় কোথায় আমাদের অভাব রয়েছে, আমাদের অসুবিধে রয়েছে, এর থেকে উত্তরণের উপায় কি, এসব নিয়ে বোঝাপড়া তৈরির জন্য আলাপ-আলোচনার স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা জরুরি।
বাকস্বাধীনতা: এশীয় মূল্যবোধ?
মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে একটি অবিচ্ছেদ্য মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও ‘এশীয় মূল্যবোধ’ বা Asian Values এর দোহাই দিয়ে অনেকেই মানবাধিকারের ধারণা প্রশ্নবিদ্ধ করেন; বিভিন্নভাবে বলা হয় মানবাধিকার, বিশেষত মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতার প্রতি এশীয়মূল্যবোধ সমর্থন জোগায় না।
এশীয় মূল্যবোধগুলো কি? সামষ্টিকতা বা কালেক্টিভিজম, আদর্শ মেনে চলা, আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ, পারিবারিক স্বীকৃতির জন্য অর্জন, নম্রতা, পিতারমাতার প্রতি ভক্তি, কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি। যেমন, ‘ব্যক্তির মঙ্গলের চেয়ে গোষ্ঠীর মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে’, ‘কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা ভালো’, ‘যাই ঘটুক না কেন, একজন পুত্র বা কন্যা হিসেবে পিতা-মাতার কথা অবশ্যই মানতে হবে’ ইত্যাদি বহু বিবৃতি এশীয়মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে।
মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ব্যাপারে এশীয় মূল্যবোধের দোহাই দিয়ে দুইভাবে সমালোচনা হতে থাকে। একপক্ষ দাবি করেন যে, এগুলো এশীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় অথবা এর সঙ্গে মাননসই নয়। এশীয় সংস্কৃতিতে সমাজের মৌলিক ভিত্তি হলো পরিবার, ব্যক্তি নয়। দ্বিতীয় পক্ষের সমালোচনা অন্যরকম, তারা দাবি করেন, এশীয়সংস্কৃতি মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের জন্য এখনো ‘প্রস্তুত’ নয়। এখানে উন্নয়ন আগে ঘটাতে হবে; অর্থনৈতিক উন্নয়নের অধিকার মানবাধিকার বা বাকস্বাধীনতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও প্রায় সমান গুরুত্বই বহন করে।
এসবের বিপরীতেও প্রচুর যুক্তি দেয়া হয়েছে। এশিয়া কোনো সমগোত্রীয় ভৌগলিক সত্তা নয়। ফলে পুরো অঞ্চলকে একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধের সুতোয় বাঁধা যাবে না। ‘এশীয় মূল্যবোধ’ তত্ত্ব বহনকারীদের বিপক্ষে আরেকটা ‘রাজনৈতিক’ যুক্তিও হাজির করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক কারণেই এশীয় মূল্যবোধের দোহাই দেয়া হচ্ছে; মূলত স্বৈরাচারী শাসনের বৈধতা দেয়ার জন্যই এটি তৈরি করা হয়েছে। অনেকেই দাবি করেছেন, এশীয় মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক তো নয়ই, বরঞ্চ পরিপূরক।
সময় পাল্টেছে, এখন মত প্রকাশের একটা বড়ো ময়দান হচ্ছে ইন্টারনেট। গবেষকরা জানিয়েছেন, প্রযুক্তির বিস্তার ও ব্যবহার স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন আরও বৃদ্ধি করে। ইন্টারনেটের ব্যবহার গণতন্ত্রের প্রতি এক ধরনের ইতিবাচক প্রভাবও ফেলে। তো, এই সময়ে (মানে ইন্টারনেটের জমানায়) এসে প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজ পর্যায়ে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে এশীয় মূল্যবোধ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সাথে ইতিবাচক নাকি নেতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই ফেই শেন ও লুকমান সুই তাদের গবেষণা চালান।৫ এগারোটা দেশে (উল্লেখ্য এখানে বাংলাদেশ নেই, ভারত-পাকিস্তান আছে) ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে এই জরিপ চালানো হয়। তিনটা দিক থেকে তারা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে পরিমাপ করেছেন: ব্যক্তিগত বাকস্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা।
ফেই শেন ও লোকমান সুই যে তথ্য-উপাত্ত পান তাতে দেখা যায়, বেশির ভাগ এশীয় দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা বাক ও ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা চেয়েছেন। কিন্তু গণমাধ্যমের প্রশ্নে বৈচিত্রপূর্ণ মতামত পাওয়া গিয়েছে। তবে, সব বিষয়ে পাকিস্তান সম্পূর্ণ চিত্র থেকে আলাদা থেকেছে। গবেষকদ্বয় তাদের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানাচ্ছেন, সামাজিক পর্যায়ে উচ্চমাত্রায় এশীয় মূল্যবোধ থাকার সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি কম সমর্থনের কোনো প্রমাণ নেই। ব্যক্তি পর্যায়েও দেখা যায়, এশীয় মূল্যবোধের সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতার কোনো নেতিবাচক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় না।
তার মানে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছাচ্ছেন, এশীয় মূল্যবোধ থাকা মানেই এই নয় যে মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন কম থাকবে। তাদের ভাষায়, ‘এশীয় মূল্যবোধ থিসিসকে বাতিল করে দেয়ার মতো যত প্রমাণ পাই, তার সমর্থনে তত প্রমাণ পাইনি।’ যদিও তারা যে কয়টা এশীয়মূল্যবোধের মাত্রা ব্যবহার করেছেন তার দুইটার সাথে (আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য) মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নেতিবাচক সম্পর্ক পাওয়া গেলেও বাকিগুলোর সাথে এই সম্পর্ক ইতিবাচক। বলছেন, ‘কিছু এশীয় মূল্যবোধ মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনকে দমন করে; কিন্তু অন্যান্য এশীয় মূল্যবোধ বাকস্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের সমতুল্য’।
তাদের ফলাফলে আরো দেখা যায় যে, ইন্টারনেটের ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়াটা একটি মুক্তিকামী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি করে। যেসব মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, তারা মুক্তবাকের প্রতি বেশি ঝোঁকে; যেসব দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার বেশি, সেখানে বাকস্বাধীনতার প্রতি সমর্থনও বেশি।
গবেষকদ্বয়ের মূল কথা হচ্ছে, কেউ ‘এশীয় মূল্যবোধ’ ধারণ করলেই যে সে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রতি সমর্থন কম দিবে বিষয়টা এমন নয়। বরঞ্চ ‘ব্যক্তি অধিকারের ধারণার সঙ্গে প্রথাগত এশীয় মূল্যবোধের কোনো বিরোধ নেই।’
বাংলাদেশ: দৌড় শুরু করতে হবে অনেক পিছন থেকে
যে ডিসক্লেইমার শুরুতেই দেয়া দরকার ছিল, সেটা এখন দেই। বাকস্বাধীনতাকে মানবীয় কর্তাসত্তার সাথে মিলিয়ে পাঠ করার রেওয়াজ আছে; ফরহাদ মজহার৬, বখতিয়ার আহমেদ৭ এ নিয়ে লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। কথা বলার স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক অধিকারই নয়, আমাদের মানবীয়তারও অংশ। বন্ধু সারোয়ার তুষারও সম্প্রতি কয়েকটা লেখাতে বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মানুষের মানবীয়তার সাথে সম্পর্কিত করে বোঝার কমনসেন্স তৈরি উপর জোরারোপ করেছেন।৮ সঙ্গত কারণেই আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়টি উল্লেখিত হয় নি, বরঞ্চ কেবল বাকস্বাধীনতার উপকারিতা বা উপযোগীতার দিকেই নজর দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিখ্যাতজনের বরাত দিয়ে।
বাংলাদেশে তাহলে আমাদের হালচাল কেমন? বাংলাদেশে আসলে আমাদের এই দৌড়টা অনেক পিছন থেকে শুরু করতে হবে। কারণ, উপরে যে বাকস্বাধীনতার ফজিলত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেই ‘বাকস্বাধীনতা’ কীভাবে প্রয়োগ করা হবে তা নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক বিভিন্ন সমাজে আছে। প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবনী নতুন নতুন তর্ক-বিতর্ক হাজির করছে। সময়ের সাথে সাথেও এর নানান মাত্রা দিয়ে আলাপ হয়েছে, হচ্ছে। যেমন, সত্তরের দশকে ‘নো প্ল্যাটফর্ম’ নামে একটা আন্দোলন হয়েছিল। মানে ফ্যাসিবাদী ও বর্ণবাদী মত প্রকাশকারীদের জন্য প্লাটফর্ম দেয়া হবে না। কেউ কেউ একে বাকস্বাধীনতা হরণ বলে অভিহিত করলেও অনেকে বলেছেন, কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে কথা বলার সুযোগ না দেয়া মানেই যে কারো কথা বলার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া তা কিন্তু না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এই যে মঞ্চ না দেয়া বা ‘নো প্ল্যাটফর্ম’ একধরনের নিরব ও পরোক্ষ সেন্সরশীপ চালু করতে পারে। সমাজে এই ধরনের তর্ক-বিতর্ক জারি থাকা সজীবতার লক্ষণ। নাগরিকগণ ক্রমাগত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে প্রায়োগিক বিষয়াদি ঠিক করে নিবেন।
এখানেই বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া। বাংলাদেশের রাষ্ট্রের নাগরিকদের সবচেয়ে বড়ো সংগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞাকে উপড়ে ফেলার সংগ্রাম। আমাদের সংবিধান চিন্তা করার স্বাধীনতা দিলেও নাগরিকদের সেই চিন্তাকে হাজির করার স্বা্ধীনতা দেয় নি। বিস্তারিত আলাপ করার পূর্বে বাকস্বাধীনতা নিয়ে এই দেশের মানুষের একটা দীর্ঘ আন্দোলনের কিছু নমুনা পেশ করি।
বাক-স্বাধীনতার জন্য আমরা পাকিস্তান আমলেও লড়েছি
খুব বেশি ঘাটাঘাটি করার দরকার পড়েনি; হাতের কাছে ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড’ ছিল। আইয়ুব আমলের শুরু থেকে একাত্তরের ২৫ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন দলিলপত্র সেখানে সংকলিত হয়েছে। যে কোনো অমনোযোগী পাঠকও যদি কেবল চোখ বুলিয়ে যান তাহলে খেয়ালে আসবে যে, পাকিস্তান আমলে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের দাবি-দাওয়াতে বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। এই স্বাধীনতাসমূহের কথা কোনো নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর ছিল না, প্রায় সকলেরই লিফলেট-প্রচারপত্রে পাওয়া যায়। অবশ্য, কখনো স্বাধীনতা এসেছে শর্তহীনভাবে, কখনো শর্তায়িতভাবে স্বাধীনতা। কয়েকটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।
১৯৬৩ সালে তৎকালীন সরকার একটা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশ জারি করেছিল। এর বিরুদ্ধে পুরো পাকিস্তানের সাংবাদিকমহল ফুঁসে উঠেছিল। প্রেস অধ্যাদেশ বাতিল, সকল প্রেস আইনের সংস্কার, ঢাকার তিনটা দৈনিক পত্রিকার কালো-তালিকাভুক্তি বাতিল এবং গ্রেফতারকৃত সাংবাদিকদের মুক্তি এমন দাবিদাওয়াসহ সারাদেশে [মানে, পুরো পাকিস্তানে] তখন সাংবাদিকরা হরতাল পালন করেন। ১৯ সেপ্টেম্বরের পাকিস্তান অবজারভার লিখেছিল, খাইবার পাস থেকে চট্টগ্রাম সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে এই ‘কালাকানুনের’ বিরুদ্ধে আওয়াজ উচ্চারিত হয়েছে। ঢাকাতেও, পত্রিকার ভাষ্যমতে, বিরাট সমাবেশ হয়েছে। সেখানে আজাদ পত্রিকার মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান বলেন, আমার এই বয়স ও শারীরিক অবস্থাতে বিছানায় শুয়ে থাকার কথা, কিন্তু দেশে যা হচ্ছে তা আমাকে উঠে দাঁড়াতে ও আওয়াজ তুলতে বাধ্য করছে। তিনি এই বয়সে, দরকার পড়লে, জেলে যেতেও রাজি আছেন বলে সমাবেশে ঘোষণা দেন। তার মতে এই আইন কেবল সংবাদমাধ্যমকে শেকলে বাঁধেনি, বরঞ্চ পুরো জাতিকেই শেকল পরিয়েছে। অন্যান্য সম্পাদকরাও এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন।
সেদিন সমাবেশ থেকে যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তার মধ্যে শুরুতেই ছিল:
‘A gagged press is a national disgrace and is essentially anti-national in character. Press freedom is the basis of all freedoms. Press curbs are a clear denial of the fundamental rights of the people. There can be no free people without a free Press..’
১৯৬৪ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য জনগণের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান কয়েকজন নেতা আবেদন জানিয়েছিলেন। ‘সর্বদলীয় সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন কর্মপরিষদ’ নামক সেই প্ল্যাটফর্মে মওলানা ভাসানী, মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, শেখ মুজিবর রহমান, মওলানা সৈয়দ মোসলেনউদ্দীন সহ আরো কয়েকজন ছিলেন। ভোটাধিকারের দাবীতে প্রদেশব্যাপী সভা, শোভাযাত্রা ও হরতালের আহ্বান সম্বলিত তাদের প্রচারপত্রের শুরুতে ‘জাতীয় জীবনের এক সংকটজনক সন্ধিক্ষণে’র কথা বলা হয়। যেসকল সঙ্কটের কথা ছোট আকারে বলা হয়েছে তাতে এও ছিল, ‘অর্ডিন্যান্স এর যাঁতাকলে বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রায় লুপ্ত’। এই প্রচারপত্রের আরেকটা বক্তব্য বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: ‘ভাইসব, পাকিস্তান অর্জিত হয় জনগণের ভোটে। আর আজ সেই পাকিস্তানের জনগণ কে ভোটাধিকার হইতে চিরতরে বঞ্চিত করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। উহার নজীর কোন স্বাধীন ও সভ্য দেশে নাই – এমনকি ব্রিটিশ আমলেও ছিল না।’ কেন সামঞ্জস্যপূর্ণ, আশা করি খোলাসা করে বলার দরকার নেই।
১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি থেকে একটি পুস্তিকা প্রচারিত হয়। আইয়ুব খান তৎকালীন নির্বাচনীয় প্রচারণায় ‘গণতন্ত্রে’র কথা বলে বেড়াচ্ছিলেন, এর জবাবে এই পুস্তিকায় ‘ভূতের মুখে রাম নাম’ শীর্ষক এক অনুচ্ছেদে লেখা হয়, ‘… কিন্তু ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে যে ‘বিপ্লব’ তিনি করিয়াছিলেন সেই ‘বিপ্লবের’ প্রথম কাজই ছিল গণতন্ত্রকে জবেহ করা। সামরিক শাসন জারির প্রথম ঘোষণাতেই আইনের শাসন উচ্ছেদ করিয়া সামরিক আইনে দেশ শাসন করার কথা ঘোষণা করা হয়। সেই ঘোষণাতে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করিয়া, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া, বাক-স্বাধীনতা হরণ করিয়া, জনগণের সভা-মিছিল করিবার অধিকার পদদলিত করিয়া এক নিমিষে সারা দেশে সামরিক সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়।’
পুস্তিকাটিতে গণতন্ত্রকে ‘হত্যা’ করার কথা বারংবার দেখা যায়। এই ‘অসহ্য অবস্থার প্রতিকারের জন্য’ একনায়কতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিসহ আরো কিছু দাবি তোলা হয়; এর মধ্যে ছিল: ‘জনগণের পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত হোক’।
ন্যাপের ১৪ দফা ‘জাতীয় মুক্তির কর্মসূচি’ প্রচারিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালের জুন মাসে। সেখানে পরিস্থিতি বিশ্লেষণে শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকগণের ‘স্বাধীন ও অবাধ বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথ’ রুদ্ধ করার নানান আইনি সরঞ্জামের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘বর্তমানে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক আরোপিত শাসনতন্ত্র ও সরকারী নীতিসমূহ শুধু যে একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী এক ব্যক্তির হাতে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া দিয়াছে তাহাই নয় ইহা জনসাধারণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতাকে অস্বীকার করিয়েছে’। সেখানে দ্বিতীয় দফাতে বলা হয় ‘পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ঘোষিত জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করিতে হইবে। সকল দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে’।
১৯৬৬ সালের ৮ জুনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রচারিত একটি লিফলেটেও বলা হয় ‘সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী এই জালিম সরকার সাম্রাজ্যবাদেরই সহযোগিতায় ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসন জারির মারফত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা পুরোপুরি কব্জা করিয়া নিয়াছে। আপামর জনসাধারণের সুখী-সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা মাটিচাপা দিয়াছে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ মানুষের সকল মৌলিক অধিকার ছিনাইয়া লইয়াছে।’ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয় সেখানে।
১৯৬৭ সালে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে একটা পুস্তিকা প্রচারিত হয়। ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ৫টি বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানায়। সেই ঘোষণাপত্রে বলা হয়, ‘প্রত্যেক সভ্য দেশে গণ-অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা মৌলিক বলিয়া স্বীকৃত এবং স্বাধীন ও সভ্য সমাজের অস্তিত্বটুকু প্রয়োজনেই তাহা অলঙ্ঘ্য ও পবিত্র বলিয়া বিবেচিত।’ ৮ দফা কর্মসূচীর প্রথম দফাতেই ‘সংবাদপত্রের অবাধ আযাদী’র কথা উল্লেখ করা হয়। পুস্তিকায় দেশবাসীর নিকট আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, ‘আজ ব্যক্তিস্বাধীনতার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। জরুরি অবস্থা অপ্রয়োজনীয়ভাবে চালু রাখা, কথায় কথায় ১৪৪ ধারা জারি করা, সভা-সমিতি ও মিছিলের সুযোগ না দেওয়া, বিনা বিচারে আটক রাখা, প্রতিরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ করা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা ইত্যাদির ফলে নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে।’ রাজনৈতিক দাবিতে বলা হয়: ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা -স্বীকার কর।’
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালে সাংবাদিকরা মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। সংবাদ মারফত জানা যায় যে, ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের আহবানে গতকল্য (রবিবার) প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে সংবাদপত্রে নিয়োজিত ঢাকায় কার্যরত সাংবাদিক, কর্মচারী ও প্রেস কর্মচারী এবং হকারদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাবেশ শেষে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সেবীদের একটি দীর্ঘ মিছিল রাজপথে নামিয়া আসে। মিছিলকারীগণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পূর্ণ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, দেশ রক্ষা বিধি, প্রেস অর্ডিন্যান্স সহ সকল কালা কানুন বাতিল, সংগ্রামের মাঝে পূর্ব-পশ্চিম এক হও, নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশ প্রত্যাহার, ইত্তেফাক ছাপাখানার বাজেয়াপ্তি প্রত্যাহার, রাজ বন্দীদের মুক্তির দাবীতে গভর্নর হাউজের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।’
১৯৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি একটি প্রচারপত্র প্রচারিত হয়, লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির পক্ষ থেকে। চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং আন্দোলনে সমর্থনে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় একটি সভা ও মিছিলের আয়োজন করেন। প্রতিবাদ সভাটি ১৫ জানুয়ারি বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণে হওয়ার কথা ছিল, সভাপতি ড. এনামুল হক। বক্তার তালিকায় জয়নুল আবেদিন, আহমদ শরীফ, সুফিয়া কামাল, সিকানদার আবু জাফর, কে জি মোস্তফা, রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লা কায়সা, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীনের নাম ছিল। সেই প্রচারপত্র যা বলা হয়েছিল সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; আমাদের বর্তমানের সময়ের বিচারে আরো গুরুত্বপূর্ণ:
‘মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। সকল উন্নত জাতির বিকাশের মূলেই রয়েছে এই অধিকারের নিশ্চয়তা। সে কারণেই প্রতিটি উন্নতিকামী স্বাধীন জাতিই চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রাণেরও অধিক মূল্যবান বলে মনে করেন এবং তা সংরক্ষণের জন্য কোন ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধাগ্রস্ত হন না। পক্ষান্তরে এও লক্ষণীয় যে কোন জাতিকে দাবিয়ে রাখতে চাইলে তাঁদের শাসকবর্গ চান প্রথমেই সে জাতির চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দিতে। এ উদ্দেশ্যে শাসকবর্গ জাতির চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিতে এমন ষড়যন্ত্র নেই যার জাল বিস্তার করতে ইতস্তত বোধ করেন, এমন কোন সরকারি মাধ্যম নেই যার সাহায্য সক্রিয় হয়ে উঠতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেন।
আমাদের বেলাতেও বিগত বাইশ বছরের ইতিহাসে দেখা গেছে, সরকার স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ করে এই প্রদেশের জনসাধারণের কণ্ঠ রোধ করা এক প্রধান নীতি হিসাবে অনুসরণ করে চলেছেন। কুখ্যাত প্রেস ও পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স জারী করে সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার যে স্বেচ্ছাচারী নজির স্থাপন করা হয়েছে, তা শুধু ব্রিটিশ শাসন নীতির সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। এই অর্ডিন্যান্স জারী করার পূর্বেই স্বাধীনতা লাভের পরপরেই পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত প্রকাশনা ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধের খাঁড়া সমানভাবে ঝুলে রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরের যে কোন কর্মচারীর মাধ্যমে লিখিত, অলিখিত যে কোন উপায়ে ‘প্রেস উপদেশ’ ও সংবাদ বিশেষের উপর ‘এমবার্গো’ জাতীয় ব্যবস্থার সাহায্যে জনমতের স্বাধীনতার উপর হামলা।
অন্যদিকে জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত রেডিও এবং টেলিভিশন সরকার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব প্রচারযন্ত্ররূপে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। সকলের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ রেডিও, টেলিভিশনে তো নেই-ই, এমনকি এইসব প্রচারযন্ত্রে স্বাধীনভাবে শব্দও ব্যবহার করা যায় না। …
এরই পাশাপাশি রয়েছে গ্রন্থ প্রকাশের ওপর সরকারের ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত দমননীতি। স্বাধীনতার পর এ প্রদেশে সরকার যে একে একে কত বই বাজেয়াপ্ত করেছেন, তার হিসাব নেই। বিশেষ করে সম্প্রতি সেই কুখ্যাত প্রেস ও পাবলিকেশন্স-এর কালাকানুনের সাহায্যেগ্রন্থ বিশেষের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে, কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী এবং কোন বই আটক ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে সরকার নতুনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের কণ্ঠরোধে তৎপর হয়ে উঠেছেন। …
বস্তুত: স্বৈরাচারী শাসকবর্গের নিকটও একটি জাতিকে অবদমিত রাখার জন্যে এটাই হলো সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা। … তাই এ মুহূর্তে লেখকদের স্বাধিকার সংরক্ষণ এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের ওপর যে কোন প্রকারের হামলার প্রতিরোধে প্রতিটি নাগরিককে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। শেষবারের মতো এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে, আমরা স্বাধীন জাতি এবং আমাদের চিন্তা ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ আমরা যে কোন মূল্যে প্রতিরোধ করবো এবং এই অনাচারকে আমরা কিছুতেই কায়েম থাকতে দেবো না।’
১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে ‘সংগ্রামী ছাত্রসমাজ’ পক্ষ থেকে এগার দফার দাবী জানানো হয়। সেখানে দ্বিতীয় দফাতে বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উল্লেখ পাওয়া যায়: ‘প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।’
সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রামের কমিটির আহবানে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র ও গণহত্যা, সহকারী নির্যাতন ও ব্যাপক হারে গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি ‘…দেশরক্ষা আইন ও নিরাপত্তা আইন বাতিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান, ইত্তেফাক ও অন্যান্য সংবাদ পত্রের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রদান…’ এর দাবি জানানো হয়।
১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারিতে পল্টনে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় কিছু প্রস্তাবলী গৃহীত হয়। সেখানে ‘শপথ প্রস্তাব’-এ বলা হয়: ‘এই সমাবেশ ঘোষণা করিতেছে যে, স্বৈরাচারী একনায়কত্ববাদী আইয়ুব সরকারের অবসান ঘটাইয়া অবিলম্বে সারা পাকিস্তানের সকল জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম ….সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম, সকল দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করিয়া ছাত্র ….কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।’
১৯৬৯ সালের এপ্রিলে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক ‘স্বাধীন জন-গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা’র কর্মসূচি পেশ করা হয়। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো এবং রাশেদ খান মেনন। কর্মসূচির রূপরেখাতে বলা হয়, ‘জনগণের বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও প্রকাশনার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।’ কিন্তু পুরো কর্মসূচিতে এই স্বাধীনতার সাথে কিছু শর্তও যুক্ত ছিল। যেমন, ‘কোন অবস্থাতেই সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজির পক্ষেও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বক্তব্য প্রকাশ ও সংগঠিত করিবার অধিকার দেওয়া হইবে না’, ‘নোংরা মার্কিনী সিনেমা, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও গণবিরোধী সকল প্রকার সাংস্কৃতিক কার্যকে উৎখাত করাহইবে ও নিষ্ঠুর হস্তে দমন করা হইবে’, এবং ‘…রাষ্ট্র মার্কসবাদকে বিৃকতকারী সংশোধনবাদী নয়াসংশোধনবাদ ভাবাদর্শে পূর্ণশিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিষিদ্ধ করিবে।’
১৯৬৯ সালের আগস্টে প্রচারিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে ‘ব্যক্তি-স্বাধীনতা’ অনুচ্ছেদে বলা হয়: ‘…মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, বই-পুস্তক, সংবাদপত্র ও প্রচারপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা, সমবেত হইবার ও সংগঠন করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং দেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা থাকিতে হইবে। …একমাত্র যুদ্ধকালীন সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে এই সকল অধিকার খর্ব করা হইবে না। ‘জরুরী অবস্থার’ অজুহাতে অন্যায়ভাবে কোন নাগরিকের অধিকার খর্ব করা চলিবে না।…’
১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন স্বাধীন জন-গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচি সম্পর্কিত একটি প্রচারপত্রের ৩ নং দফাতে ছিল: ‘জনগণের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মতাদর্শের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে’। ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৪ দফা দাবি জানায়। সেখানেও ৪র্থ দফাতে ছিল: ‘ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিজ বিবেক অনুযায়ী দল, সংঘ-সংগঠন গঠনের অধিকার, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারের পূর্ণ গ্যারান্টি থাকিতে হইবে…’
১৯৭১ সালের ৩ মার্চে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে যে ইশতেহার পাঠ করা হয় সেখানে তিনটা লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়। তৃতীয় লক্ষ্যে স্পষ্টত বলা হয়েছে: ‘স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে’।
অতি অল্প কিছু নমুনা হাজির করলাম কেবল; সেগুলোতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন দল সংগঠনের দাবিদাওয়াতে বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা একেবারে মৌলিক প্রশ্ন হিসাবে হাজির হয়েছিল। তারা যখন জনগণের সামনে দেশের তৎকালীন দুরবস্থার কথা বলছিলেন তখন সেগুলোর ‘অনুপস্থিতি’র দিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। ফলস্বরূপ আন্দোলনের দাবি-দাওয়াতেও এই স্বাধীনতাগুলো ‘নিশ্চিত’ করার ওয়াদাও বারেবারে দিয়েছেন, বা তাদেরকে দিতে হয়েছে। দুয়েকটা দল বা সংগঠন বাদে অধিকাংশ সময়ই এই স্বাধীনতাকে প্রায় ‘নিঃশর্ত’ আকারেই হাজির করা হয়েছিল। এমনকি বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকারের বর্গেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই আন্দোলনে কেবল রাজনৈতিক সংগঠনই জড়িত ছিল না, আমরা দেখেছি সাংবাদিক মহল ও লেখক-বুদ্ধিজীবী মহলও বিভিন্ন সময়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য রাস্তায় নেমেছেন। আন্দোলনে শরিক হয়েছেন।
সংবিধানে চিন্তার স্বাধীনতা থাকলেও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নানাভাবে শৃঙ্খলিত
দীর্ঘ পঁচিশ বছরের নানামুখী সৃজনশীল অহিংস সংগ্রাম, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, পঁচিশ মার্চের রাতের পর সশস্ত্র লড়াই, জেনোসাইডে তিরিশ লাখ লোকের প্রাণহানি- এতো এতো ত্যাগ তিতিক্ষার পর আমরা যে সংবিধান তৈয়ার করলাম বাহাত্তর সালেই, সেখানে বাক-স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। ‘জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকাররক্ষণ’ সংক্রান্ত ৩২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, ‘আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।’ এই বাক্যকে উল্টো করে পড়লে দেখা যাবে, জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে যদি সেটা আইনানুযায়ী হয়ে থাকে। এর সবচাইতে ‘কার্যকর’ ব্যবহার আমরা দেখতে পাই ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘বন্দুকযুদ্ধে’। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে লড়াইয়ের কালে জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সাথে কোনো শর্তারোপ না করলেও লড়াই সফল হওয়ার পর বলা হচ্ছে, সেই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে যদি সেটা আইন অনুযায়ী হয়ে থাকে। ঔপনিবেশিক আইনকাঠামো দিয়ে নাগরিককে জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার নজির আমাদের দেশে প্রচুর। আবার, ‘চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা’ শীর্ষক ৩৯ নং অনুচ্ছেদে ‘চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা’ দেয়া হলেও বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে করা হয়েছে শর্তাধীন। সাম্প্রতিক একটি ঘটনা দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করা যাক।
৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাউল শরিয়ত সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে মামলা করা হয়; ১১ জানুয়ারি ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে মির্জাপুর থানা পুলিশ; এবং ১৪ জানুয়ারি তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়। বেশ কিছুদিন জেল খাটার পর অতঃপর শরিয়ত সরকারের জামিন হয়। বাউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে; বলা হয়েছে যে, বাউল বলেছিলেন, গান-বাজনা হারাম বলে ইসলাম ধর্মে কোনো উল্লেখ নেই। কেউ প্রমাণ দিলে তিনি গান ছেড়ে দেবেন। এমন বক্তব্য শুনেই বাদী মামলা করেছিলেন।
বাউল কী বলেছেন? বা বাউল কি আদৌ ধর্মকে অবমাননা করেছিলেন? বা, বাউলের কথায় যৌক্তিকতা ছিল কি না বা তার জামিন সংক্রান্ত কোনো ধরনের আলাপে আমরা প্রবেশ না করে বরং বাউলের ঘটনাকে একটা বিশেষ বিষয়ের কেসস্টাডি হিসেবে পাঠ করতে চাই: বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সাংবিধানিক বাকস্বাধীনতার অস্তিত্বের স্বরূপ চিহ্নিত করতে এবং সংবিধানের এই স্বাধীনতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে (৩৯ নং) যে প্যারাডক্স হাজির আছে তা তুলে ধরতে।
বাউল শরিয়তকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন মূল প্রশ্নটা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে ঘিরে তৈরি না হয়ে বরং শিল্পী-বাউল-গান-বাজনার উপর আঘাতই মূল প্রশ্ন হিসাবে হাজির হয়েছিল। করোনা পরিস্থিতিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সরকার সমালোচকদের গণ-গ্রেফতার বা গণ-মামলার অভিজ্ঞতা এই আইন এবং বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মূল প্রশ্ন হিসেবে হাজির করেছে। আন্দোলনে তাই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলই মূখ্য দাবি।
যারা এই আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এমন মতও পোষণ করেন যে, বাংলাদেশের সংবিধান বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। অভিজ্ঞতা বলে যে, প্রগতিশীল রাজনীতি চর্চায় জড়িতদের সিংহভাগই সংবিধান প্রদত্ত বাকস্বাধীনতায় গভীর আস্থা প্রকাশ করেন। ফলে, অনেকেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে সংবিধানের পরিপন্থী বা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে দাবি করছেন। কিন্তু, এই আমরা বলতে চাচ্ছি যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে যে মামলাগুলো করা হচ্ছে সেগুলোকে সাংবিধানিকভাবেও ‘বৈধ’ হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব। মানে, আদতে এগুলো যে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না সেটা প্রমাণ করা সম্ভব। উল্টো সাংবিধানিক এখতিয়ারের আওতায় এ ধরনের মামলা-জুলুম করা সম্ভব।
উল্লেখ্য, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যে বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পথকে রুদ্ধ করে দেয় তার প্রমাণ দেয়াটা এই মুহূর্তে বাহুল্যই হবে; বিস্তর লেখাপত্র অনলাইন-অফলাইনে রয়েছে।
বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে মূলত বাকস্বাধীনতা সংক্রান্ত আলাপ রয়েছে। এই অনুচ্ছেদের নামকে দুইভাবে ভাগ করা যায়: ১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ২) বাক স্বাধীনতা। ‘ভাব-প্রকাশের স্বাধীনতা’ এবং ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা’ দুটোকে বাক-স্বাধীনতার মধ্যেই ফেলে দেয়া যায়।
সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের প্রথমেই কোনো বিধিনিষেধ বা ‘সাপেক্ষে’ ছাড়াই ‘চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান’ করা হয়েছে। কিন্তু বাকস্বাধীনতা, ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে এভাবে নির্বিঘ্নে ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং একটা বিরাট বাক্যের অধীনে এই স্বাধীনতাগুলোকে শর্তায়িত করে রাখা হয়েছে। শর্তগুলো হলো,
‘রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে…’
এই অনুচ্ছেদ খেয়াল করে পড়লে বোঝা যাচ্ছে, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা দেয়া হলেও বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বেড়াজালে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হলো, বাক স্বাধীনতা ছাড়া চিন্তার স্বাধীনতা আদৌ কি কোনো অর্থ বহন করে? ধরুন, আমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই চিন্তাকে ভাষার মাধ্যমে হাজির করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত সেই চিন্তা কি আদৌ ‘চিন্তা’ হয়ে উঠতে পারবে? বা পেরেছে বলে কি আমি নিশ্চিত হতে পারি? উদাহরণস্বরূপ এই লেখাটার কথাই ধরা যাক। আমি সংবিধানের একটা ধারার প্যারাডক্স নিয়ে চিন্তা করছি, কিন্তু আমি যদি সেটা মৌখিক বা লিখিত রূপে ভাষার মধ্যে দিয়ে হাজির করতে না পারি তাহলে সেই চিন্তার অস্তিত্ব তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই চিন্তার থাকা বা না থাকাটা কি তখন তাৎপর্য বহন করে? চিন্তা বা চিন্তার বিষয়বস্তু পরীক্ষিত বা পরিশীলিত বা যুক্তির কঠিন ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বা এমনকি ভুল প্রমাণিত হওয়ার জন্যও সেই চিন্তাকে প্রকাশ ঘটাতে হবে। সংবিধানের যে বিষয়টা আমার কাছে প্যারাডক্স মনে হচ্ছে, সেটা আমার বুঝতে ভুলও হতে পারে, সেটা নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু সেই তর্ক-বিতর্ক তো হবে চিন্তার প্রকাশ ঘটার পর। মানে, মত প্রকাশের পর।
জে. বি. বিউরি যখন ‘চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস’ লিখা শুরু করেন, তখন একেবারে গোড়াতেই ঘোষণা দেন, চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস আসলে বাক স্বাধীনতারও ইতিহাসও বটে। ‘কথা বলার স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া চিন্তার স্বাধীনতা কোনো অর্থ বহন করে না’।
বিষয়টা তাহলে দাঁড়ালো এই, আমাদের সংবিধান বলছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন স্বাধীনভাবে, কিন্তু সেই চিন্তার প্রকাশ করার বেলায় আপনি পরাধীন, শর্তায়িত। যে শর্তগুলোর কথা সংবিধানে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে, মানে যেসব ব্যাপারে আপনার বাকস্বাধীনতা সীমিত সেগুলো হচ্ছে, ‘রাষ্ট্রের নিরাপত্তা’, ‘বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক’ , ‘জনশৃঙ্খলা’, ‘শালীনতা’ বা ‘নৈতিকতা’ ইত্যাদি।
উপরে উল্লিখিত বাউল শরিয়তের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে ‘জনশৃঙ্খলা’ ও ‘নৈতিকতা’ এই দুটোর সাপেক্ষে বিবেচনা করতে পারি। ‘নৈতিকতা’ সবসময়ই নির্ধারিত হয় মূলধারার বয়ান অনুযায়ী। প্রমিন্যান্ট ডিসকোর্সই মূলত ঠিক করে দেয় কোনটা নৈতিক আর কোনটা অনৈতিক। এটা একেবারেই স্থান-কাল-ধর্ম-আচার-ক্ষমতা সাপেক্ষ। বাউল শরিয়ত বলেছেন ইসলামে গান বাজনা হারাম নয়; দাবি করা যেতেই পারে, বাউলের এই উক্তি এখনকার বিদ্যমান ইসলামের আধিপত্যশীল বয়ানের সাথে খাপ খায় না। বাংলাদেশের অধিকাংশ ধর্মীয় পণ্ডিতরা মনে করেন, গান বাজনা হারাম। ইসলামি জগত ও দর্শনে এ নিয়ে বিস্তর জ্ঞানতাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক থাকলেও সেটা এখানে একেবারে ‘গৌণ’ হয়ে পড়ে, কারণ ‘নৈতিকতা’ সর্বত্রই নির্ধারিত হয় মূলধারা ও ক্ষমতার ইচ্ছাধীন। একইভাবে যখনই কেউ কোনো সামাজিক ট্যাবু ভাঙ্গতে চান বা যান বা সেই ট্যাবু নিয়ে কথা বলতে যান তখনও একইভাবে মূলধারার ‘নৈতিকতা’র মানদণ্ডে আটকা পড়তে পারেন। সাম্প্রতিক সমকামিতা সংক্রান্ত আলাপও এখানে ‘নৈতিকতা’ বা ‘শালীনতা’র বেড়াজালে বন্দী হতে পারে। সেটা খুব সহজেই ধর্মীয় অবমাননা বা বিভিন্নধরনের অনুভূতিসংক্রান্ত ফ্যাসাদের দিকে ধাবিত হতে পারে। মানে, নৈতিকতা ও শালীনতার ‘স্বাপেক্ষে’ কখনোই মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায় না। দেখা যাচ্ছে, বাউলের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে আনীত অভিযোগ যে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় সেটা প্রমাণ করা সম্ভব।
‘নৈতিকতা’র সাথে কীভাবে ‘জনশৃঙ্খলা’ মিশে যেতে পারে তার একটা ধ্রুপদী উদাহরণও হচ্ছে শরিয়ত বাউলের ঘটনা। বাউলকে রিমান্ড শেষে জামিন না দিয়ে জেলে পাঠানোর আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ; বলা হয় যে, ‘আসামী জামিনে মুক্তি পাইলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে এবং … সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে’। এই লেখার প্রাথমিক খসড়া তৈরি পর্যন্ত তার জামিন ঝুলে ছিল, বারেবারে আবেদন করা হচ্ছিল, কিন্তু ‘জামিন পেলে আবারও এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হতে পারে…’ এই কারণে তাকে জামিন দেয়া হচ্ছিল না। (প্রথম আলো, বাউল শরিয়তের জামিন আবেদন নাকচ, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০)। সমাজে চালু থাকা কোনো মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতানুসারী কর্তৃক ‘জনশৃঙ্খলা’ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকায় আপনার মতকে কাটছাঁট করেই প্রকাশ করতে হবে, আর নাহলে মত প্রকাশকে দমন করতেই হবে। আর এই ক্ষেত্রে, বাউল যে অপরাধ করেছেন তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষমতাতন্ত্রের একেবারে চূড়ায় বসে থাকা ব্যক্তিটি। ২২ জানুয়ারিতে (২০২১) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন, ‘অপরাধে জড়িত বলেই বাউল শরিয়তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’ [প্রবন্ধের খসড়া তৈরির মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্ধৃতি ডেইলি স্টারের বরাত উল্লেখ করা হয়েছিল। পাণ্ডুলিপি রেডি করার সময় যখন লিঙ্কে প্রবেশ করতে গেলাম, আবিষ্কার করলাম, লিঙ্ক আর কাজ করছে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্য অন্যান্য অনলাইন মিডিয়াতেও প্রকাশিত হয়েছে।]
সহজ কথা হচ্ছে, ‘শালীনতা’ বা ‘নৈতিকতা’ ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা এত বিস্তৃত এবং ক্ষমতা ও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনযোগ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছয়মাস পূর্বের বাউল শরিয়ত বা এই সময়ের সিরাজাম মুনিরা, তারা যে সংবিধানের বরখেলাপ করেছেন, তা শালীনতা বা নৈতিকতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ দেয়া সম্ভব।
পাশপাশি, এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ‘রাষ্ট্রের নিরাপত্তা’, বা ‘বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক’ এর মতো বাক্য বাকস্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে। যেমন, একজন গবেষক চিন্তা করলেন তিনি ভারতের সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটা গবেষণা করবেন। তিনি সেই গবেষণার চিন্তা করতেই পারেন, কেননা তিনি চিন্তায় স্বাধীন। কিন্তু, এখন ভারত যেহেতু আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র গবেষকের সেই চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বা গবেষণা প্রকাশিত হলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। বা, কোনো সংবাদপত্রে এমন কোনো রিপোর্টের বেলায় আমাদের রাষ্ট্র মনে করতেই পারে যে, এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। তখন আপনি সংবিধানের বেড়াজালে আটকা পড়ে গেলেন, আপনার গবেষণা তখন অ-সংবিধানিক।
ফলে এটা বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধান আসলে ‘চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা’ নিশ্চিত করলেও সেই চিন্তাকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা (মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা) নিশ্চিত করে নি। তাই বাকস্বাধীনতার প্রশ্নে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হিসাবে দেখার যে জনপ্রিয় মত চালু আছে সেটা আসলে কোনো অর্থ বহন করে না।
‘চিন্তা’র সাথে ‘চিন্তাকে হাজির করা’র মধ্যে যে দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে সেটা আসলে একটা জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত চিন্তাকে, চিন্তার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। চিন্তা আসলে কোনো ‘ব্যক্তি’র বিষয় নয়, এটা আসলে ‘কালেক্টিভ’ বিষয়। তাই জ্ঞান উৎপাদন ও চর্চাও আসলে ‘কালক্টিভ’ বিষয়। আমার চিন্তা বহু জনের চিন্তার সাথে মিলবে, বহুজনের চিন্তা আমার চিন্তার সাথে মিলবে, মোলাকাত করবে, পরীক্ষা দিবে, খারিজ হবে, গৃহীত হবে – এমন বহু যৌথ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই আসলে চিন্তাচর্চা এগিয়ে যায়। কিন্তু এই সব ‘কর্মকাণ্ড’ কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন সেই চিন্তাকে হাজির করার স্বাধীনতা বজায় থাকবে। এটাই আসলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। এটাই আসলে বাক স্বাধীনতা। এটাই এর ফজিলত।
ফলে, বাকস্বাধীনতাকে কীভাবে কাজে লাগাবে এই জিজ্ঞাসার পূর্বে তাকে স্বাধীনতার সেই অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য রাজপথে নামতে হচ্ছে। মরার ওপর খাড়ার ঘা স্বরূপ যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। ২০১৯ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছিল ৭৩২টি, গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ৬০৭। এবং ২০২০ সালে প্রথম ৫ মাসেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে ৪০৩টি, গ্রেপ্তার হয়েছেন ৩৫৩ জন। অর্থাৎ, করোনাকালে কথা বলার দায়ে দমন-পীড়নের হার বেড়ে গিয়েছে। মামলার প্রধান প্রধান ‘খাত’ হচ্ছে: মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে ‘মিথ্যা সংবাদ’ পরিবেশন, ফেসবুকে লেখা, বঙ্গবন্ধু, তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী, প্রধানমন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে ফেসবুকে ‘কটূক্তি’, করোনাভাইরাস ও এর চিকিৎসা নিয়ে ‘গুজব ছড়ানো’, ত্রাণ চুরির ‘মিথ্যা তথ্য’ ছড়ানো ও সংবাদ পরিবেশন, সরকারবিরোধী প্রচারণা, পুলিশের সমালোচনা করে সংবাদ পরিবেশন ও ফেসবুক লেখা, ধর্ম নিয়ে কটূক্তি বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ইত্যাদি।৯
অর্মত্য সেন স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, উপনিবেশকালে কেবল যে সরকারের সমালোচনা করলেই গ্রেফতার করা হয়েছে, তা কিন্ত না; সুযোগ পেলে সরকারের সমালোচনা করতে পারে এই ‘আন্দাজ’ থেকে ‘সম্ভাব্য দুষ্কৃতিকারী’কে গ্রেফতার করা হতো। আমাদের গর্দানের উপর জারি থাকা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনেও এমন ঔপনিবেশিক আমলের ইশারা আছে। এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ আপনার না করলেও চলবে, কেবল রাষ্ট্রীয় বাহিনী যদি মনে করে অপরাধ ‘হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে’ তাহলেও আপনাকে গারদে ভরতে পারবে। অর্থাৎ যদি উর্দিওয়ালাদের মনে হয় আপনার অপ্রকাশিত ‘মত’ খতরনাক হতে পারে তাহলে আপনি আইনের জালে বন্দী হতে পারেন।
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাগরিকদের মূল দ্বন্দ্ব তাই রাষ্ট্রের সাথেই। এই রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবেই মত প্রকাশকে বিবিধ শর্তের অধীন করে করেছে, উপরন্তু দিনকে দিন মানুষের বাকস্বাধীনতাকে কেড়ে নেয়ার জন্য আরো বেশি আইনি হাতিয়ার তৈরি করছে। আবার, ইতিহাস-বিকৃতি রোধের জন্য বিভিন্ন আইন তৈরির খায়েশ রয়েছে জাতীয়তাবাদী মহলেরও; ইতিহাসের সত্য- মিথ্যা নির্ধারনের ভার আমরা তুলে দিতে চাই রাষ্ট্রের হাতে। [উল্লেখ্য, একসময় আমিও ইতিহাস-বিকৃতি রোধের আইনের পক্ষে ওকালতি করেছি। ইতিহাসের সত্যমিথ্য নির্ধারণের ভার আদালত বা রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিতে চেয়েছি। নিঃসন্দেহে এই লেখা আমার পূর্বের অবস্থান থেকে একটি ‘উত্তরণ’; এবং কেন- সেটাও এই লেখাতে হাজির করতে পেরেছি বলে মনে করি।] ফলে, একদিকে এমনিতেই এই রাষ্ট্র বাকস্বাধীনতার অনুমোদন দেয় না, অন্যদিকে যেটুকু স্বাধীনতা আছে সেটুকুও কেড়ে নেয়ার বাস্তবতা শাসকগোষ্ঠী ক্রমাগত তৈরি করছে। ফলে, আমাদের লড়াই একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হচ্ছে। আমার কথা বলার উপর রাষ্ট্রীয় খবরদারিকে ন্যাস্যাৎ করতে হবে। এর ফজিলত কি- তার কিছুটা আভাসমাত্র উপরে দেয়া হয়েছে।
বর্তমানে যখন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের জন্য জোরেশোরে আওয়াজ উঠছে, তখন আমাদের এও মনে রাখা উচিৎ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের মাধ্যমেই আমাদের বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত হয়ে যাবে না। খোদ আমাদের সংবিধানেই এই স্বাধীনতার নিশ্চয়তা নেই। তাই, আমাদের দীর্ঘমেয়াদি দাবি তুলতে হবে সাংবিধানিকভাবে আমরা বাকস্বাধীনতা চাই। নিঃশর্ত কথা বলার অধিকার চাই। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে, কোনো আইনের বিরুদ্ধে জনমত ফুঁসে উঠলে এটাকে সংশোধন করে আরো বেশি নিপীড়নমূলক আইন বানানো হয়। ফলে, এমন গণবিরোধী আইন তৈরির যে কাঠামো চালু আছে খোদ সেটাকেও আমাদের বদলাতে হবে। অন্যথায়, গণ-আন্দোলনের মুখে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল হলেও সেটা আরো নয়া নয়া রূপে ফিরে আসবে।
শেষ কথা
দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান আমলের দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামে যে দাবি-দাওয়া সবচাইতে স্পষ্ট ছিল একাত্তরের পর রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সেগুলোই বরঞ্চ বিভিন্ন শর্তের বেড়াজালে বন্দী হয়ে গেলো। খাঁচার ভেতর পাখির উড়াউড়ি। উল্টো, এই স্বাধীনতাগুলো সবচাইতে ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়েছে বর্তমান কালে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আক্ষরিক অর্থেই কারাগারে পুরে দিয়েছে। এই আইনের ব্যবহার যে ‘আপেক্ষিক’ খোদ সেটা বাংলাদেশের ‘অগণতান্ত্রিক’ প্রধানমন্ত্রীও মেন নেন।১০ অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, যে মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ সংগ্রামে ‘বাক-স্বাধীনতা’, ‘মত প্রকাশের স্বাধীনতা’, ‘সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা’ ইত্যাদির উপস্থিতি সবচাইতে স্পষ্ট ছিল, বর্তমানে সেই স্বাধীনতাগুলোকে বন্দী করা হচ্ছে খোদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে।[ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]১১ বাকস্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের দীর্ঘ লড়াই জানান দিচ্ছে, গণমানুষের যে মুক্তিযুদ্ধ ও তার সংগ্রামের চেতনা, তার সাথে বিদ্যমান রেজিমের ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ নামক মতাদর্শিক বয়ানের কোনো মিল নাই। বরঞ্চ দুটোর গতি-প্রকৃতি ভিন্ন ও উল্টো।
বহুদিন যাবত বলা হচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে একধরনের অঘোষিত ‘স্বাভাবিক জরুরি অবস্থা’ জারি আছে। মাত্রাগত রকমফের হচ্ছে কখনো সখনো। ফলে এখানে রাষ্ট্রের কাছে মহামারি মোকাবিলার করার চেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে ভিন্নমতাবলম্বী বা সমালোচকদেরকে মোকাবিলা করা। অন্য অর্থে, খোদ নাগরিকের বিরুদ্ধেই এক অন্তহীন এক ‘যুদ্ধে’ লিপ্ত হওয়া; ব্যক্তি ও সমাজকে রাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত করা। ডিজিটাল নিরাপত্ত আইন বাতিল এবং সংবিধানে বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করার আমাদের এই লড়াইয়ে ক্রমাগত সক্রিয়তার যেমন কোন বিকল্প নাই, ঠিক তেমনি বিকল্প নাই এহেন স্বৈরাচারী আইন প্রনয়ণ করতে পারার মত একব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পাল্টানোর।
দোহাই:
১) John Stuart Mill, On Liberty, 1859
২) Nigel Warburton, Free Speech: A Very Short Introduction, OUP Oxford, 2009
৩) চমস্কিকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই বিতর্কের হদিস পাবেন: Noam Chomsky, Some Elementary Comments on The Rights of Freedom of Expression, [Appeared as a Preface to Robert Faurisson, Mémoire en défense, October 11, 1980], chomsky.info; The Faurisson Affair, Noam Chomsky writes to Lawrence K. Kolodney, Circa 1989-1991, chomsky.info; Faurisson affair, Wikipedia; Film: Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media, 1992
৪) উন্নয়নের সাথে স্বাধীনতার সম্পর্ক নিয়ে অর্মত্য সেনের বহু আলাপ আছে। এই প্রবন্ধের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে: Amartya Sen, ‘Speaking of Freedom: Why Media Is Important for Economic Development’, The Country of First Boys, 2015
৫) ফেই শেন ও লোকমান সুই, ‘এশীয়মূল্যবোধ ফিরে দেখা: ইন্টারনেটের ব্যবহার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা’, প্রতিচিন্তা, ২০১৮। [অনুবাদ: খলিলুল্লাহ]
৬) ফরহাদ মজহার, প্রস্তাব, আগামী প্রকাশনী, ১৯৭৭
৭) বখতিয়ার আহমেদ, ‘ভাষা, সংস্কৃতি ও মানবসত্তা: একটি নৃবৈজ্ঞানিক আলাপচারিতা’, রাষ্ট্রচিন্তা, ২০২০
৮) সারোয়ার তুষার, ‘বাকস্বাধীনতা রাজনৈতিক শর্তের অধীন নয়, মানবীয়তার অংশ’, সময়ের ব্যবচ্ছেদ, গ্রন্থিক, ২০১৯
৯) প্রথম আলো, করোনাকালে সমালোচনা-কটূক্তির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা-গ্রেপ্তার বেড়েই চলেছে, ৭ জুলাই ২০২০
১০) ‘আইন তার আপন গতিতে চলে। আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে কিনা, এটা হলো দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। কোনটা আপনার কাছে অপপ্রয়োগ আর কোনটা অপপ্রয়োগ না, এটাও একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। আমি মনে করি, আইন তার নিজ গতিতে চলছে এবং চলবে। যদি কেউ অপরাধ না করে, তার বিচারে শাস্তি হবে না।’- প্রধানমন্ত্রী; ডেইলি স্টার, “আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে কিনা, এটা হলো দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার: প্রধানমন্ত্রী”, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১।
১১) মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রপাগান্ডা বা প্রচারণার দণ্ড:
২১। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রপাগান্ডা ও প্রচারণা চালান বা উহাতে মদদ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১(এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা ৩(তিন) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
This post has already been read 21 times!