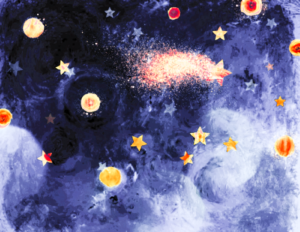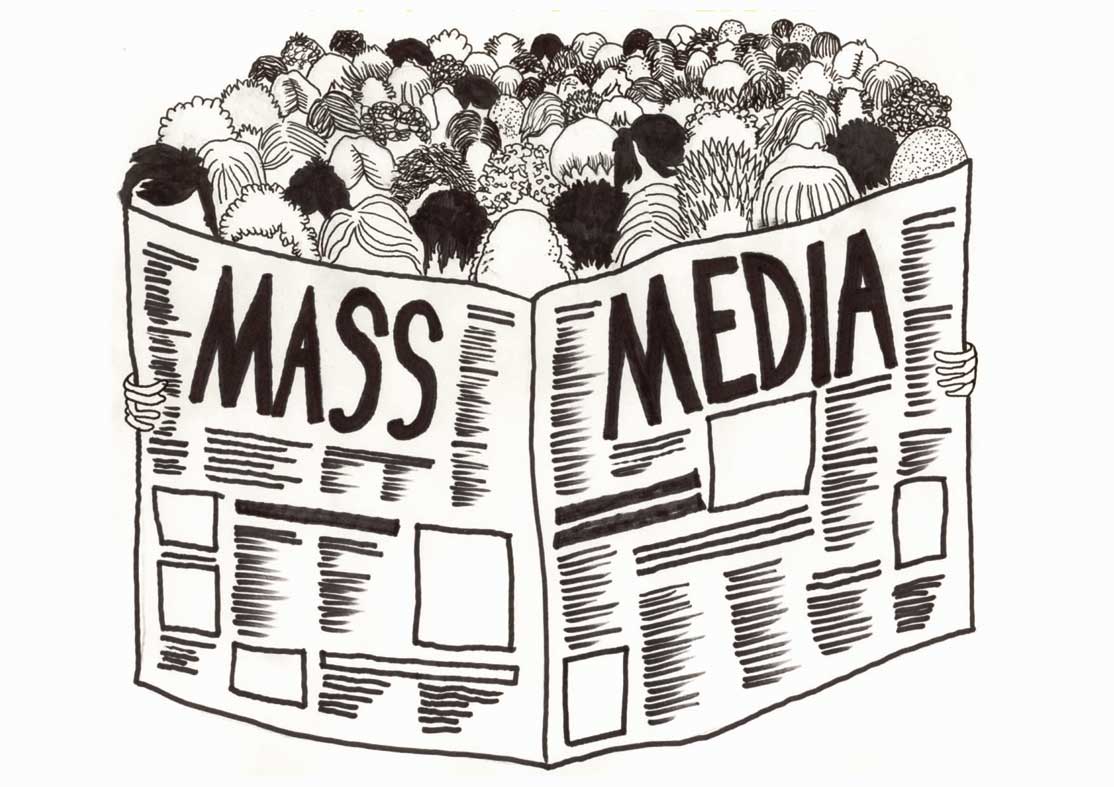
গণমাধ্যমগুলো কখন গণমাধ্যম
গণমাধ্যমগুলো আসলে গণমাধ্যম কি না, এই প্রশ্ন বাংলাদেশে এখন জোরেশোরে হলেও গণমাধ্যমে গণমানুষের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি আসলে নতুন কোনো আলোচনার বিষয় নয়। যোগাযোগবিজ্ঞানে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত অনেক আগেই হয়েছে; মীমাংসা হয়েছে, তা বলা যাবে না। ১৯৫৬ সালে ফ্রেড সিবার্ট, থিওডর পিটারসন ও উইবার শ্র্যাম ফোর থিওরিজ অব প্রেস নামে একটি বই প্রকাশ করেন। সেখানে তাঁরা দেখান, প্রেসের ভূমিকা এবং পরিচালনাকে চারটি তাত্ত্বিক মডেলে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে কর্তৃত্ববাদী, লিবারটারিয়ান, সামাজিক দায়িত্বশীল ও সোভিয়েত মডেল।
গণমাধ্যমের চার মডেল
কর্তৃত্ববাদী মডেলে গণমাধ্যমের মালিকানা ব্যক্তি ও রাষ্ট্র—দুই খাতে থাকলেও এর ভূমিকা একই রকমের। এদের দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকদের ‘শিক্ষিত’ করা এবং সরকারের প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করা; উদ্দেশ্য স্থিতাবস্থা বহাল রাখা। লিবারটারিয়ান মডেলে গণমাধ্যম নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করবে, মালিকানা থাকবে ব্যক্তি খাতে। গণমাধ্যমের কাজ হবে জানানো, বিনোদন দেওয়া, (পণ্য) বিক্রি করা, ওয়াচডগ হিসেবে নজরদারি করা এবং সরকারকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা, অর্থাৎ তার বাড়াবাড়ির দিকে নজর রাখা। সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি থিওরি বা সামাজিক দায়িত্বশীল গণমাধ্যম পরিস্থিতি হচ্ছে রাষ্ট্রের সব ধরনের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে খবর প্রকাশ করা। গণমাধ্যমে সবার প্রবেশযোগ্যতা থাকার পক্ষে নয় এই তত্ত্ব। গণমাধ্যম ব্যক্তি খাতেই থাকবে কিন্তু এটি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে কিছু মানগত স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে। এই তত্ত্বের কথা হচ্ছে যে গণমাধ্যমের একটি নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে জানানো। গণমাধ্যম উঁচু পেশাগত মান বজায় রাখবে এবং সত্যতা ও নির্ভুলতার নিশ্চয়তা বিধান করবে।
সোভিয়েত মডেলের প্রধান বিষয় হচ্ছে, গণমাধ্যম সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং তার কাজ হচ্ছে স্থিতাবস্থা বদলের লক্ষ্যে কাজ করা, স্থিতাবস্থা বদল মানে হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের নির্ধারিত ‘জনকল্যাণমূলক’ কাজের বাস্তবায়নের পথে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের এই লক্ষ্যে পরিচালিত করা। গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব থাকবে গুটিকয় মানুষের হাতে, যাঁরা দলের হয়ে এই নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখবেন। গণমাধ্যম কী প্রচার করবে না করবে, সেটাও তাঁরা নির্ধারণ করবেন।
গণমাধ্যম কার স্বার্থ দেখে
এই চার তত্ত্বের আলোকে কোন ধরনের গণমাধ্যম প্রকৃতপক্ষে জনগণের কথা বলতে পারে, কোন ব্যবস্থায় কোন মাধ্যমকে জনগণের কণ্ঠস্বর বলে কে বিবেচনা করবে, সেটা নির্ভর করছে ওই ব্যক্তির রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর। কিন্তু এসব তত্ত্বের পরও যা আলোচনার বিষয় তা হলো, যখন গণমাধ্যম ব্যক্তিমালিকানায় থাকে, তখন এটি কার স্বার্থ দেখে। অনেক গবেষক দেখালেন, আসলে পুঁজির স্বার্থ দেখাই হচ্ছে গণমাধ্যমের কাজ। এই ধারা গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি গবেষণার যে ধারা, তাকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এই ধারার গবেষকেরা গণমাধ্যমের কনটেন্ট এবং মালিকানা বিষয়ে গবেষণা করে দেখালেন, এমনকি লিবারটারিয়ান এবং সামাজিক দায়িত্বশীল গণমাধ্যমব্যবস্থায়ও গণমাধ্যম কার্যত সবার কথা বলে না। এগুলো সবার কাছে পৌঁছে যাওয়ার অর্থে গণমাধ্যম হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলার মাধ্যম নয়, তাঁদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। আরমান্দ মাতেলা ও সেথ সিগেলেবের সম্পাদিত গ্রন্থ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ক্লাস স্ট্রাগল (দুই খণ্ড, ১৯৭৯) এ বিষয়ে আলোচনাকে শক্তিশালী করে। এই ধারার আরও অনেক গবেষক আছেন, যাঁদের মধ্যে হার্বার্ট শিলার, রবার্ট ম্যাকচিসনির কথা বলতে পারি, নোয়াম চমস্কি ও অ্যাডওয়ার্ড হারমানের লেখা ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট (১৯৮৮) অন্যতম উদাহরণ।
গণমাধ্যমে কোন খবর আসে?
গণমাধ্যমগুলো যে খবর দিচ্ছে, যে মত প্রকাশ করছে, সেগুলো বিভিন্নভাবে ফিল্টার হয়। কিন্তু এর মধ্যে দুটো ফিল্টার গুরুত্বপূর্ণ—গণমাধ্যমগুলোর আদর্শিক অবস্থান এবং কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এগুলো চালু থাকছে। গণমাধ্যমের মালিক কে বা কারা, সেটা একটা বড় বিষয়। কিন্তু এখানে বিরাজমান রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেক। গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোচনায় এটাও উঠে এল যে রাষ্ট্র আইনকানুন করে কনটেন্টের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে; আবার কখনো কখনো সেটার দরকার হয় না। কেননা, গণমাধ্যমের মালিক বা পরিচালকেরাই এমন সিদ্ধান্ত নেন, যা ওই আইনের দ্বারা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। গণমাধ্যমের জনগণের মাধ্যম হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে জটিল বিষয়টি উপস্থিত থাকে, তা হচ্ছে পুঁজি, মালিকানার ধরন এবং রাষ্ট্রের জটিল সম্পর্ক; সেটাই নির্ধারণ করে গণমাধ্যম কার কথা বলবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই এই সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।
কীভাবে এই সম্পর্ক কাজ করে, তার বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ আছে। যেমন ধরুন ২০০৩ সালে অধিকাংশ মার্কিন গণমাধ্যম ইরাক যুদ্ধের পক্ষে দামামা বাজিয়েছে, যখন তাদের উচিত ছিল এটা অনুসন্ধান করা যে জর্জ বুশ প্রশাসন ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র থাকার যে কথা বলছে, সেটা আদৌ ঠিক কি না। অথচ সে সময় খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে। গণমাধ্যমের একটা বড় অংশই সে সময় প্রশাসনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেছে। কেননা, তারা আদর্শিকভাবে এটাকে যথাযথ বলে মনে করেছে। আরও পুরোনো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত গ্লাসগো মিডিয়া স্কুলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—ব্যাড নিউজ, মোর ব্যাড নিউজ ও রিয়েলি ব্যাড নিউজ। এগুলোতে গবেষকেরা দেখিয়েছেন, ব্রিটেনের টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদে পক্ষপাতিত্ব কতটা স্পষ্ট, মিডিয়া খনিশ্রমিকদের আন্দোলনের সময় সরকারের অবস্থানকেই সমর্থন করেছে। এই ধরনের গবেষণা প্রমাণ করে যে গণমাধ্যম সব সময়ই যে জনসাধারণের সব কথাই বলে, তা নয়।
গণমাধ্যম কি কেবল সেই সব খবরই প্রকাশ করে, যা পুঁজি ও পুঁজিমালিকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট? না, তা নয়। গণমাধ্যমকে প্রাসঙ্গিক, বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য থাকতে হয় অন্তত পক্ষে দুটো কারণে—প্রথমত, এই আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থা যেন অব্যাহত রাখা যায়, তার জন্য মানসিক অবস্থা তৈরি করা; যাতে বিরাজমান ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এই ব্যবস্থার সঙ্গে গণমাধ্যমের স্বার্থ যুক্ত। দ্বিতীয়ত, একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের দ্বারা পরিচালিত গণমাধ্যম, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ব্যবস্থাটার খোলনলচে বদলে দেওয়া, তারা ব্যতিক্রম।
নির্ভরযোগ্যতা, আস্থা ও বস্তুনিষ্ঠতা
প্রচলিত রাষ্ট্রকাঠামো হচ্ছে এই ব্যবস্থার রক্ষক। তার মানে গণমাধ্যম ও রাষ্ট্র একই উদ্দেশ্যে কাজ করছে। এই বিবেচনা থেকে লুই আলথুসার গণমাধ্যমকে বলেছেন ‘রাষ্ট্রের আদর্শিক হাতিয়ার’। গণমাধ্যম সেভাবেই সমাজে গণ-আলোচনার সূচি বা পাবলিক অ্যাজেন্ডা তৈরি করে। আমরা কী নিয়ে ভাবব, সেটাই ঠিক করে দেয় গণমাধ্যম। কিন্তু গণমাধ্যম যা বলে, তার সবটাই যেভাবে চায় আমরা সেভাবে গ্রহণ করি? কালচারাল স্টাডিজের পুরোধা স্টুয়ার্ট হল দেখিয়েছেন তিনভাবে গণমাধ্যমের বার্তা গ্রহণ করা হয়—এর একটি হচ্ছে গণমাধ্যম যেভাবে চায় সেইভাবে; একটি হচ্ছে খানিকটা আপসরফা করে, মানে খানিকটা গণমাধ্যমের পছন্দের, খানিকটা নিজের; আর হচ্ছে একেবারে উল্টোভাবে। ফলে ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য গণমাধ্যম ভোক্তাকে যা এবং যেভাবে দিচ্ছে, ভোক্তারা সবটাই সেইভাবে গ্রহণ করছেন, এমন মনে করার কারণ নেই। গণমাধ্যমকে তাই এমনভাবে দিতে হয়, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।
দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, গণমাধ্যমকে এমন পণ্য তৈরি করতে হয়, যা তারা বিক্রি করতে পারে। তথ্যই হচ্ছে তার পণ্য। বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের কারণেই গণমাধ্যমকে সততার সঙ্গে তুলে ধরতে হয় ঘটনা কী ঘটেছে। সবটাই সব সময় তুলে ধরছে, তা নয়, যেটাকে গণমাধ্যম মনে করছে গুরুত্বপূর্ণ, সেটাকে তুলে ধরছে, বাছাই করেই দিচ্ছে। এটাই হচ্ছে গেটকিপিং। এতে গণমাধ্যমকে এমনভাবে বলতে হয়, যা সত্যের অপলাপ নয়। কেননা, তাহলে তা ভোক্তারা গ্রহণ করবেন না। এটা নিশ্চিত করার উপায় হচ্ছে কতগুলো মান বজায় রাখা। কয়েক শ বছর ধরে গণমাধ্যমের ধারার মধ্যে এই মানগুলো তৈরি হয়েছে; এর উৎস হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ববোধ। তাকে অর্জন করতে হয় নির্ভরযোগ্যতা, আস্থা; নিশ্চিত করতে হয় বস্তুনিষ্ঠতা।
গণমাধ্যমের গণসংশ্লিষ্টতা
গণমাধ্যম আদর্শিকভাবে বিরাজমান ব্যবস্থার পক্ষে হলেও এই ব্যবস্থার অসংগতিগুলো তুলে ধরা, ক্ষমতাশালীদের জবাবদিহির মুখোমুখি করা এবং রাষ্ট্রের ওপর নজরদারি করা তার কাজ। ক্ষমতাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক জবাবদিহির মুখোমুখি করাই হচ্ছে গণমাধ্যমের দায়িত্ব। গণমাধ্যমকে যদিও বলা হচ্ছে রাষ্ট্রের আদর্শিক হাতিয়ার, কিন্তু তার অবস্থান হচ্ছে সিভিল সোসাইটিতে—রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের মাঝামাঝি। তার কাজ হচ্ছে তার ভোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা; কেবল ভোক্তা বলেই নয়, নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসেবেও। তথ্য জানা নাগরিকের অধিকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জবাবদিহি কেবল নির্বাচনের মধ্যে সীমিত নয়।
যেকোনো গণমাধ্যমের গণসংশ্লিষ্টতা বিচারের জন্য এগুলোকে মাপকাঠি বলে বিচার করতে হবে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো গণমাধ্যম কি না, সেই প্রশ্ন বিচারের জন্যও দরকার এই মাপকাঠিগুলোকে মাথায় রাখা। গণমাধ্যমে তথ্য হিসেবে যা পরিবেশিত হচ্ছে, তা নাগরিকদের এক বড় অংশের কাছে পৌঁছাচ্ছে, এই হিসেবে এগুলোকে গণমাধ্যম বলে বিবেচনা করতেই হবে। কিন্তু গেটকিপার হিসেবে কোন ধরনের তথ্য বাদ দিচ্ছে, সংবাদমূল্য বিবেচনায় বাদ দিচ্ছে, নাকি অন্য বিবেচনা কাজ করছে, কী বিষয়কে গণ-আলোচনার সূচি করছে, পেশাগতভাবে যে মানগুলো বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আছে—সত্যতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও প্রাসঙ্গিকতা, সেগুলো পালন করা হচ্ছে কি না, সেগুলো কার্যত নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। সেসব বিবেচনায়ই বাংলাদেশের এক বড়সংখ্যক গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ; এই দুর্বলতা এই মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্রমাগতভাবে দুর্বল করেছে। মনে রাখা দরকার, গণমাধ্যমের সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলার নামে সংবাদমূল্যহীন বিষয়কে উপস্থাপন করাই গণমাধ্যমের গণবিচ্ছিন্নতাকে আড়াল করতে পারে না।
গণমাধ্যম রাষ্ট্র ও রাজনীতির স্থিতাবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিংবা আদর্শিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে এটা সত্য কিন্তু গণমাধ্যমের নীতিনির্ধারক সম্পাদকেরা এই যুক্তিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে কিংবা দল, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নিরঙ্কুশভাবে সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন না। কেননা, বস্তুনিষ্ঠতা, সত্যতা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের মৌলিক শর্ত পূরণ করা ছাড়া, যার অন্যতম হচ্ছে ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহির মুখোমুখি করা, গণমাধ্যম কখনো গণমাধ্যম হয়ে ওঠে না; নাগরিকের মৌলিক যে অধিকার, সেটিকে পাশ কাটিয়ে গণমাধ্যম তার অন্য দায়িত্ব পালন করছে, এমন মনে করার কারণ নেই।
সাংবাদিকতার দায় কার কাছে, সাংবাদিকের দায়িত্ব কী
একটি গণমাধ্যমে প্রচারিত বা প্রকাশিত সব সংবাদের দায় কি ওই প্রতিষ্ঠানের সব সাংবাদিকের? এ প্রশ্ন আপাতদৃষ্টে খুব হাস্যকর বলে মনে হলেও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর বিষয়ে বিতর্কে প্রায়ই প্রশ্নটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসে উপস্থিত হয়। অনেকেই কোনো গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার সময় এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন যে ওই প্রতিষ্ঠানের সব সাংবাদিকই এ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দায়ী। অন্ততপক্ষে তাঁদের উচিত এই ইচ্ছাকৃত বা নীতিবিষয়ক ত্রুটির কারণে অবিলম্বে পদত্যাগ করা। এ ধরনের বক্তব্য খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে, কেননা এতে দায় অনেকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এ ধরনের বক্তব্য না বাস্তবসম্মত, না সাংবাদিকতার কোনো রকমের নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ ধরনের কথাবার্তা স্বল্প মেয়াদে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেও এর সঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংশ্লিষ্ট, সে বিষয়ে আলোচনার কোনো ধারা এখনো গড়ে ওঠেনি। তা হচ্ছে সাংবাদিকতার দায় কী, কার কাছে এ দায়, সাংবাদিকের দায়িত্ব কী?
সাংবাদিকতার জগতের তিন ধরনের মানুষ
সাংবাদিক বললে গণমাধ্যমে সংশ্লিষ্ট একাধিক ধরনের পদাধিকারী ব্যক্তিদের বোঝায়। মোটা রেখায় আমরা সাংবাদিকতার জগতের তিন ধরনের মানুষের কথা বিবেচনা করতে পারি, যাঁরা তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের উপস্থাপনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁরা হচ্ছেন প্রতিবেদক; সংবাদের গুরুত্ব ও স্থান নির্ধারণ করেন যাঁরা এবং যাঁরা প্রতিবেদন সম্পাদনা করেন—ডেস্কে কর্মরত সহসম্পাদক থেকে বার্তা সম্পাদক এবং সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিরা।
সাংবাদিকতার জগৎ বিষয়ে অবগত ব্যক্তিরা জানেন, এই তিন ধরনের সাংবাদিকের মধ্যে প্রতিবেদকদের পরিচিতি বেশি এ কারণে যে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ; তাঁরাই বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো তাঁদের বিবেচনায় যথাযথভাবে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু একটি আদর্শ গণমাধ্যমে তাঁরা এ সিদ্ধান্ত নেন না যে তাঁদের সংগৃহীত খবর আদৌ প্রচারিত হবে কি না, কখন ও কীভাবে প্রচারিত হবে। অন্যদিকে, সংবাদ প্রতিষ্ঠানে যাঁরা গেটকিপারের দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন কোন খবর প্রকাশিত হবে বা হবে না। এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন, অবস্থানগতভাবে তাঁদের মধ্যে দায়িত্বের বণ্টন হয়। একজন বার্তা সম্পাদক বা তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কোন খবর প্রকাশিত হবে, কীভাবে হবে। সংবাদ বিভাগের অন্য কেউ এ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সম্পাদকীয় বিভাগে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা প্রাত্যহিক সংবাদ পরিবেশনা বিষয়ে অবগত থাকেন না; গণমাধ্যমের নীতি অনুযায়ী তাঁরা উপসম্পাদকীয় লেখেন বা মতামত প্রকাশ করেন, সম্পাদকীয় নীতিমালা তৈরিতে অবদান রাখেন।
দায়িত্বের এই বণ্টন থেকে বোঝা যায়, প্রকাশিত সংবাদ এবং মতামত সবার জ্ঞাতসারে প্রকাশিত হয় না, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সবার অংশগ্রহণ থাকে না। ফলে, একটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের তথ্য, তার গুরুত্ব বা প্রকাশিত মতের দায়িত্বও সবার ওপরে বর্তায় না। সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যত্যয় বা বিচ্যুতির দায় যাঁরা ওই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত—প্রতিবেদক থেকে সম্পাদক এবং যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, তাঁদের। এই বিচ্যুতি যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমের নীতির প্রতিফলন ঘটায়, তবে ওই গণমাধ্যমের নীতিগত অবস্থানের সমালোচনা করা দরকার, সেই নীতিনির্ধারকদের সমালোচনার মুখোমুখি করা দরকার। যেকোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি-ব্যত্যয় বা নীতিগত অবস্থানের জন্য কোনো গণমাধ্যমের সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের অর্থ হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যুক্ত ব্যক্তিদের দায়মুক্ত করা।
কিন্তু সাংবাদিকতার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত—প্রতিবেদক থেকে সম্পাদক—তাঁদের অবশ্যই কতগুলো মৌলিক দায়িত্ব আছে, যেগুলো এড়িয়ে গিয়ে সাংবাদিকতা করা সম্ভব নয়; অন্যার্থে সাংবাদিকতার নীতিমালার ভিত্তিগত কিছু বিষয় আছে, যা সর্বজনীন এবং দায়িত্বনির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। সাংবাদিকতার প্রথম বাধ্যবাধকতা বা দায়িত্ব হচ্ছে সত্যের প্রতি। সাংবাদিকতার এই সত্য দর্শনশাস্ত্রের সত্য নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের চূড়ান্ত সত্য নয়। বিল কোভাচ ও টম রোসেন্টিয়েল দ্য এলিমেন্টস অব জার্নালিজম গ্রন্থে একে বলেছেন ‘আ প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড ফাংশনাল ফর্ম অব ট্রুথ’—বাস্তব এবং কার্যকর সত্য। এ সত্যের ভিত্তি হচ্ছে পেশাদারিভাবে তথ্য-উপাত্ত ও ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ এবং তা যাচাই করা।
সাংবাদিকতা আসলে কেবল তথ্য-উপাত্ত ও ঘটনার বিবরণ সংগ্রহের পেশা নয়; এটির ভিত্তি হচ্ছে তথ্য যাচাই করাও। ইংরেজিতে যাকে বলে ভেরিফিকেশন, একে আমরা সত্য প্রতিপাদন বলে বর্ণনা করতে পারি। এই ভেরিফিকেশনের কি কোনো সুনির্দিষ্ট সূত্র আছে? অবশ্যই তা নেই। একেক সময়ে একেকভাবে ভেরিফাই করতে হবে। কিন্তু যা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে অনুসৃত পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ কি না। প্রতিবেদক কিংবা সম্পাদনায় যুক্তরা ব্যক্তি হিসেবে বস্তুনিষ্ঠ হবেন, এমন আশা করা যায় না, কিন্তু তথ্য বা ফ্যাক্টস সংগ্রহের ও উপস্থাপনার পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন। এই যাচাই-বাছাই বা ভেরিফিকেশনকে বিল কোভাচ ও টম রোসেন্টিয়েল বলছেন সাংবাদিকতার ‘এসেন্স’—সারমর্ম। আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউট বলছে, এটাই সাংবাদিকতাকে প্রোপাগান্ডা, বিজ্ঞাপন, ফিকশন বা বিনোদন থেকে আলাদা করে। এ তালিকায় জনসংযোগকেও যুক্ত করা যায়। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার বর্তমান অবস্থায়—কেবল আলাদা আলাদা প্রতিবেদনের বিষয়ে নয়, সামগ্রিকভাবে যদি আমরা বিবেচনা করি, তবে এই ভেরিফিকেশনের কী উদাহরণ দেখতে পাই? গণমাধ্যম তথ্য প্রকাশে যতটা আগ্রহী, ভেরিফিকেশনে ততটা নয়। দুই বা বহু পক্ষের বক্তব্য দেওয়া ভেরিফিকেশন নয়। একইভাবে সাংবাদিকতার একটা কাজ হচ্ছে যেকোনো আলোচনায় কেবল আরেকটা কণ্ঠস্বর যুক্ত করা নয়, আলোচনার মানোন্নয়ন; সেটা সংবাদেই হোক কিংবা সম্পাদকীয়তে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রবণতা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অনেক সময় অনেক অজানা বিষয়কে আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপন করে, গণমাধ্যমে আসে না—এমন অনেক বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মুহূর্তের মধ্যে কোনো বিষয়কে সবার অবগতির ব্যবস্থা করে, নিয়ন্ত্রণমুক্তভাবে পরিস্থিতি প্রচার করে, বিভিন্ন ধরনের মতপ্রকাশের সুযোগ করে দেয়—এগুলোকে অস্বীকার করা যাবে না। তারপরও একসময় যে সামাজিক মাধ্যম ছিল বিভিন্ন ধরনের স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রচারের ও সংগঠিত হওয়ার হাতিয়ার, তা এখন স্বৈরাচারীদের ব্যবহারের উপাদানে পরিণত হয়েছে। গোষ্ঠীস্বার্থ এবং অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ঘটনাও ঘটছে—ফেক নিউজ প্রপঞ্চের ভিত্তি হচ্ছে এটাই। যে কারণে সোশ্যাল মিডিয়ার শক্তি সত্ত্বেও এগুলোকে ‘সাংবাদিকতা’ বলার বিবিধ রকমের বিপদ আছে।
আজকের দিনে যখন আমরা ‘অলটারনেটিভ ফ্যাক্টস’ এবং ‘পোস্ট ট্রুথ’-এর কল্পিত এক জগতে বাস করছি এবং যে পোস্ট ট্রুথের অর্থ হচ্ছে মানুষ আসল ঘটনা বা সত্যের বদলে তাদের আবেগ ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে কোনো একটি যুক্তিকে গ্রহণ করে নিচ্ছে, সেই সময়ে সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয়ের দিকেই আগে তাকাতে হবে। ফ্যাক্টস সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা একজন রিপোর্টারের প্রথম কাজ। কী ছাপা হবে, কী প্রচারিত হবে, সেই সিদ্ধান্তের কথা বিবেচনা না করেই তাঁকে এই ফ্যাক্টস সংগ্রহ করতে হবে, লিখতে হবে। অন্যদিকে, সম্পাদনার দায়িত্ব যিনি আছেন—প্রধান প্রতিবেদক থেকে সম্পাদক পর্যন্ত সবাইকে মনে রাখতে হবে, এর ব্যত্যয় মানে সাংবাদিকতা নয়। এই ফ্যাক্টসের বিষয়ে স্বচ্ছতাও দরকার; কোন সূত্র এ তথ্য দিচ্ছে, কীভাবে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, যাতে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকেরা বুঝতে পারেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু। বাংলাদেশে প্রায়ই সরকারি ভাষ্যকে এমনভাবে প্রচার করা হয়, যেন সেটাই খবর।
সাংবাদিকতার দায়
সাংবাদিকতার দায় একমাত্র জনসাধারণের কাছে; এমনকি যখন এই সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তি এবং সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায়। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের একমাত্র উপায় এই দায়ের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া। আর তার জন্যই সাংবাদিকতাকে থাকতে হয় স্বাধীন; নিরপেক্ষতাই যথেষ্ট নয়। এই স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে সাংবাদিকতাকে পেশা ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং সাংবাদিককে ব্যক্তি হিসেবে যাঁদের বিষয়ে সংবাদ বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করবে, তাঁদের থেকে স্বাধীন থাকতে হবে; কেবল তবেই গণমাধ্যম ওয়াচডগের ভূমিকা পালন করতে পারবে।
বাংলাদেশের সাংবাদিকতার বিবেচনায় এই কথাগুলো কেবল তত্ত্বগতভাবে বলে উড়িয়ে দেওয়ার মতো মানুষের অভাব হবে না। কিন্তু সাংবাদিকতার এই মৌলিক বিষয়গুলোকে ধর্তব্যে না নিয়ে, এসব দিকে মনোযোগ না দিয়ে ঘটনার প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে, সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলে ফলোদয় হবে তা নয়। গত ৫০ বছরে বিশেষ করে গত তিন দশকে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় সাংবাদিকতার জগৎ থেকে এসব মৌলিক নীতিমালাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে।
প্রথমত, সাংবাদিকতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এটি এক বা একাধিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার বিষয় নয়। সাংবাদিকতাই যে একটি প্রতিষ্ঠান, সেই ধারণা স্বাধীনতার আগে যেভাবে বিকশিত হচ্ছিল, তা স্বাধীনতার পরে ক্রমাগতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এমনকি ১৯৮২-১৯৯০ পর্যায়েও সাংবাদিকতার সেই সম্ভাবনা বিরাজ করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৯০ সালের পরে সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকেনি।
দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকতা এবং সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কার্যকর ট্রেড ইউনিয়নের অভাব। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো দলীয় ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে এবং তাতে ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিকদের লাভবান হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে, কিন্তু সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয়গুলোর চর্চা অবসিত হয়েছে।
তৃতীয়ত, বাংলাদেশের গণমাধ্যমের মালিকানার কাঠামোয় পরিবর্তন। ব্যক্তি খাতের বিকাশের ফলে গণমাধ্যমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু মালিকানার ধরন পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে গণমাধ্যমগুলো নিজেই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠছে অন্যান্য ব্যবসার স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার।
গণমাধ্যমের কে মালিক, কীভাবে মালিক
বাংলাদেশে গণমাধ্যমবিষয়ক আলোচনার ধারা অত্যন্ত দুর্বল, এর মধ্যে গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতিবিষয়ক আলোচনা প্রায় অনুপস্থিত। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পাঠ্যক্রমে এই বিষয়ের তাত্ত্বিক দিক যতটা আলোচিত হয়, ইম্পিরিক্যাল বা বাস্তবে বিরাজমান অবস্থার তথ্যনির্ভর গবেষণা ততটা হয় না। হলেও সেগুলো সহজে লভ্য নয়। যে কারণে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের মালিকানাবিষয়ক আলোচনার কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ নেই। গণমাধ্যমের মালিকানা নিয়ে অনেক বিষয় সর্বজনবিদিত, আড্ডায়-আলাপচারিতায় বহুলভাবে চর্চিত; কিন্তু সেগুলো প্রামাণিক নয়। সাম্প্রতিককালে ঘটনা পরম্পরায় গণমাধ্যমের মালিকানার বিষয় আলোচিত হচ্ছে, যা খানিকটা সাধারণ জ্ঞাননির্ভর, অনেক ক্ষেত্রেই সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজের (সিজিএস) পৃষ্ঠপোষকতায় করা একটি গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য আংশিকভাবে, ক্ষেত্রবিশেষে ভুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেকেই তথ্যের উৎসের স্বীকৃতি পর্যন্ত দিচ্ছেন না।
বহুদলীয় রাজনীতি এবং উন্মুক্ত অর্থনীতিতে যে তিন ধরনের গণমাধ্যম থাকে: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং রাজনৈতিক দলের মালিকানাধীন বা পরোক্ষ সমর্থনপুষ্ট—বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনা থেকেই সেগুলো ছিল। তবে ১৯৯৭ সালে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রথম টেলিভিশন চ্যানেল এবং ১৯৯৮ সালে কমিউনিটি রেডিও চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন গণমাধ্যম বলতে কেবল মুদ্রিত সংবাদপত্র ও সাময়িকীই ছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সরকারি এক হিসাবে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৩০, অর্ধ সাপ্তাহিকের সংখ্যা ৩ এবং সাপ্তাহিকের সংখ্যা ১৫১। ১৯৭৫ সালে একদলীয় ব্যবস্থা চালু করে জানুয়ারি মাসে জাতীয় দৈনিকের সংখ্যা চারটিতে নামিয়ে আনা হয় এবং তা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। এই ব্যবস্থা ছিল স্বল্পমেয়াদি। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমের মধ্যে টেলিভিশন এবং রেডিও থাকলেও এবং সেগুলোর একচেটিয়া উপস্থিতি সত্ত্বেও এগুলো কখনোই সংবাদমাধ্যম হিসেবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো কোনো দৈনিক ও সাপ্তাহিকের জনপ্রিয়তা ছিল, সীমিত আকারে হলেও সেগুলো বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল। একদলীয়ভাবে পরিচালিত দেশ ছাড়া পৃথিবীর কোথাও দলীয়ভাবে প্রকাশিত বা সমর্থনপুষ্ট গণমাধ্যম সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবের কারণে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকটের সময় নাগরিকেরা বিদেশি গণমাধ্যমের ওপর আস্থা রাখেন।
গণমাধ্যমের সংখ্যা বৃদ্ধির রাজনৈতিক অর্থনীতি
১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিভিশনকে ‘সাহেব-বিবির বাক্স’ বলেই অভিহিত করা হতো। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যম মাত্রই বিশ্বাসযোগ্যতার সংকটে থাকবে, তা নয়। ব্রিটেনে বিবিসি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত পাবলিক ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের আওতায় রেডিও এবং টেলিভিশন দুই-ই আছে; সেগুলো সাহেব-বিবির বাক্স নয়। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগুলো সাংবাদিকতার নীতিমালা দিয়ে পরিচালিত। ১৯৯০ সালের গণ-আন্দোলনের সময় সব রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতি ছিল, অন্ততপক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন বিবিসির আদলে গড়ে তোলা হবে। কিন্তু অবস্থার আরও অবনতিই হয়েছে।
তবে ১৯৯০ সালের পর ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের ব্যক্তিমালিকানার সূচনা হয়েছে; প্রথমে টেলিভিশন এবং পরে রেডিও চালু হয়েছে; সংখ্যা বেড়েছে। একটি হিসাবে দেশে মোট টেলিভিশন চ্যানেল ৪৫টি, ২৮টি এফএম এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও, ১ হাজার ২৪৮টি দৈনিক পত্রিকা এবং কমপক্ষে ১০০টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল। ১৯৯০ সালের পর গণমাধ্যমের সংখ্যার এই বৃদ্ধির রাজনৈতিক অর্থনীতি, বিশেষ করে এগুলোর মালিকানার দিক বোঝার জন্য এই সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শাসনের কয়েকটি দিক উল্লেখ করা দরকার।
অর্থনীতির প্রাসঙ্গিক দিকটি হচ্ছে, এই সময়ে বাংলাদেশ এক নতুন ধনিক শ্রেণির বিস্তার ঘটেছে; এর সূচনা হয়েছিল সেনাশাসনের আওতায় ১৯৮০-এর দশক থেকেই। কিন্তু তা ব্যাপক রূপ নিয়েছে ১৯৯০-এর পরে। রাষ্ট্রীয় পরিপোষণে এই শ্রেণি বেড়ে উঠেছে। অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ যথার্থই বলেছেন যে গত ৪৭ বছরে বাংলাদেশে তিন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এক লুটেরা শ্রেণি, ‘লুম্পেন কোটিপতি’ শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে। ‘প্রথম পর্বে ছিল লাইসেন্স, পারমিট, চোরাচালানি, মজুতদারি, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানা, সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বে এর সঙ্গে যোগ হয় ব্যাংকঋণ ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকানা লাভ।’ তৃতীয় পর্বে, ‘পুরো ব্যাংক খেয়ে ফেলা, …এমনকি সর্বজনের সব সম্পদই এখন বাংলাদেশে এই শ্রেণির কামনা-বাসনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে’ (‘লুম্পেন কোটিপতিদের উত্থানপর্ব’, প্রথম আলো ২৮ মার্চ ২০১৮)। এই শ্রেণির মানুষেরাই গণমাধ্যম খাতে বিনিয়োগ করেছেন। এই শ্রেণি একসময় রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে গড়ে উঠলেও অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান মনে করেন, তাঁদের বিকাশের ধারা এমন হয়েছে যে তাঁরা এখন রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণের জায়গায় পৌঁছেছেন; তাঁর ভাষায়, ‘ফ্রম ডিপেনডেন্স অন স্টেট টু স্টেট ক্যাপচার’ (দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তাকে অর্থনীতিবিদ মির্জা হাসান বর্ণনা করেছেন পার্টিয়ার্কি বলে (পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট ডাইনামিকস ইন অ্যা লিমিটেড এক্সেস অর্ডার-দ্য কেইস অব বাংলাদেশ, ২০১৩); সহজ ভাষায় যাকে আমরা সর্বভুক দলবাজি বলেই চিহ্নিত করতে পারি। কেবল সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রেই তা ঘটছে তা নয়, এমনকি সিভিল সোসাইটির ভেতরে তা বিষের মতো ঢুকে পড়েছে। পরিণতি হয়েছে সিভিল সোসাইটির সংগঠন, এমনকি সাংবাদিক ইউনিয়ন পর্যন্ত দলের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের গণতন্ত্র উল্টো পথে যাত্রা করেছে। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে যে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুষ্ঠু প্রক্রিয়া হিসেবে নির্বাচনী ব্যবস্থা দাঁড়ায়নি, তা কমবেশি সবাই স্বীকার করেন। সম্প্রতি রেহমান সোবহানও বলেছেন যে ২০০৮ সালের পর বাংলাদেশে আর কোনো নির্বাচন হয়নি, যাকে সুষ্ঠু নির্বাচন বলে স্বীকার করা যায় (প্রথম আলো, ৪ মার্চ, ২০২১)। অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে একটি জবাবদিহিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।
গণমাধ্যমের মালিকানা
এই দুই প্রেক্ষাপটে কারা গণমাধ্যমের মালিক হয়েছেন, তা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এন্ডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসির অর্থানুকূল্যে সিজিএসের পৃষ্ঠপোষকতায় আমি এবং মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান অক্টোবর ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত একটি সমীক্ষা চালিয়েছি। ২০২১ সালে জানুয়ারি মাসে ‘হু ওউনস দ্য মিডিয়া ইন বাংলাদেশ’ নামে তা প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে করা গবেষণায় আমরা দেখতে পাই, ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ঠ না হয়ে গণমাধ্যমের, বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ সালে বিভিন্ন সরকারের সময়ে দেওয়া টেলিভিশন চ্যানেলের অনাপত্তিপত্রের হিসাবেই তা স্পষ্ট। ১৯৯৬-২০০১ সালে অনাপত্তি দেওয়া হয়েছে ৪টি, ২০০১ থেকে ২০০৮ সালে দেওয়া হয়েছে ৫টি, ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালে দেওয়া হয়েছে ২৯টি এবং ২০১৪-২০১৮ সালে দেওয়া হয়েছে ৭টি। ২০০৮ সালের পর বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা যতই জবাবদিহিহীন হয়েছে, লাইসেন্স দেওয়ার হার ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালের অক্টোবরে ১০টি লাইসেন্সের অনুমোদনের ঘটনাও ঘটেছে।
আমাদের এই গবেষণায় আমরা ৪৮টি গণমাধ্যম আউটলেট, অর্থাৎ সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও এবং ওয়েব পোর্টালের মালিকানা বিশ্লেষণ করে যে তিনটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ করেছি, তার একটি হচ্ছে মালিকদের ক্ষমতাসীন দলের সংশ্লিষ্টতা। এই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণেই প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বদল হয়েছে ক্ষমতা বদলের পর। গত ১২ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাই যে এখন গণমাধ্যমের এক বড় অংশের মালিক তা সহজেই দৃশ্যমান হয়েছে। এসবের মালিক হচ্ছে ৩২টি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, দেখা গেছে যে এসব গণমাধ্যমের পরিচালকদের এক বড় অংশই হচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা; অর্থাৎ একই পরিবারের সদস্যরা একই গণমাধ্যমের পরিচালক বোর্ডের সদস্য; মালিকানার এক বৃত্তচক্র। যেকোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিক হলেও গণমাধ্যমের দায়দায়িত্ব বিবেচনায় তা কতটা এমন প্রতিষ্ঠানের নিজস্বতা বজায়ের জন্য অনুকূল, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। আমরা এ-ও দেখতে পাই যে যৌথ মূলধনি কোম্পানিতে যেসব তথ্য নিয়মিতভাবে দেওয়ার কথা এবং যা সহজেই জনগণের কাছে লভ্য হওয়ার কথা, সেগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি আছে, নিয়মিতভাবে না দেওয়ার ঘটনাও আছে। এগুলো অস্বচ্ছতার লক্ষণ।
আমরা যে তৃতীয় বিষয়টি লক্ষ করেছি তা হচ্ছে, এসব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং মালিকেরা অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এটা মোটেই বিস্ময়কর বা উদ্বেগের বিষয় হতো না যদি এসব ব্যবসাক্ষেত্র গত এক দশকে বড় রকমের বিতর্কের সম্মুখীন হতো।
এই প্রবণতাগুলো থেকে মোটা দাগে যে কথাটি বলা যায়, সাংবাদিকতার একটি অন্যতম মৌলিক শর্ত পালনে এসব গণমাধ্যম ব্যর্থ হতে বাধ্য। সাংবাদিকতাকে পেশা ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং সাংবাদিককে ব্যক্তি হিসেবে যাঁদের বিষয়ে সংবাদ বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করবে, তাঁদের থেকে স্বাধীন থাকতে হবে; কেবল তবেই গণমাধ্যম ওয়াচডগের ভূমিকা পালন করতে পারবে। যাঁদের ওপরে নজরদারি করার কথা, সেই ক্ষমতাসীনদের অংশ হয়ে কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় শরিক হয়ে নজরদারি করা অসম্ভব। বরং এটাই স্বাভাবিক যে এই গণমাধ্যমগুলো সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে মালিকদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে এটা বোঝা দুরূহ নয়, কেন দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব গণমাধ্যমই তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। এ জন্য কেবল কে মালিক সেটা দেখাই যথেষ্ট নয়, নজর দিতে হবে লুটেরা অর্থনীতির বিকাশের নীতি এবং জবাবদিহিহীন রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার দিকে যেগুলো এ ধরনের গণমাধ্যমব্যবস্থা তৈরি করেছে।
স্বাধীন সাংবাদিকতার বাধা কারা
বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর, তথা সাংবাদিকতার, স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই; ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল, সাংবাদিক ও সিভিল সোসাইটির সদস্য, সাধারণ পাঠক, এমনকি রাজনৈতিক দলের সর্বনিম্ন পর্যায়ের কর্মী পর্যন্ত এই বিষয়ে একমত যে গণমাধ্যমের এবং নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা অবশ্যই দরকার। বাংলাদেশের সংবিধানে এই বিষয়ে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তা শর্তসাপেক্ষ এবং তা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের হাতে বেশুমার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার পরিধি অস্পষ্ট।
মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক আলোচনায় একটি বিষয় প্রায়শই উঠে আসে। এটা হলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমা থাকার প্রশ্ন। বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে যাঁরা যখনই ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরা দাবি করেন যে দেশে মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা আছে, এমনকি তা আগের চেয়ে অনেক বেশি; তবে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে তাঁরা এ-ও বলেন যে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবাধ হতে পারে না। এই দুইয়ের মধ্যে একটি বিরোধ আছে। এটা হয় তাঁরা উপলব্ধি করতে অপারগ অথবা সেটা স্বীকার করতে অনীহ। লক্ষণীয়, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমার বিষয়ে কেবল ক্ষমতাসীন এবং তাঁদের সমর্থকদেরই নয়; বাংলাদেশে, অন্য অনেক দেশেও, যাঁরা ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমাজজীবনে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাঁরাও একই রকম মনে করেন। তাঁদের একটি পার্থক্য হচ্ছে কোনো বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে সীমা থাকা দরকার, কিন্তু কখনো কখনো তাঁদের মধ্যে ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে গত চার-পাঁচ বছরে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সরকার এবং ইসলামপন্থী ও সামাজিক জীবনে ধর্মের ভূমিকায় বিশ্বাসীদের একধরনের ঐকমত্য লক্ষণীয়।
দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা কী এবং কোথা থেকে সেই বাধা আসে? ক্ষমতাসীন এবং তাঁদের সমর্থকদের ভাষ্য হচ্ছে, বাধাটি আসে রাষ্ট্রের বাইরে থেকে, তাঁরা বরং সেই বাধা মোকাবিলায় সবাইকে সাহায্য করছেন। রাষ্ট্রের আইন ও আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলাকেই তাঁরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অপব্যবহার বলে চিহ্নিত করেন।
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা
সাংবাদিকতার স্বাধীনতা বা ফ্রিডম অব প্রেস নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও এটি যে কোনো রকম বাধানিষেধ, এমনকি সরকারি সেন্সরশিপ ছাড়া যেকোনো নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতারই অংশ, সেই বিষয়ে কোনো রকমের ভিন্নমত নেই। যার অর্থ হচ্ছে, একটি দেশে নাগরিকের মতপ্রকাশের অধিকার যদি সংকুচিত হয়, তবে সেখানে গণমাধ্যম আলাদা করে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। সারা পৃথিবীতে মতপ্রকাশের অধিকার এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার ওপর নজর রাখে, এমন সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হিসাবে দেখাচ্ছে যে কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে সেই অধিকার সংকুচিত হয়েছে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের হিসাবে ২০২০ সালে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫২, যা আগের বছরের তুলনায় এক ধাপ পেছনে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য সব দেশের চেয়েও খারাপ। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাবেও বাংলাদেশে মতপ্রকাশের অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়েছে।
এই রকম একটা প্রেক্ষাপটেই যখন গণমাধ্যমের কোনো একটি বিশেষ সংবাদের অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে আলোচনাটি কার্যত অসম্পূর্ণই থাকছে। কেননা, আলোচনায় গণমাধ্যমের মালিকানার বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন এসব প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে ওঠা এবং রক্ষা করা কেবল বাণিজ্যিক বিষয়, যেন এগুলো স্বায়ত্তশাসিত এবং মালিকানার প্রশ্নটির সঙ্গে রাষ্ট্র ও সরকারের কোনো রকমের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকেরা যে এভাবেই বিষয়টি বিবেচনা করবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এ বছরের ৪ মে তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সিকে প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন যে গণমাধ্যমগুলোর মালিক হচ্ছেন করপোরেট হাউস, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদেরা। সেই জন্য সাংবাদিকেরা কথা বলা এবং লেখার স্বাধীনতা ভোগ করছেন না; তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী সরকারের কোনো ‘সেন্সরশিপ নেই’, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তিনি এ-ও বলেছেন যে যেহেতু সাংবাদিকদের চাকরি হারানোর ঝুঁকি থাকে, তাই এই অবস্থার সূচনা হয়েছে।
কিন্তু এই ধরনের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। কেননা, সারা বিশ্বে যেখানেই গণতন্ত্রের ক্ষয় হয়েছে, কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে দেশ অগ্রসর হয়েছে, সেখানে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের যেসব নতুন কৌশল বেছে নেওয়া হয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানাকে নিয়ন্ত্রণ করা। স্টিভেন লেভিটস্কি এবং লুকান ওয়ে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কর্তৃত্ববাদবিষয়ক বইয়ে উল্লেখ করেছেন, অনেক দেশে গণমাধ্যমের ওপর শাসকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তার পরিবর্তে ক্ষমতাসীনেরা বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন; তবে প্রচ্ছন্ন মালিকানা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং অন্যান্য অবৈধ উপায়ে প্রধান গণমাধ্যমগুলো শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
আইরিয়া পুয়োসা লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের কথা উল্লেখ করে গ্লোবাল আমেরিকান নামের এক সাময়িকীতে ২০১৯ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে লিখেছেন, ‘সরকারি তহবিলে (ভর্তুকি ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে) সহানুভূতিশীল গণমাধ্যম পরিচালিত হয়। একই সময়ে স্বাধীন এবং সমালোচনামূলক মাধ্যমগুলো কাগজ সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং ট্যাক্স আইনের চূড়ান্ত প্রয়োগসহ বিভিন্ন ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়।’ অনুগত সমর্থক এবং ব্যবসায়ীদের গণমাধ্যমের লাইসেন্স সরবরাহ করা হয়। আর বিরোধী এবং স্বতন্ত্র গণমাধ্যমগুলো যাবতীয় সমস্যার মুখোমুখি হয়। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আলী রীয়াজ, নিখোঁজ গণতন্ত্র, প্রথমা, ২০২১)।
এগুলো যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য, মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান এবং আমি এক গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছি। সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) পৃষ্ঠপোষকতায় অক্টোবর ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে করা সমীক্ষা ২০২১ সালে জানুয়ারি মাসে ‘হু ওউনস দ্য মিডিয়া ইন বাংলাদেশ’ নামে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে দেখা যায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমের মালিকদের দলীয় সংশ্লিষ্টতা সুস্পষ্ট।
‘দুঃস্বপ্নের বাস্তবতা’
গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পথে মালিকানার এই ধরন যে এক বিশাল বাধা, সেটি নিঃসন্দেহে বলা যায়; এই বিষয়ে ভিন্নমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এই মালিকানার ধরন বোঝার জন্য রাষ্ট্র এবং ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কিংবা ক্রমাগতভাবে গণতন্ত্রের পথ থেকে উল্টো যাত্রা যে এই পটভূমিকা তৈরি করে, তাকে এড়ানোর অর্থ মূল জায়গায় নজর না দেওয়া। এই ব্যবস্থাই গণমাধ্যমের পরাধীনতাকে লালন করে সেটা বিস্মৃত হওয়ার সুযোগ নেই, যদি না আমরা তাকে আড়াল করতে চাই।
গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সরকার এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা কেবল মালিকানা নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে কার্যকর হয় তা নয়। আইনি এবং আইনবহির্ভূতভাবে সরকার ও ক্ষমতাসীনেরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করেন। আমাদের গবেষণায় আমরা অন্ততপক্ষে কুড়িটি আইন শনাক্ত করেছি, যেগুলো গণমাধ্যমের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০১৮। এর আগে ২০১৩ সাল থেকে আইসিটি অ্যাক্ট, বিশেষ করে ৫৭ ধারা ব্যবহৃত হয়েছে। এই সব আইনের দুটি দিক আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। প্রথমত, এগুলো কেবল গণমাধ্যমের জন্যই প্রযোজ্য নয়। দুই আইনেরই পরিধি এতটাই ব্যাপক যে তা গোটা সমাজেই একটি ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছে। এই আইনের প্রয়োগ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তাকে সম্পাদক পরিষদ বলেছে ‘দুঃস্বপ্নের বাস্তবতা’ (প্রথম আলো, ২০ মে ২০২০)। এই আইনের প্রয়োগ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এ থেকে কারোরই রেহাই নেই (আলী রীয়াজ, ‘ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট কীভাবে প্রয়োগ হচ্ছে’, সিজিএস, এপ্রিল ২০২১)। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে আইন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে সরকার প্রত্যক্ষভাবে এই আইন ব্যবহার না করলেও তা এমনভাবে ব্যবহৃত হয়, যা ভিন্নমত প্রকাশের জন্য হুমকি হয়ে ওঠে। সরকার-সমর্থকেরা এইভাবেই এই আইনের ব্যবহার করছেন।
আইনের এই সব দিকের বাইরেও যে রাষ্ট্র যেকোনো ব্যক্তিকে ভীতিগ্রস্ত করতে পারে, তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে পারে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত বলার দরকার নেই। রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা কী ভূমিকা রাখছে, নাগরিকের সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলো যেসব প্রতিষ্ঠানের রক্ষা করার কথা, তারা কী করছে, সেটাও লক্ষ করা দরকার। আইনি ও আইনবহির্ভূত ব্যবস্থাদি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ বা সেলফ-সেন্সরশিপের প্রপঞ্চকে স্বাভাবিক করে তুলেছে।
জবাবদিহিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকের অন্যান্য অধিকার, বিশেষ করে মতপ্রকাশের অধিকার যখন সীমিত হয়ে যায়, তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আলাদাভাবে টিকে থাকে না; সাংবাদিকেরা আলাদা করে স্বাধীনতা ভোগ করবেন, এমন আশা করার কারণ নেই। ফলে স্বাধীন সাংবাদিকতার বাধাগুলোকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দরকার বিরাজমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শাসনের ধরন, তার রাজনৈতিক অর্থনীতি একত্রে বিবেচনা করা।
প্রথম আলো’তে প্রকাশিত, ২০ মে – ২৩ মে ২০২১