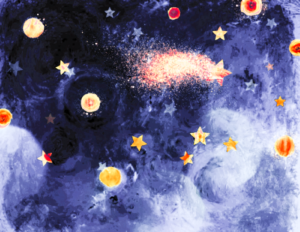Share the post "রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও অর্থনৈতিক ফলাফলঃ দ্বন্দ্ব্বমূলক বৈপরীত্যের সংশ্লেষ (১৯৭৬-৯০)"
১৯৭৫ থেকে ১৯৯০— বাংলাদেশের ঘটনাবহুল অস্থির রাজনৈতিক ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বৈপরীত্যের সংশ্লেষ। ১৯৭৫ সালে সহিংস পটপরিবর্তন হয়; অস্থিরতা বিরাজ করে, অনেকগুলো সামরিক ক্যু হয়, সামরিক শাসন শুরু হয়, কিছুদিন এমন অবস্থার পর বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে। একপর্যায়ে আরো একটি সহিংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং সামরিক শাসন জারি হয়। পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরুর মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।
অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বড় ধরনের বাঁকবদল ঘটে। এদিকে আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও কিছু উন্নয়নশীল দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যাপী উপনিবেশগুলো মুক্ত হয়ে নতুন যে রাষ্ট্রগুলো গঠিত হয়, তাদের কেউ ছিল জোটনিরপেক্ষতার পক্ষে, কেউ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী ছিল। আন্তর্জাতিক পরাশক্তি বা আঞ্চলিক শক্তি ওই দেশগুলোর ক্ষমতা পরিবর্তনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সঙ্গ নিয়েছে বড় রকমের অর্থনৈতিক পরিবর্তন। এ সময়ে রাজনীতির যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি আন্তর্জাতিক নীতি কাঠামোতেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়। অর্থশাস্ত্র ধাবিত হতে থাকে নতুন দিকে। এখানে গোটা প্রক্রিয়ার লক্ষ্যটাই ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বাজারমুখীন করা। এ তত্ত্বের আলোকেই নতুন একটি সংস্কার কাঠামো গঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী বাজারমুখীন রাজনীতিবিদদের প্রাধান্যের সঙ্গে যোগ হয় তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট। যেহেতু তেল সংকট দেখা দেয়, এ কারণে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোয় বৈদেশিক লেনদেনের স্থিতিতে বড় রকমের ঘাটতি দেখা দেয়। একদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন, অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে এক ধরনের অস্থিরতা; অর্থনীতির এ সংকটগুলো কাজে লাগিয়ে নতুন অর্থ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সংস্কার কাঠামো তৈরি করা হয়।
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তি এবং অর্থনীতির নেতৃত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের মাধ্যমে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম বা কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি নামে নতুন এ প্যাকেজটি চালু করে। আগে যে পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণ করা হতো বা প্রকল্প অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করা হতো, সে মৌলিক কাঠামোতে সংস্কার আনা। এ দেশগুলোর অর্থনৈতিক নীতিকাঠামোর মৌল সংস্কারই এ প্যাকেজের মূল লক্ষ্য ছিল। অর্থাৎ বাজারভিত্তিক সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বাজারের মাধ্যমেই সব কাজ পরিচালিত করা এবং রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সংকুচিত করা। বৈদেশিক লেনদেন স্থিতির সংকটে আক্রান্ত অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ আইএমএফের কাঠামোগত সমন্বয় তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে লেনদেন ভারসাম্য প্রশমিত করার জন্য পুরো অর্থনীতির বাজারমুখীন কাঠামোর সংস্কার শুরু করে। সংস্কারগুলো হয় তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে— বাণিজ্য উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিনিয়ন্ত্রিতকরণ।
এখানে দুটো লক্ষণীয় বিষয়। যেকোনো অর্থনৈতিক ফলাফলে দুটো শর্ত ক্রিয়াশীল থাকে। একটি প্রয়োজনীয় শর্ত ও অন্যটি দরকারি শর্ত। ধরে নেয়া হয়েছিল, বাজার ব্যবস্থাই দরকারি শর্ত তথা গণতান্ত্রিকতা তৈরি করবে। তাত্ত্বিক কাঠামোটি ছিল যে, যদি বাজারমুখীন সংস্কার করা যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশে এ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তথাকথিত স্বৈরাচারী সরকারের মাধ্যমে। এ সরকারগুলোর বৈধতার সংকট ছিল; ছিল জনগণ থেকে বিযুক্ত। এরা মূলত বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের রাজনৈতিক কাঠামো ও নেটওয়ার্ক পুরোমাত্রাই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। দুর্নীতি ও লুটপাটের অবাধ বিস্তার হয়েছিল। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর টেকসই অর্থনৈতিক বিবর্তন অর্জনকারী দেশগুলোর সংখ্যা নগণ্য থেকেছে।
প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর টেকসই অর্থনৈতিক বিবর্তন অর্জনকারী দেশগুলোর যেসব নীতিকাঠামো গ্রহণ করা হয়েছিল, সে ধরনের প্রবণতা আলোচ্য সময়ে লক্ষ করা গেছে কি? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর টেকসই অর্থনৈতিক বিবর্তন অর্জনকারী দেশগুলো সৃজনশীলতার যে পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসলগ্নতায় নিবিষ্ট থেকে দেশোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন করেছে কি? অর্থাৎ টেকসই রূপান্তরে রাষ্ট্র শুধু নিজেকে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির মধ্যে সীমিত করেনি। রাষ্ট্র যেমন একদিকে পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনা প্রদান করেছে, তেমনি যদি পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনার অপব্যবহার হয়েছে, রাষ্ট্র কঠোর হাতে পুঁজিপতিদের দমন করেছে কি? প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে কি? রাজনৈতিক ব্যবস্থা কতটুকু অন্তর্ভুক্ত ছিল?
দুই
এ সময় বাংলাদেশের কৃষিতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। পাশাপাশি শিল্প ও শ্রমেরও ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়। কারণ এ সময় আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে বাংলাদেশের পুঁজির এক ধরনের সংশ্লিষ্টতা দেখা দেয়। অনেকেই বিষয়টিকে বিশ্বায়নের শুরুর সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। এদিকে বাংলাদেশে পুঁজির গঠন, পুঁজির বিকাশ, শ্রমের বিকাশ ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটেছে।
কৃষিতেও বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয়। বীজ, পানি ও সার ব্যবহারের পরিবর্তনের মাধ্যমে তথাকথিত সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়। এ সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে। কৃষি থেকে বড় অংশের উদ্বৃত্ত শ্রমিক অন্যদিকে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেছে এবং পরবর্তীতে প্রশ্নটি আরো বড় আকার ধারণ করেছে যে, পরিবর্তনটি আসলে কতটা টেকসই? কৃষিক্ষেত্রে শুধু দানাদার শস্যকেন্দ্রিক পরিবর্তন হয়েছে। প্রধানত ধানের ক্ষেত্রে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি এবং রাসায়নিক সার। অর্থাৎ এ সময়গুলোয় বাংলাদেশের জন্য উপযোগী প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পরবর্তীতে মাটির নিচে ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ কমে গেছে। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বেড়েছে। তবে সেই সঙ্গে উৎপাদন খরচ যেমন বেড়েছে, তেমনি মাটির উর্বরাশক্তি হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া এককেন্দ্রিকতা হওয়ার ফলে কৃষির বহুমুখীকরণ সম্ভব হয়নি। এদিকে দ্বিতীয় পরিবর্তনটি আজ পর্যন্ত বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। জমির ফ্রাগমেন্টেশন হয়েছে। এক জমি ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবারগতভাবে ভূমি বণ্টন হওয়ায় ভূমিগুলো ক্রমে খণ্ডিত হয়েছে। এমন খণ্ড খণ্ড ভাগে কৃষিজমি বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ভবিষ্যতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের উৎপাদনশীলতা বেশি। কিন্তু উৎপাদনশীলতা বেশি থাকলেও তারা এমন পর্যায়ের উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পারছে না, যার মাধ্যমে নতুন জমি কিনতে পারবে এবং তাদের খামার বড় হচ্ছে না। এ অবস্থায় জমিগুলো ক্ষুদ্র কৃষকের হাতে নয়, বরং কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত নয় এমন লোকদের কাছে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রকৃত কৃষক যদি কৃষিজমির মালিক হতেন, তাহলে কৃষিকাজে উৎপাদনশীলতার বড় রকমের পরিবর্তন ঘটত।
একটা সময় শিল্প মালিক খুঁজে না পাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। তবে সেখান থেকেও বিকল্প তৈরি হয়নি। বরং বাংলাদেশে মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় লুটতরাজের মাধ্যমে সম্পদশালী হয়েছে। এদিকে পুঁজির জোগানের অভাবে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। তবে এ সময় বাংলাদেশে নতুন শিল্প হিসেবে পোশাক শিল্পের আবির্ভাব ঘটে, যা বড় ধরনের আলোচনার দাবিদার। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিল্পটি নতুন হলেও আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ দেশে শিল্প বিপ্লবের সূচনায় ছিল পোশাক শিল্প।
বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের আবির্ভাবের পেছনে কতগুলো বিষয় কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেমন কাজ করেছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বড় ভূমিকা রেখেছে। আবার রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষক ব্যবস্থার কারণেও পরিবর্তন ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তত্কালে মাল্টি ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট ব্যবস্থা ছিল, যার মাধ্যমে কোটা ব্যবস্থা চালু ছিল এবং প্রত্যেকটি দেশের জন্য নির্দিষ্টকরণ করা ছিল যে কোন কোন দেশ থেকে তারা কতটুকু আমদানি করবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমের ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ পরে জাপান থেকে শ্রমঘন শিল্প দক্ষিণ কোরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়া যখন তাদের কোটার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন শিল্পটা বাংলাদেশে আসে। এ পরিবর্তনে রাষ্ট্র বড় ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ওষুধ শিল্পে বড় ধরনের বিকাশ ঘটে। রাষ্ট্র এখানেও তার সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।
তবে প্রকৃত খাতের উদ্বৃত্ত থেকে যেমন নতুন শিল্পের কিংবা নতুন কর্মসংস্থান বিকাশ ঘটে, তেমনি আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আরো একটি বিকাশ প্রক্রিয়া ঘটমান থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটনাটা তেমন সুখবর হয় না। কারণ তখন বাংলাদেশে পুঁজির জোগানের জন্য শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থার মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু লক্ষ করা হয়, ওই ব্যাংক ও শিল্প সংস্থাগুলো বড় রকমের ঋণ ঘাটতিতে পরিণত হচ্ছে। যার মানে এখানকার ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো (ডিএফআই) নতুন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখেনি। বরং ঋণ ফেরত না দেয়ার ফলে ব্যাংকঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পগুলো রুগ্ণ বলে ঘোষিত হয়।
একটি সহজ কায়দার প্রযুক্তি এসে কৃষিতে এক ধরনের বিকাশ ঘটাল, অন্যদিকে শ্রমিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রমঘন শিল্প তৈরি হলো। কৃষি ও শিল্পে প্রযুক্তির দুই রকমের বিকাশ আমরা লক্ষ করলাম। কৃষি, পোশাক শিল্পের সঙ্গে তখন ওষুধ শিল্পেরও শুরু হলো। ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবস্থাপনাগত কায়দার মাধ্যমে এগুলো দেশীয় পুঁজিপতিদের কাছে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং কোম্পানির ম্যানেজাররা ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তায় পরিণত হচ্ছেন।
কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত শ্রমিক নিজের টিকে থাকার সংগ্রামে বাধ্য হলো শহরমুখীন হতে। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন তথা কম খরচের শ্রমের দিকে শ্রমঘন শিল্পের প্রতিস্থাপন রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পোশাক শিল্পে ব্যাপক আকারে নারীর কর্মসংস্থান তৈরি করল। অন্যদিকে তেলপ্রাপ্ত দেশে নতুন শ্রমিক নিয়োজনে কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত শ্রমিক বিদেশমুখীন হলো। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক বড় পরিবর্তনের যাত্রা হলো। গ্রামীণ দারিদ্র্য কমতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ব্যয় বাড়াতে থাকল। মোট দেশজ উৎপাদনও বাড়তে থাকল। এদিকে শ্রমদক্ষতার ঘাটতি কিন্তু রয়েই গেল। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ছিল সীমিত। সীমিত অভ্যন্তরীণ সম্পদের গুণগত ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করা হলো না। ফলে উচ্চ উৎপাদনশীলতাসম্পন্ন শ্রমশক্তিও তৈরি করা সম্ভব হলো না। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশোপযোগী প্রযুক্তির বিকাশের সীমাবদ্ধতার কারণেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টাও অনুপস্থিত।
তিন
ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ নির্মাণে এ সময়ের অভিজ্ঞতা কতগুলো প্রশ্নের যেমন উদ্রেক করে, তেমনি সমাধানও প্রদান করে। কী কারণে কৃষিতে, শিল্পে এ পরিবর্তন ঘটল? এ পরিবর্তন কি নীতি-কাঠামোর পরিবর্তন তথা বেসরকারীকরণ, উদারীকরণ ও বিনিয়ন্ত্রণের কারণে ঘটল, না অন্য কারণে? যদি কেউ যুক্তি দেয় যে, বাংলাদেশে এ বিকাশমানতার ক্ষেত্রে সস্তা শ্রম একটি বড় রকমের পরিচালক হিসেবে কাজ করেছে, তাহলে প্রশ্ন আসে অন্যান্য শিল্পের বিকাশ হলো না কেন? কিংবা এ সময় থেকে কেন অভিবাসন শুরু হলো? এক্ষেত্রে কার ভূমিকা কেমন? আবার কেনইবা ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো (ডিএফআই) যে ঋণ দিল তা দিয়ে বড় শিল্প গড়ে উঠল না, বরং রুগ্ণ শিল্পে পরিণত হলো? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুবই জরুরি।
অভিজ্ঞতার আলোকে নীতি প্রণয়ন করা সৃজনশীলতার প্রকাশ। কেতাবি কায়দায় অন্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের উপযোগী নীতি প্রণয়ন যে জরুরি— এ অভিজ্ঞতাগুলো তা নির্দেশ করে। পোশাক শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে কতগুলো প্রবণতা খুবই পরিষ্কার। প্রথমত. যেকোনো শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত প্রয়োজন হয়— পুঁজির জোগান, প্রশিক্ষিত জনবল বা তার সঙ্গে প্রযুক্তির সংমিশ্রণ এবং বাজারের অভিগ্যমতা বা উৎপাদিত পণ্যের বাজার থাকা। পোশাক শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে তথাকথিত সংস্কারের একটিও কাজে লাগেনি, বরং উল্টো চিত্র লক্ষণীয়। বাজারের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তত্কালীন মাল্টিফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকার কারণে উৎপাদিত পণ্যের মান যদি প্রতিযোগিতামূলক হয় এবং পণ্যটি যদি বাজারে টিকে থাকতে পারে, তাহলে পণ্যটির বাজার নিশ্চিত থাকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স বা জিএসপি বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা। জিএসপির আওতায় উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নত দেশে রফতানি পণ্যের শুল্ক ও কোটায় ছাড় দেয়া হয়।
পোশাক শিল্পে রাষ্ট্রের বড় ধরনের ভূমিকা লক্ষণীয়। বর্তমানে বাংলাদেশে যে পোশাক শিল্পের ভিত তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশ পোশাক শিল্পের ভিত যারা রচনা করেছেন, তারা দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্র গ্যারান্টি দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াকে। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে তারা সেই প্রশিক্ষণটা নিয়ে এসেছেন— কীভাবে শ্রমকে ব্যবহার করে প্রযুক্তির মধ্যে এনে মানযুক্ত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাসম্পন্ন পণ্য ও উদ্বৃত্ত তৈরি করা যায়। লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্পের তুলনায় পোশাক শিল্পের শ্রম ব্যবস্থাপনাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরবর্তীতে লক্ষ করা যায়, তাদের শ্রম অধিকারও খুবই নগণ্য। কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থাপনার অধীনে তারা কাজ করতে বাধ্য হয়। শ্রমিকদের মজুরি কম হলেও মনিটরিংয়ের জন্য পোশাক কারখানাগুলোয় বড় অংকের অর্থ ব্যয় করা হয়। পোশাক কারখানায় শ্রম ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি অর্থাৎ শ্রমিকের থেকে কীভাবে উদ্বৃত্ত তৈরি করতে হয়, তা কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্প-কারখানায় লক্ষণীয় নয়। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে পুঁজির প্রবাহ। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে দেখা যায়, পুঁজি যখন উদ্যোক্তার কাছে গেছে তখন তা আর ফেরত আসেনি, বরং শিল্পটি রুগ্ণ শিল্পে পরিণত হয়েছে। পুঁজি ফেরত আনার ক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়া হয়েছে। পুুঁজির প্রবাহ যাতে চলমান ও বর্তমান থাকে, সেজন্য ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট পদ্ধতি চালু করা হয়। অর্থাৎ কারখানা ক্রেতার কাছ থেকে কাজের আদেশ আসছে, তার বিপরীতে ব্যাংক কাঁচামাল কেনার অর্থ দিচ্ছে, কাঁচামাল আসছে, পুরো কারখানাটিকে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে, উৎপাদন হচ্ছে, উৎপাদিত পণ্য আবার রফতানি করা হচ্ছে, রফতানির পর অবশিষ্টাংশ মালিকের কাছে যাচ্ছে। পুঁজি গতিময়তা পাচ্ছে। শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকা হয়নি, রাষ্ট্র বিভিন্ন রকমের প্রণোদনা তৈরি করেছে। নীতিকাঠামোগত প্রণোদনা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে আর্থিক প্রণোদনা। রাষ্ট্র এখানে পৃষ্ঠপোষকতা বা রেন্ট বণ্টন করেছে। রাষ্ট্রের এ পৃষ্ঠপোষকতা উৎপাদন খাতে ব্যয়িত হয়েছে। যেহেতু তা বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার আলোকে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়ে করা হয়েছে। ফলে খেলাপি ঋণ বাড়েনি। অনুৎপাদনশীল খাতে পুঁজির প্রবাহ স্থানান্তরিত হয়নি।
ওষুধ শিল্প খাতের একই অভিজ্ঞতা। রাষ্ট্র ওষুধনীতির মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য ভূমিকা রেখেছে। রাষ্ট্র নিশ্চিত করেছে দেশীয় শিল্পের ওষুধ নীতির মাধ্যমে যে সংস্কারগুলো করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রথম জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়ন করে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কর্তৃক বিপুলভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়। এ ওষুধ নীতির ফলে বাংলাদেশের ওষুধের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং মান উন্নত হয়, ওষুধের দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমদানি নির্ভরতা কমে দেশ ওষুধের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে শুরু করে, ওষুধ সেক্টরে বিদেশী আধিপত্য কমে আসে, দেশীয় ওষুধ কোম্পানিগুলো আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বৃহদাকার কারখানা স্থাপন করতে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ওষুধ সেক্টরের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এবং এক সময়কার ওষুধ আমদানিকারী দেশটি ওষুধ রফতানিকারী দেশে পরিণত হয়। ১৯৮২ সালে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বাজারজাত বন্ধ করে দেয়া হয়। স্বাস্থ্যসেবার প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় ওষুধের মূল্য তুলনামূলকভাবে কম এবং ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার নাগালে রাখা সম্ভব হয়।
বাংলাদেশকে যদি শিল্পমুখীন করতে হয় তাহলে কতগুলো বিষয় লক্ষণীয়। পোশাক শিল্পে রফতানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি শিল্পের ওপর নির্ভরশীল ক্রমে বেড়ে চলছে। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে লক্ষ করা হয়নি, কেন পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটল কিংবা ওষুধ শিল্পের বিকাশ ঘটল কিন্তু অন্য শিল্পের বিকাশ ঘটল না। অতীতের থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করার ফলে বাংলাদেশের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে না। বহুমুখীকরণ সম্ভব হচ্ছে না। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়নি। নীতির ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা দেখানো হয়নি। অন্যদিকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা হয়নি। পরবর্তীতে লক্ষ করি, পোশাক শিল্পের ম্যানেজার পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তিকে অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। অর্থাৎ সৃজনশীল ও দেশোপযোগী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র কীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করবে এবং পুঁজি গঠনে সহায়তা করবে, যাতে করে পুঁজি আবার খেলাপি ঋণে পরিণত না হয়, শৃঙ্খলা বজায় থাকে— এটা যেমন করা হয়নি; দ্বিতীয়ত. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক রেখে দেশের উপযোগী করে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেনি। তৃতীয়ত. শ্রমের দক্ষতা বিকাশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকে জোর দেয়া হয়নি। শ্রমের ওপর রাষ্ট্র কখনই জোর দেয়নি। ফলে দিন দিন বৈষম্য বেড়েই চলছে। মূলধন থেকে যে প্রাপ্তি বা রিটার্ন পুঁজিপতিরা পেয়েছেন, শ্রমিকরা অনেক কম পেয়েছেন। শ্রম অধিকারও সীমিত। বাংলাদেশের রূপকার শ্রমিকরা বঞ্চিত থাকছেন।
বাংলাদেশ বিনির্মাণে মানুষের ইচ্ছা ও অভিযোজন শক্তি বিশাল। কৃষিতে, পোশাক শিল্পে ও অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষণীয়। ফলে দারিদ্র্য পরিস্থিতি হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের আগমন। নারীরা উৎপাদনশীল ও রিপ্রডাক্টিভ— দুই ক্ষেত্রেই বড় অবদান রাখছেন। গ্রাম থেকে নারীরা শহরে এসেছেন, পোশাক শিল্পের উত্তরণে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তির উচ্চতর দক্ষতা বৃদ্ধির বড় ধরনের ঘাটতি রয়ে গেছে। তাদের অধিকারহীনতা যেমন জাজ্বল্যমান, তেমনি তাদের পুরুষতান্ত্রিক সহিংসতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।
বেসরকারীকরণ কোনো আশাপ্রদ ফল দেয়নি। অনেক কম দামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে ওগুলোকে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। অধিকাংশ চালু করা হয়নি বা রুগ্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। এরই আবর্তে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প পাট খাত তলিয়ে গেছে। বিশ্বব্যাংকের সংস্কার কর্মসূচির আওতায় পাট শিল্প হারিয়ে যায়। অন্যদিকে আশির দশকে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় সম্পদের মালিকানার মাধ্যমে গোষ্ঠীতন্ত্র প্রক্রিয়া বেগবান হয়।
বিনিয়ন্ত্রিতকরণ প্রক্রিয়াও ভোক্তা বা উদ্যোক্তাকে লাভবান না করে গোষ্ঠীতন্ত্র প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করেছে। ব্যাংকে ঋণখেলাপির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় সেখানে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হলো। যুক্তি দেয়া হলো, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকগুলো বিনিয়ন্ত্রিত করলে এবং ব্যক্তিখাতে ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি দিলে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং সুদের হার কমবে। বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে ব্যাপক পরিসরে আর্থিক খাতের সংস্কার কর্মসূচি চালু হলো। বেসরকারীকরণ হলো এবং নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হলো। কিন্তু সঙ্গে দেখা গেল, এতে সুদের হার কমেনি। ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে এবং ক্ষমতা মাধ্যমে পুঁজির আদিম সঞ্চায়ন ঘটে— এ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির দুর্বলতা ছিল। কেতাবি কায়দায় তারা মনে করেছিল, যদি সরকারি ব্যাংক কমিয়ে ফেলা যায় এবং ব্যক্তিখাতে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে সুদের হার কমবে। কিন্তু সুদের হার কমেনি বরং বেড়ে যায়। এর মানে রাষ্ট্র শৃঙ্খলা আনতে পারেনি, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় লুটপাট আশির দশকের শেষের দিকে আরো বেড়ে যায়। শ্রমশক্তির সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে পুঁজি গঠন— এটাই যে মূলত পুুঁজি গঠনের মূলশক্তি, এ বিষয়টি শুরু হলেও ধাক্কাপ্রাপ্ত হয়।
চার
অভিবাসনের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন, অর্থাৎ কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমিক বিশেষ করে পোশাক শিল্পে নারীর নিয়োজন, শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়ার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন, কৃষির পরিবর্তন এবং শিল্পমুখীনতা— এসবের পরও আশির দশকের শেষের দিকে কেন মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হলো— এ প্রশ্নটিরও উত্তর খোঁজা খুবই জরুরি।
বাংলাদেশের ইতিহাসলগ্নতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ধারা অনুধাবন প্রয়োজনীয়। ব্রিটিশ আমলে অধিকাংশ মানুষ অল্পসংখ্যক মানুষের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েছে। এ অল্পসংখ্যক মানুষ হিন্দু জমিদার বা ব্রাহ্মণবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে অধিকাংশ মানুষ নিষ্পেষিত ছিল। তারা ধর্মীয়ভাবে মুসলিম ছিল। যদিও বাংলায় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় করের হার কম ছিল; কিন্তু বাংলার অধিকাংশই ছিল ঋণগ্রস্ত। তাই প্রথম নির্বাচনে মুসলিম লীগকে নির্বাচিত না করে কৃষক প্রজা পার্টিকে নির্বাচিত করেছিল। কারণ তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ঋণগ্রস্ততা, নিপীড়ন থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছিল। তত্কালীন ব্রিটিশ বাংলার পরিবর্তনে লক্ষ করা যায়, অধিকাংশ মানুষ নির্যাতন থেকে মুক্তি খুঁজছিল। অনেকে এটাকে ধর্মীয়ভিত্তিক হিসেবে বলার চেষ্টা করে থাকেন। তবে তখন এ মানুষগুলো নিপীড়িত হচ্ছিল এবং তত্কালীন পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে নিপীড়ন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল।
এ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের নিপীড়ন ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি আবার অন্যদিকে মধ্যবর্তী শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা এবং অগ্রগতির এই যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক— এর প্রতস্ফুিরণ ঘটে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর দেখা যায়, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে পাঞ্জাবি মুসলমানের প্রশাসনিক ও পুঁজি সঞ্চয়নের ক্ষেত্রে যে বড় রকমের দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছিল, এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছিল। সামরিক শাসন অনেক বছর ধরে চলছিল। অধিকাংশ মানুষ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেনি। অর্থাৎ তাদের স্বাধিকার স্থাপিত হয়নি। অধিকাংশ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক অধিকার নিষ্পেষণের একটা পর্যায় গিয়ে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক থেকে উত্তরণ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। রাষ্ট্র যখনই নিপীড়ক হয়েছে, তখনই সমাজের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশী মানুষের মধ্যে সংগ্রাম করে নিপীড়ক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্থানটা মজ্জাগত। যদিও পুঁজিবাদ ব্যক্তিসংলগ্নতা বা একব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ার দিকে তাড়িত করে কিংবা পরিবারগুলো ভেঙে ভেঙে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে চলে যাচ্ছে, তবু নিপীড়ক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামটা জারি রয়েছে।
১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বৈধতার সংকট ছিল। ১৯৭১ সালে যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতা নিয়েছিল, তাদের পেছনে বাংলাদেশের মানুষের সমর্থন ছিল। ফলে দলটির বৈধতা ছিল। কিন্তু অন্তর্ভুক্তির অনুপস্থিতি, জনগণের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা এবং নাগরিক রাষ্ট্র গঠনের ব্যর্থতা ও এককেন্দ্রিকতার ফলে একটা ছেদ ঘটে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত এ ধরনের একটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তত্কালীন শাসকরা বিভিন্ন রকমের ফ্যাকশন নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্লাটফর্ম তৈরির চেষ্টা করেন এবং কতগুলো কালেকটিভ কর্মসূচিও চালু করেন। যেমন- খাল কাটা কর্মসূচি, গণশিক্ষা অভিযান ইত্যাদি। তেমনি শিল্প খাতে পোশাক শিল্পের বিকাশে অবদান রাখে। একইভাবে বিদেশে শ্রমশক্তি রফতানির ব্যবস্থা করে। কিন্তু আরো একটি সহিংস ঘটনার মাধ্যমে ওই রাজনৈতিক বন্দোবস্ত স্থিতিশীলতার দিকে যাওয়ার পথেই ছেদ ঘটে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যহীনতা ও অস্থিতিশীলতার মধ্যেই সহিংস হত্যা ঘটে। এরপর একটা পর্যায়ে সামরিক শাসক আবির্ভূত হয়, যার মাধ্যমে একটি দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি তৈরি হয়। মানুষের টিকে থাকার বাধ্যবাধকতা থেকে উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের মাধ্যমে একদিকে কৃষি ও শিল্পের এক ধরনের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে বৈধতার অভাবে বিভিন্ন রকমের চেষ্টা ও নিরীক্ষা চালু থাকে। তার মধ্যে বড় রকমের একটি নিরীক্ষা শুরু হয় উপজেলা তৈরির মাধ্যমে। কিন্তু বৈধতা না থাকার কারণে সেই অভিজ্ঞতা কাঙ্ক্ষিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তৈরি করেনি। প্রশাসনিক নতুন ধাপ যুক্ত হলেও প্রশাসনের আরো কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে, বরং তা গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত দুর্নীতির একটি কাঠামো তৈরি করে এবং লুটপাট সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। পাকিস্তানি সামরিক শাসক তৎকালীন ওভারডেভেলপড আমলাতন্ত্রকে ক্ষমতায়িত করার জন্য ব্রিটিশ আমলে স্থানীয় পর্যায়ের জেলা পরিষদ বা অন্যান্য যেসকল ব্যবস্থা ছিল, সেগুলোকে তুলে দিয়ে তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ওপর আমলাতান্ত্রিক শক্তির যে প্রকাশ ঘটিয়েছিল, সে জায়গা থেকে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী বৈধতা অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ গঠন করার জন্য একটা চেষ্টা করে। স্থানীয় পরিষদ গঠনের চেষ্টা করলেও দুর্নীতির বিকাশ সম্প্রসারিত হয়। স্থানীয় পরিষদ তখনই কাজ করবে যদি ডিভলুয়েশন ঘটে। অর্থাৎ ডিসেন্ট্রালাইজেশন করলেই হবে না, ডিভলুয়েশন করতে হবে। একদিকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কেন্দ্রীকরণ চালু ছিল, অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা নিশ্চিত করা ছিল, অন্যদিকে স্থানীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সমর্থকদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা সর্বজনীন পাবলিক ইউটিলিটি নিশ্চিত করা। এ দ্বন্দ্ব এখনো বিরাজমান।
বৈধতার সংকট তৈরি হওয়া এবং একটা পর্যায়ে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কারণে একটি আন্দোলন গড়ে উঠছিল। আন্দোলনে বড় রকমের ভূমিকা রেখেছিল এখানকার মধ্যবর্তী শ্রেণী। ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণ পেশাজীবীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ার ফলে মানুষের মধ্যে একটি চুক্তি তৈরি হলো— কীভাবে নতুন রকমের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি হতে পারে। নিপীড়নকারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে নাগরিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি চাপ সৃষ্টি করা হলো।
বণিক বার্তা;বিশেষ সংখ্যা/উন্নয়ন অমনিবাস ২;২০:১৯:০০ মিনিট, আগস্ট ১৩, ২০১৮